শিক্ষক দিবস আসে, শিক্ষক দিবস (Teacher’s Day) যায়। কোনও বছর ৫ সেপ্টেম্বর হাজির হই নেতাজি ইন্ডোরে, কোনও বছর মন্ত্রী বা বিধায়কের দেওয়া সংবর্ধনা সভায়, কোনও বছর বিদ্যায়তনে ছাত্রছাত্রীদের অনুষ্ঠানমঞ্চে। এমন করে কেটে গেল বারো বছর… চব্বিশ বছর… ছত্রিশ বছর। বুঝতে পারি না শিক্ষক হয়ে উঠতে পেরেছি কি না অথবা এই শিক্ষক দিবস আমার জন্যই আয়োজিত হয় কি না!
‘শিক্ষক’ শব্দের অর্থ যেখানে শাসনকর্তা, সেখানে তবু হালে পানি পাওয়া যায়। কিন্তু শিক্ষাদাতা অর্থে আত্মবিশ্বাসে যে একটু টান পড়ে না, তা আর অস্বীকারের উপায় কী! ‘আত্মবিশ্বাস’ শব্দটা লেখার সময় আচমকা ছাত্রজীবনের একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। আমাদের গ্রামের হাইস্কুলে নাইন-টেনে জীবনবিজ্ঞান ক্লাস নিতেন মানসবাবু। তাঁর পড়ানো্র গুণে সকলে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে থাকত, ক্লাসে বিরাজ করত পিন পতনের নিস্তব্ধতা। সেই মুগ্ধতা এমনই যে বছরের পর বছর ধরে ছেলেমেয়েদের প্রিয় বিষয় হয়ে উঠেছিল জীবনবিজ্ঞান এবং মাধ্যমিকের মার্কশিটে দেখা যেত কম-বেশি সকলেই জীবন বিজ্ঞানে সর্বাধিক নম্বর পেয়েছে। একদিন স্যরকে সাহস করে জিজ্ঞাসা করে উত্তর পেয়েছিলাম, ‘সফল শিক্ষক হওয়ার রসায়ন লুকিয়ে রয়েছে দু’টি বিষয়ে— এক, যে বিষয় পড়াবে সেই বিষয়ে গভীর জ্ঞান এবং দুই, আত্মবিশ্বাস।’ সেদিন স্যর ‘আত্মবিশ্বাস’ বলতে ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছিলেন সম্যক বুঝিনি। আজ নিজের বিষয়ে ‘গভীর জ্ঞান’-এর অভাবে যখন হীনমন্যতায় ভুগি তখন বুঝতে পারি গভীর জ্ঞান-ই নিয়ে আসতে পারে আত্মবিশ্বাস।
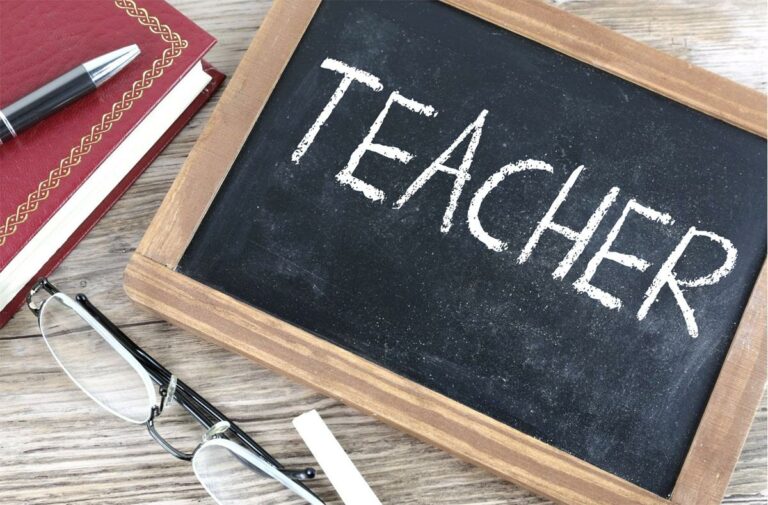
মধুসূদন সংহিতা জানাচ্ছে, জ্ঞান বহির্জগৎ সম্বন্ধীয় বিচারশক্তি। জ্ঞান দান করা যায়। জ্ঞানী সত্যদর্শক ও সত্যপ্রকাশক। তাহলে গভীর জ্ঞান রয়েছে যে শিক্ষকের, তাঁর জ্ঞান দানের মাধ্যমে শিক্ষাদাতা হয়ে ওঠায় কোনও বাধা নেই। কিন্তু জ্ঞানের যেহেতু সীমা-পরিসীমা নেই এবং জ্ঞানার্জনও যেখানে ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, তাই শিক্ষকের পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজন নিজের বিষয়ে অবিরাম এবং নিরন্তর চর্চা। আর দান যেহেতু অর্পণ বা সম্প্রদান, তাই নিজের ভাণ্ডারের পূর্ণতা নিশ্চয়ই দানের প্রাথমিক শর্ত। না হলে দান করা কিন্তু বেজায় মুশকিল! চর্চার অভাবে অনেক সময় যখন মরচে পড়া ধারণা নিয়ে ক্লাসে পড়াতে গিয়েছি তখনই হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি জ্ঞান দান করতে না-পারার ব্যর্থতা এবং প্রকৃত শিক্ষক হয়ে উঠতে না-পারার মর্মব্যথা।
আরও পড়ুন: ছাত্র-শিক্ষকের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ কোনও নির্দিষ্ট দিবস-কেন্দ্রিক হতে পারে না
শিক্ষককে সত্যদ্রষ্টা হতে হবে— কথাটা বলা যত সহজ, বাস্তবে কিন্তু বিষয়টা ততটা সহজ নয়। সত্য বিষয়টা এমনিতেই ভারি গোলমেলে, তার উপরে এই পোস্ট-ট্রুথ জমানায়, যখন গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো সোশ্যাল মিডিয়া-বাহিত ফেক নিউজের প্লাবন প্রতিনিয়ত আছড়ে পড়ছে, তখন সত্যকে ঠিক মতো চিহ্নিত করতে পারাই একটা বেশ চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার। উন্নাসিকতায় আক্রান্ত না হয়ে, সমস্ত রকম সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে, সঙ্কীর্ণতার প্রাচীর টপকে, দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে, অসাম্প্রদায়িক-উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সত্যকে দেখতে এবং দেখাতে গেলে শিক্ষিত মনন না হলে কিন্তু চলবে না। মনে রাখতে হবে, ‘সত্য যে কঠিন’। আর সেই শিক্ষকই ছাত্রের কাছে আদর্শস্বরূপ হয়ে ওঠেন, যিনি জ্ঞানতাপস তো বটেই, সাথে সাথে সত্যদ্রষ্টাও।
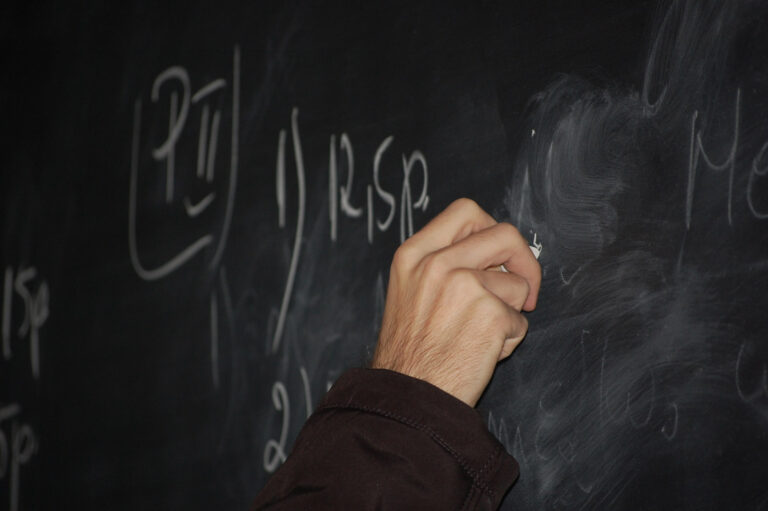
প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিকস্তরে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষককে ভালবাসার মূল কারণ বোধহয় শিক্ষকের প্রতি এক গভীর আস্থা— স্যর বা ম্যাডাম/মিস/দিদিমণি সব জানেন। জানার আগ্রহই শিক্ষার্থীকে ঠেলে নিয়ে যায় শিক্ষকের কাছে। কেউ শ্রদ্ধাবনত চিত্তে আন্তরিকতার সঙ্গে কিছু শিখতে চাইলে শিক্ষকও শেখানোর ক্ষেত্রে ভিতর থেকে সাড়া পান এবং নিজের ভিতরে জেগে ওঠা সেই আন্তরিক আগ্রহের কারণে শিক্ষার্থীর প্রতি স্নেহশীল হয়ে ওঠেন, উপরন্তু তার জন্য মায়া-মমতা-ভালবাসায় আপ্লুত হতে থাকেন। এভাবেই ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে গড়ে ওঠে শ্রদ্ধা-ভালবাসার অটুট বন্ধন, যা তৈরি করে দেয় শিক্ষক দিবসের ভিত।
শিক্ষক দিবস এমন এক দিন যখন গ্রহীতা দাতার ভূমিকা পালন করার সুযোগ পায়। উঁচু ক্লাসের শিক্ষার্থীরা নিজের বিদ্যালয়ে নিচু ক্লাসে শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে পাঠদান করে। এভাবে কোথাও যেন একটা শিক্ষাদানের বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে। স্বপ্ন ছোঁয়ার এই দিনে কত শিক্ষার্থীর মনে জন্ম নেয় সঙ্কল্প এবং প্রতিজ্ঞা, যা সত্যই তাদের পরবর্তী জীবনে করে তোলে প্রকৃত শিক্ষক।

প্রাক-গুগল যুগে ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ সম্পর্কে বক্তব্য রাখার জন্য বক্তৃতা তৈরি করতে গিয়ে শিক্ষক মহাশয়রা বেশ সমস্যায় পড়ে যেতেন। রাধাকৃষ্ণণ সম্পর্কিত তথ্য সবসময় হাতের কাছে মজুত থাকত না, খুব কম রচনা বইয়ে সে সব পাওয়া যেত। কিন্তু তাতে শিক্ষক দিবসের উৎসাহ-উদ্দীপনায় কোনও ভাঁটা পড়েনি। আসলে ১ জুলাই-এর চিকিৎসক দিবস যেমন অনেকাংশে ঢাকা পড়েছে পশ্চিমবঙ্গের রূপকার ভারতরত্ন ডা. বিধানচন্দ্র রায় নামক বিরাট মহীরুহের আড়ালে, শিক্ষক দিবসের ব্যাপারটা ঠিক তেমন নয়। ৫ সেপ্টেম্বর আগে শিক্ষক দিবস, পরে ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের জন্মদিন। অন্তত এ বঙ্গে তো বটেই। অবশ্য তাতে রাধাকৃষ্ণণের এতটুকু মর্যাদাহানি হয়নি, তিনি আরও বেশি মহিমান্বিত হয়ে উঠেছেন।

বিগত দু’বছর ২০-২১-এর করোনাকালে শিক্ষক দিবস ছিল নিষ্প্রাণ। শিক্ষার্থীদের কচি-কাঁচা মুখগুলো হয়ে পড়েছিল নিষ্প্রভ, অনুজ্জ্বল। তাদের প্রিয় শিক্ষকরা ছিলেন ভার্চুয়াল। অনলাইন পাঠের বিরক্তিকর একঘেয়েমিতে ক্লান্ত হতে হতে ছটপটে তরতাজা প্রাণগুলো ক্রমশ হতাশ হয়ে উঠেছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের আনন্দের মধ্যে ঘনিয়ে উঠেছিল অনিশ্চয়তার মেঘ। সেসময়ে দাঁড়িয়ে সে মেঘ যে নিকট-ভবিষ্যতে কেটে যাবে, সে আশাটুকু করার ব্যাপারেও আত্মবিশ্বাস টাল খেয়ে যাচ্ছিল। তবু মানবসমাজ আশায় বুক বেঁধেছিল— সব মন্দেরই একটা শেষ আছে।
গতানুগতিক শিক্ষার বাইরে গিয়ে, জীবনের সবচেয়ে বড় শিক্ষক প্রকৃতির কাছ থেকে যে প্রকৃতিপাঠের মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ করবে, সে সুযোগ থেকেও শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত ছিল করোনাকালের দু’বছর। সুস্থতা এবং সুস্বাস্থ্যের খাতিরে প্রকৃতিরাজ্যে নিজের ইচ্ছামতো তারা ঘুরে বেড়াতে পারেনি। তাদের পায়ে বেড়ি পরিয়ে রাখা হয়েছিল। শিক্ষার লেনদেন না থাকায় খুব স্বাভাবিকভাবে শিক্ষক দিবসও হয়ে উঠেছিল প্রাণহীন-আনুষ্ঠানিক। আসলে যত যা-ই হোক শ্রদ্ধা-সম্মান-ভালবাসার পারস্পরিক মেলবন্ধন তো আর ঠিক ভার্চুয়াল হয় না! নিছক উদযাপন হয়তো করা যায়, কিন্তু তার মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় না।
সুস্থতা এবং সুস্বাস্থ্যের খাতিরে প্রকৃতিরাজ্যে নিজের ইচ্ছামতো তারা ঘুরে বেড়াতে পারেনি। তাদের পায়ে বেড়ি পরিয়ে রাখা হয়েছিল। শিক্ষার লেনদেন না থাকায় খুব স্বাভাবিকভাবে শিক্ষক দিবসও হয়ে উঠেছিল প্রাণহীন-আনুষ্ঠানিক।
গতবছর শিক্ষক দিবস তা-ই হয়ে উঠতে পারত বন্ধনমুক্তির প্রকৃত উদযাপন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তা সম্ভবপর হয়ে উঠতে পারেনি মূলত দু’টি কারণে— একটি ভিতরের কারণ, অন্যটি বাইরের।
প্রলম্বিত গ্রীষ্মাবকাশের কারণে শিক্ষাবর্ষের নকশায় শিক্ষাবিভাগ যে পরিবর্তন আনতে একপ্রকার বাধ্য হয়েছে, তাতে প্রাথমিক-মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় পর্বের পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল শিক্ষক দিবস। ফলে শিক্ষক দিবস উদযাপনের যে মূল ক্ষেত্র বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ, সেখানে গতবছর পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে তা পালন করা হয়ে উঠেছিল প্রায় অসম্ভব। সঠিক পরিকল্পনার অভাবজনিত বাইরের এই কারণের তুলনায় ভিতরের কারণ কিন্তু ছিল যথেষ্ট চিন্তা উদ্রেককারী। তা অবশ্য এ বছরেও এতটুকু বদলায়নি। বর্তমান সময়ে শিক্ষাক্ষেত্রে ঘটে চলা চরম অনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ তার-ই অশনিসংকেত। সুতরাং, সাধু সাবধান! আর তা যদি এখনও উপলব্ধি করা সম্ভব না হয়, তাহলে শিক্ষককুলের প্রকৃত সম্মানপ্রাপ্তি এবং ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের পারস্পরিক বিশ্বাস-ভালবাসা বোধহয় অদূর ভবিষ্যতে সহজে ফিরবে না।
*ছবি সৌজন্য : Wikimedia Commons, Pickpic, Wikipedia
পেশায় শিক্ষক দিলীপকুমার ঘোষের জন্ম হাওড়ার ডোমজুড় ব্লকের দফরপুর গ্রামে। নরসিংহ দত্ত কলেজের স্নাতক, রবীন্দ্রভারতী থেকে বাংলা সাহিত্যে স্নাতকোত্তর। নেশা ক্রিকেট, সিনেমা, ক্যুইজ, রাজনীতি। নিমগ্ন পাঠক, সাহিত্যচর্চায় নিয়োজিত সৈনিক। কয়েকটি ছোটবড় পত্রিকা এবং ওয়েবজিনে অণুগল্প, ছোটগল্প এবং রম্যরচনা প্রকাশিত হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে 'সুখপাঠ' এবং 'উদ্ভাস' পত্রিকায় রম্যরচনা এবং দ্বিভাষীয় আন্তর্জালিক 'থার্ড লেন'-এ ছোটগল্প প্রকাশ পেয়েছে।


























One Response
দিলীপ শিক্ষক দিবস উপলক্ষে তোমার লেখা টা পড়লাম ।ভালো লাগলো ।বর্তমান সময়ে শিক্ষার হালহকিকত স্থান পেয়েছে স্বাভাবিক ভাবে ।তবে মানবসম্পদ উন্নয়ন দপ্তর, সর্ব শিক্ষা অভিযান, বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন, মানবাধিকার এসব মিলিয়ে যে জটিল নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন (যা কিনা সোনার পাথরবাটি হয়ত) এ বিষয়ে কিছু আলোচনা আগামী তে থাকবে এই আশা রইল।শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র ছাত্রীদের চরিত্র এবং মূল্যবোধ ও সুনাগরিকত্বের পাঠ বোধহয় প্রয়োজনীয় ।ধন্যবাদ ।