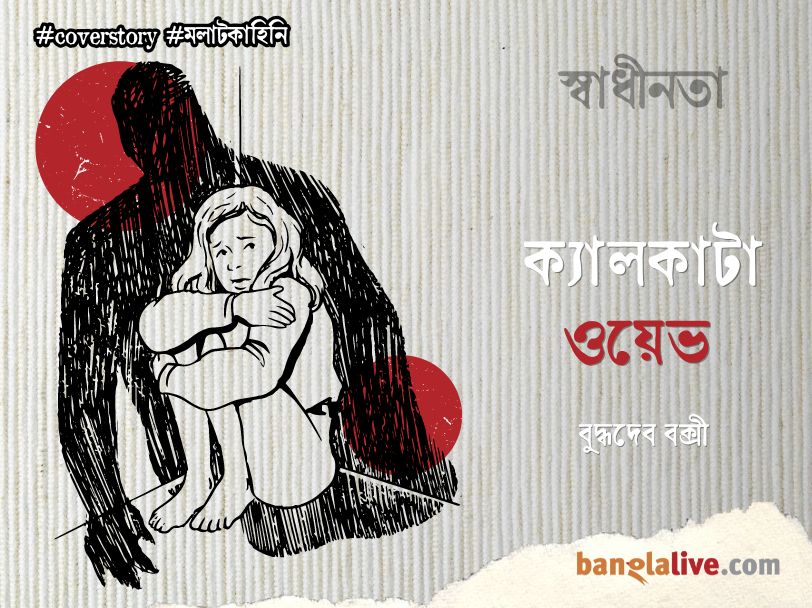“সাপিনীর মতো বাঁকা আঙুলে ফুটেছে তার কঙ্কালের রূপ, ভেঙেছে নাকের ডাঁশা, হিম স্তন হিম রোমকূপ!”
বাংলা সাহিত্যে মৃত্যুর ভয়াবহ ছবি জীবনানন্দ এঁকেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের “মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান” এর বিপ্রতীপ অবস্থানে। কিন্তু সেই ছবিকে প্রত্যক্ষ করার জন্য অপেক্ষা করতে হল ২০২৪ এর আগস্ট মাস অবধি, যখন ডাক্তার মেয়েটির নিথর দেহের ছবি ভাইরাল হয়ে গেল (Calcutta Wave)। ভয়াতুর সভ্যতায় অঙ্গুলি হেলনে অডিও, ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে মুহূর্তে। অথচ এরকম হওয়ার কথা ছিল না। মেয়েটির অনেক বড়ো চিকিৎসক হয়ে, নাম, প্রতিষ্ঠা, যশ উপার্জন করে, অনেক অনেক দিন থেকে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তাঁর ছিন্ন ভিন্ন শরীর থেকে মৃত্যুর কারণ সন্ধান করে দাহ করে দেওয়া হল। পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেল শরীর। যা হওয়ার কথা নয় তাই হয়ে গেল।
এ মৃত্যুকে পাশবিক বলা অনুচিত, কারণ মানবেতর প্রাণী, এভাবে হত্যা করে না। পশুর হত্যা খাদ্য খাদকের প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে, অথবা অন্য কোনও প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার তত্ত্বে। শুধু মানুষের কগনিটিভ চেতনা পারে এরকম করে কিছু ঘটিয়ে দিতে।
ডাক্তার তাঁর রুগীদের দেখেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ডিউটি করেন, রাতে ক্লান্ত শরীরটাকে খানিক বিশ্রাম দিতে কর্মক্ষেত্রে এক শয্যায় শুয়েছিলেন। তথাকথিত সেই নিরাপদ আশ্রয়ে ঘটে গেল এক ভয়ংকর মৃত্যু। এ মৃত্যুকে পাশবিক বলা অনুচিত, কারণ মানবেতর প্রাণী, এভাবে হত্যা করে না। পশুর হত্যা খাদ্য খাদকের প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে, অথবা অন্য কোনও প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার তত্ত্বে। শুধু মানুষের কগনিটিভ চেতনা পারে এরকম করে কিছু ঘটিয়ে দিতে।
তথাকথিত মানব সভ্যতার ঊষালগ্নে, এই কগনিটিভ চেতনা, ধর্ম ভাবনা এবং তার সঙ্গে স্বর্গ- নরকের একটা ধারণা নিয়ে আসে। আসে পাপ, পুণ্যের ভাবনা। এই ধারণা যূথবদ্ধ মানুষকে সংযত করেছে, অপরাধ বোধের সংকেত দিয়েছে। যূথবদ্ধ জীবনে নিয়ম কানুন তৈরি করা হল অপরাধ রোধের জন্য। অনেক যূথপতি একত্রে নিয়ে এল দলপতিকে। তৈরি হল বিচার ব্যবস্থা। অপরাধ করলে শাস্তি পেতে হবে।
লেখকের পিতৃদেব অনেক অনেক বছর আগে ট্রায়াল কোর্টের জজ হিসেবে সেন্ট্রাল কলকাতার এক সম্পন্ন ব্যবসায়ী পরিবারের গৃহবধূর ডাউরি হত্যার বিষয়ে দেখেছিলেন যে মেয়েটিকে এক বহুতলের বারান্দা থেকে রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয়েছে। হত্যা না আত্মহত্যা হিসেবে ডাক্তার বলেন যে দুটোই সম্ভব।
রাষ্ট্র ব্যবস্থার উন্নতির সাথে, কেউ অপরাধ করলে, তার তদন্ত কী করে হবে, তার প্রটোকল তৈরি হয়। দেশে, দেশে সেসব লিপিবদ্ধ আছে। পুলিশকে, investigatorকে সেসব ফলো করতে হয়। তবুও, আজ ২০২৪ সালে, ইনভেস্টিগেশন দেখে, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি মন্তব্য করেন, “entire procedure followed by Bengal Police is something I have not encountered in 30 years”.
সুনির্দিষ্ট প্রসিডিওর ফলো করে ইনভেস্টিগেশন করে, ট্রায়াল কোর্টে সেসব তথ্য পেশ করতে হয়। ট্রায়াল কোর্ট তথ্য প্রমাণ দেখে দোষী বা নির্দোষ সাব্যস্ত করে। কোয়ান্টাম অফ পানিশমেন্ট নির্ধারিত হয়। তারপর হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টে আপিল চলে।
লেখকের পিতৃদেব অনেক অনেক বছর আগে ট্রায়াল কোর্টের জজ হিসেবে সেন্ট্রাল কলকাতার এক সম্পন্ন ব্যবসায়ী পরিবারের গৃহবধূর ডাউরি হত্যার বিষয়ে দেখেছিলেন যে মেয়েটিকে এক বহুতলের বারান্দা থেকে রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয়েছে। হত্যা না আত্মহত্যা হিসেবে ডাক্তার বলেন যে দুটোই সম্ভব। জজ সাহেব অবজার্ভ করেছিলেন যে শরীরে উনিশটা ইনজুরি আছে। বলেন এটা হত্যা। যাবজ্জীবনের আদেশ দিয়েছিলেন কয়েকজনকে। পরবর্তীকালে উচ্চ ন্যায়ালয়ে বোধহয় একজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়।
ফেমিনিস্ট আন্দোলনের প্রথম ওয়েভ নারীদের ভোটের অধিকারের লড়াই ছিল। দ্বিতীয় ওয়েভে লিঙ্গবৈষম্য, পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে ভূমিকা, কর্মক্ষেত্রে সমানাধিকার, প্রজননের অধিকার মুখ্য ছিল। পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল ষাট এবং সত্তরের দশকের আন্দোলন। থার্ড ওয়েভ শুরু হয় নব্বইয়ের দশকে।
আরজিকরের তদন্ত নিয়ে ক্ষোভ জমা হচ্ছিল সাধারণ মানুষের মনে। জমা হচ্ছিল ছাত্রদের মনে। আজ তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে, কোনও বিষয়কে ধামা চাপা দেওয়া প্রায় অসম্ভব। জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতি শুরু হয়। আরজিকরে যথার্থ তদন্তের স্বার্থে সাধারণ মেয়েরা পথে নেমেছেন নির্যাতিতার বিচার চেয়ে। কলকাতা হয়ে বাংলা হয়ে দেশের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে গণ আন্দোলন। দেশের নানাপ্রান্তে জুনিয়র ডাক্তার কর্মবিরতি পালন করা শুরু করেছেন। আন্দোলন দেখে, বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট সুও মটো বিষয়টি নিয়েছেন। আন্দোলন জারি আছে।
ফেমিনিস্ট আন্দোলনের প্রথম ওয়েভ নারীদের ভোটের অধিকারের লড়াই ছিল। দ্বিতীয় ওয়েভে লিঙ্গবৈষম্য, পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে ভূমিকা, কর্মক্ষেত্রে সমানাধিকার, প্রজননের অধিকার মুখ্য ছিল। পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল ষাট এবং সত্তরের দশকের আন্দোলন। থার্ড ওয়েভ শুরু হয় নব্বইয়ের দশকে। মোটামুটি দ্বিতীয় ওয়েভের এক্সটেনশন। ফেমিনিস্ট মুভমেন্টের ফোর্থ ওয়েভ – #Me_Too. এখানে ডিজিটাল মিডিয়ার ব্যপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। সমান সুযোগের, বেতনের জন্য আন্দোলন। আরও গুরুত্বপূর্ণ কর্মক্ষেত্রে যৌনহেনস্থাকারীর নাম করে তাদের বিরুদ্ধে মোর্চা তৈরি করা। আমেরিকা থেকে আন্দোলন ভারতে ছড়িয়ে পড়ে।
আজ মেয়েদের এই রাত দখলের আন্দোলন হয়তো ফেমিনিস্ট আন্দোলনের “ক্যালকাটা ওয়েভ”। কলকাতার মেয়েদের হাত ধরে এই আন্দোলনের শুরু নির্যাতিতার বিচারের জন্য। তবে এই আন্দোলন একান্তভাবে মেয়েদের নিজস্ব। নির্যাতিতার বিচারের সাথে কর্মক্ষেত্রে অধিকার, সেফটি, সিকিউরিটির লড়াই। এই লড়াই হয়তো ভবিষ্যতে আরো স্ট্রাকচার্ড হবে। সমস্ত রকম ওয়ার্কিং ওমেন আন্দোলন করবেন নিজের নিজের কর্মক্ষেত্রে, ব্যাপকভাবে।
মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে কাজের সূত্রে দেখেছি সেখানে কমপ্লেইন হয় এবং জিরো টলারেন্স পলিসির জন্য perpetuatorকে ইমিডিয়েট তাড়ানো হয়। কিন্তু মেয়েটি বা কোম্পানি বিচার ব্যবস্থার কাছে অ্যাপ্রোচ করে না। নিজেদের মধ্যে কথা শেষ করে দেয়। অর্থাৎ perpetuatorএর নেমিং, শেমিং হল না। আইনের আওতায় এল না।
সব মেয়েদের কাজের ক্ষেত্রে সেক্স্যুয়াল হ্যারাসমেন্ট এর undercurrent আছে। কবছর আগে বিখ্যাত জার্নালিস্টকে দেখলাম মন্ত্রিত্ব হারাতে। শিক্ষাজগতে শোনা যায় অনেক অন্যায় হয়ে চলে। দেখলাম মালায়ালম ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির দুর্গন্ধ। Me too # এর সময় দেখা গেল বড়ো বড়ো নাম সামনে আসছে।
যদি সমাজের একজন ব্রিলিয়ান্ট ডাক্তারের এইভাবে কাজের জায়গায় মৃত্যু হতে পারে তবে সব প্রফেশনের মেয়েদের আরও সাবধান হওয়ার সময় এসেছে।
উচ্চশিক্ষিত মহিলা থেকে সাফাই কর্মচারী, প্রত্যেকের কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা জরুরি।
সেদিন অভিনেত্রী বেণী বোসের পোস্টে দেখলাম একটা প্রশ্ন করেছেন। সিনেমা, থিয়েটার জগতের মহিলা কর্মীদের উদ্যেশে- “Are you safe in your workspace dear one? Or do you always live in fear of the one with Power?”
প্রশ্নটি অতীব গুরুতর, এবং সবরকম প্রফেশনের জন্য প্রযোজ্য। যদি সমাজের একজন ব্রিলিয়ান্ট ডাক্তারের এইভাবে কাজের জায়গায় মৃত্যু হতে পারে তবে সব প্রফেশনের মেয়েদের আরও সাবধান হওয়ার সময় এসেছে।
বেণীর লেখার শেষ লাইন দুটো কোট করছি:
“কে সাফ করে নিজের ঘর
তার চেয়ে সহজ R.G.Kar”
ফেমিনিস্ট আন্দোলনের “ক্যালকাটা ওয়েভ” আরও সম্বৃদ্ধ হোক, সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ুক।
অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। কাজের ক্ষেত্র তথ্যপ্রযুক্তি। কিছুদিন স্মার্ট সিটিতে কাজ করেছেন। আড্ডাবাজ মানুষ। বইপড়া আর সিনেমা দেখা নেশা। কাজের সুত্রে সলিউশন ব্লুপ্রিন্ট, স্পেক্স, প্রপোজাল ইত্যাদি অনেক লিখেছেন। ইদানিং বাংলায় প্রবন্ধ, গল্প, ফিল্ম রিভিউ লেখার একটা চেষ্টা চলছে।