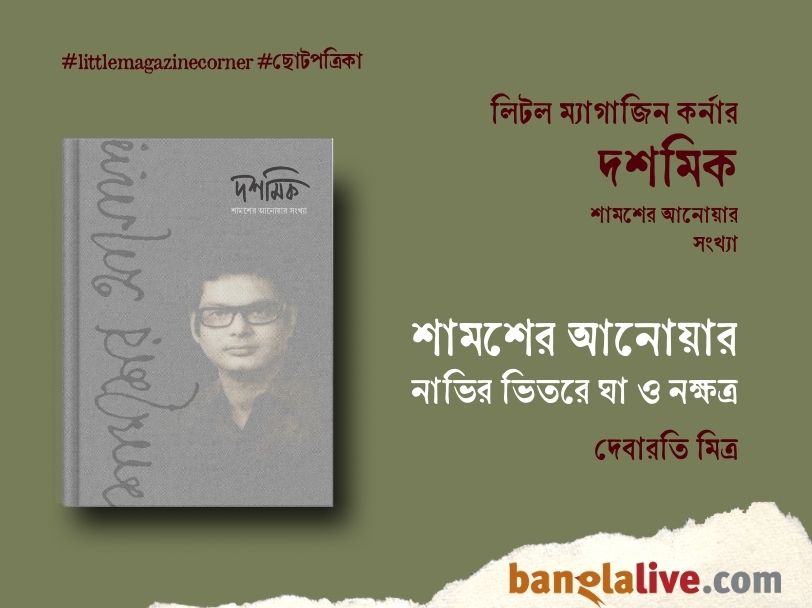(Little Magazine)
কবিতাচর্চার গোড়ার দিকে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা পড়তে-পড়তে শামশের আনোয়ার তাঁর নিজের ভাষা কেমন হবে ভাবছিলেন— ‘‘পাতাল থেকে ডাকছি’ কবিতায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় ‘রম্য’, ‘লীঢ়’, ‘সম্পত্তি-সম্বৃত’ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন। ঐ শব্দগুলি আজ থেকে মোটামুটিভাবে কুড়ি বছর আগে চমৎকার লেগেছিল।… কিন্তু ‘সম্পতি-সম্বৃত’ জাতীয় শব্দকে কবিতা লেখার ক্ষেত্রে আমি পুরোপুরি এড়িয়ে যাব ঠিক করেছিলাম।’
শামশেরের কবিতা পড়ে পাঠকের মনে হতে পারে, পূর্বাপর বাংলা কবিতার সঙ্গে তাঁর বুঝি তেমন পরিচয় নেই। কিন্তু আসলে তা নয়, উপরের উদ্ধৃতিই বলে দিচ্ছে তিনি স্বেচ্ছায়-সচেতনে পূর্ববর্তীদের প্রভাব এড়িয়ে নিজের পথ, নিজের কাব্যভাষা খুঁজতে চেয়েছিলেন।
(Little Magazine)
নিজস্ব জীবনযাপন বা চিন্তাধারা সম্বন্ধে তাঁর রাখঢাক ছিল না। যতদূর পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব, ততদূর তিনি নান্দনিক বা সামাজিক সংস্কার না মেনে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। ফলে তাঁর কবিতায় র্যাঁবোসুলভ একটা টকঝাল স্বাদ এসেছে। ‘কৃত্তিবাস’-এর এবং হাংরিদের কেউ-কেউ অবশ্য আগেই এ-ধরনের কিছু সাহসিকতা দেখিয়েছিলেন, কিন্তু এক্ষেত্রেও শামশের আলাদা। তাঁর জীবনই তাঁকে আলাদা করে দিয়েছিল। শামশেরের নাগরিক, স্বেচ্ছাচারী, আত্মভুক যন্ত্রণা বাইশ বছর বয়স থেকেই তাঁর সত্তার মধ্যে শিকড় গেড়েছিল—
‘আমার বিছানার পাশে বনলতা সেন নয় কোনো এক জলজ্যান্ত
পাপিয়া বসুর মণ্ডূকের মতো দুই স্তন ওৎ পেতে থাকে
শস্তা তেলের দুর্গন্ধে বিদিশার নিশা খুঁজতে গিয়েই আমি
অপ্রতিভ হেসে ফেলি
পায়ের নিচেই ক্ষুরধার রোদ, আমি বলতে পারি না আহা
বাইরে কি মনোরম বৃষ্টি…
ব্যর্থতা ও গ্লানির ক্ষুধায় হস্তমৈথুনের সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েই
আমি পুনরায় ব্যর্থতা ও গ্লানির নিঃসীম তটে ফিরে আসি’
(‘এই কলকাতা আর আমার নিঃসঙ্গ বিছানা’)
রোম্যান্টিকতার খোসা ছাড়িয়ে ফেলা বাস্তবতা— যুবক-যুবতীর প্রেমহীন দেহমিলনের তেতো যন্ত্রণা এবং পরিশেষের মনোহীন ক্লান্তি ও আচ্ছন্ন বিষাদ শামশেরের কবিতায় এক দারুণ চিত্রকল্প সৃষ্টি করেছে :
‘একটা পতঙ্গভুক বৃক্ষের মতো ওর তৃষিত ডালপালাগুলো
আপ্রাণ চেপে ধরে আমার শরীর…
পরিশ্রম হয়
ভালোবাসাহীনতার পরিশ্রমে মেঝে থেকে দেয়াল অবধি বেঁকে যায়…
আমি ওর ডালপালার জঙ্গলে একটা মৃত
পতঙ্গের মতো আটকে থাকি।’
(‘ভালোবাসাহীনতার কষ্ট’)
শুধু ভালোবাসাহীন নরনারীর যৌনাবেগ ও খেলা-শেষের তিক্ততা নয়, তার চেয়েও অস্তিত্বমূলের গভীর বিষাদ এবং বিস্তীর্ণ অন্ধকার ছেয়ে আছে শামশেরকে।
১. ‘আমার অন্য কোনো ভঙ্গি নেই;
শুধু একটিই। কপালে হাত নিয়ে ব’সে রয়েছি
একজন প্রৌঢ় তরুণ;’ (‘জীর্ণ ছবি’)
২. ‘আমার কপালে আঁকা রয়েছে পলাতক হরিণ
ও জেব্রাদের পায়ের ছাপ…
ফাঁসিকাঠের পাটাতনের নিচে যে-রকম ভয়াবহ
শূন্যতা থাকে, আমার দুচোখ সে-রকম শূন্যতায় ভর্তি।’ (‘একজন ব্যর্থ লোক’)
৩. ‘এই অবসর, যেন এক লম্বা শববস্ত্র মুড়িয়ে
রেখেছে আমাকে
যেসব নারীরা এখানে আসে, তারা মৃত্যুর ওপারের
কালো বৃষ্টির মতো অচেতন, অসার হয়ে ঝরে—’ (‘দীর্ঘ অবসর’)
এইসব ইতস্তত মৌলিক পংক্তিতে শামশের নিজের, ইহজন্মের ও তাঁর নারীদের অচেতনা, শূন্যতা ও নিরর্থকতার তীক্ষ্ণ অব্যর্থ বর্ণনা দিয়েছেন।
শামশেরের মাতৃবন্দনা
(Little Magazine)
মা-কে নিয়ে শামশেরের কবিতাগুলি বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়। মায়ের সঙ্গে ছেলের এমন সম্পর্ক, আমার মনে হয়েছে, অভারতীয়। শামশের নিজেকে কখনো ঈডিপাস, কখনো হ্যামলেট, কখনো নষ্টামি-দুষ্টামি মেশানো এক বালক যুবক মনে করেন। তাঁর এই পর্যায়ের কবিতা বুঝতে গেলে, মাতা-পুত্রের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানতেই হবে।
তাঁর মা ছিলেন বিবাহবিচ্ছিন্না, কৃশাঙ্গী, তীক্ষ্ণ ধরনের সুন্দরী, হয়তো-বা ছেলের মতোই একটু উৎকেন্দ্রিক। শামশের তাঁর একমাত্র সন্তান; কিন্তু ছেলের সঙ্গে তাঁর বনে না, একটুতেই তাঁদের মধ্যে লেগে যায়। মায়ের মা নানি ছিলেন স্নেহের আকর, শামশেরের আশ্রয়স্থল। এইসব জটিল কবিতা বিচিত্র মনোবিকলনের ফল। এরকম কবিতা কস্মিনকালে পড়েছি বলে মনে হয় না। (Little Magazine)
মা-কে উদ্দেশ্য করে শামশেরের উক্তি :
‘তোমার মা সেদিন স্নেহে পাগলিনী প্রায়
ব্যাকুল বাঘিনীর মতো সাহসে তেজে আমায় স্তন্যপান করিয়েছিলেন
আমার তৃষ্ণার কান্না তাঁর শুকনো বুকের
দুকূল ছাপিয়ে দুধের বান ডেকেছিলো
অফুরন্ত হৃদয় ঝরেছিলো দুচোখের পাতা বেয়ে
তোমরা যা পাও নি আমি পেয়েছি সে সবই
আমি তাঁর গর্ভের চোরাকুঠুরিতে ভ্রূণের মতো লুকিয়ে বেঁচেছি।’
(‘মা কিংবা প্রেমিকা স্মরণে’)
নানি বা দিদিমার স্নেহের এই বর্ণনার পরেই ঈডিপাসের মুগ্ধতা নিয়ে শামশের নিজের মা-কে বর্ণনা করেন—
‘আমি তোমার সবুজ তলপেট জরায়ু আর হৃদয় খুঁড়ে-খুঁড়ে
ফিরে পেতে চেয়েছিলাম স্মৃতির ধ্বংসাবশেষ।
কুসুমিত স্তন দুটির কাছে প্রার্থনা ছিলো
তোমার মায়ের কৈশোরিক গোলাপের ঘ্রাণ’
মায়ের শরীর সম্বন্ধে তাঁর গর্ভজাত ছেলের এই অনুভূতিময় বন্দনা আমাদের সাধারণ মধ্যবিত্ত মনোবৃত্তিতে কল্পনা করাই শক্ত। লক্ষ করুন, কবিতাটি শেষে কীভাবে অভাবিতের রাজ্য থেকে সুন্দরের দেশের দিকে বেঁকে গেল।
শামশেরের মাথায় কত কী যে খেলত! শামশের বলত, তাঁকে নাকি পাশ থেকে বিবেকানন্দের মতো দেখায়। আমাদের এক প্রবীণ বন্ধুর মতে, কথাটা নেহাত মিথ্যে নয়। যাক গে, এসব পাগলামির কথা।
বিড়ালে স্নেহাসক্ত, একা, ডিভোর্সি, মাথাগরম মা আর তার ঘরে বসে, নিজের মনে বকবক করা, গান করা, ঝগড়া করা আধপাগল ছেলের একটা তুমুল কথা-কাটাকাটির নাটক ঘনিয়ে উঠেছে ‘মেমসাহেব, আমি ও বিড়াল’ কবিতায়।
‘… মেমসাহেব
রেগে কখনো : ‘এই শুয়োর, লোকে তোর নাম দিয়েছে
কি জানিস? পাগল। সবাই হাসে তোকে নিয়ে, পাড়ায়।’
ছেলে : ‘দূর হ মাগী; পাড়ার লোকের ওখানটায়।’
‘মরবি তুই, দেখিস, বাজ পড়ে তুই মরবি।’
‘অভিশাপ? এঃ, মুতে দিই। পাড়ার তোর নাম দিয়েছে
কি জানিস?— বিড়ালওয়ালী!’’
অভিজাতবাড়ির মা-ছেলের এই প্রাকৃত ভাষায় সংলাপ সমানে চলতে থাকে। শেষে মা ‘দীর্ঘ আনুনাসিক/ গলায় বিড়ালটিকে শুরু করেন ডাকতে : ‘কাল্লু,/ উঠে আয় তাড়াতাড়ি, লক্ষ্মী ছেলে… তক্ষ্মী/ দেবো হাতে…।’ এ-কবিতা শুধু মজার না, সত্য ঘটনা অবলম্বনে লেখা না, এখানে ভাষার সুরুচি ও সম্পর্কের ভদ্রতাকে আমল না দিয়ে শামশের জীবনের অন্য এক গভীর অচেনা বোধকে উন্মোচন করেছেন। মায়ের বেড়ালদের গল্প শামশেরের মুখে অনেক শুনেছি। হয়তো মায়ের অত প্রিয় বলেই তারা ছিল শামশেরের দু-চক্ষের বিষ—
‘আমি একটু বেশি ভয় পাই, নাজনিন কম
ওর ধারণা বিড়ালদের অভিশাপ গায়ে লাগে না
আমি জানি লাগে।
ইতিমধ্যে মামলা শুরু হয়েছে বাড়িটা নিয়ে
টাকা ফুরিয়ে আসছে
মৃত বিড়ালগুলো এই বাড়ির কলিং বেল টিপে ধরলে
এখন আমি ভয়ে ও আতঙ্কে শিউরে উঠি।’
(‘কলিং বেল’)
এই কবিতা শামশেরের জীবনের শেষ দিকে লেখা। ভয়, বাড়ি নিয়ে মামলা এবং টাকা ফুরিয়ে আসার উল্লেখে বুঝতে পারি, তাঁর বাঁচার ইচ্ছাও ক্রমশ ফুরিয়ে আসছিল।
শামশের কখনো-কখনো বিরল ধরনের প্রেমের কবিতা লিখেছেন। তখন মেয়েদের শরীর ও মনকে তিনি দেখছেন স্নেহক্ষরিত বিচিত্র চোখে—
‘তার স্তন-দুটি ছিল একটি শান্ত, ছোট দ্বীপ—
নদীর হালকা শরীর নিয়ে সে ঘুরে বেড়াতো
নিজেরই স্তনের চারিপাশে
দেহের বালু নিয়ে খেলা করতো আত্মমগ্ন বালিকার মতো
তার ঊরু দুটি ছিল একটি অকর্ষিত পশ্চাৎ-ভূমি
অনন্ত শৈশব এবং সারল্যে ভরা…’
(‘বালিকা’)
নিজের বালিকা-শরীরের স্পর্শমুখর অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে নিয়ে বুঁদ হয়ে থাকা মেয়েটি বাধ্যতামূলক পুরুষসঙ্গের পরেও যেন পুতুল-খেলা বালিকাই থেকে গেছে; শামশের এভাবেই তার নিষ্পাপতাকে দেখতে পান। যেন স্নেহ দিয়ে তিনি ঘিরে রাখেন কবিতাটিকে।
‘স্তন’ আরেকটি কবিতা। স্নেহ-প্রেম-আনন্দ ও সখা-সখীর খেলার এই কবিতা মানুষের শরীর থেকে যাত্রা করে পাখির প্রাণের উল্লাস পর্যন্ত পৌঁছে যায়।
‘তোমার স্তনে হাত রাখলে মনে হয় যে একটা
ছোট্ট পাখি চেপে ধরেছি মুঠোর ভিতর;
জোরে চেপে ধরলেই ম’রে যাবে—
আঙুলের ডগা বুলিয়ে বুলিয়ে আমি তোমার
স্তনের পালকগুলো খাড়া ক’রে তুলি!
স্তনের ঠোঁটের মুখে গুঁজে দিই মমতার ক্ষুদ এবং কুঁড়ো,
তখন খুশিতে ডাকতে শুরু করে তোমার স্তনদুটো—
ডানা ঝাপটে উড়ে বেড়ায় আমার মুখ, কপাল, বুক
এবং ঘাড়ের ওপর!’
(‘স্তন’)
কিশোরবয়সি মেয়ের কথা বলতে-বলতে শামশের পূর্ণ নারীদের কথায় এসেছেন। আর বর্ণনা করতে গিয়ে তাদের অদ্ভুত এক পরিমণ্ডল ও ছবি এসেছে তাঁর মনে—
‘তোমাদের গোটা শরীর ঢাকা থাকে
অসম্ভব লম্বা ঘাসে
সমস্ত শরীর ঘাসে ঢেকে তোমরা রাঁধো
টেবিলে ডালের বাটি এগিয়ে দাও
ঘাস কিঞ্চিৎ সরিয়ে সঙ্গম কর’
(‘ঘাস’)
ঘাস হচ্ছে রহস্য, আবরণ, নির্মোক, মায়া, ডাইনি বা অদ্ভুত কোনো প্রাণীর মতো নিজেকে গোপন রাখার প্রাকৃতিক ছদ্মবেশ, অথবা আরও ভয়ংকর কিছু। কারণ—
‘মাকড়সা, আরশোলা ও পোকামাকড়দের মৃত্যুর ফাঁশ
ঐ ঘাসের জঙ্গল
বিষাক্ত সাপেদের আনাগোনার রাস্তাও ঐ ঘাস।’
পুরো কবিতাটিই একটি অদ্ভুত চিত্রকল্প। কিন্তু সেই চিত্রকল্প চরম সৌন্দর্যে মুক্তি পায় কবিতার শেষ দুটি লাইনে—
‘শুধু যখন চুল খুলে আয়নার সামনে গুনগুন গান কর
ঘাসের জঙ্গল থেকে তোমাদের মুখ বেরিয়ে আসে।’
এই অপূর্ব ছবিটি, একজন মেয়ে হিসেবে আমার মনে হয়, একশোতে একশো ভাগ ঠিক। শামশেরের অন্তর্যামী দূরদর্শিতা আমাদের অবাক করে।
আমরা জানি, দাম্পত্য-প্রেমের কবিতা লেখা বড়োই কঠিন। বেশি তর্কবিতর্ক ও গবেষণায় না গিয়েও বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দ প্রমুখ কবিরাও এক্ষেত্রে যেন একটু ক্লান্তি বোধ করেছেন। তাহলে শামশেরের মতো খ্যাপাটে, মায়ামমতা-স্নেহার্থী একজন লোক কী করে এরকম হৃদয়ডুবি গূঢ় কবিতা লিখতে পারলেন ভেবে আশ্চর্য হই। অবশ্য আমরা জানি, তাঁর স্ত্রী নাজনিন কত আদরে-কত ধৈর্যে তাঁর বিক্ষুব্ধ মনকে ছোটো শিশুর মতো কোলে করে, চাপড়ে, পুষ্টিকর সুস্বাদু খাবার খাইয়ে শান্ত রাখার চেষ্টা করতেন। শামশেরও সেটা বুঝতেন। ‘উপকথা’ কবিতাটি আমি পুরোই উদ্ধৃত করছি। মন দিয়ে কবিতাটি পড়লে মর্মজ্ঞ পাঠকের কিছুই অজানা থাকবে না। (Little Magazine)
‘সে আমার ক্ষুধার চক্রের মধ্যে বসে নিজের মনেই গান করে ও
সেলাই করে তার পুরনো হাউজকোটখানা
মুদির সঙ্গে ঝগড়া বাধায় তেল নিয়ে
যত্ন করে ছেলের সর্দি মুছিয়ে দেয়
একদিন তাকে জিজ্ঞেস করি তার শৈশবের কথা
সে আমাকে বলে : ‘জানো, আমার বাবার মুসলমান
প্রজারাই তাকে মেরে ফেলে একদিন
এত ভালো ছিল লোকগুলো
কিন্তু হঠাৎ কি যে হল ওদের’
শুনে তার গলা থেকে লেজের শেষ পাকটাও খুলে নিই
আজকাল তার সাহস বেড়েছে
সে প্রায়ই আঙুল দিয়ে আমার চোয়াল ফাঁক করে বলে : ‘দেখি,
তোমার বিষদাঁত কেমন আছে?’
বলেই সে আমার মাথাটা জড়িয়ে ধরে নিজের বুকে
যেন সত্যিই একটা মানুষের মাথা ওটা’
(‘উপকথা’)
‘ছবি’ বলে ‘শিকল আমার গায়ের গন্ধে’ বইয়ের একটি কবিতার কথা বলি— কবিতা বা শিল্প সম্বন্ধে শামশের হয়তো এইরকম ভাবতেন। গোড়া থেকেই তো তিনি পাখি বা ফুল আঁকা শীতলতার বিপক্ষে। তাঁর চিহ্নিত শিল্পে মাধুর্য বা পেলবতা নেই, আছে সৃষ্টির নিষ্ঠুরতা—
‘আমি দেয়ালে কখনও পাখি আঁকি না বা ফুল
আঁকি শাণিত হাঙর বা করাল তিমি’
অপার বিক্ষুদ্ধ সমুদ্রের কথা অকথিত থাকলেও তরঙ্গের প্রবল ধ্বনি ও নিঃসীম নীল যেন অনুভব করা যায়। তারপর—
‘আঁকি একটি পুরুষ বাঁদর
অপর একটি স্ত্রী বাঁদরকে দমন করছে।’
এটা কোনো সাধারণ, স্বাভাবিক মেয়ে-পুরুষের মিলনদৃশ্য নয়। স্থূল এবং নড়বড়ে মানুষের প্রতীক হিসেবে শামশের উপস্থিত করেছেন বাঁদরের চিত্রকল্প। ‘দমন’ শব্দটাতে প্রকাশ পায় পুরুষ-প্রাধান্যের নিষ্ঠুরতা ও অবিচার। এটা অবশ্য এমনও ভাবা যায় : প্রকৃতিকে চালনা করছে এক অনির্ণেয় স্রষ্টা, যার ভঙ্গি ওইরকম। শেষে—
‘নাভির ভিতর যে ঘা আছে
নক্ষত্র আছে
জ্বলন্ত কয়লা দিয়ে সেই ঘা আর
সেই নক্ষত্র আঁকি’
আমাদের স্থূল ও আধ্যাত্মিক দেহের কেন্দ্র হচ্ছে নাভি, সেখানে ঘা ও নক্ষত্র দুটোকেই দেখতে পেয়েছিলেন শামশের।…
‘সন্নিধি’, ডিসেম্বর ২০০৬
(বানান অপরিবর্তিত)
বাংলালাইভ একটি সুপরিচিত ও জনপ্রিয় ওয়েবপত্রিকা। তবে পত্রিকা প্রকাশনা ছাড়াও আরও নানাবিধ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে থাকে বাংলালাইভ। বহু অনুষ্ঠানে ওয়েব পার্টনার হিসেবে কাজ করে। সেই ভিডিও পাঠক-দর্শকরা দেখতে পান বাংলালাইভের পোর্টালে,ফেসবুক পাতায় বা বাংলালাইভ ইউটিউব চ্যানেলে।