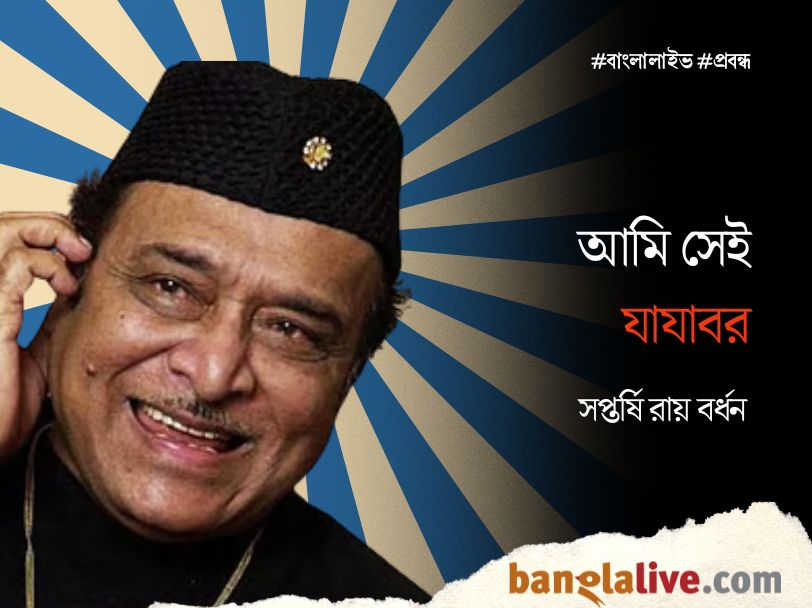(Bhupen Hazarika)
১৯৭৭ সাল, দেশের রাজনৈতিক পালাবদলের ক্ষেত্রে, এক ব্যতিক্রমি বছর।
দুই বছর আগে, দেশে ঘোষিত হয়েছিল জরুরি অবস্থা। জুন মাসের ২৫ তারিখ। ভারতীয় সংবিধানের ইতিহাসে অন্যতম অন্ধকার অধ্যায়, এই জরুরি অবস্থা। দীর্ঘ একুশ মাস জুড়ে চলা রাজনৈতিক এবং সামাজিক নিষ্পেষণের ফলে দেশের সংবিধান প্রদত্ত গণতান্ত্রিক অধিকার, সংবাদ মাধ্যমের অধিকার- সবকিছু কেড়ে নেওয়া হয়৷ কারাগারে বন্দি করা হয় বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা, ছাত্রছাত্রী, অভিনেতা, শিল্পী, সমাজকর্মী এবং সাধারণ মানুষকে৷ মিথ্যাচার এবং সন্দেহের আবহে সারা দেশ জুড়ে চলেছিল অকথ্য নিপীড়ন। (Bhupen Hazarika)
কোন গান গাওয়া যাবে, চলচিত্রের সেলুলয়েডের ফ্রেমে কোথায় কাঁচি চলবে, গণ মাধ্যমে (তখন মূলত আকাশবাণী) কোন শিল্পীর গান হবে বর্জিত– এ সবই ঠিক হত সরকারের কতিপয় জো-হুজুরি আমলার সিদ্ধান্তে। প্রখ্যাত সাংবাদিক কুলদীপ নায়ার, যিনি জরুরি অবস্থার দুঃসহ দিনের বর্ণনা লিখেছিলেন তাঁর “দ্যা জাজমেন্ট” বইটির পাতায় পাতায়, একবার বলেছিলেন “Indians must never forget this day. It was the time when the country lost her independence after freedom from the British. About 1,00,000 people were detained without trial. The Press was gagged. There was fear and people were afraid to speak up”। (Bhupen Hazarika)
কিন্তু ইতিহাসের পিছনে ফেলে আসা পথের দিকে তাকালে আমরা দেখি, দুঃখ দিনের অবসানে শান্তির বার্তা নিয়ে ফিরে আসে সুস্থ সময়। আর মানুষের হাত ধরেই আসে সেই পরিবর্তন। (Bhupen Hazarika)

সেবারও এসেছিল। কেন্দ্রে এবং পশ্চিমবঙ্গে– কংগ্রেস সরকারের হয়েছিল “নীরন্ধ্র, নির্মম পতন”!
এর ঠিক এক বছর বাদে, অর্থাৎ ১৯৭৮ সালে গ্রামোফোন কোম্পানির পূজার গানের সম্ভারে প্রকাশ পেয়েছিল শিল্পী ভূপেন হাজারিকার প্রথম আট খানা বাংলা গানের সংকলন “আমি এক যাযাবর”। রেকর্ডের অধিকাংশ গানের মূল রচনা অহমিয়া ভাষায় শিল্পীর নিজেরই, যার কাব্যিক রূপান্তর ঘটেছিল গীতিকার শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনীতে। এই গান সেইবার বেজেছিল মণ্ডপে মণ্ডপে। শ্রোতারা প্রাণ ভরে শুনেছিলেন “বিস্তীর্ণ দুপারের, অসংখ্য মানুষের- হাহাকার শুনেও, নিঃশব্দে নীরবে- ও গঙ্গা তুমি- গঙ্গা বইছ কেন?” যা আগে শোনা গিয়েছিল “ক্যালকাটা ইউথ কয়্যার” এর রেকর্ডে রুমা গুহ ঠাকুরতার পরিচালনায়। অথবা “সাগর সঙ্গমে সাঁতার কেটেছি কত”– “জীবন তৃষ্ণা” ছবিতে স্বয়ং উত্তমকুমারের ঠোঁটে। (Bhupen Hazarika)
“ভূপেন হাজারিকার গানের কথায় ছড়িয়ে থাকে এক আন্তর্জাতিকতাবাদের কথা। প্রচ্ছন্ন বা প্রত্যক্ষ তার উপস্থিতি। হেমাঙ্গ বিশ্বাস যাকে বলেছিলেন “লোকসঙ্গীতের বাহিরিয়ানা” এও বোধহয় তাই।”
সাতের দশকের শেষ প্রান্তে এসে বাঙলা গানের শিল্পী হিসেবে তিনি স্বীকৃতি পেলেও পাঁচের দশক থেকে ভূপেন ছিলেন বাঙলা গানের সঙ্গে যুক্ত। এর আগে অসংখ্য বাঙলা গানের সুর বেঁধেছেন তিনি। “রঙ্গিলা বাঁশিতে কে ডাকে”, ‘ফেলে আসা পথ পানে’, ‘অন্ত আকাশে বনের চিতা জ্বলে’(লতা মঙ্গেশকর), “সপ্তডিঙ্গা মধুকর”, “ চৈতালি চাঁদ” ( শ্যামল মিত্র), “ওগো শকুন্তলা” (সুবীর সেন), “একখানা মেঘ ভেসে এল আকাশে” (রুমা গুহ ঠাকুরতা) এরকম সব অসাধারণ সুর, যা ইদানীংকালের শ্রোতার কাছে হয়তো বা থেকে গেছে অশ্রুত বা অজ্ঞাত। (Bhupen Hazarika)
“মাইলফলক” শব্দটা যদি ব্যবহার নাও বা করি, বাঙলা ফিল্ম সঙ্গীত এবং আধুনিক গানের সোনালি অধ্যায়ের ধারায় ৭০-এর দশকের প্রান্তে যুক্ত হল ভূপেন হাজারিকার গান। মানুষের কথা, সমাজের কথা, মানবিক মূল্যবোধের কথা ধরা পড়ল তাঁর গানে। আর যেহেতু একটা দীর্ঘ সময় তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন তাঁর জন্মস্থান অহম রাজ্যের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে, সুতরাং তাঁর সুরসৃষ্টিতে অনুপ্রবেশ ঘটল সেখানকার মাটির সুর– বিহুগীত, ভারিগান, ওজাপালি, গোয়ালপাড়িয়া, ঝুমুর ইত্যাদি এবং বৈষ্ণব কীর্তনের। নিজেই বলেছিলেন মা এর কাছে শোনা একটি ঘুমপাড়ানি গানের সুর থেকে জন্ম নিয়েছিল কল্পনা লাজমির “রুদালি” ছবিটির কিছু সুরের অংশ। (Bhupen Hazarika)

ভূপেন হাজারিকার গানের কথায় ছড়িয়ে থাকে এক আন্তর্জাতিকতাবাদের কথা। প্রচ্ছন্ন বা প্রত্যক্ষ তার উপস্থিতি। হেমাঙ্গ বিশ্বাস যাকে বলেছিলেন “লোকসঙ্গীতের বাহিরিয়ানা” এও বোধহয় তাই। ১৯৩৬ নাগাদ ঘর ছাড়েন তিনি। শৈশবে সঙ্গীতের শিক্ষা পেয়েছিলেন বিষ্ণু প্রসাদ রাভার কাছে। সুতরাং সেই সুরকে সঙ্গী করে কবি ও চিত্র পরিচালক জ্যোতি প্রসাদ আগরওয়ালার সঙ্গে আসেন কলকাতায়। বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক। ১৯৪৯ সাল নাগাদ দেশ ছাড়েন। আমেরিকার কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হন মাস কমিউনিকেসনের কোর্সে। দেশান্তরি হয়ে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেনে আমেরিকা ছাড়াও পৃথিবীর আরও অনেক দেশ– যে অবস্থানটির কথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন গানের কথায়-
“…বলেছিলেন, “ইট ইজ এ সোশ্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট। উইথ এ স্ট্রাম অফ এ গিটার ইউ ক্যান চেন্জ দি সোসাইটি। উইথ এ বিট অফ এ ড্রাম, ইউ ক্যান মেক দি হোল নেশন থিঙ্ক। এই দৃষ্টিকোণ থেকে গান গাইবে, কথা বলবে।”
“আমি এক যাযাবর, পৃথিবী আমারে আপন করেছে, ভুলেছি নিজের ঘর”!
দেশ ঘোরার পাশে পাশে ভূপেন সংস্পর্শে এসেছিলেন নানান গুণী মানুষের। পিকাসোর সঙ্গে দেখা করতে পেরেছিলেন ফ্রান্সে। কৃষ্ণাঙ্গ গায়ক পল রবসনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল আমারিকায়। রবসন তখন গাইছেন, কালো মানুষদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। তাঁর গানে প্রতিধ্বনিত হত পৃথিবীর অন্য প্রান্তে শোষিত মানুষের কথাও। আর এভাবেই রবসনের প্রতিবাদী গান “ওল’ ম্যান রিভার” দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন ভূপেন হাজারিকা। অহমিয়া ভাষায় রচনা করলেন “বিস্তির্নো পারোরে… বুরহাঁ লুই তুমি বুয়া কিও” যা পরে হিন্দিতে “বিস্তার অপার… ও গঙ্গা বেহতি হো কিউ” এবং বাঙলায় “বিস্তীর্ণ দুপারের, অসংখ্য মানুষের- হাহাকার শুনেও, নিঃশব্দে নীরবে- ও গঙ্গা তুমি- গঙ্গা তুমি বইছ কেন” হিসেবে রূপান্তরিত হয়। (Bhupen Hazarika)
রবসনের এই গানটি শান্তি এবং মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি সার্বজনীন দলিল হিসেবে আজও রয়ে গেছে। মিসিসিপি, ভল্গা, রাইন, ব্রহ্মপুত্র এবং গঙ্গা মিলেমিশে এক হয়ে দেশের সীমানাকে যেন মিলিয়ে দিয়েছে এই গানে। (Bhupen Hazarika)
“সেই দিন থেকে অনুভব করতে শিখেছি, মানুষের ভাষায় যদি গান গাওয়া যায়, হৃদয়ের ভাষায় যদি কথা বলা যায়, তবে সব বিরোধ, বৈষম্য দূর হয়ে যায়। চেতনার দিগন্তে, একদিন না একদিন সূর্য উঠবেই।”
হাজারিকা তাঁর স্মৃতি চারণে লিখেছেন– “পল রবসন একটা গীটার দেখিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন-
“এটা কী বলতো, ভূপেন?”
“গীটার”, সপ্রতিভ উত্তর দিয়েছিলাম আমি।
“গীটার কী?”
“সঙ্গীতের অনুষঙ্গ, একটি যন্ত্র”
“নো”, আমার উত্তর শুনে রেগে উঠেছিলেন তিনি । বলেছিলেন, “ইট ইজ এ সোশ্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট। উইথ এ স্ট্রাম অফ এ গিটার ইউ ক্যান চেন্জ দি সোসাইটি। উইথ এ বিট অফ এ ড্রাম, ইউ ক্যান মেক দি হোল নেশন থিঙ্ক। এই দৃষ্টিকোণ থেকে গান গাইবে, কথা বলবে। তা হলেই এই পৃথিবীকে সুন্দর করে তুলতে পারবে।” (Bhupen Hazarika)
সেই দিন থেকে অনুভব করতে শিখেছি, মানুষের ভাষায় যদি গান গাওয়া যায়, হৃদয়ের ভাষায় যদি কথা বলা যায়, তবে সব বিরোধ, বৈষম্য দূর হয়ে যায়। চেতনার দিগন্তে, একদিন না একদিন সূর্য উঠবেই”। (Bhupen Hazarika)

আর এই বিশ্বাস থেকেই হয়তো তিনি প্রশ্ন করেন “মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য, একটু সহানুভুতি কি মানুষ পেতে পারে না, – ও বন্ধু? মানুষ মানুষের জন্য” গানটি লেখা হয় ১৯৬১-৬২ সাল নাগাদ যা পরে অহমিয়া থেকে অনুদিত ও গীত হয়েছিল বাংলাতে। (Bhupen Hazarika)
জানা যায় ওপার বাংলার মানুষ নিজেদের জাতীয় সঙ্গীতের পরে দ্বিতীয় প্রিয়তম গানের তালিকায় রেখেছিলেন এই গানটিকে। কারণ ভূপেন হাজারিকা নামে মানুষটির কাছে তদের ঋণ সেই মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন “গঙ্গা আমার মা, পদ্মা আমার মা / ও আমার দুই চোখে দুই জলের ধারা মেঘনা যমুনা” এবং “সবার হ্রদয়ে রবীন্দ্রনাথ / চেতনাতে নজ্রুল”– আর এই দুটি গানই ভূপেন তাঁর দৃপ্ত কণ্ঠে গেয়েছিলেন নিজের সুরে। (Bhupen Hazarika)
আরও পড়ুন: আসলেই শোলে: ঘটনার ঘনঘটা
আমেরিকা থেকে ফিরে এসে একটা দীর্ঘ সময় তিনি জড়িয়ে পরেন গণনাট্য সঙ্ঘের কাজে। ক্রমশ অহমের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গেও নিজেকে যুক্ত করেন। ১৯৬৭ থকে ১৯৭২, অহম বিধানসভার নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। সমান্তরালে চলেছিল সিনেমার গানে সুরারোপ। অহমিয়া, বাঙলা এবং হিন্দি মিলিয়ে প্রায় চল্লিশটি ছবির সুর রচনা করেছেন তিনি। একদিকে “চামেলি মেমসাহেব” ছবির “হাওয়া নেই, বাতাস নেই” আর “রুদালি” ছবির “দিল হুম হুম করে” দুটি গানের সুরমূর্ছনার মধ্যে তৈরি হয় এক অদ্ভুত আকুতির অনুরণন যা কালের সীমারেখা পেরিয়ে যায়, অপরদিকে তাঁর সঙ্গীত এই বিভিন্নতার নৈরাজ্যে বিহুর সঙ্গে ভাটিয়ালি মিশে বাজায় সংহতির করতালি। (Bhupen Hazarika)
এভাবেই ভারতরত্ন ভূপেন হাজারিকা যাযাবর হয়েও ঘর বাঁধেন আমাদের মনের মাঝে।
মুদ্রিত ও ডিজিটাল মাধ্যমে সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
সপ্তর্ষি রায় বর্ধনের জন্ম, কর্ম এবং বর্তমান ঠাঁই তার প্রাণের শহর কলকাতায়। প্রথাগত ছাত্রজীবন কেটেছে কলকাতার পাঠভবন স্কুল, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ এবং যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে। লেখাজোকা, ছবি তোলা, নাট্যাভিনয় আর হেরিটেজের সুলুক সন্ধানের নেশায় মশগুল। সঙ্গে বই পড়া, গান বাজনা শোনা আর আকাশ পাতাল ভাবনার অদম্য বাসনা। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা তিন- "রূপকথার মতো- স্মৃতিকথায় প্রণতি রায়", "খেয়ালের খেরোখাতা" এবং "চব্য চোষ্য লেহ্য পেয়"।