সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা নিয়ে আগ্রহ ও কৌতূহল আমার সেই ছোটবেলা থেকে। কলেজের পাট শেষ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতার পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ক্লাসের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসেছিলাম গুরুজনদের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে। যেদিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের নামের তালিকা বেরুল, দেখা গেল আমার নাম দু’জনের পরেই। অগত্যা বাড়ির লোককে অনুমতি দিতেই হল।
দ্বারভাঙা বিল্ডিংয়ের দোতলায় বিকেলে হত আমাদের ক্লাস। ছাত্রসংখ্যা ছিল ছাত্রীদের তুলনায় অনেক বেশি। আমরা মেয়েরা বেশিরভাগই কলেজের স্নাতক-পাঠ শেষ করে সাংবাদিকতা নিয়ে পড়তে এসেছিলাম। দু’একজন আবার সাংবাদিকতার পাশাপাশি দিনের বেলায় এমএ ক্লাসও করত। শকুন্তলা দাশগুপ্ত আর অজয় চট্টোপাধ্যায়– দু’জনেই ছিলেন আমার তিন বছরের বড় দিদির এমএ ক্লাসের সহপাঠী। ওঁরা বাংলাতে এমএ পাশ করে সাংবাদিকতা পড়তে এসেছিলেন। দিদির সুবাদে আগে থেকেই চিনতাম ওঁদের দু’জনকে। প্রথম দিন ওঁদের ক্লাসে দেখে আমি তো অবাক। ইতিমধ্যে অজয়দা সরকারি পর্যটন বিভাগে কাজ করতে শুরু করেছিলেন।

শকুন্তলাদি আসতেন কপালে একটা মস্ত টিপ পরে, বিনুনি ঝুলিয়ে। ওঁর বাবা নিজে একটি পত্রিকা বের করতেন যার সম্পাদক ছিলেন তিনি নিজেই। পত্রিকার নাম ‘বিচার’। কেন তিনি পত্রিকার এমন নাম রেখেছিলেন তা অবশ্য জানা নেই আমার। আর অজয়দা ছিলেন বেশ ছটফটে স্বভাবের। খুব মজা করে কথা বলতেন। আড্ডা জমাতে ওঁর জুড়ি মেলা ভার ছিল। দু’জনে একসঙ্গে আসতেন। ক্লাসেও পাশাপাশি বসতেন। পরে ওঁরা বিয়েও করেন।
[the_ad id=”266918″]
স্মৃতি দাস ছিলেন সম্ভবত আমাদের ক্লাসের ছাত্রীদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ। মধ্য কলকাতার এক নামী ইংরেজি মাধ্যম মেয়েদের স্কুলের প্রধানশিক্ষিকা ছিলেন তিনি। বয়সোচিত গাম্ভীর্য থাকলেও আমাদের সঙ্গে মিশতেন বন্ধুর মতো। কত যে স্নেহ পেয়েছি ওঁর কাছে, আজও ভুলিনি। বয়সে বড় হলেও অত্যন্ত মনোযোগী ছাত্রী ছিলেন। ফাইনাল পরীক্ষাতে দ্বিতীয় হয়েছিলেন। প্রথম হয়েছিল বাচ্চি কাঙ্গা — আজ সংবাদপত্র জগতে যাঁর পরিচিতি বাচ্চি কারকারিয়া নামে। সফল সাংবাদিক ও কলামনিস্ট হিসেবে বাচ্চির নাম কে না জানে এখন!

বাচ্চি ছিল কলকাতার এক শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পার্সি পরিবারের মেয়ে। ছোট্টখাট্টো চেহারা। বব কাট চুল, পরনে স্কার্ট, এমব্রয়ডারি করা সাদা টপ। ভাঙা ভাঙা বাংলা বলত। আমারই মতো লম্বায় সে পুরো পাঁচ ফুটও নয়। এজরা স্ট্রিটে থাকত ওরা। ওদের পরিবার থেকে বেরুত ‘নওরোজ’ নামে একটি পার্সি পত্রিকা যার সম্পাদক ছিলেন বাচ্চির বাবা। একবার বাচ্চি ওর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছিল আমাদের কয়েকজনকে। এজরা স্ট্রিটের সেই বাড়িতেই আমার পার্সি খাবারের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। বাচ্চির মায়ের হাতে রান্না করা মুরব্বা আর ধানশাক খেয়ে আমরা তো মুগ্ধ! এ গল্প আমি অন্যত্র সবিস্তারে করেছি।

আমাদের ক্লাসে দু’জন রত্না ছিল। একজন ভট্টাচার্য, অন্যজন সেন। রত্না ভট্টাচার্য সাংবাদিকতার পাশাপাশি দিনের বেলায় এমএ ক্লাস করত। ওর কাকা অরুণ ভট্টাচার্য ছিলেন দুঁদে সাংবাদিক, যাঁকে নিয়ে রত্নার গর্বের শেষ ছিল না। চিন-ভারত যুদ্ধে উনি সীমান্ত থেকে যুদ্ধের রিপোর্ট পাঠাতেন। এসব শুনে আমাদের খুব ইচ্ছে হল ওঁর সঙ্গে দেখা করার। রত্নাকে জানাতে ব্যবস্থা হয়ে গেল। অরুণকাকা রাজি হলেন শুধু নয়, আমাদের প্রেস ক্লাবে একদিন চায়ের নেমন্তন্ন করলেন। আমি, বাচ্চি আর দুই রত্না যথা সময়ে হাজির। প্রচুর গল্প করলেন। যুদ্ধক্ষেত্রের সে সব রোমহর্ষক কাহিনি শুনে আমরা প্রায় বাকরুদ্ধ। আর লা মার্টিনিয়ার স্কুলে পড়া রত্না সেন ছিল ভাবভঙ্গিতে দারুণ কেতাদুরস্ত। দারুণ গাড়ি চালাত আর চোস্ত ইংরেজি বলত। আমি ছিলাম বাংলা স্কুলে পড়া অতি সাদাসিধে একটি মেয়ে। এসব সত্ত্বেও রত্না সেন আর বাচ্চির সঙ্গে বেশ গাঢ় বন্ধুত্ব হয়েছিল আমার। ক্লাস শুরু হবার পরে জেনেছিলাম সে আমার প্রতিবেশী। সেই শুরু হল ক্লাস শেষে একসঙ্গে বাড়ি ফেরা।

আমাদের বিভাগের নিয়ম ছিল, ছাত্রছাত্রীদের কোনও একটি সংবাদসংস্থায় শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ করতে হবে। ছেলেদের খুব একটা সমস্যা হত না। বাচ্চিও তার পারিবারিক কাগজে সাব এডিটিংয়ের কাজে ঢুকে পড়েছিল। রত্না ও আমার ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজ হয়নি। আমরা দু’জনে উঠেপড়ে লেগেছিলাম খবরের কাগজে ঢুকে কাজ শেখার জন্য। শহরের সংবাদপত্র অফিসগুলির দরজায় দরজায় ঘুরে হতাশ হয়েছিলাম। ষাটের দশকে খবরের জগতে মেয়েরা প্রায় ব্রাত্য ছিল। কিন্তু হাল ছাড়িনি আমরা। শেষ পর্যন্ত রত্না ঢুকল ইউ এন আই তে আর আমি দৈনিক বসুমতীতে, পরে কালান্তর পত্রিকায়। তবে বাচ্চি ডেস্কে কাজ করত আর রত্নাও খুব একটা রিপোর্টিংয়ের সু্যোগ পেত না। ক্কচিৎ কদাচিৎ ও রাইটার্স বা বিধানসভায় আসত। কিন্তু বসুমতীতে কাজ করার সময় থেকেই আমি নিয়মিত রিপোর্টারি করার সুযোগ পেয়েছিলাম। খুব ভাল লাগত যখন ছাপার অক্ষরে আমার লেখা রিপোর্ট বেরুত আর শিরোনামের তলায় লেখা থাকত ‘স্টাফ রিপোর্টার’।
[the_ad id=”266919″]
সাংবাদিকতার পাঠ শেষ হলে বাচ্চি টাইমস অব ইন্ডিয়াতে চাকরি পেল। তারপরে ওকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। রত্না ও আমি ভিন্ন ভিন্ন কারণে এই পেশাতে টিঁকে থাকতে পারিনি। রত্না দীর্ঘদিন কলকাতার এক নামকরা বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজে পড়িয়েছে আর আমি সাউথ পয়েন্টে। এক শহরে কাছাকাছি থাকি বলে তবু রত্নার সঙ্গে সামান্য যোগাযোগ রয়েছে। কিন্তু বাচ্চি মুম্বই চলে যাবার পরে ওর সঙ্গে সব যোগাযোগ আস্তে আস্তে ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎই বছর দুয়েক আগে কয়েক দশক বাদে অক্সফোর্ড বুক স্টোরের এক অনুষ্ঠানে ওর সঙ্গে দেখা হল। মুহূর্তের জন্য দু’জনেই সেদিন ফিরে গিয়েছিলাম ছাত্র জীবনের সেই ফেলে আসা দিনগুলিতে। ঠিকানা, ফোন নম্বর আদানপ্রদান হল। ই মেলে দু’চারবার মনের কথার বিনিময়ও হল। তারপরে আবার চুপচাপ। যে যার বৃত্তে ঘুরতে ঘুরতে আবার ছিটকে গেছি আমরা!

এই তো গেল সাংবাদিকতা ক্লাসের ছাত্রীদের কথা! ছাত্রদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত। সারাদিন অফিস করে ক্লাস করতে আসতেন। কেউ আসতেন মফস্সল থেকে। কেউ কেউ বিভিন্ন সংবাদপত্রে জেলার সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করতেন। দু’একজন আবার সংবাদপত্র দফতরেরই নানা বিভাগে কাজ করতেন, তবে প্রত্যক্ষভাবে সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। সকলেরই স্বপ্ন একটাই — পাঠক্রমের শেষে ডিপ্লোমাধারী হয়ে পুরোদস্তুর সাংবাদিকের তকমা লাগিয়ে কলকাতার কোনও বাণিজ্যিক কাগজের অফিসে ঢুকে পড়া। আমাদের এক সহপাঠী, শৈলপতি রায় স্টেটসম্যান পত্রিকায় কাজ করত প্রুফ রিডার হিসেবে। স্টেটসম্যানের মতো নামী ইংরেজি কাগজে কাজ করত বলে ক্লাসের অনেকেই তাকে একটু সমীহ করে চলত। শৈলপতি সারা শীতকাল স্যুট পরে ক্লাসে আসত। অদ্ভুত এক অ্যাকসেন্টে ইংরেজি বলত আর আমরা মেয়েরা তা নিয়ে হাসাহাসি করতে ছাড়তাম না। তবে মানুষটা সে মন্দ ছিল না। কোনও দিন কেউ কোনও কারণে ক্লাস করতে না পারলে শৈলপতি সে দিনের নোট যেচে এসে দিয়ে যেত। তবে আমরা মেয়েরাই এ ব্যাপারে ওর কাছ থেকে বেশি সাহায্য পেতাম, একথা স্বীকার করতে বাধা নেই।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপকদের কথা বলতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে মোহিত মৈত্রের কথা। ওই সময়ে উনি ক্যানসার আক্রান্ত। অত অসুস্থ শরীর নিয়ে যতদিন ওঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে, ক্লাস নিয়েছেন। শুনেছি যন্ত্রণা কমাতে ব্যথার ইঞ্জেকশন নিয়ে আমাদের পড়াতে আসতেন।
সে সময়ে আমাদের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন চপলাকান্ত ভট্টাচার্য। তিনি ছিলেন ঘোর কংগ্রেসি আর মোহিতবাবু ছিলেন কট্টর মার্ক্সবাদী। তিনি ক্লাসে আমাদের ‘কমরেডস’ বলে সম্বোধন করতেন। ভারতীয় সাংবাদিকতার ইতিহাস পড়াতেন। রাজনৈতিক বিশ্বাসের দিক থেকে দু’জন ছিলেন দুই ভিন্ন মেরুর মানুষ। কিন্তু তাতে কী এসে যায়! বন্ধুত্বের দিক থেকে বিচার করলে দু’জনে ছিলেন হরিহর আত্মা। কতদিন দেখেছি মোহিত স্যারকে চপলাবাবুর ঘরে বসে আড্ডা দিতে। এমনিতে চপলাবাবু রাশভারী মানুষ ছিলেন। কিন্তু দুই বন্ধু একসঙ্গে হলে ওঁর ঘর থেকে ওঁদের দ্বৈত হাসির আওয়াজ করিডোরে ছাত্রছাত্রীদের কানে পৌঁছত।

আমাদের রিপোর্টিং সংক্রান্ত একটি পেপার পড়াতেন অজিত দাশ। তবে পড়ানোর চাইতে তিনি গল্প করতেন বেশি। কত দেশে যেতে হত ওঁকে আর খুব রসিয়ে সে সব দেশের গল্প করতেন। আমরা খুব উপভোগ করতাম ওঁর ক্লাস। যতদূর মনে পড়ছে, উনি কাজ করতেন ইউপিআই নিউজ এজেন্সিতে। কর্মসূত্রে বেশি যেতে হত সিকিম এবং সেই সূত্রে সিকিমের রাজা চোগিয়াল পালডেন ও রানি হোপ কুকের সঙ্গে নাকি তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ওঁর কথা, গল্প থেকে আমরা অন্তত সেই আভাসই পেতাম। এমনও শোনা যেত যে অজিত দাশ যে গাড়ি চালিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতেন, সে গাড়ির নম্বর প্লেটটি ছিল সিকিমের। সত্যি মিথ্যে জানি না- ওঁর ঘনিষ্ঠ দু’একজন ছাত্রছাত্রীর সূত্র থেকে কানে এসেছিল যে এই গাড়ি নাকি আমাদের মাস্টারমশাই পেয়েছিলেন সিকিমের রানির স্নেহের স্মারক হিসেবে।
‘কনস্টিটিউশনাল ল’ পড়াতেন ড. বি এন মুখোপাধ্যায়। সাহেবদের মতো গায়ের রং। অত্যন্ত সুদর্শন। পড়াতেন চমৎকার। ওঁর যেদিন ক্লাস থাকত, সেদিন ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি হত লক্ষ্যণীয়। ড. সুনীত মুখোপাধ্যায় পড়াতেন ‘কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স’ ও ‘ অ্যাডভার্টাইসমেন্ট’। পরে অবশ্য ওঁকে চিনেছি অমৃতবাজার পত্রিকায় আমার স্বামী শঙ্কর ঘোষের সহকর্মী হিসেবে। শঙ্কর তখন ওই পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক আর সুনীতবাবু অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর। ২০০৯-এ শঙ্করের মৃত্যুর পরে আমার সঙ্গে দেখা করতেও এসেছিলেন স্যার। আমিও গিয়েছি ওঁর বাড়িতে ওঁর অসুস্থতার খবর পেয়ে। অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তিনি আমার স্বামীর প্রতি। সেই সময়ে ওঁদের কাগজের অফিসের নানা গল্প শুনেছি ওঁর মুখে।
[the_ad id=”270084″]
হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড-এর সম্পাদক সুধাংশুকুমার বসুও আমাদের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ছিলেন অর্থনীতির এমএ, ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। প্রথম জীবনে অধ্যাপনা করলেও, পরবর্তী কালে তিনি খবরের কাগজে যোগ দেন। সুধাংশুবাবুকে অধ্যাপক হিসেবে যখন ক্লাসে দেখেছি, আমাদের তখন বয়স কম। ওঁর প্রতিভা এবং কর্মক্ষমতা বোঝার ইচ্ছে এবং ধৈর্য, আমাদের ছিল না। ওঁর কথায় একটু জড়তা ছিল। কথা বুঝতে অসুবিধে হত আর তা নিয়ে ক্লাসের দুষ্টু ছেলেরা হাসাহাসি করত। স্যার কিন্তু এসব গ্রাহ্যই করতেন না। পড়ানো শেষ করে বেরিয়ে যেতেন। কোনও বিষয় বুঝতে অসুবিধে হলে বা কোনও রকম সাহায্যের প্রয়োজন হলে তিনি কোনও ছাত্রকে কোনওদিন বিমুখ করতেন না।

আর এক অধ্যাপক দক্ষিণারঞ্জন বসু তখন যুগান্তর কাগজের নিউজ এডিটর। লেখক হিসেবেও তাঁর মোটামুটি খ্যাতি ছিল। একবার তিনি আমাদের মধ্যে থেকে তিন/চার জন ছাত্রীকে একদিন ওঁর অফিসে যেতে বললেন। উদ্দেশ্য খবরের কাগজের খুঁটিনাটি টেকনিক্যাল দিকগুলি প্রেসে নিয়ে গিয়ে দেখান। কেন শুধু মেয়েরা এই সুযোগ পাবে, এবং তাও আবার মাত্র কয়েকজন… এই নিয়ে ছেলেদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। কেউ কেউ সরাসরি অসন্তোষ প্রকাশ করে দক্ষিণাবাবুকে জানাল। প্রায় বাধ্য হয়েই স্যারকে চারজন ছাত্র্কেও আমাদের সঙ্গে প্রেস দেখতে যাবার অনুমতি দিতে হল। আমরা ক’জনও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।
[the_ad id=”270085″]
কলেজ স্ট্রিটে দু’বছরের পাঠ্যক্রমের সময়, বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে এমন একজন মানুষের সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয়েছিল যাঁর কথা আপাতদৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও, আমাকে তাঁর কথা বলতেই হবে। তিনি অভিনেত্রী কেয়া চক্রবর্তী, আমার কেয়াদি। একবার আমাদের বিভাগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। ঠিক হল আমরা নাটক করব। নাটক শেখাতে এলেন নাট্যজগতের দুই বিশিষ্ট ব্যক্তি রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত আর কেয়া চক্রবর্তী। কী কারণে শেষ পর্যন্ত নাটক মঞ্চস্থ হল না, সে কথা আমার আজ আর মনে পড়ে না। কিন্তু রুদ্রদা, বিশেষ করে কেয়াদির সঙ্গে এই উপলক্ষ্যে বিশেষ ভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ হয়েছিল আমার। সেই শুরু। কলেজ স্ট্রিটের সেই দিনগুলিতে কেয়াদি আমার জীবনের সঙ্গে এমন ভাবে জুড়ে গিয়েছিলেন, যে ওই সময়ের কথা লিখতে গিয়ে আজ ওঁর কথা বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে। ওঁদের সঙ্গে দেখা হওয়ার মুহূর্ত থেকে কেয়াদি কী কারণে জানি না আমাকে স্নেহপাশে বেঁধে ফেলেছিলেন। আর আমি? আমি তো মুগ্ধ ওঁর অপার তেজোদীপ্ত সৌন্দর্যে। কী প্রাণবন্ত মানুষ! কী মায়াময় তাঁর চোখের ভাষা!তাঁর ঔদার্য, তাঁর মমতা বিস্মিত করত আমাকে। এমন মানুষকে ভাল না বেসে পারা যায়!

আমি তখন বসুমতীতে কাজ করছি। দুপুর দুপুর বাড়ি থেকে কাগজের দফতর। তারপরে সন্ধ্যেয় ক্লাস। তারই মাঝে নিয়ম করে কেয়াদির সঙ্গে দেখা হওয়া। কখনও দ্বারভাঙা বিল্ডিংয়ের সিঁড়িতে বসে গল্প, কোনওদিন সময় থাকলে বসন্ত কেবিনে চায়ে চুমুক দিতে দিতে গল্প। পুঁটিরামের লুচি তরকারি বা প্যারামাউন্টের শরবতের স্বাদ পাওয়া, সবই কেয়াদির কল্যাণে। দক্ষিণ কলকাতার মেয়ে আমি। এসব কিছুই চেনা ছিল না। কেয়াদির হাত ধরে প্রথম চেনা। কোনও কোনও দিন আমাকে ধরেবেঁধে কফি হাউসে নিয়ে যেতেন কেয়াদি। খাওয়া তো হতই, কিন্তু তার চেয়েও আমার কাছে আকর্ষণীয় ছিল কেয়াদির সঙ্গ। কত কিছু যে জেনেছি, ওঁর উৎসাহে কত নতুন বই যে পড়েছি সেসব কথা আজও ভুলতে পারিনি।
জাঁ পল সার্ত্রের সাহিত্য-সঙ্গিনী সিমন দ্য বোভোয়া সম্পর্কে কেয়াদির মুগ্ধতা সেই বয়সে আমার মনকেও স্পর্শ করেছিল। কাগজে আমার লেখা বেরুলে কেয়াদি কী যে খুশি হতেন। আবার লেখায় কোনও ত্রুটি চোখে পড়লে তা নিয়ে সমালোচনা করতেও কোনও দ্বিধা ছিল না। কেয়াদির কাছে ওঁর বন্ধু সুনন্দা বসুর কথা শুনেছিলাম। সুনন্দা তখন সবে কলকাতার ম্যাক্সমুলার ভবনে জার্মান শিক্ষকের পদে বহাল হয়েছে। জানি না কী বলেছিলেন কেয়াদি আমার কথা! কেয়াদির সূত্র ধরে সুনন্দার সঙ্গে আমার পরিচয় হল আর সেই থেকে গভীর বন্ধুত্ব। কেয়াদি আজ নেই। কিন্তু সুনন্দার সঙ্গে আজও আমার বন্ধুত্ব অটুট, নিবিড়।

সাংবাদিকতা, পড়াশুনো সবই চলছিল ঠিকঠাক মতো। হঠাৎই এর মধ্যে গুরুতর অসুস্থ হয়ে আমি শয্যাশায়ী হলাম। খবর পেয়ে আমাকে দেখতে কেয়াদি ছুটে এসেছিলেন আমার বাড়িতে। এক অদ্ভুত রোগ ধরেছিল আমাকে। সারা মুখে, গায়ে কালশিটে। সঙ্গে ধূম জ্বর। আমার চেহারা দেখে চোখে জল এসে গিয়েছিল ওঁর। অনেকদিন লেগেছিল সুস্থ হতে। সাংবাদিক হওয়ার স্বপ্নেরও ওখানেই ইতি। কেয়াদি সে সময়ে একদিকে নাটকের অভিনয়, মায়ের চিকিৎসার জন্য টাকা রোজগারের চিন্তা, সাংসারিক নানাবিধ সমস্যা, সব মিলিয়ে একটা খুব খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। কলেজে চাকরি করে, বাড়িতে ছাত্রছাত্রীদের পড়িয়ে, নাটক লিখে, অনুবাদ করে অনায়াসে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করতে পারতেন কেয়াদি। কিন্ত নাটকের প্রতি ওঁর প্রচণ্ড দায়বদ্ধতা, নিষ্ঠা থেকে তিনি নিশ্চিন্ত আয়ের পথটি ত্যাগ করেছিলেন অতি তাচ্ছিল্যভরে। এক এক সময়ে মনে হয় নিজের প্রতি বড়ই উদাসীন ছিলেন তিনি।
[the_ad id=”270086″]
ইতিমধ্যে আমি নিজেও সংসার, নতুন চাকরি এসব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। কেয়াদির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। মাঝে মাঝে ফোনে কথা হত মাত্র। ওঁর নাটক দেখতে যেতে বলতেন। কেয়াদি অভিনীত ‘ফুটবল’ দেখতে গিয়েছিলাম অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে। নাটকের শেষে দেখাও করেছিলাম। ভারি খুশি হয়েছিলেন কেয়াদি আমাকে দেখে। সেই স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করেছিলেন! ভাবতেও পারিনি কেয়াদির সঙ্গে সে দেখাই আমার শেষ দেখা হবে!
পেশা শুরু হয়েছিল সাংবাদিকতা দিয়ে। পরে নামী ইস্কুলের বাচ্চাদের দিদিমণি। কিন্তু লেখা চলল। তার সঙ্গে রাঁধা আর গাড়ি চালানো, এ দুটোই আমার ভালবাসা। প্রথম ভালবাসার ফসল পাঁচটি বই। 'নানা রাজ্যের অন্নব্যঞ্জন', 'মছলিশ' আর 'ভোজনবিলাসে কলকাতা' অন্যতম।











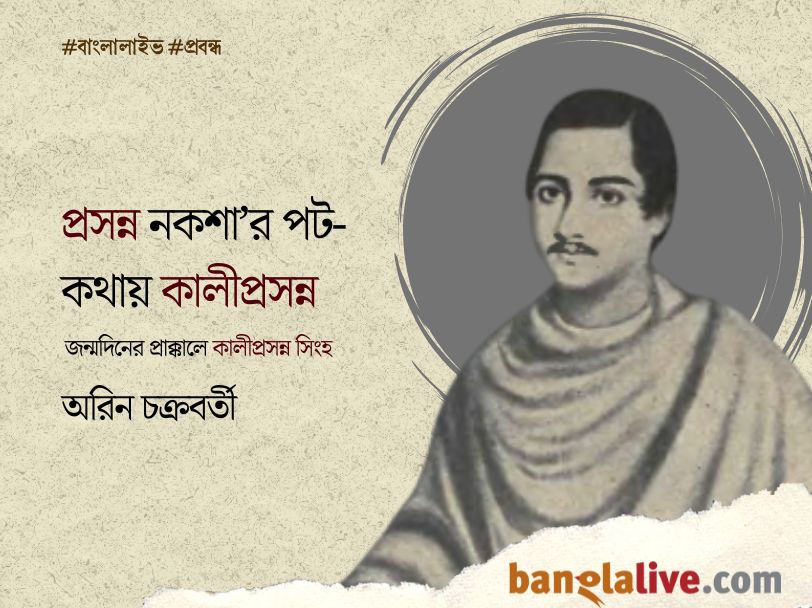








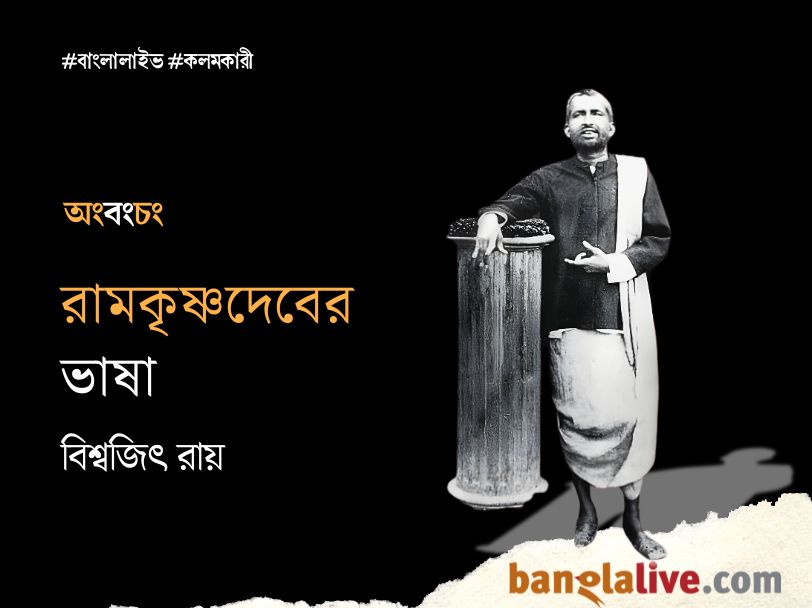





12 Responses
Protibar mugdho hoi….aaro aaro porte chai….apnar lekhoni cholte thakuk
একটি জিজ্ঞাসা, এখানে লেখা হয়েছে ‘প্যারাগনের সরবৎ’, আওটা কি প্যারামাউন্ট? মানে আগে প্যারাগন নাম ছিল? নাকি প্যারাগন আলাদা সরবতের দোকান?
প্যারাগন- প্যারামাউন্ট নাম নিয়ে একটু দ্বন্দ ছিল অনেকের মনে, আমারও। যাই হোক সংশোধন করা হয়েছে। ধন্যবাদ
As I recall, Paragon and Paramount were two sharbet shops side by side behind the College Square.
Pore mugdho holam
Pore mugdho holam
Ato sundor sohoj bhabe lekha jano protiti chobi chokher samne bheshe utheche. Khub buffalo laglo purono diner golpo sunte
khub bhalo laglo.er aager gulo sob besh legheche.
আপনি তো নেশা ধরিয়ে দিচ্ছেন । সাগ্রহে অপেক্ষায় থাকি। যখন পড়ি , গোগ্রাসে পড়ি।
Actually আপনি তো লেখেন না ছবি আঁকেন ।
অপেক্ষায় রইলাম এর পরের টির জন্য ।
সেই সময়ের এই স্মৃতিচারণ বড় ভালো লাগে।
আমার স্মৃতিও শ্রী শক্তি মুখার্জী মশাইয়ের সঙ্গেই যায়। কলেজ স্কোয়্যারের পেছুনে এক সময়ে পাশাপাশি দুটো শরবতের দোকান ‘প্যারামাউন্ট’ আর ‘প্যারাগন’ ছিল, পরবর্তীকালে যে কোনো কারণেই হোক ‘প্যারাগন’ দোকানটা বন্ধ হয়ে যায়।
রচনাটা ইতিহাসের আঁতুর ঘরে নিয়ে গিয়ে স্মৃতির আস্বাদন পাইয়ে দেওয়ার প্রচন্ড সহায়ক। উনার কলম সচল থাকুক। সুদীর্ঘকাল।