বড় পাপ তোমার রাজ্যে রাজন্, বড় অন্ধকার। বাতাস কলুষিত, সূর্য উঠতে লজ্জা পায়, ফুলেরা ফুটতে ভুলে গেছে। অসহায় মানুষের শ্বাসরোধ করছে কিছু ক্ষমতার পুজারী, উস্কানি দিচ্ছে ভাইয়ের বিরুদ্ধে, প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের, ধর্মের দোহাই দিয়ে, জাতের দোহাই দিয়ে। রাজপথ রাঙা হয়ে গেছে শিশুর রক্তে, শত বর্ষাতেও সে রক্ত ধোয় না। তোমরা ভুলে গেছ যে তোমাদের সৃষ্টি করেছে সে ধ্বংসও করতে পারে, তোমরা ভুলে গেছ…
— কী হল দাদু, বল। দিয়া ভুরু কোঁচকায়।
— আমিও ভুলে গেছি। মাধববাবু হতাশ হয়ে বলেন।
— উফ্ দাদু, কালকে তোমার প্লে। এখনও মুখস্থ হয়নি? দিয়া ঝাঁঝিয়ে ওঠে।
হবে কী করে? মাধববাবু মনে মনে অমর্ত্যর মুণ্ডপাত করেন। সবে এদেশে এসেছে, চার-পাঁচবছর কলকাতায় কোন গ্রুপ থিয়েটারে নাটক করে এখানে তার বিদ্যে ফলাচ্ছে। মহাভারতের “মুষলপর্ব” আধুনিক পরিপ্রেক্ষিতে ঢেলে সে একটা স্ক্রিপ্ট লিখেছে, সেটাই এবারের পুজোয় মঞ্চস্থ করতে চায়। নাটকের দলের বাকিরা মাধববাবুকে গিয়ে ধরেছিল।
— আপনি একটু বুঝিয়ে বলুন না, আপনি সিনিয়ার লোক, কথা শুনবে।
— অমর্ত্য, একটু হাসির নাটক করি না আমরা, এটা বড় সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছে। বলেছিলেন তিনি।
— মাধববাবু, আমি সিরিয়াস নাটক করছি না, সিরিয়াসলি করছি। মানুষ তার রিয়ালিটিকে বুঝতে চায় না বলে মিনিংলেস কতকগুলো ভাঁড়ামি থালায় সাজিয়ে দিতে হবে? অমর্ত্যর সোজাসাপ্টা জবাব।
মাধববাবু আমেরিকায় আছেন বছর দশেক, তিনি এখানকার দর্শকের পাল্স কিছুটা বোঝেন। তারা পুজোতে একটু আনন্দ করতে আসে, ভুলতে আসে গায়ের কালশিটেগুলো। পুজোটা আর যাই হোক, সমাজসচেতনতার পাঠ পড়ানোর জায়গা নয়।
— তা কেন, হাসির নাটক মানেই কি ভাঁড়ামি? কত ভাল ভাল নাটক আছে, মেসেজ আছে। একটু আমতা আমতা করে বলেন মাধববাবু।
— ঠিক আছে, পরের বার দারিও ফো-র একটা ফার্স করা যাবে। এবার এটাই হোক। অমর্ত্য তার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল।
— তোমার মেয়াদ এই এক বছরই বাবা — মনে মনে বলেন মাধববাবু। চান্স পেয়েছ তো এবারের পুজো কমিটির চেয়ারম্যানের ভাইপো বলে, আর কেশবের বাইপাস হয়েছে বলে। পরের বছর থেকে অডিয়েন্সে।
***
কেশবের সঙ্গে নাটক করা খুব মিস করেন মাধববাবু। বেশি মিস করেন রিহার্সাল। সারা সপ্তাহ মুখিয়ে থাকতেন রিহার্সালের জন্য, বলা ভাল রিহার্সালের মেনুর জন্য। কেশব খুব মেথডিক্যাল, রিহার্সাল শুরুর একমাস আগে একটা সাইন আপ শিট পাঠাতেন কবে কার বাড়ি রিহার্সাল হবে সেটা ঠিক করতে। যার বাড়ি রিহার্সাল, তার দায়িত্ব লাঞ্চ বা ডিনারের। এবং একটা অলিখিত কম্পিটিশান শুরু হয়ে যেত তার মেনু নিয়ে। লখনৌ বিরিয়ানি আর গলৌটি কাবাব, তিল আর সরষে দিয়ে তিলোত্তমা রুই, ডিম বেগুনের ভুজিয়া, চাটগেঁয়ে শুঁটকি, মাটন্ চাঙ্গেজি… ভাবতে ভাবতে কীরকম আবেশে বুঁদ হয়ে যান মাধববাবু। বস্তুতঃ এই নাটকের অজুহাতে এমন সব জিনিস খেয়েছেন, যেগুলো আগে কখনও খাননি। মৌমিতা সরকার বলে একটি বাংলাদেশি মেয়ে নাটক করেছিল কয়েকবার তাঁদের সঙ্গে। সে একবার রান্না করেছিল মুরগির গলা, কলজে আর চামড়া দিয়ে করলা ভাজা। এটা নাকি নারায়ণগঞ্জের স্পেশালিটি। খুব ভয়ে ভয়ে মুখে একটুখানি দিয়ে চমকে গিয়েছিলেন মাধববাবু। সত্যিই খুব সুস্বাদু, এতটা তিনি আশা করেননি!
তাই বলে রিহার্সালে যে শুধু খাওয়াদাওয়া হত, তা নয়। নাটকটাও হত। আসলে নাটক নিয়ে কারও মনে বিশেষ ভয় ছিল না। কারণ একটাই। প্রম্পটার।
— প্রম্পটার? আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন? প্রম্পটিং করে নাটক হয় নাকি? অমর্ত্য এমনভাবে তাকিয়েছিল মাধববাবুর দিকে, যেন তিনি অন্য গ্রহের লোক।
— কেউ মনে রাখতে পারবে না। আর কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টাচার্যের মতো অভিনেতারাও তো প্রম্পটারের সাহায্য নিতেন।
— সে তখন ছিল, আজ অন্যরকম। প্রম্পটিং একটা ক্রাচ, যে হাঁটতে পারে তাকে দিচ্ছেন। সে তো কোনও দিন হাঁটতেই শিখবে না!
হয়তো সত্যি। কিন্তু ঐ প্রম্পটিং- এর হাত ধরেই তো নাটকের সঙ্গে পরিচয়। অফিস ক্লাবের নাটকের ডিরেক্টার ছিলেন বরুণদা। একদিন খুব হন্তদন্ত হয়ে মাধববাবুকে ধরেন ক্যানটিনে।
— আপনি নাটক করেছেন কখনও?
— হ্যাঁ, স্কুলে ছোটবেলায়…
— আমাদের অ্যানুয়াল ফাংশানে নাটকের জন্য প্রম্পটার দরকার। বিশ্বেশ্বর আমাদের প্রম্পটার, অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, ছ মাস বিছানায়। আপনাকে করতে হবে।
— আমি প্রম্পটিং কখনও করিনি।
— নাটক করতে পারেন, বাংলা পড়তে পারেন – ওতেই চলবে।
সেই শুরু। মঞ্চের সঙ্গে, নাটকের সঙ্গে, অভিনয়ের সঙ্গে আলাপ। কাজটা যতটা সহজ ভেবেছিলেন, দেখলেন অতটা সহজ নয়। প্রম্পটারকে নাটকটা আগাপাশতলা জানতে হবে, জানতে হবে কে কখন কোথা থেকে ঢুকছে, বেরচ্ছে, পজ় দেবার মাত্রা তৈরি করতে হবে, যাতে অভিনেতা পার্ট ভুলে গেলে প্রম্পটিং ঠিক সময় পৌঁছে যাবে তাদের কানে। প্রম্পটার নাটকের দ্বিতীয় পরিচালক, উইংসের পাশ থেকে, তার উপর দায়িত্ব নাটকটা ঠিক ভাবে চালিয়ে নিয়ে যাবার, একটা সিম্ফনির কন্ডাক্টারের মতো।
— মাধব, প্রম্পটিংটা একটা আর্ট। বরুণদা বলেছিলেন। বরুণদা নাটকের অনেক বই পড়তেন, স্তানিস্লাভ্স্কি, ব্রেশট্, থেকে অ্যালবি, মিলার … ওদিকে বাংলায় উৎপল দত্ত, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, বাদল সরকার, মনোজ মিত্র।
— জানো তো, বিখ্যাত অস্ট্রেলিয়ান ডিরেক্টর টেরেন্স ক্লার্ক বলেছিলেন প্রম্পটিং শুড বি ওয়ান্স, লাউড, এনাফ। একবার বলবে, জোরে বলবে আর ঠিক ততটুকুই বলবে যতটুকু অ্যাক্টরের দরকার।
একটু সময় লাগল। প্রথমে ভয় ভয় করছিল। তারপর ভাল লাগতে শুরু করল, নেশা ধরল। আস্তে আস্তে নতুন অভিনেতারা এসে পরামর্শ নিতে লাগল, মাধববাবু খুব মেধাবী ছাত্রের মতো বরুণদার ডিরেকশান দেখতেন। ফলে তিনি যা চান, সেটা বোঝাতে অসুবিধে হত না। আর এভাবেই সুপ্রভার সঙ্গে আলাপ।
— মাধবদা, বুঝতে পারছি না এই জায়গাটা কী করে বলতে হবে। একটু দেখিয়ে দেবেন?
মাধববাবু গ্রিনরুমে বসে মনে মনে দ্বিতীয় দৃশ্যের গোড়াটা আর একবার ঝালিয়ে নিচ্ছিলেন। সবার আগে আসেন তিনি, ঘরে একাই ছিলেন। খেয়াল করেননি ঘরে এন্ট্রি হয়েছে আর একটি চরিত্রের।
সুপ্রভা দাঁড়িয়েছিল জানলাটার সামনে তার মেঘের মতো চুল নিয়ে। ঠিক সেই সময় কোথাও কোনও এক অদৃশ্য স্ক্রিপ্টের নিয়ম মেনে বিদ্যুৎ চমকাল আকাশে, সুপ্রভার মাথার ঠিক পিছনটাতে। আলো-আঁধারিতে সুপ্রভার পানপাতা মুখটা রহস্যময় লাগছিল, একটা আশ্চর্য মখমলি লাবণ্য ঝরে পড়ছিল তার মুখ থেকে, আকাশ তার লাইট আর সাউন্ড এফেক্টের যুগলবন্দি চালিয়ে যেতে লাগল, আর বৃষ্টি ঝরল মাধববাবুর বুকের মধ্যে। সারা জীবনের মতো।
— কী হল দাদু? হোয়্যার আর ইউ লস্ট? দিয়া অধৈর্য হয়ে পড়ে।
— সরি দিদি। আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম।
— ইউ মিন আনমাইন্ডফুল? দ্যাখো, আই ডু নট কেয়ার অ্যাবাউট পুজো। তুমি প্লে করছ বলে আমি তোমাকে হেল্প করছি। বাবা আমাকে তোমার কথাগুলো ইংলিশ স্ক্রিপ্টে লিখে দিয়েছে, আর আমি বসে আছি এখানে। প্লিজ় পে অ্যাটেনশান।
মাধববাবু নাতনির ধমক খেয়ে মনে মনে হাসেন। এই ধমকটার সঙ্গে উনি পরিচিত। অনেক বছর ধরে। বিয়ের পর থেকেই।
সুপ্রভা আর মাধববাবুর সংসারটা একটা সুন্দর ছন্দে চলত। আসলে তাঁদের মধ্যে ঐ থিয়েটারের ভাষায় যাকে বলে একটা ‘কেমিস্ট্রি’ ছিল। দু’জনেই দু’জনকে বুঝতেন। শুধু পছন্দ, অপছন্দ নয়, সীমারেখাটাও। অনেক ভালবাসার মধ্যে জড়িয়ে থাকা দম্পতি কখনও কখনও যেটা বোঝে না, বোঝে না মানুষকে তার জায়গা কিছুটা ছেড়ে দিতে হয়। দিলে সে আবার নিজের টানেই ফিরে আসে তার ঘরে।
অফিসের থিয়েটারে মাধববাবু যতই প্রম্পটিং করুন না কেন, সংসারের প্রম্পটিংটা তিনি পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছিলেন সুপ্রভার উপরে। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করেই পার্ট ভুলে যেতেন তিনি, অপেক্ষা করে থাকতেন কখন প্রম্পটারের গলা শুনতে পাবেন। সুপ্রভার রাগ, বিরক্তি, আর ভালবাসা মিলে মিশে একাকার হয়ে যেত তাঁদের সংসারের উঠোনে।
— আচ্ছা দিদি, তোর পুজোর উপর এত রাগ কেন? মাধববাবু প্রশ্ন করেন।
— তোমাকে তো আগেই বলেছি দাদু। আমার পুজোর সেক্সিস্ট রিচুয়ালস্গুলো ভাল লাগে না। সিঁদুর খেলা, কুমারী পুজো, সব মেয়েদের অনুষ্ঠান, গ্লোরিফাই করছ মেয়েদের মাদারহুড, রোলস অ্যাজ় ওয়াইফ, যেন মেয়েদের পরিচয় শুধু ওটাই। কোথাও তো ছেলেদের সিমিলার কোনও রিচুয়ালস নেই। ফ্যামিলি কি শুধু একা মেয়েদের?
দিয়া যখন খুব ছোট, বছর ছয়-সাত, তখন একবার কুমারী পুজোতে সে যোগ দিয়েছিল। সেটা তার কাছে একটা ট্রম্যাটিক অভিজ্ঞতা। ঐ ঘণ্টা, কাঁসর, ঢাক, ধুনো —– সবাই ঘিরে দাঁড়িয়ে চারদিকে, একটা ভয়ের আবহাওয়া ঘিরে ফেলেছিল তাকে। পুজোর মণ্ডপ থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এসেছিল সে। তার মায়ের শত চেষ্টাতেও আর ফেরেনি। হয়তো তখন থেকেই অ্যাভারশান তৈরি হয়েছে।
— কিন্তু দেখ এটা তো নারীপুজো, পুরুষেরাই তো তাকে পুজো করছে।
— সেটা তো পুরুষদেরই তৈরি। ফর সেঞ্চুরিজ় কোনও মেয়ের পুজো করার অধিকার ছিল কি? শুধু ছেলেরাই কেন মেয়েদের পুজো করবে? জাস্ট টু অ্যাটোন ফর দেয়ার অ্যাট্রোসিটিস এগেন্সট উইমেন? যা আজও ঘটে চলেছে বেঙ্গলের ঘরে ঘরে, রাস্তায় ঘাটে?
মাধববাবুর সামনে সুপ্রভা বসে আছে। সেই চোখ, সেই বাঁকানো ঘাড়, সেই ভুরুর ভাঁজ।
— আর নারীপুজো বলছ দাদু? দিয়া তখনও থামেনি। “দুর্গাকে তো ক্রিয়েট করেছে মেন গডস, তাদের শরীর, তাদের ওয়েপন, তাদের পাওয়ার দিয়ে। কিসের নারী?”
— পুজোটা তোদের ঐ গুগল আর উইকিপিডিয়া দিয়ে বুঝবি কী করে দিয়া? দিয়ার বাবা সুব্রত শুনছিল দাদু আর নাতনির কথা পাশের ঘর থেকে। সে এবার ঘরে আসে। “পুজোটা বাঙালির আনন্দ, তাদের থেরাপি, মরতে মরতে বেঁচে থাকা। তুই আমেরিকার পুজো দিয়ে কিচ্ছু বুঝবি না। বুঝতে গেলে তোকে যেতে হবে কলকাতায়। থাকতে হবে কোনও বাড়ির পুজোয়, কয়েকশো বছর ধরে যেখানে পুজোর প্রচলন। তোকে ট্র্যাডিশানের আসল মানেটা বুঝতে হবে।”
— কিন্তু দিয়া তো ভুল কিছু বলছে না সুব্রত। এই কয়েকশো বছর ধরে চলা রীতিনীতিগুলো নিয়ে একটু ভাবার দরকার তো আছে। এ চেঞ্জ ইন থিঙ্কিং ইস নিডেড। দিয়ার মা এবার আলোচনায় যোগ দেয়। মাধববাবু বোঝেন আজকের মতো পার্ট মুখস্থ করার পাট চুকল।
***
— দাদা, চেঞ্জটাই একমাত্র কন্সট্যান্ট, এটা নিয়ে দুঃখ করে কী লাভ? পলাশ বলছিল ক্যান্টিনে বসে। বরুণদা ততদিনে রিটায়ার করেছেন। নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা আসছে অফিসে। অনেকের নাটক থিয়েটারে খুব আগ্রহ। তারা নাটক করে কোনও প্রম্পটিং ছাড়াই। মাধববাবুর থিয়েটারের সঙ্গে যোগাযোগটা গেছে। এখন তিনি শুধুই দর্শক।
— দাদা থিয়েটার এত মিস করো। বলে দ্যাখো না যদি নতুন ডিরেক্টর তোমাকে কোনও রোল টোল দ্যায়? মনু মুখোপাধ্যায়ের মতো অভিনেতাও শুনেছি নাটকে এসেছিলেন প্রম্পটিং-এর হাত ধরে। পলাশ তাঁকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করে।
— তুমিও পার পলাশ। কোথায় মনু মুখোপাধ্যায় আর কোথায় আমি?
দু’একবার ছোটখাটো রোলে চেষ্টা করেছিলেন, জমেনি। পারেননি চৌকাঠটা পেরোতে। সবাই পারে না।
সুযোগটা আবার এল বছর দশেক আগে, অপ্রত্যাশিতভাবেই। সুপ্রভা বহুদিন লিভার ক্যানসারে ভুগে সংসারের প্রম্পটারের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন চিরতরে। মাধববাবু রিটায়ার করেছেন। একাই থাকেন। ছেলে, মেয়ে দু’জনেই আমেরিকায়। একদিন বাজারে যেতে গিয়ে পড়ে গেলেন তিনি।
— মাইল্ড স্ট্রোক হয়েছিল, এ যাত্রা বেঁচে গেলেন।
ছেলেমেয়ে কালকের মধ্যে এসে পড়বে। হাসপাতালের বেডে শুয়ে ডাক্তারের কথা শুনে মাধববাবু খুব যে খুশি হলেন তা নয়। এমনিতেই সুপ্রভা যাবার পর জীবনের খেই হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। বেঁচে থাকাটা একটা রুটিনের মতো লাগছে এখন। তার উপর পরিষ্কার বুঝতে পারলেন এবার ছেলেমেয়েরা চাপ সৃষ্টি করবে, তাঁকে তাদের সঙ্গে নিয়ে যাবার। সুপ্রভা বেঁচে থাকতে জোরের সঙ্গে ঠেকাতে পেরেছিলেন বিদেশবাস। এবার কী করবেন? যা ভেবেছিলেন তাই হল।
— শোনো বাবা, পাসপোর্টটা রিনিউ করার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছি। গণেশকে বলে দিয়েছি, টাকাও দেওয়া আছে। ও সবটা দেখবে। হয়ে গেলেই ভিসার ফর্ম ভরতে হবে। সঞ্জনা বেশ জোরের সঙ্গে বলে। কোনও পরামর্শ নয়, সিদ্ধান্ত জানায়।
— তোরা কি পাগল হলি? আমি আমেরিকায় গিয়ে থাকব? এই বয়েসে?
— এটাতে আকাশ থেকে পড়ার কী আছে? এটাই এখন নিয়ম, ঘটছে প্রত্যেকটা ঘরে।
হ্যাঁ, সেটা খুব সত্যি। যতদিন জোড়া আছ, দেশে থাক, দূরে থাকা ছেলেমেয়েকে ফোন আর ল্যাপটপে বসিয়ে জন্মদিন আর বিজয়ার আশীর্বাদ কর। যেই একা হলে, ওমনি নতুন চ্যাপটার শুরু হল – পরবাসে নির্বাসন। ঘর ঘর কি কাহানি।
— বাবা, শোনো, মা যখন ছিল একরকম ছিল। এখন তোমাকে দেখার কেউ নেই। প্রত্যেকবার তোমার কিছু হলে আমি আর সঞ্জু ছুটে আসতে পারব না। ছেলে প্রতীক এবার বোনের গলায় গলা মেলায়।
— দেখ, নভেম্বরে তোমাকে আসতেই হবে লাইফ সার্টিফিকেট জমা দেবার জন্য। তখন মাস দুয়েক কাটিয়ে যেও। সঞ্জনা বাবার মনের ভাব বুঝতে পেরে নরম গলায় বলে।
এর পরের গল্পটা আর পাঁচটা গল্পের মতোই। দু’মাসের মধ্যে মাধববাবুর প্লেনটা মাটি ছাড়ল। সারাটা পথ পাড়ি দিয়ে ইমিগ্রেশানের পোর্ট অফ এন্ট্রিতে যখন পৌঁছলেন, মনের অসন্তোষটা বোধ হয় মুখে ছায়া ফেলেছিল।
— নো মিস্টার চক্রবর্তী, আই ক্যানট লেট ইউ গো। ইমিগ্রেশান অফিসারের গলাটা গম্ভীর।
ব্যাটা বলে কী? তবে কি আশা আছে? মাধববাবুর মনটা হঠাৎ খুশি খুশি লাগে।
— আনলেস ইউ স্মাইল ফর দ্য ক্যামেরা। নোবডি লিভস মাই কাউন্টার উইদাউট এ স্মাইল।
ব্যাজার মুখে লাগেজ কার্টটা যখন সঞ্জনা আর দিয়ার উচ্ছ্বসিত হাত নাড়ার দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখনও জানতেন না জীবন তাঁকে দ্বিতীয়বার একটা সুযোগ দিচ্ছে।
***
— কী কেশব, এবার পুজোয় কী নাটক করছ?
নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও সঞ্জনা আর সুব্রতর পীড়াপীড়িতে ওদের এক বন্ধুর বাড়ির পার্টিতে এসেছেন মাধববাবু।
— শাশ্বতর বাবা-মা এসেছেন দেশ থেকে, ও খুব করে তোমায় নিয়ে যেতে বলেছে। চলো না বাবা। সঞ্জনার গলাটা কাতর শোনায়। বাবাকে নিয়ে তো এসেছে তাদের কাছে। কিন্তু তাঁর হাঁড়িমুখ আর মেজাজ সামলাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে।
— তোরা ঘুরে আয় না। আমি টিভি দেখে কাটিয়ে দেব। এখানে এসে নতুন করে বন্ধু বানাবার কোনও ইচ্ছাই তাঁর ছিল না।
— দাদু, চলো। আমার বন্ধুদের সঙ্গে তোমায় ইন্ট্রো করিয়ে দেব। দে আর ভেরি কুল। দিয়া বায়না ধরে।
— কিন্তু আই ফিল লাইক এ ফুল। বেমানান।
— আচ্ছা, তুমি যদি আসো আমাদের সঙ্গে, আমি বাবাকে বলে সানডেতে বাভারিয়ান টাউনে যাব। দিয়া টোপ ফেলে।
এই জায়গাটা মাধববাবুর পছন্দ। একটা ছোট্ট জার্মান শহরের মতো সাজানো। অনেক দোকান, রেস্তোরাঁ। তবে মাধববাবুর যেটা সবচেয়ে পছন্দ, সেটা একটা দোকান। নাম স্টেজডোর। একটা দোকান, সেখানে ঢোকা মানে জার্মান থিয়েটারের জগতে ঢুকে পড়া। কস্টিউম, মেক আপ, লাইট, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগের সময় থেকে শুরু করে জার্মান নাটকের বিবর্তনের ইতিহাস সারা দেয়াল জুড়ে। সেই সঙ্গে আছে বিখ্যাত সব নাট্যকারের ছবি। ব্রেশট, মুলার, গ্যেটে আরও কতজন। একটা ক্যাফে আছে এক কোণে, তাতে নানা জার্মান স্পেশালিটি পাওয়া যায়। একটা কফি নিয়ে এখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারেন মাধববাবু। দিয়া খেয়াল করেছিল এই দোকানে ঢুকে দাদুর চোখে একটা আলো ফুটে উঠেছিল, যেমনটা ও দেখত ছোটবেলায় কলকাতায় গেলে, দাদু আর দিদানের বাড়িতে।
শাশ্বতর বাড়িতে বসে থাকতে থাকতে মনে হচ্ছিল টোপটা গিলে ভাল করেননি। কাঁহাতক আর পেনশান আর ডায়াবিটিসের পথ্যি নিয়ে খোশগল্প চালানো যায়।
— নাটক তো ঠিক করেছি। কিন্তু একটা মুশকিল হচ্ছে। মাধববাবু এবং আরও কয়েকজন ডাইনিং টেবিলে বসে খাচ্ছিলেন। কেশব নামের ভদ্রলোকটি তাঁর পাশেই বসেছিলেন। ইলিশ মাছের কাঁটা থেকে মাছকে মুখের ভিতরে চালান করে উত্তরটা দিলেন।
— কী মুশকিল? নাটক পেয়ে গেছ, রিহার্সাল শুরু করে দাও। রগড়ের নাটক বেছেছ তো?
— সে সব ঠিক আছে। কিন্তু প্রম্পটার পাচ্ছি না।
— কেন, তোমার তো অনেক প্রম্পটার। তরুণ, হীরক, ঝুলন, তারা কেউ অ্যাভেলেবল নয়?
— না, এবার সবাই অ্যাক্টিং করতে চাইছে। কেউ প্রম্পট করতে চাইছে না।
— সে কী! তরুণের তো ‘স’-এর দোষ, আর ঝুলন তো স্ট্যাচুর মতো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলে। ওরা স্টেজে উঠবে?
মাধববাবু খেয়াল করেছেন বাঙালিরা খুব দিল খুলে পরনিন্দা করতে পারে। এও জানেন আজ যাকে সমালোচনা করছে, কাল তার বাড়িতে গিয়ে কচি পাঁঠার ঝোলে চুমুক দিয়ে অনুপস্থিত অন্য কারও পিছনে কাঠি করবে। সব জায়গার বাঙালির এক চেহারা। এটা একটা জেনেটিক ব্যাপার মনে হয়। কিন্তু সেদিকে মাধববাবুর মন ছিল না। তিনি তখন অন্য কথা শুনছেন।
— এ নাটকটায় অনেক ক্যারেক্টার। আমার এমনিতেই লোক লাগবে। কেশব বলছিলেন।
— আপনারা প্রম্পটিং করেন? মাধববাবুর গলা থেকে প্রশ্নটা উঠে কখন সুড়ুৎ করে মুখের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসেছে, তিনি নিজেও খেয়াল করেননি।
কেশব ঘাড় ঘুরিয়ে মাধববাবুকে আপাদমস্তক জরিপ করে। “দেখুন, এখানে কোনও দেবশঙ্কর, গৌতম হালদার নেই। যাদের পাই তাদের নিয়েই নাটক করি। সবাই মিলে একটা আনন্দ করার জন্য। সারা সপ্তাহ অফিস করার পর অনেক কিছু কম্প্রোমাইজ় করে লোকে উইকএন্ডে রিহার্সাল দ্যায়। তাই আমিও কিছু কম্প্রোমাইজ় করি।”
— আমি করতে পারি?
— আক্টিং করবেন?
— না, প্রম্পটিং।
— আপনি প্রম্পটিং করবেন?
সঞ্জনা এতক্ষণ দূর থেকে শুনছিল। এবার এগিয়ে আসে। “কেশব কাকু, বাবা পনেরো বছর অফিস থিয়েটারে প্রম্পটিং করেছেন, বেশ সুনাম ছিল।”
— নমস্কার, আমি কেশব চট্টোপাধ্যায়। আপনার নামটা জানা হয়নি।
আচমকা ঘরের সবগুলো লাইট ঘুরে মাধববাবুর উপর ফোকাস করল। পরের সংলাপ তাঁর।
— আমি মাধব চক্রবর্তী।
বাতাসটা ঘরে আটকে ছিল, জানলাটা খুলতেই বেরিয়ে পড়ল। একটা বহতা নদীর গতি রুদ্ধ হয়ে ছিল, পাথর সরিয়ে দিতেই স্রোত বইতে লাগল আবার। অনেক বছর পর মাধববাবু আবার পুরনো রোলে ফিরলেন। এখানে বাঙালিরা নাটক ভালবাসে। বছরে দু’টো নাটক হয়, নববর্ষে আর দুর্গাপুজোয়। নাটক হয়, কিন্তু রিহার্সালটা হয় এলোমেলো। কেশব আসলে যত ভাল অরগানাইজার, তত ভাল ডিরেক্টর নন। মোটামুটি লোকে নিজেদের খুশিমতো নিজের পার্টটা বলত, ফলে নাটকটা অনেকগুলো আলাদা আলাদা সংলাপের পরিবেশনা মনে হত। দুর্গাপ্রতিমার সবগুলো মূর্তিকে পাশাপাশি বসানো হয়েছে, কিন্তু একচালা নয়। মাধববাবুর অভিজ্ঞতা কেশবের কাজে লাগল। প্রম্পটিং করতে করতে ছোটখাটো সাজেশান দিতেন তিনি, অভিনেতা কোথায় দাঁড়ালে দর্শকরা ভাল শুনতে পাবে, কীভাবে পজ় দিলে সেও প্রম্পটিং শুনতে পাবে, সবটার মধ্যে একটা সিস্টেম আছে। এই সিস্টেমটাই মাধববাবু চালু করলেন। বড় নাটকে একজন সহকারীও নিয়ে নিতেন তিনি যে অন্য উইংসে থাকবে। একটা ছন্দ এল নাটকে। প্রতিমা একচালা হল।
সঞ্জনা আর প্রতীক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল বাবার এই পরিবর্তনে। বুঝেছিল একটা মানে, যেটা হারিয়ে গিয়েছিল, মাধববাবু খুঁজে পেয়েছেন আবার অনেকদিন পর। তাই খুব অবাক হয়নি যখন অল্প চেষ্টাতেই গ্রিন কার্ড করতে রাজি হয়ে গেলেন মাধববাবু। কলকাতা যেতেন বছরে একবার, মাস তিনেকের জন্য, কালীপুজোর পর। চলছিল ভালই, অমর্ত্য সব বিগড়ে দিল।
— নাঃ প্রম্পটিং থাকবে না, কিন্তু আপনাকে আমার চাই। একটা পার্ট করতে হবে। অমর্ত্য বলেছিল।
— ওটি আমার দ্বারা হবে না ভাই। উইংসের ধার থেকে আমি বেরতে পারব না। সবাই পারে না।
— সেটা বললে চলবে না মাধবদা। পার্টটা ঈশ্বরের, সে রাজ্যের রাজাকে ভর্ৎসনা করছে অরাজকতার জন্য, এবং ভবিষ্যদ্বাণী করছে ধ্বংসের। মুষলপর্বের উপর বেস করে, কিন্তু পুরোটাই সিম্বলিক। অনেক আজকের রেফারেন্স আছে, রেলেভেন্সটা বোঝাতে চেয়েছি।
— সে সব ঠিক আছে, কিন্তু আমি নার্ভাস হয়ে যাই স্টেজে উঠলে।
— আপনার তো পুরো নাটকটাই মুখস্থ থাকে। জাস্ট এক্সপ্রেশান দিয়ে বলা। আমি জানি আপনি কেশবদার নাটকে অনেক অ্যাক্টরকে দেখিয়ে দ্যান। প্লিজ় না বলবেন না।
না বলতে না পারাটার জন্য মাধববাবু সারাজীবন অনেক বিপদে পড়েছেন। আবার পড়লেন।
***
ঘরের নানাদিকে ছড়ানো ছিটনো আছে কিছু চেয়ার। তার একটাতে বসেছিলেন মাধববাবু। একটু কোণের দিকে। সেখান থেকে মা দুর্গার মুখের বাঁ দিকটা দেখা যাচ্ছে। শিল্পীর হাতের নিঁখুত টানে প্রতিমার মুখের দু’দিকটাই হুবহু খাপে খাপে মিলে গেছে। মাধববাবু জানেন সব মানুষের মুখ এ রকম হয় না। ডান দিকের উইংস থেকে যাকে কুৎসিত লাগে, বাঁ দিকের উইংস থেকে সে-ই অপরূপ সুন্দরী। মহিলারা সুন্দর সুন্দর শাড়ি পরে একবার ডান দিকে, একবার বাঁদিকে মুখ ঘুরিয়ে ছবি তোলেন। এই নিয়ে সুব্রত একবার সঞ্জনাকে ভীষণ ঠাট্টা করেছিল। তখন মাধববাবু বুঝিয়েছিলেন। মানুষের দু’দিক সমান ফোটোজিনিক হয় না। ঈশ্বরের সৃষ্টিতেও তো খুঁত থাকে।
এই ঘরটা একটা চার্চের বেসমেন্টে। এই সময় এখানে কেউ নেই। সবাই উপরে তনু ও মনুর যুগলবন্দি শুনছে। এরা কোন এক রিয়েলিটি শো থেকে উঠে আসা ভাইবোন। সবাই সেই শো দেখতেই ব্যস্ত, দেখতে আর নাচতে। মাধববাবু কয়েকবার দেখেছেন, এই কলকাতা থেকে আসা শিল্পীদের শোগুলো যখন চলে, তখন হলের চেয়ারগুলো ভারী একা হয়ে যায়। সবাই স্টেজের সামনে, নাচছে, মানে হাত পা ছুঁড়ছে ইচ্ছেমতো। নানারকম ছন্দে। তার ছন্দগুলো যে সব মিউজ়িকের ছন্দে মিলছে তা নয়, তাতে কী? এটা তো আর ‘ডান্স পে চান্স’-এর অডিশান হচ্ছে না!
এই সময় বেসমেন্টটাও খুব একলা থাকে। তাই এখানে চলে এসেছেন তিনি। ভিড় থেকে পালিয়ে। গাড়ি চালাতে জানলে এখনই বাড়ি চলে যেতেন।
— দাদা ভাল করেছেন, তবে নাটকটা একটু শক্ত। মাথার উপর দিয়ে গেল।
— একটু অডিওর গন্ডগোল হচ্ছিল। তবে আপনার নাটক করার অভ্যেস যে আছে বোঝা যায়।
— দাদু, খুব ভাল লাগছিল তোমাকে দেখতে।
— কী হল এটা মাধববাবু। বড় সিরিয়াস হয়ে গেল তো। হাসি কই?
কথাগুলো এক কান দিয়ে ঢুকছিল, আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল মাধববাবুর। সত্যিই এটা কী হল? দিয়ার সঙ্গে এত ভাল করে রিহার্সাল দিলেন তিনি। ঠিক করলেন কোন কথাটা কী ভাবে বলবেন। মঞ্চের কোনদিকে হেঁটে যাবেন কোন কথার সঙ্গে। সব গুলিয়ে গেল। স্পটলাইটের গরমে মুখের মেকআপ গলছে। দর্শকদের মুখের দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারেন তাঁদের দৃষ্টি বিদ্ধ করছে তাঁকে। পিছন থেকে কেউ চেঁচিয়ে বলল – “শুনতে পারছি না মাধবদা, জোরে বলুন।“ জোরে বলুন? তিনি তো কিছু বলেনইনি। যন্ত্রচালিতের মতো তাকালেন উইংসের দিকে, সেখানে তো তাঁরই থাকার কথা ছিল। এখন সেখানে অমর্ত্যর ভয়ার্ত মুখ। লোকে দেখল চোখ বুজে বিড়বিড় করে চলেছেন মঞ্চের ঈশ্বর। তিনি তখন তাঁর পরমেশ্বরের কাছে প্রাণপণে চেয়ে চলেছেন তাঁর সংলাপগুলো।
এর পরের কথা মাধববাবুর আর ভাল মনে নেই। অমর্ত্য দৌড়ে স্ক্রিপ্টটা নিয়ে এসে তাঁর লাইনগুলো বলেছিল, না কো-অ্যাক্টর তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছিল, নাকি তাঁর নিজেরই মনে পড়ে গিয়েছিল, এসব ভুলে গেছেন তিনি। শুধু মনে আছে নাটকের শেষে স্টেজে দাঁড়িয়ে পরিচয় পর্বের সময় তিনি চাইছিলেন যদি আধুনিক স্টেজগুলোর মতো এটারও মাঝখানটা একটা লিফটের মতো নেমে যেত তাঁকে নিয়ে, বেশ হত। অথচ সমস্ত লাইনগুলো এখন ঝরঝর করে বলে যেতে পারেন মাধববাবু, এই ফাঁকা ঘরে, মা দুর্গাকে অডিয়েন্স রেখে। মা দুর্গার বাঁ দিকটা দেখতে দেখতে এই সব কথা ভাবতে ভাবতে মাধববাবু খেয়াল করেননি কখন ঘরটা ভরে উঠেছে। আরতির সময়। ঢাকে কাঠি পড়ছে। কাঁসর ঘণ্টা বাজছে। ধুনুচির ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করছে। এতক্ষণ অডিটোরিয়ামে নাচছিল যারা, তারা এবার নেমে পড়েছে ঠাকুরের সামনে। তাঁর দিকে কেউ ফিরেও তাকাল না।
— কেলো হয়েছে। মন্ত্রের প্রিন্টআউটটা বাড়িতে ফেলে এসেছি। অমর্ত্য আর্তনাদ করে ওঠে। তার এবার ডাবল রোল। পুজোর পুরুতও সে। এটাও রিপ্লেসমেন্ট।
— অষ্টমী পুজোর মন্ত্র তো? ঠিক আছে ফোনে বার করে নিচ্ছি। কেউ একজন বলে ওঠে।
— পারবেন না। কোনও সিগন্যাল নেই এখানে। এখানকার ওয়াইফাই পাসওয়ার্ডও জানা নেই। অরগানাইজ়ারদের কেউ একজন বলে ওঠে।
— কাউকে পাঠান না কাছে পিঠের কোন কিঙ্কোস-এ। অবশ্য যদি এখন খোলা থাকে। তৃতীয় একজন মন্তব্য করে।
— থাক, আমিই বাড়ি গিয়ে নিয়ে আসছি। আপ অ্যান্ড ডাউন ঘণ্টাখানেক লাগবে। অমর্ত্যর গলাটা হতাশ শোনায়।
—- আমি অষ্টমী পুজোর মন্ত্র জানি, বলে দিতে পারি।
সারা ঘরের সবগুলো চোখের ফোকাস মাধববাবুর উপর। লোকটা বলে কী? মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে রিহার্স করা পার্ট ভুলে গেল, আর স্মৃতি থেকে সংস্কৃত মন্ত্র বলবে?
— আমার বাবা যজমান ছিলেন। দেশের জমিদার বাড়িতে দেড়শো বছরের পুরনো পুজো হত। উনিই পুজো করতেন। আমি সবসময় বাবার সঙ্গে থাকতাম। আমার পুজোর সব মন্ত্র মুখস্থ।
নমঃ সৃষ্টিস্থিতি বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনী…।
ঘরের মধ্যে শ’খানেক লোক হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। মা দুর্গার নিঁখুতভাবে তৈরি ডান, বাঁ দু’চোখেই ঝরে পড়ছে কৌতুক। তিনি দেখছেন তাঁর পায়ের কাছে বসে পুজো করছে একজন সাবস্টিটিউট পুরোহিত। আর পাঁচহাত দূরে বসে তাকে মন্ত্র প্রম্পট করে চলেছে এক প্রৌঢ়, নিজের চেনা পৃথিবীতে ফিরতে পারার নিদারুণ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে যাঁর মুখ!
ডঃ আনন্দ সেনের জন্ম কলকাতায়। হিন্দু স্কুল ও পরে সেন্ট জেভিয়ার্সে স্কুলজীবন কাটিয়েছেন। ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউটে স্নাতকস্তরের পড়া শেষ করেই পাড়ি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানেই বাসা। পেশায় ডেটা সায়েন্টিস্ট হলেও কবিতা লেখা আজও প্যাশন। আরও এক প্যাশন বাংলা থিয়েটার। প্রবাসে থেকেও নিয়মিত থিয়েটারের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত আনন্দ। নিয়মিত লেখেন বিভিন্ন ই-পত্রপত্রিকাতেও।



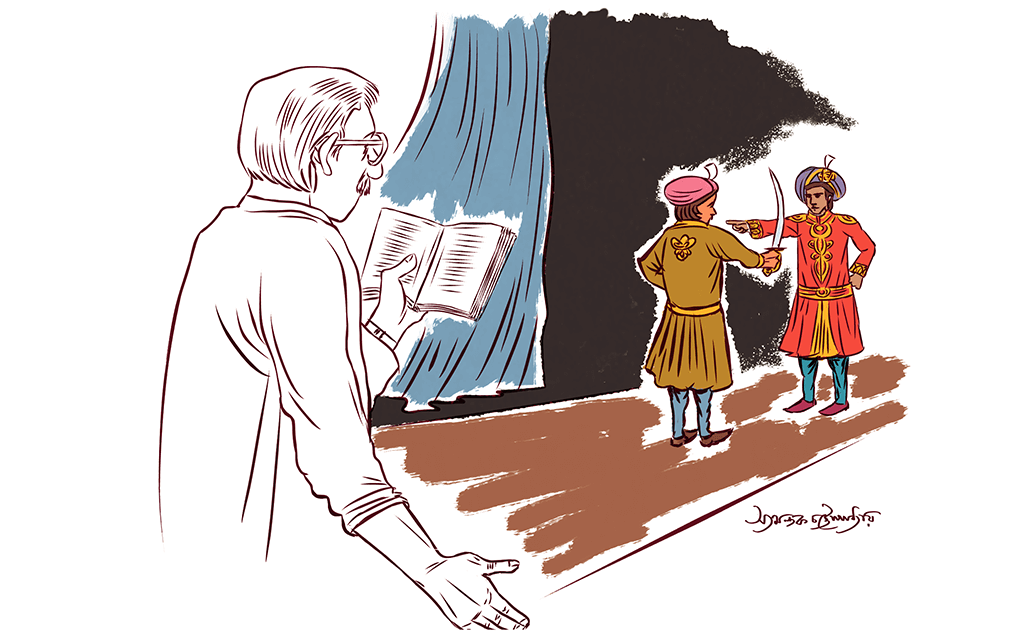






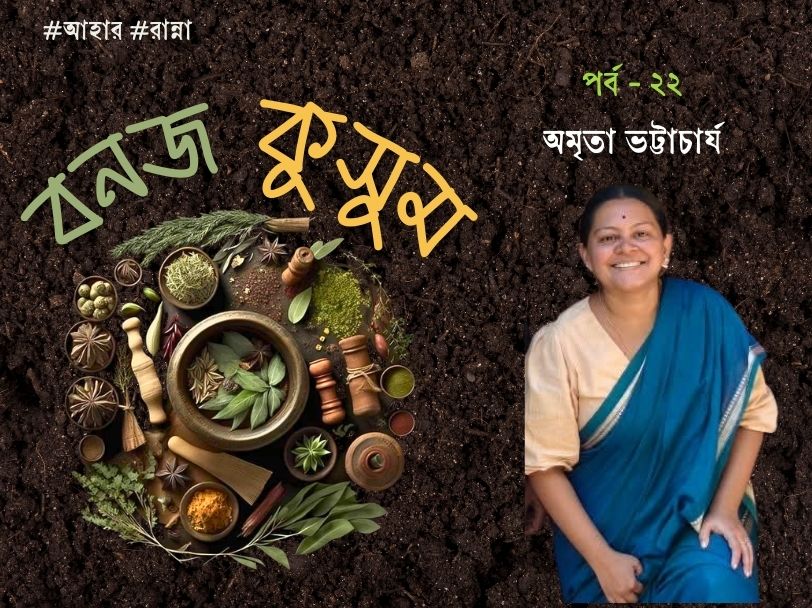





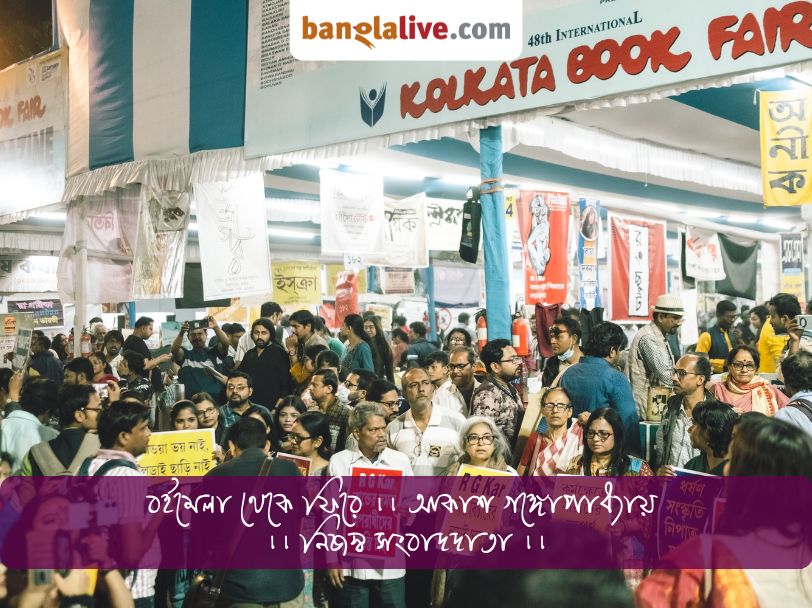







3 Responses
এই প্রজন্মের কথা তুলে ধরলে।এই টানাপোড়েন নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ করেছ,তাই হয়তো সুন্দর অনুভব নিয়ে গল্পের আকারে প্রকাশ করলে।আমারাও হয়তো এই টানাপোড়নের মধ্যে পড়বো।কি ভাবে মোকাবিলা করবো কে জানে? ভাল লাগলো।
গ্লপ্টা অসাধারুন ছিল। বাস্তবতার সাথে অনেক মিল আছে। পড়ে খুভ ভালো লাগল
সুন্দর ছিল