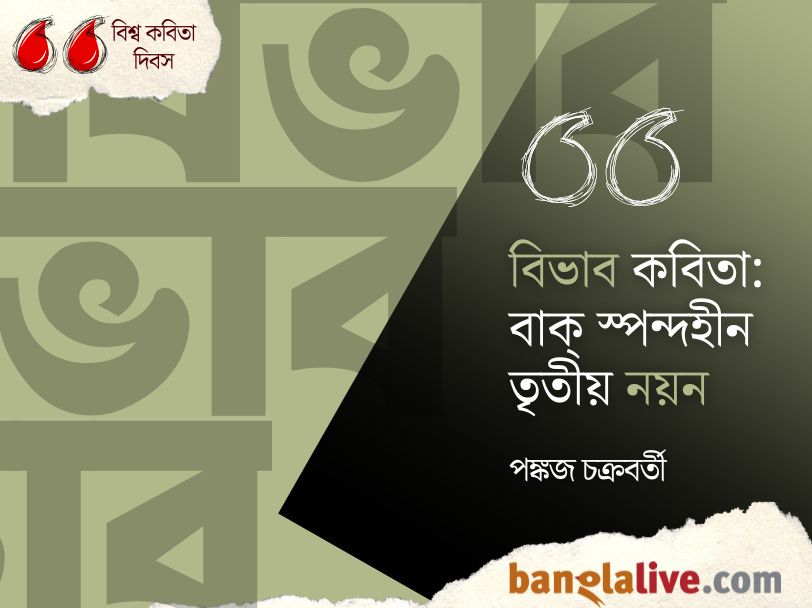(Poetry)
(Poetry) বিভাব কবিতা আসলে ইস্কুলের প্রার্থনাসঙ্গীতের মতো- অবশ্যম্ভাবী কিন্তু অনিবার্য নয়। সে জড়িয়ে আছে জীবনের সঙ্গে কিন্তু মূল কাঠামোর খানিকটা বাইরে। তাকে নজর করা যায় মাত্র। আর থাকে দূর থেকে পাঠকের মনস্ক প্রণাম। কিন্তু ভিতর ঘরে সে যেন খানিকটা অপেক্ষায় আছে। না থাকলেও চলে এমন, তবু একটি কাব্যগ্রন্থের উদাসীন দর্শন তাকে ঘিরে থাকে। না থাকলেও চলে তবু তার আসন ইদানিং খানিকটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। শুধু এটুকুই বলার বিভাব কবিতা জরুরি না কী জরুরি নয় সে বিষয়ে আমরা কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারিনি এখনও। (Poetry)
একথা ঠিকই বিভাব কবিতা বলে যে একটি বস্তু হতে পারে তার প্রথম ধারণা আমরা পাই পঞ্চাশের কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর ‘যৌবন বাউল’ কাব্যগ্রন্থ থেকে।
(Poetry) যা কবির নিজস্ব ইচ্ছার অধীন তাকে স্থায়ী কোনও নিয়মের প্রত্যাশায় আমরা বাঁধতে পারিনি। হয়তো উচিতও নয়। তাই লক্ষ্য করলে আমরা দেখব একই কবি কিছু কাব্যগ্রন্থে বিভাব কবিতা রাখছেন এবং কিছু কাব্যগ্রন্থে তার প্রয়োজন বোধ করছেন না। বিষয়টি অনেকটাই কাব্যগ্রন্থের বিষয় এবং আঙ্গিকের সঙ্গে জড়িত এবং বিভাব কবিতার মুহূর্তটি কখনও কখনও কবির তৎকালীন তুরীয় অবস্থার বিবেচনা। ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেবে। একথা ঠিকই বিভাব কবিতা বলে যে একটি বস্তু হতে পারে তার প্রথম ধারণা আমরা পাই পঞ্চাশের কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর ‘যৌবন বাউল’ কাব্যগ্রন্থ থেকে। বলাবাহুল্য তা আসলে প্রথম চিহ্নিত বিভাব কবিতা। তারও একটি শুরুয়াৎ আছে। একটু পিছনে তাকালেই দেখব কোনও কোনও কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ আছেন। যদিও তা বিভাব কবিতা হিসেবে স্বীকৃত নয়। এমনকি কল্পনাকে আরেকটু প্রসারিত করে তুললে হয়তো বলাই যায় মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের বন্দনাংশ বা আত্মপরিচয় অংশটি আসলে বিভাব কবিতা। (Poetry)
আরও পড়ুন: এই গ্রামদেশ, স্বপ্নাদেশে লিখিত কবিতা
(Poetry) চৈতন্যচরিতামৃতের বিভিন্ন পদের শুরুতে যে সংস্কৃত শ্লোকগুলি তাকেও কি বিভাব কবিতা হিসাবেই বিবেচনা করব? কিংবা নবারুণের ‘হারবার্ট’ উদ্ধৃত কবিতাগুলিকেও কি এর আওতায় রাখা যায়? এসব নেহাতই কথার কথা। খানিকটা হয়তো মেধার আত্মগৌরব। তাই এসব ছাড়িয়ে আমাদের প্রকৃত স্বীকৃতি দেওয়া থাক অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তকে। এবং বিষয়টিকে প্রাথমিকভাবে জরুরি করে তুলেছেন অলোকরঞ্জন। তার কারণ বিভাব কবিতা যে একটি অসামান্য স্বয়ংসম্পূর্ণ কবিতা হতে পারে শুরুতেই অলোকরঞ্জন প্রমাণ করে দিয়েছেন। না হলে হয়তো এত দূর আসার প্রয়োজন পড়ত না। পরপর দুটি কাব্যগ্রন্থে (‘যৌবন বাউল’ এবং ‘রক্তাক্ত ঝরোখা’) তিনি বিভাব কবিতার মাস্টারপিস রচনা করলেন। প্রথম কাব্যগ্রন্থের বিভাব কবিতার সামান্য একটু অংশ উদ্ধৃত করি
ভগবানের গুপ্তচর মৃত্যু এসে বাঁধুক ঘর
ছন্দে, আমি কবিতা ছাড়বো না,
অপ্রসর সমুদ্রকে শামুক দেখুক প্রেমের চোখে
বিমাতা মাটি তার কাছে যাবো না।
ধরিত্রীর নীবিবন্ধে জগৎ যদি মহানন্দে
অন্ধ, আমি প্রহরী যন্ত্রণা
মানুষ গিলে নামের খনি, আমার পরে এই ধরণী
সঙ্গোপনে অলোকরঞ্জনা।।
(Poetry) শুরু হল বিভাব কবিতার আয়োজন। কিন্তু তা স্থায়ী হল না। এমনকি সিদ্ধান্তে আসা গেল না। বরং তা হয়ে রইল কবিরই মনোভাবের বিষয়, খেয়ালের বিষয়। রবীন্দ্রনাথ থেকে সুধীন্দ্রনাথ, জয় গোস্বামী থেকে মৃদুল দাশগুপ্ত, ফল্গু বসু কিংবা উৎপলকুমার বসু বিভাব কবিতার ক্ষেত্রে কখনও অনিবার্য কখনও অনুপস্থিত। অলোকরঞ্জনের কবিতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে অথচ তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের বিভাব কবিতাটির কথা আসেনি এমনটি প্রায় দুর্লভ। এমনই কিছু অনিবার্য বিভাব কবিতা আমাদের কাব্যভাষার সম্পদ। পাঠক লক্ষ্য করুন উৎপলকুমার বসুর কবিতা সংগ্রহের বিভাব কবিতা কিংবা প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘উত্তর কলকাতার কবিতা’ কাব্যগ্রন্থের বিভাব কবিতা যেগুলি ছাড়া শুধু বিভাব কবিতার আলোচনাই নয় বাংলা কবিতার ঐশ্বর্যের আলোচনা অসম্পূর্ণ। বিভাব কবিতা হয়েও কাব্যগ্রন্থকে ছাড়িয়ে তারা জেগে উঠেছে স্বমহিমায়। যেন একটি একক কবিতায় অখন্ড এক কাব্যগ্রন্থ। বিভাব কবিতা তেমনই এক কবিতা যা কাব্যগ্রন্থের শুরুতে শুধু প্রবেশক নয় কখনও নিজেই একটি একক স্বনির্ভর কাব্যগ্রন্থ। দুটি অনিবার্য বিভাব কবিতার মুখোমুখি হই আমরা এবার
অতিকাল যাও… আমার অপর এই গঙ্গাধধারে বটবৃক্ষমূলে দ্যাখে গামছা পেতেছে… বাঁকুড়ার গোলাপী গামছা…
পাবে আমাকেও। বাদার জঙ্গলে
এক পোর্তুগিজ অশ্বতর তোমাকে দেখাবে
আমি ও হেঁতাল কাঁটা ও-পশুর মাংসে বিঁধে আছি। লৌহকণার গান শুনে যাও। শ্বেতকণিকার ক্ষিপ্ত নৃশংসতা শোনো।
বিষ-যার চোখ নেই, বৃদ্ধি আছে, খসে-পড়া আছে, নেই ত্বক, শুধু ঝুলন্ত প্রদর আছে, পুঁজ আছে, -এঁকে নমস্কার করো।
(উৎপলকুমার বসু)
অতিকাল যাও… আমার অপর এই গঙ্গাধধারে বটবৃক্ষমূলে দ্যাখে গামছা পেতেছে… বাঁকুড়ার গোলাপী গামছা… আহা কী শীতল… অতিকাল যাও… ওকে একটু শুতে দাও বিরক্ত কোরো না… ক্ষমতা বাচনে ঘেরা সমসত্ত্বা থেকে দূরে
ঐ গামছাটি পাতা… যাবতীয় মাধ্যমের
উদ্বেজনা থেকে দূরে ঐ গামছাটি পাতা… বাগবাজারে গঙ্গাধধারে পক্ষীবিষ্ঠাময় কোনও বটমূলে বাঁধানো চাতালে… থামো অতিকাল…
দূর থেকে গামছাটিকে প্রণাম জানাও
(প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়)
আমি ও হেঁতাল কাঁটা ও-পশুর মাংসে বিঁধে আছি। লৌহকণার গান শুনে যাও। শ্বেতকণিকার ক্ষিপ্ত নৃশংসতা শোনো।
(Poetry) আরেকটি প্রশ্ন তোলা জরুরি বলে মনে করছি বিভাব কবিতা কি স্বতঃস্ফূর্ত বা স্বয়ম্ভু? বিভাব কবিতাটি জন্ম নেয় না কাব্যগ্রন্থের প্রয়োজনে জন্ম দেওয়া হয়। এ বিষয় নিয়ে আমরা ভাবতেই পারি। কখনও কখনও কাব্যগ্রন্থের প্রয়োজনে বিভাব কবিতা লেখা হতেই পারে। কিন্তু আসলে তা স্বতঃস্ফূর্ত এক কবিতা। যা কাব্যগ্রন্থের অনিবার্য স্রোতে তৈরি হয়নি বরং নিজেই খেয়ালী জন্ম নিয়ে একক হয়ে আছে। যার কাব্যগ্রন্থে যাওয়ার অধিকার নেই বিষয় কিংবা ফর্মের দিক থেকে অথচ যে কবিতা অমোঘ, কবি তাকেই কি নির্বাচন করেন বিভাব কবিতার জন্য? আমার মনে হয়, যে কথা কাব্যগ্রন্থে বলা হয়নি অথবা কাব্যগ্রন্থের কেন্দ্রীয় সুর তা বিভাব কবিতার মাধ্যমে ধরা সম্ভব। তাছাড়া কখনও কখনও এমন কবিতা আসে যে কবিতার আলাদা করে নামকরণ দিয়ে অস্তিত্ব রচনা করা সম্ভব নয়। তখন সেই কবিতাটি বিভাব কবিতার চেহারায় কাব্যগ্রন্থের শুরুতে স্থান পায়। আরেকটি কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। বিভাব কবিতায় এক ধরনের দর্শন ফুটে ওঠে। যাকে আলাদা করে কবিতা হিসেবে দেখতে ইচ্ছে করে না। এমন নির্ভার একটি লেখা নিজেই অনাহুত জন্ম নেয়। কোনও প্রস্তুতিও থাকে না। (Poetry)
নব্বইয়ের কবি রানা রায়চৌধুরীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘একটি অল্পবয়সী ঘুম’ এর বিভাব কবিতাটি তার একটি নিদর্শন হতে পারে।
(Poetry) একটু লক্ষ্য করলেই আমরা দেখব অনেকক্ষেত্রে মূল কাব্যগ্রন্থের চেহারার সঙ্গে বিভাব কবিতার কোনও মিল নেই। মূল কাব্যগ্রন্থের আঙ্গিক এবং বিভাব কবিতার আঙ্গিক সম্পূর্ণ পৃথক। মূল কাব্যগ্রন্থটি যদি গদ্যের খর উত্তাপে প্রবাহিত তাহলে বিভাব কবিতাটি যেন ছন্দোময় গীতিময় এক স্বগতোক্তি। নব্বইয়ের কবি রানা রায়চৌধুরীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘একটি অল্পবয়সী ঘুম’ এর বিভাব কবিতাটি তার একটি নিদর্শন হতে পারে। আবার লক্ষ্য করি নব্বইয়ের আরেক কবি শোভন ভট্টাচার্যের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘ব্যক্তিগত আলেখ্যর প্রতি’ যেখানে পাঁচটি পর্যায়ে চারটি করে চতুর্দশপদী আছে এবং প্রতি পর্যায়ের শুরুতে একটি করে অসামান্য বিভাব কবিতা। এই দুটি বিভাব কবিতা কাব্যগ্রন্থ ছাড়িয়েও অমোঘ এবং অনিবার্য। পৃথক এক তীব্র কবিতার দাবিদার। যা মূল কাব্যগ্রন্থের খর উত্তাপের চেয়ে সর্বাংশেই আলাদা। (Poetry)
ভালোবাসার কথা তো বলতে চাইনি
আমি রাজিও নই প্রণত প্রস্তাবে
যদি সংজ্ঞা চাও প্রেমের
তবে ছবি আঁকব পিলসুজের
আগুনকে দাঁড় করাব আলোর মুখোমুখি
আমি প্রণাম দিয়েই উসকে দিয়েছি সলতে
এই দেখো সেই পোড়া দাগ…
(রাণা রায়চৌধুরী)
যতদূর জানি আমি আমাদের ঠাকুরমার কাছে মান্ধাতা-আমল থেকে কাঁসার বাসন কিছু আছে।
…শস্যে, আলস্যে আছি, প্রভু আর অন্যত্র যাব না। সব ছেড়ে তোমার ওই চুলার দুয়ারে যাওয়া কেন? একান্তই যাবে যারা তাদের গন্তব্যগাথা যেন আমার মুখস্থ প্রায়- সাতের নামতায়- হাতে গোনা।
যতদূর জানি আমি আমাদের ঠাকুরমার কাছে মান্ধাতা-আমল থেকে কাঁসার বাসন কিছু আছে।
পলায় বাঁধানো আছে মায়ের করুণ হাত-কানাকড়ি সোনা।।
(শোভন ভট্টাচার্য)
(Poetry) কাব্যগ্রন্থের কবিতার চেয়ে বিভাব কবিতা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এবং জনপ্রিয় এমন ঘটনা আছে কি? অলোকরঞ্জনের কিংবা প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখিত কবিতা দুটি তার নিদর্শন হতে পারে। এর সবচেয়ে জোরালো নিদর্শন বোধহয়, জয় গোস্বামীর ‘ঘুমিয়েছ, ঝাউপাতা?’ কাব্যগ্রন্থটি। শুধু এই বিভাব কবিতাটি অনিবার্য হয়ে ঘুরে বেরিয়েছে দীর্ঘদিন শহরে এবং মফস্বলে। আবৃত্তিকারের গলায়। এমনকি কবির কাব্যোপন্যাসেও। বাংলা ভাষায় বিভাব কবিতার মধ্যে এতদূর জনপ্রিয় আর সম্ভবত কোনও কবিতাই হতে পারেনি। আপনারা জানেন এবং চেনেন তবুও আরেকবার এই কবিতাটি পাঠের সুযোগ নিন। (Poetry)
-‘পড়ে রইল যে!’ পড়েই থাকত- সে-লেখা তুলবে বলে
কবি ডুবে মরে, কবি ভেসে যায় অলকানন্দা জলে।।
হৃদি ভেসে যায় অলকানন্দা জলে
অতল, তোমার সাক্ষাৎ পেয়ে চিনতে পারিনি বলে হৃদি ভেসে গেল অলকানন্দা জলে
করো আনন্দ আয়োজন করে পড়ো
লিপি চিত্রিত লিপি আঁকাবাঁকা পাহাড়ের সানুতলে
যে একা ঘুরছে, তাকে খুঁজে বার করো
করেছো, অতল; করেছিলে; পড়ে হাত থেকে লিপিখানি
ভেসে যাচ্ছিল- ভেসে তো যেতই, মনে না করিয়ে দিলে;
-‘পড়ে রইল যে!’ পড়েই থাকত- সে-লেখা তুলবে বলে
কবি ডুবে মরে, কবি ভেসে যায় অলকানন্দা জলে।।
(Poetry) জয় গোস্বামী সত্তরের কবি এবং একথাও বলা থাক সত্তরের অনেক কবি বিভাব কবিতাকে গুরুত্ব দেননি। রনজিৎ দাশ, নিশীথ ভড়, অনুরাধা মহাপাত্র, চন্দ্রানী বন্দোপাধ্যায়, রমা ঘোষ প্রমুখ অনেকেই কাব্যগ্রন্থে বিভাব কবিতা রাখেননি। পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলালেরও বিভাব কবিতার সংখ্যা নগণ্য কিংবা দেবদাস আচার্য। অথবা পঞ্চাশের স্বদেশ সেন, দীপংকর দাশগুপ্ত কাব্যগ্রন্থে বিভাব কবিতা রাখেননি। নয়ের দশকে বিভাব কবিতার চেহারা খানিকটা সাবলীল হল। নব্বইয়ের কবিদের হাতে তো বটেই এবং পরবর্তী তরুণ কবিদেরও দেখছি বিভাব কবিতার প্রতি তীব্র আগ্রহ আছে। (Poetry)
বাবা শিল্প বোঝে না
বোঝে, আমরা তিন অভুক্ত প্রাণী
রাষ্ট্র নামক কোনও কুয়োর ভিতর আটকে আছি আরও অনেক প্রাণীর সাথে
(Poetry) আবারও বলা প্রয়োজন মূল কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে বিভাব কবিতার দূরত্ব আছে, আছে বৈপরীত্য। আরও স্পষ্ট করে বললে বিরোধ। কিন্তু স্ববিরোধ নয়। বরং অলংকারিকের ভাষায় বলব বিরোধাভাস। যা আপাতবিরুদ্ধ কিন্তু মর্মে এক সত্তায় লীন হয়ে আছে। একটি কাব্যগ্রন্থের সামগ্রিক দর্শন ধারণ করে আছে বিভাব কবিতা। অথচ অদ্ভুত এক সন্ন্যাসী উদাসীনতা। নির্ভার। উচ্চকিত নয় অথচ তীব্র। অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখে। কাব্যগ্রন্থে প্রবেশ করতে দেয় না সহজে। পাঠক এবার সাম্প্রতিক তরুণ কবিদের কয়েকটি বিভাব কবিতার উদাহরণ দিই। দেখুন সেগুলি নিজগুণেই বাংলা ভাষার সম্পদ হয়ে উঠেছে –
ঘরে ভাঙা সন্ধ্যা, ভাঙা গান
চোখের উছলকোণে ‘হ্যাঁ, দিন গিয়েছে বটে’
সেই কাঙ্ক্ষা, প্রিয়তোষ-আবার জননী হলে
১.
এঁটো বাসন-কোসন মেজে
মা যখন চকচকে থালায় ভাত বাড়ে
হে রাষ্ট্র, তখন তোমার কথা না
মনে পড়ে, খেটে খাওয়া বাবার কথা
বাবা শিল্প বোঝে না
বোঝে, আমরা তিন অভুক্ত প্রাণী
রাষ্ট্র নামক কোনও কুয়োর ভিতর আটকে আছি আরও অনেক প্রাণীর সাথে
(মায়াজন্ম/সেলিম মণ্ডল)
২.
সমস্ত শুভেচ্ছার কাছে সে ঋণী
প্রতিটা আকুল থেকে ঝরে পড়ছে মেলানকোলিক সুর
সে আর সে মিলে, দুটিতে তারা হয়ে
আকাশে আকাশে হাঁটাহাঁটি
সেখানেই দেশ, বেশ, রান্নাবাটি
আর যুগোত্তীর্ণ জড়িয়ে জড়িয়ে থাকার মায়া
(ঘুম হও অজস্র অপরাজিতা/সুমন সাধু)
মহানগরের ডিভাইডারে
মেলে দিয়েছি নিজেকে
বাসের জানালা থেকে টিটকিরি মারছে পাবলিক
৩.
অপরাধ যে করেছি
আজ তা স্বীকার করছি
মহানগরের ডিভাইডারে
মেলে দিয়েছি নিজেকে
বাসের জানালা থেকে টিটকিরি মারছে পাবলিক
কমরেডস্ ও বন্ধুগণ-
হুলাবিলা হুল্লোড় করো
এখানে জীবন ফ্ল্যাট
ফিফটি পারসেন্ট অফ্!
(যে কোনও রাস্তায়/ সৌম্যজিৎ রজক)
করো আনন্দ আয়োজন করে পড়ো
লিপি চিত্রিত লিপি আঁকাবাঁকা পাহাড়ের সানুতলে
যে একা ঘুরছে, তাকে খুঁজে বার করো
৪.
ভয় নেই… চাদ্দিকে ভয়ের বিজ্ঞাপন
শান্তিদূত ঘুমোনোর মহড়ায়, দ্যাখো-
দু’পা পেরোলেই কত কিছু
একই ট্রাফিক জ্যামে
হাত পেতে
হকার, ভিকিরি, পুলিশ
দৃশ্যের যে দিক দিয়ে দেখি
আড়াল কাটে না
(অজানা জ্বর/প্রশান্ত হালদার)
৫.
ডেলাইলা আজও আছে স্যামসন, ব্রুটাসরা
ছুরি নিয়ে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে।
অনাদি-অনন্তকাল ধরে, বিশ্বাসহন্তার দল
খেয়ে ফেলে প্রাচীন মুগ্ধতা।
(প্রিয় শয়তান/ মিলন চট্টোপাধ্যায়)
মেঘ জানে না, পাটিগণিত-বীজগণিত
জানে না আব্বার রাগ জলের মতো
৬.
দু-জনেই জলে আছি, শুধু কোনো হাবুডুবু নেই কবেকার লতাপাতা তোমাকে চিনিনি আজও ভালো
ব্যর্থ কাকের মতো ঠাঁই নিয়ে থেকে গেছি ঘোরে খেয়ালও করিনি স্রোতে আমাদের কোথায় পাঠাল…
(খইয়ের ভিতরে ওড়ে শোক/ পৃথ্বী বসু)
৭.
এই কাব্য দুপুরের, এই কাব্য ডোরাকাটা বাঘ
এই কাব্য জীবনে যা ছিটেফোঁটা ঈগলের দাগ নাগাড়ে শব্দের স্রোতে এই কাব্য অযতি-প্রত্যয় এই কাব্য উন্মাদের যৌনভাষে বর্ণপরিচয়
শাদা কার্ডিগানে ছোপ, কুরুশে রক্তের কালোবীজ
এই কাব্য থাবা তুলে চিরে দেখছে ম্যাটিনি টকিজ
(উল ও ম্যাটিনি/ নীলাঞ্জন দরিপা)
৮.
বারান্দার টেবিলে কালো ব্যাগ দেখলে ভুল করি এই বুঝি ফিরে এল লোকটা
হাতধোয়া জলের শব্দে বুঝতে পারি রেগে আছে লোকটা
মেঘ জানে না, পাটিগণিত-বীজগণিত
জানে না আব্বার রাগ জলের মতো
শুধু জানে জমা জলে পোকাদের বাস
( আব্বাচরিত /সোহেল ইসলাম )
“স্মৃতির চরণ থেকে এইসব আহুতির ছাই
সাদাকালো আবির হয়ে উঠে আসে হাতে
মুঠোবদ্ধ হয়, জল পড়ে, কালি হয়,
লেখা হয়…
আবার সে ফিরে যায় উৎসর্গ পাতায়…
এসবই প্রথম বই, তবু যেন
গতজন্মে পড়ে ফেলা মায়ের হাতের লেখা খাতা
শেকড় পরিয়ে সূচে, বুনে দেওয়া পাতায় পাতায়
কবিতা মায়ের মতো… পদবি লুপ্ত হয়ে
ছড়িয়ে পড়েছে কাজে কাজে…
এসব আমার বলা সাজে?
প্রভু জন্ম, তবু জন্ম হয়…”
(এসেছ জন্ম পক্ষী দোহাই/ সুপ্রিয় মিত্র)
একটি কাব্যগ্রন্থের সামগ্রিক দর্শন ধারণ করে আছে বিভাব কবিতা। অথচ অদ্ভুত এক সন্ন্যাসী উদাসীনতা। নির্ভার। উচ্চকিত নয় অথচ তীব্র।
(Poetry) বিভাব কবিতার আরেকটি ধরনের কথা এখানে বলতে চাই। যেখানে কবিতাটি আসলে উৎসর্গের ছলনা। সে সম্পূর্ণ একটি কবিতা তবুও কোথাও একটি ব্যক্তি মানুষের দিকে তার যাত্রা আছে। অথচ তা অস্পষ্ট এবং অনির্দিষ্ট। যেন তাকে লক্ষ্য না করলেও চলে। কেন না ব্যক্তিকে দিয়ে কোনও একটি ব্যক্তিগত দীর্ঘশ্বাস অথবা উদ্যাপন এখানে ছুঁয়ে ফেলা হচ্ছে। আড়ালে ব্যক্তি আর সামনে রয়েছে সামগ্রিক এক উদাসীনতা। অনেকটা আয়নার মতো। অস্পষ্ট অথচ পাঠক সেখানে নিজের মুখটি দেখতে পান। আর শুরুতে এভাবে পাঠক নিজেও হয়ে ওঠেন কবি। এবং নিজের সমস্ত দাবি এবং ভূমিকা নিয়ে কাব্যগ্রন্থে প্রবেশ করেন। এমন দু-একটি উদাহরণ দিই যাকে বিভাব কবিতা নিশ্চয়ই ভাবতে পারেন কিন্তু খেয়াল করে দেখুন কোথাও যেন এক অলক্ষ্য উৎসর্গের বোধ আছে
ফুরিয়ে গিয়েছে ছুটি, মেঘ থেকে উঠে দীর্ঘশ্বাস
মুছে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে দিগন্তেও আলো নিভে যাবে
ফিরতি পথের মনে যার যার সূর্যাস্ত দেখি
এ-বই তাদেরই দেব, অন্য কোনো স্বত্ব থাকবে না
( জ্যোৎস্নার ছৌ/ আকাশ গঙ্গোপাধ্যায়)
এত যে নিষেধকথা, ‘বিসমিল্লা’ বলে সব
জায়েজ হয়েছে
ঘরে ভাঙা সন্ধ্যা, ভাঙা গান
চোখের উছলকোণে ‘হ্যাঁ, দিন গিয়েছে বটে’
সেই কাঙ্ক্ষা, প্রিয়তোষ-আবার জননী হলে
বিবিজান, দাঁড়াব কোথায়?
বলেছে, তাহার নামে বইয়ের নামটি লেখা যায়
(দীপাবলি নাকি শবযাত্রা/ তন্ময় ভট্টাচার্য)
আরও পড়ুন: হেলাল-তর্পণ: জনপ্রিয়তা, জিজ্ঞাসা ও সংশয়
(Poetry) আমাদের পূর্বজ কথাসাহিত্যে অনেক ক্ষেত্রে পাগলের যে ভূমিকা বিভাব কবিতারও তাই। আজ থেকে তিরিশ বছর আগেও রাস্তার পাগলের জন্য আমরা ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা করতাম। এমনকি এক চিলতে থাকার জায়গা। তাকে অ্যাসাইলামে পাঠাইনি। কথাসাহিত্যে এই পাগলদের কথায় আছে দার্শনিকতা। এবং একথা সে বলতে পারে কী না এই প্রশ্ন তোলা কঠিন। তার কারণ শিল্পের কথা বলতে গেলে লেখক বলবেন তা আসলে পাগলের প্রলাপ এবং যদি শিল্পের কথা না তুলি তবে ওই দার্শনিকতাতেই রয়েছে লেখকের জীবন দর্শন। যার ডিভিডেণ্ড লেখক ঘরে তুলতে চান। বিভাব কবিতা এমন কবিতা যেখানে শিল্পের দাবি নেই। শিল্পকুশলতার দাবি অর্থহীন। ফলত সে নির্ভার। এমনকি সে আলাদা করে নিজেকে কবিতা হিসেবে দাবি করে না। কবির ব্যর্থতা বোধ এখানে অনেক কম। দুর্বল বিভাব কবিতা নিয়ে কেউ প্রশ্ন তোলেন না। এমনই এক স্বাধীনতা। (Poetry)
বিভাব কবিতার কোনও সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব কি? সম্ভবত নয়। কবিতারই যেখানে সংজ্ঞা নেই বিভাব কবিতার থাকেই বা কী করে? যা আছে তা হল লক্ষণ, তাকে চিনিনে এবার নানা ভঙ্গিমা।
(Poetry) স্বচ্ছ জলে দাগ কাটার মতো এলোমেলো ভূমিকা মাত্র। উদাসীনতাই বিভাব কবিতাকে সুন্দর করেছে। তার একান্ত লৌকিক ব্যক্তিগত চরণই তাকে কবিতার সার্থকতা থেকে একটু দূরে দাঁড় করিয়েছে। দূরে কিন্তু জীবনের দিকে ঝুঁকে। সমগ্রের দায়িত্ব নিয়ে একই সঙ্গে সে দৃশ্যমান এবং অনুপস্থিত। (Poetry)
(Poetry) বিভাব কবিতার কোনও সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব কি? সম্ভবত নয়। কবিতারই যেখানে সংজ্ঞা নেই বিভাব কবিতার থাকেই বা কী করে? যা আছে তা হল লক্ষণ, তাকে চিনিনে এবার নানা ভঙ্গিমা। সম্প্রতি এই বছর বইমেলায় (২০২৫) তরুণ কবি অমিত পাটোয়ারীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘অশ্রু দাও দেবতা রাক্ষস’ প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে দু’লাইনের একটি চমৎকার বিভাব কবিতা আছে। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করি এই কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতাটি হয়ে উঠতে পারে বিভাব কবিতার একরকম সংজ্ঞা। ‘যৌবন বাউল’- এর পর প্রায় সাত দশক পেরিয়ে যেন একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ হল। (Poetry)
বহুজন্ম ফিরে আলো
আলতায়
শ্রীপটে দেখেছি, টিপ থেকে টিপ
যেতে পারে কতদূর চাঁদ যেন আভরণহীন তাঁর নথ।
সরল বিনুনি ঘরের আর ঘোমটায়
ঢাকা পড়া খেত নিরক্ষর
বন্যায়
বিভাব কবিতা হয়ে আছে। এ পৃষ্ঠা ছেড়ে চলো, উদাসীন
ভঙ্গুর দেবতা তুমি
যতিমাত্র চমকে পূর্ণ করো তাঁর অনঙ্গ বন
শূন্যসুন্দর ঘুম, বাক্স্পন্দহীন তৃতীয় নয়ন
( ব্রতকথা)
ফুরিয়ে গিয়েছে ছুটি, মেঘ থেকে উঠে দীর্ঘশ্বাস
মুছে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে দিগন্তেও আলো নিভে যাবে
ফিরতি পথের মনে যার যার সূর্যাস্ত দেখি
এ-বই তাদেরই দেব, অন্য কোনো স্বত্ব থাকবে না
(Poetry) ফিরে আসি স্কুলের প্রার্থনাসঙ্গীতে। মাঝে মাঝেই আমরা ঠিকমতো উপস্থিত হতে পারিনি। ফলত প্রার্থনাসঙ্গীত ছাড়াই ক্লাসে ঢুকেছি। বলা যায় কিছুটা ছাড় পেয়েছি। প্রার্থনাসঙ্গীত না করার একটা সামান্য দুঃখ অবশ্যই ছিল এবং তা বয়সের পক্ষে খুব দুঃসহনীয় নয় হয়তো আনন্দের। তবুও টের পাই প্রার্থনাসঙ্গীতে সবাই হোটোপাটি করে লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। শেষে সবার আগেই দৌড় দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আর প্রার্থনাসঙ্গীতেই টের পেয়েছি বন্ধুর গায়ের ঘামে উষ্ণ গন্ধ। সিলেবাসের চেয়ে ওই গন্ধটুকুর কথাই মনে পড়ে বেশি। বন্ধুর নাম মনে নেই কিন্তু গন্ধটুকু মনে আছে। তা বিভাব কবিতার মতোই নামহীন, গোত্রহীন। তাকে ছাড়া আমরা মফস্বলের দিনগুলি কাটানোর কথা ভাবিনি কোনওদিন। অথচ বিবাহ পরবর্তী দিনগুলিতে বুকের ভেতর গোপন বন্ধুর নামটি মুছে গেছে কবে। (Poetry)
জন্ম ১৯৭৭। লেখা শুরু নব্বইয়ের দশকে। পঞ্চাশের বাংলা কবিতার আতিশয্যর বিরুদ্ধে এযাবৎ কিছু কথা বলেছেন। ভ্রমণে তীব্র অনীহা। কিংবদন্তি কবির বৈঠকখানা এড়িয়ে চলেন। এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ - বিষণ্ণ দূরের মাঠ চার ফর্মার সামান্য জীবন, উদাসীন পাঠকের ঘর, লালার বিগ্রহ, নিরক্ষর ছায়ার পেনসিল, নাবালক খিদের প্রতিভা। গদ্যের বই- নিজের ছায়ার দিকে, মধ্যম পুরুষের ঠোঁট। মঞ্চ সফলতা কিংবা নির্জন সাধনাকে সন্দেহ করার মতো নাবালক আজও।