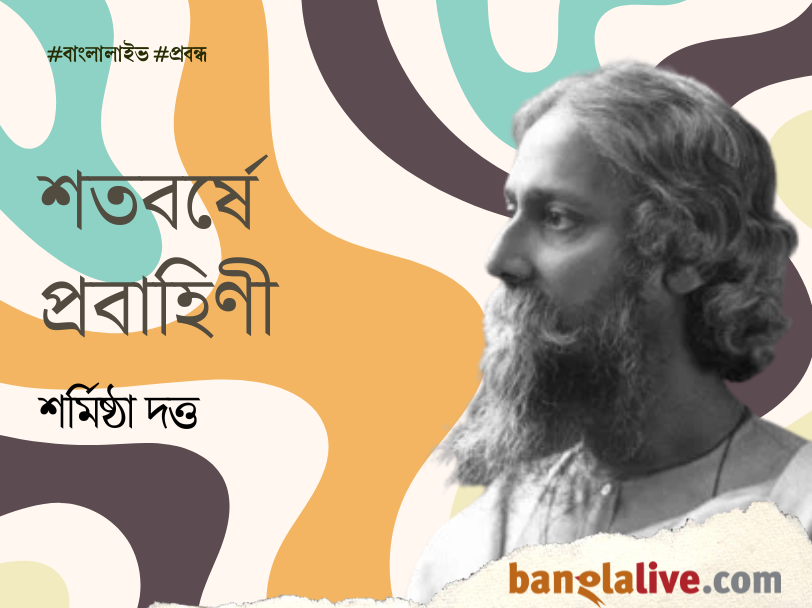(Prabahini)
গণেশকে বাদ দিয়ে তাঁর ইঁদুরকে ধরে রাখতে চাননি রবীন্দ্রনাথ। হ্যাঁ, তুলনাটা করেছিলেন গানের বই ছাপানোর প্রসঙ্গেই।
জীবন-স্মৃতি-র ‘গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ’ রচনায় লিখছেন,
গীতিকলার নিজেরই একটি বিশেষ প্রকৃতি ও বিশেষ কাজ আছে। গানে যখন কথা থাকে তখন কথার উচিত হয় না সেই সুযোগে গানকে ছাড়াইয়া যাওয়া, সেখানে সে গানেরই বাহনমাত্র। গান নিজের ঐশ্বর্যেই বড়ো; বাক্যের দাসত্ব সে কেন করিতে যাইবে… বাক্য যাহা বলিতে পারে না গান তাহাই বলে। এইজন্য গানের কথাগুলিতে কথার উপদ্রব যতই কম থাকে ততই ভালো। …এই কারণে চিরকাল গানের বই ছাপাইতে সংকোচ বোধ করি। কেননা, গানের বহিতে আসল জিনিসই বাদ পড়িয়া যায়। সংগীত বাদ দিয়া সংগীতের বাহনগুলিকে সাজাইয়া রাখিলে কেমন হয়, যেমন গণপতিকে বাদ দিয়া তাঁহার মুষিকটাকে ধরিয়া রাখা। (Prabahini)
আরও পড়ুন: গামানুষের গল্প আর অন্য রাজশেখর
সেই তেইশ বছর বয়স থেকেই গানের বই প্রকাশিত হচ্ছে তাঁর। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী-কেও এখানে গানের বই ধরতে হবে। ১৮৮৪-তে আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে কালিদাস চক্রবর্তী যে-বই ছাপলেন তার ২১টি পদেই ছিল রাগ-রাগিণীর উল্লেখ। (Prabahini)

তবু রবীন্দ্রনাথ তাদের কবিতা বলছেন। ‘উৎসর্গ’ পৃষ্ঠায় লিখছেন,
ভানুসিংহের কবিতাগুলি ছাপাইতে তুমি আমাকে অনেকবার অনুরোধ করিয়াছিলে। তখন সে অনুরোধ পালন করি নাই। আজ ছাপাইয়াছি, আজ তুমি আর দেখিতে পাইলে না। (Prabahini)
পরিণত বয়সে সে সব কবিতা ‘একটু বাজাইয়া বা কষিয়া দেখিলেই তাহার মেকি বাহির হইয়া পড়ে’, মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের। কারণ সে-সবে আমাদের দিশি নহবতের প্রাণ-গলানো ঢালা সুর নেই, সে সব আজকালকার সস্তা আর্গিনের বিলিতি টুংটাং মাত্র। (Prabahini)
আরও পড়ুন: সন্জীদা খাতুন (১৯৩৩-২০২৫): সহজ কঠিন দ্বন্দ্বে ছন্দে
তবু, শতবর্ষ আগে, ১৯২৫-এ পুরোপুরি গানের একটা বই প্রকাশ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তার নাম প্রবাহিণী। তখন আর সেই গণেশ-ইঁদুর উপমার সংকোচ ছিল না। কারণ কবির বিশ্বাস ছিল,
প্রবাহিণীতে যে সমস্ত রচনা প্রকাশ করা হইল তাহার সব গুলিই গান, সুরে বসানো। এই কারণে কোনো কোনো পদে ছন্দের বাঁধন নাই। তৎসত্ত্বেও এগুলিকে গীতিকাব্যরূপে পড়া যাইতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস। (Prabahini)
সেই বিশ্বাস থেকেই রবীন্দ্রনাথ প্রবাহিণীর গানগুলি থেকে রাগ-তালের উল্লেখ বাদ দিলেন। আর এই বইতেই এল পূজা, বিবিধ, ঋতুচক্রের মতো পর্যায়। ‘প্রবাহিণী’ গ্রন্থে গানগুলি এইভাবে বিন্যস্ত করলেন:
গীতগান
প্রত্যাশা
পূজা
অবসান
বিনীত
ঋতুচক্র
গীতগান পর্যায় রেখেছিলেন ৩৫ টি গান। তারপরে প্রত্যাশা পর্যায়ে ৩৩ টি গান। এরপর পূজা পর্যায় সেখানে রেখেছিলেন ৩০ টি গান। এরপরের পর্যায় অবসান। সেখানে গান সংখ্যা ২১। বিনীত পর্যায় রেখেছিলেন ৩৩ টি গান। আর সর্বশেষ ঋতুচক্রের ৮৩ টি গান। (Prabahini)
এখানে ঋতুসংগীতগুলিকে ‘ঋতুচক্র’ নামাঙ্কিত করে স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত করায় নতুনত্ব লক্ষ করা যায়। ভাগ মোট ছয়টি। পরবর্তীকালে ‘গীতবিতান’ প্রথম সংস্করণে (১-২ খণ্ড: ১৩৪৫-৪৬ সাল) যে পর্যায়-ভাগ করা হয় তাও ছয়টি। (Prabahini)
গানের কথাকে সেই কবে তরুণ বয়সে একেবারে মূল্য দিতে চাননি রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু প্রবাহিণী প্রকাশের বছর চারেক আগে ভাদ্র ১৩২৮-এর সবুজ পত্র-এ রবীন্দ্রনাথের অনুভব, (Prabahini)
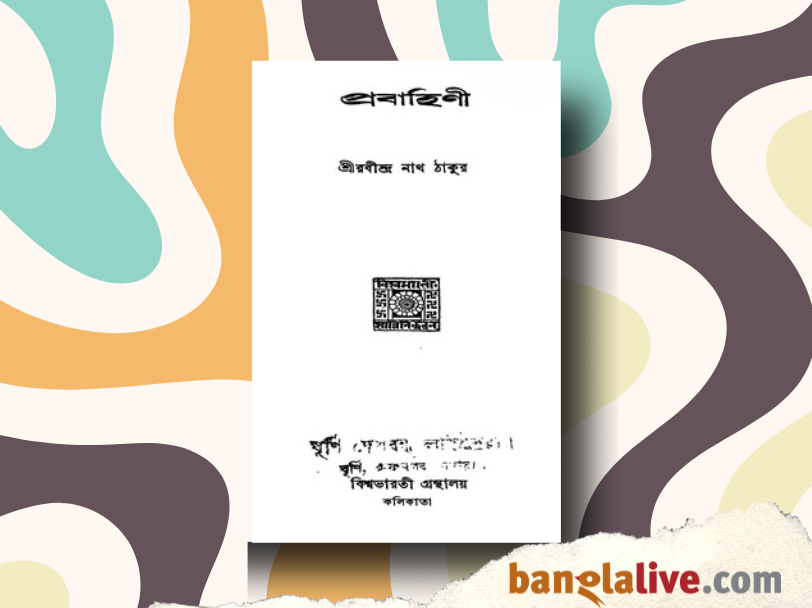
‘বাংলা দেশে সংগীত কবিতার অনুচর না হোক, সহচর বটে। …বাংলা দেশে হৃদয়ভাবের স্বাভাবিক প্রকাশ সাহিত্যে। ‘গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি’— সে দেখতে পাচ্ছি সাহিত্যের মধুচক্র থেকে। বাণীর প্রতিই বাঙালির অন্তরের টান; এইজন্যেই ভারতের মধ্যে এই প্রদেশেই বাণীর সাধনা সব চেয়ে বেশি হয়েছে।’ প্রবাহিণীর পরেও, ১৯৩৭-এ, মৃত্যুর বছর চারেক আগে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপে জানাচ্ছেন,
আমরা যে গানের আদর্শ মনে রেখেছি তাতে কথা ও সুরের সাহচর্যই শ্রদ্ধেয়, কোনো পক্ষেরই আনুগত্য বৈধ নয়। সেখানে সুর যেমন বাক্যকে মানে, তেমনি বাক্যও সুরকে অতিক্রম করে না। কেননা, অতিক্রমণের দ্বারা সমগ্র সৃষ্টির সামঞ্জস্য নষ্ট করা কলারীতিবিরুদ্ধ। যে বিশেষ শ্রেণীর সংগীতে বাক্য ও সুর দুইয়ে মিলে রসসৃষ্টির ভার নিয়েছে সেখানে আপন গৌরব রক্ষা করেও উভয়ের পদক্ষেপ উভয়ের গতি বাঁচিয়ে চলতে বাধ্য। (Prabahini)
তেলে জলে যেমন মেলে না, কথা ও সুর তেমনতরো অমিশুক নয়— মানুষের ইতিহাসের প্রথম থেকেই তার পরিচয় চলেছে। তাদের স্বাতন্ত্র্য কেউ অস্বীকার করে না, কিন্তু পরস্পরের প্রতি তাদের সুগভীর স্বাভাবিক আসক্তি লুকোনো নেই।
ধূর্জটিপ্রসাদকেই, আর একটি চিঠিতে লিখছেন,
তেলে জলে যেমন মেলে না, কথা ও সুর তেমনতরো অমিশুক নয়— মানুষের ইতিহাসের প্রথম থেকেই তার পরিচয় চলেছে। তাদের স্বাতন্ত্র্য কেউ অস্বীকার করে না, কিন্তু পরস্পরের প্রতি তাদের সুগভীর স্বাভাবিক আসক্তি লুকোনো নেই। নিয়তি নিয়মকে রক্ষা করবার খবরদারিতে বাঁধা পথে বারংবার স্টীম রোলার চালায়, ইতিমধ্যে সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টির ঝরনাকে বইয়ে দিতে থাকেন তারই স্বকীয় গতিবেগের বিচিত্র শাখায়িত পথে— এই পথে কথার ধারা একলা যাত্রা করে, সুরের ধারাও নিজের শাখা ধরে চলে, আবার সুর ও কথার স্রোত মিলেও যায়। এই মিলে এবং অমিলে দুয়েতেই রসের প্রবাহ। (Prabahini)
রবিচ্ছায়া থেকে রবীন্দ্রনাথের গানের বইয়ের যে-ধারা শুরু তাতে একটি অদ্বিতীয় স্থান নিয়ে শতবর্ষে পড়ল প্রবাহিণী। (Prabahini)
ডিজিটাল ও মুদ্রিত মাধ্যমে সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
ছবি সৌজন্য- আন্তর্জাল
শর্মিষ্ঠা দত্ত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের স্নাতকোত্তর। একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রবীন্দ্রসংগীতে স্নাতকোত্তর এবং রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী। রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে গবেষণা করেন। বিভিন্ন সংবাদ ও সাময়িকপত্রের নিয়মিত লেখিকা এবং আকাশবাণী কলকাতার মহিলা মহলের উপস্থাপিকা। শখ স্বদেশী ও বিদেশী রান্নার নানা নিরীক্ষা।