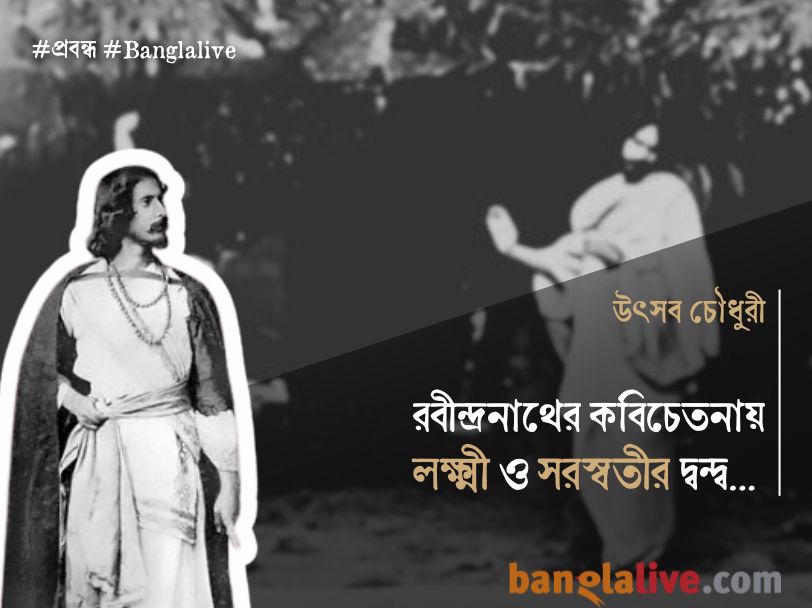বাঙালি সমাজে অনেকদিন ধরে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে… লক্ষ্মী ও সরস্বতীর একত্রে কৃপালাভ নাকি ভারী দুর্লভ! কেন? দেবতার মানবায়নে অভ্যস্ত বাঙালি বলে থাকে, আহা, এই দুই দেবী যে পরস্পরের সপত্নী, এঁদের মধ্যে সদ্ভাব হবে কী করে? সেই চৈতন্যপূর্ব যুগে লেখা কবি গুণরাজ খান তথা মালাধর বসুর ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ বইয়ের শুরুতেই দেখি কবি-বচন… “সব দেবগণের সে করিয়া বন্দন। কৃষ্ণের চরিত্র কিছু করিয়ে রচন।। লক্ষ্মী সরস্বতী বন্দো তাঁহার দুই নারী। যাহার প্রসাদে সর্ব লোক পুরস্করি।।” কৃষ্ণলীলায় এই দুই কৃষ্ণপত্নী লক্ষ্মী-স্বরূপা রুক্মিণী ও ভূ-স্বরূপা সত্যভামার দ্বন্দ্বকথা যেমন বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ ইত্যাদি প্রাচীন শাস্ত্রে আছে, তেমনই আছে শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত নবীন নাটক ‘ললিতমাধব’-এর পাতায়। এর মূল আছে বেদের পুরুষসূক্তে… সেখানে আদিপুরুষ ভগবান সম্বন্ধে বলা হয়েছে “হ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্নৌ অহোরাত্রে পার্শ্বে”। নারায়ণের পার্শ্বে অহোরাত্রি থাকেন তাঁর দুই পত্নী হ্রী-সরস্বতী ও লক্ষ্মী-কমলা। (Rabindranath Tagore)
রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ও গানে রথ-প্রসঙ্গ : উৎসব চৌধুরী
কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এই রমা-বাণী দ্বন্দ্ব এবং তার পরিণতি নিয়ে আজ দু-চার কথা বলা যাক।
কবি রবীন্দ্রনাথ যাঁকে কাব্যগুরু বলে স্বীকার করেছিলেন, সেই বিহারীলাল চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ রচনা ‘সারদামঙ্গল’। নামে মধ্যযুগীয় কাব্যধারার ছোঁয়াচ থাকলেও স্বভাবধর্মে এই কাব্য আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার সূচনাস্রোত বলা চলে। এই সারদামঙ্গলের অনুপ্রেরণায় রবীন্দ্রনাথ লিখলেন ‘বাল্মীকিপ্রতিভা’ গীতিনাট্য। অভিনয়ে তিনি স্বয়ং সাজলেন বাল্মীকি, আর তাঁর ভাইঝি প্রতিভা সাজলেন সরস্বতী… নাট্যনামের মধ্যে এই ইঙ্গিতটি ধরা রইল৷ দেবী সরস্বতীর কৃপায় দস্যুপতি বাল্মীকির মহাকবি বাল্মীকিতে রূপান্তর এই নাটকের আখ্যানবস্তু। তবে, সরস্বতীর চূড়ান্ত কৃপা পাওয়ার আগে লক্ষ্মীর কাছে বাল্মীকিকে পরীক্ষা দিতে হয়েছে। লক্ষ্মী বাল্মীকিকে “রতন রাশি রাশি” দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে সারস্বত মার্গের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা পরখ করেছেন। বাল্মীকি তাতে ভোলেননি, তিনি স্পষ্ট বলেছেন লক্ষ্মীর দেওয়া এই জাগতিক সম্পদ বিতরণের উপযুক্ত ক্ষেত্র কুবেরের অলকাপুরী অথবা দেবেন্দ্রের অমরাবতী; দীন বাল্মীকির কুটীরে এহেন “মণিময় ধূলিরাশি” অপ্রয়োজনীয়। কমলার পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন আদিকবি।
নিতান্ত তরুণ বয়সে লেখা এই সারস্বত আশীর্বাণী কবি রবীন্দ্রনাথের উত্তরজীবনে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই।
নাটকের শেষে সরস্বতী স্বয়ং এসে বাল্মীকির হাতে তুলে দিচ্ছেন বীণা… বলছেন, “যে করুণ রসে আজি ডুবিল রে ও হৃদয়/ শত স্রোতে তুই তাহা ঢালিবি জগৎময়।/… মোর পদ্মাসনতলে রহিবে আসন তোর,/ নিত্য নব নব গীতে সতত রহিবি ভোর।/বসি তোর পদতলে কবিবালকেরা যত/ শুনি তোর কণ্ঠস্বর শিখিবে সঙ্গীত কত…।” নিতান্ত তরুণ বয়সে লেখা এই সারস্বত আশীর্বাণী কবি রবীন্দ্রনাথের উত্তরজীবনে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই।
কবিদের জীবনেও অর্থ জিনিসটার প্রয়োজন থাকে বইকি। রবীন্দ্রনাথের ‘সোনার তরী’ কাব্যগ্রন্থের ‘পুরস্কার’ কবিতার কবিগৃহিণীর কণ্ঠে তাই ঝঙ্কার শোনা যায়, “ভারতীরে ছাড়ি ধরো এইবেলা/ লক্ষ্মীর উপাসনা।”
অবশ্য, কবিদের জীবনেও অর্থ জিনিসটার প্রয়োজন থাকে বইকি। রবীন্দ্রনাথের ‘সোনার তরী’ কাব্যগ্রন্থের ‘পুরস্কার’ কবিতার কবিগৃহিণীর কণ্ঠে তাই ঝঙ্কার শোনা যায়, “ভারতীরে ছাড়ি ধরো এইবেলা/ লক্ষ্মীর উপাসনা।” বাকচতুর কবি দমবার পাত্র নন, গৃহিণীকে প্রসন্ন করার অভিপ্রায়ে তিনি তাঁকেই দিব্যি গৃহলক্ষ্মীর পদে অভিষিক্ত করেন, চাটুবচনে বলেন, “ভয় নাহি করি ও মুখ-নাড়ারে/ লক্ষ্মী সদয় লক্ষ্মীছাড়ারে,/ ঘরেতে আছেন নাইকো ভাঁড়ারে/ এ কথা শুনিবে কেবা!/ আমার কপালে বিপরীত ফল/ চপলা লক্ষ্মী মোরে অচপল/ ভারতী না থাকে থির এক পল/ এত করি তাঁর সেবা।।” গৃহিণী মনে মনে প্রসন্ন হলেও বাইরে জেদ ছাড়লেন না, প্রতিবেশীদের ঘর থেকে আনা বসনভূষণে সাজিয়ে কবিকে পাঠালেন রাজদরবারে, রাজার অনুগ্রহের প্রত্যাশায়। রাজসমীপে কবি যে বাণী-বন্দনা করলেন, তাতেও কি অর্থের অভাবের চাপা সুর ফুটল না? ফুটল।
কবির খেদ মিটল, গৃহিণীর মধ্যে তিনি একই সঙ্গে বাণী ও রমার ঐশ্বর্য দেখতে দেখতে ভাবলেন, “বাঁধা প’ল এক মাল্য-বাঁধনে/ লক্ষ্মী সরস্বতী।”
সরস্বতীর উদ্দেশে কবি গাইলেন, “চারি দিকে সবে বাঁটিয়া দুনিয়া/ আপন অংশ নিতেছে গুনিয়া–/ আমি তব স্নেহবচন শুনিয়া/ পেয়েছি স্বরগসুধা॥/ সেই মোর ভালো, সেই বহু মানি–/ তবু মাঝে মাঝে কেঁদে ওঠে প্রাণী,/ সুরের খাদ্যে জান তো মা বাণী,/ নরের মিটে না ক্ষুধা।” রাজা কবির অন্তরের বেদনা বুঝেছিলেন নিশ্চয়ই, তাই রাজভাণ্ডার থেকে যথেচ্ছ পুরস্কার দেবার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন, কিন্তু কবি কী চাইলেন? নির্লোভ, সংসার-বুদ্ধিহীন কবি চাইলেন কেবল রাজার গলার পুষ্পহার। সেই রাজকণ্ঠমালা শিরে ধারণ করে গৃহে ফিরলেন কবি, গৃহিণী প্রথমে রোষের ভাণ করলেও শেষে কবিকে চুম্বনে চুম্বনে বিহ্বল করে দিয়ে সেই মালা পরলেন নিজের কণ্ঠে। স্ত্রীর সেই প্রেমপূর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে কবি উপলব্ধি করলেন, তাঁর পত্নী মুখে যাই বলুন, অন্তরে তিনি কবিরই মতো নির্লোভ, স্বর্ণসম্পদের বদলে সারস্বত পুরস্কারেই তিনি তৃপ্ত, প্রসন্ন, আনন্দিত। কবির খেদ মিটল, গৃহিণীর মধ্যে তিনি একই সঙ্গে বাণী ও রমার ঐশ্বর্য দেখতে দেখতে ভাবলেন, “বাঁধা প’ল এক মাল্য-বাঁধনে/ লক্ষ্মী সরস্বতী।”
আর কবি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যখন নিজ পত্নীর অন্তর্নিহিত দেবীত্বের সন্ধান করেন, তখন? কবিপত্নী মৃণালিনী দেবীর প্রয়াণের পর রবীন্দ্রনাথ যে শোককবিতার গুচ্ছ রচনা করেছিলেন, তা ‘স্মরণ’ কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়৷
আর কবি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যখন নিজ পত্নীর অন্তর্নিহিত দেবীত্বের সন্ধান করেন, তখন? কবিপত্নী মৃণালিনী দেবীর প্রয়াণের পর রবীন্দ্রনাথ যে শোককবিতার গুচ্ছ রচনা করেছিলেন, তা ‘স্মরণ’ কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়৷ সেই কাব্যের ৬ নং কবিতায় কবি গতাসু পত্নীর উদ্দেশে বলছেন, “আজি বিশ্বদেবতার চরণ-আশ্রয়ে/ গৃহলক্ষ্মী দেখা দাও বিশ্বলক্ষ্মী হয়ে।” অত:পর, গৃহ-পরিসর থেকে বৈশ্বিক পরিসরে সমুত্তীর্ণ কবিপ্রিয়া হয়ে উঠছেন রমা-বাণীর যুগ্ম-আলোকে ধৌতবিগ্রহা… “হে লক্ষ্মী, তোমার আজি নাই অন্তঃপুর।/ সরস্বতীরূপ আজি ধরেছ মধুর/ দাঁড়ায়েছ সঙ্গীতের শতদলদলে।” (৯ নং কবিতা)৷ মরণের পারে, দেহ ও গৃহের সীমানা ছাড়িয়ে সেই মানসসরসীতে মৃণালিনী অন্তহীনা। সেই অপার্থিব অলৌকিক দেবীপ্রতিমাই সকল দ্বন্দ্বাতীত পূর্ণ প্রেমময়ী… তাঁর উদ্দেশে কবি বলেন, “সেই বিশ্বমূর্তি তব আমারি অন্তরে/লক্ষ্মীসরস্বতীরূপে পূর্ণ রূপ ধরে।”
তথ্য ঋণ:
‘বাল্মীকিপ্রতিভা’ গীতিনাট্য
‘সোনার তরী’ ও ‘স্মরণ’ কাব্যগ্রন্থ
সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে সাম্মানিক বাংলা সহ স্নাতক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর ও এম ফিল, বর্তমানে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, কলকাতায় পিএইচডি গবেষণারত।