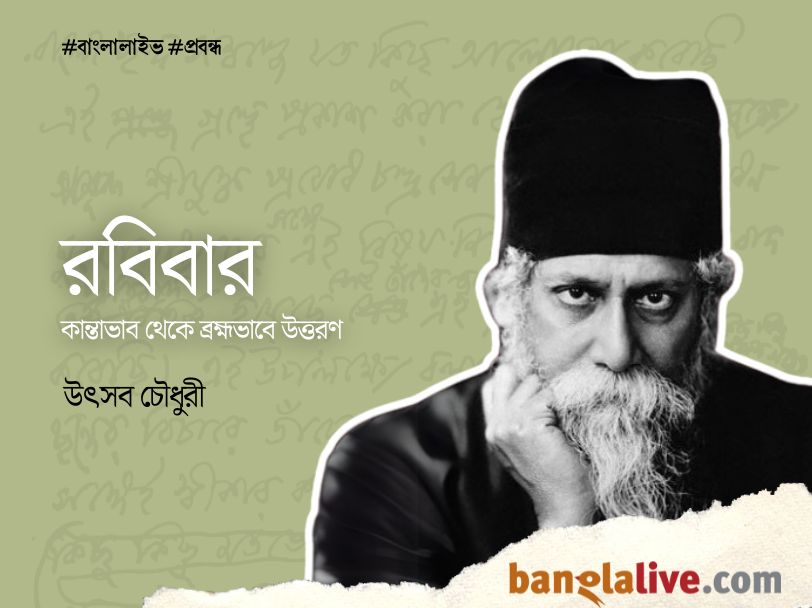(Rabindranath Tagore)
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘রবিবার’ গল্পের শুরুতেই নায়ক সম্বন্ধে বলছেন “আমার গল্পের প্রধান মানুষটি”…। গল্পটি তাঁরই রচনা, অতএব সেই কর্তৃত্বের ভূমিকা থেকে তাঁকে “আমার গল্প” বলে তিনি উল্লেখ করতেই পারেন। কিন্তু, এই গল্পের নায়কের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তাও কি কোথাও সঙ্গোপন নেই? তাহলে তো “আমার গল্প” কথাটার অন্য অর্থ দাঁড়াবে। দেখা যাক, এই অন্য অর্থটি এই গল্পের ক্ষেত্রে কতখানি প্রাসঙ্গিক। (Rabindranath Tagore)
গল্পের শুরুতেই রয়েছে নায়কের নামবদলের আখ্যান। নিজের সাবেকি ‘অভয়াচরণ’ নামটির মধ্যে যে কুলধর্মের ছাপ ছিল, নায়ক সেটি মান্য করল না। “অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত।।”… মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যের বিখ্যাত ভণিতা। ‘অভয়াচরণ’ নামটির মধ্যে ভয়নাশিনী দেবীর চরণে আত্মনিবেদিত ভক্তির যে অনুষঙ্গ ছিল, তা পছন্দ না হওয়ায় নায়ক নিজের নতুন নাম রাখল ‘অভীককুমার’, কালক্রমে বিভা-সহ বন্ধুদলের মুখে মুখে, এবং তার চিঠির নীচে স্বাক্ষরেও সেই নাম সংক্ষিপ্ত হয়ে হল ‘অভীক’। ‘অ’ উপসর্গ এবং ‘ভী’ ধাতুর প্রয়োগ ‘অভয়া’ আর ‘অভীক’ দুটি শব্দেই আছে বটে, কিন্তু তারপর প্রত্যয়গত পার্থক্যের জন্য অর্থ গেছে বদলে। (Rabindranath Tagore)
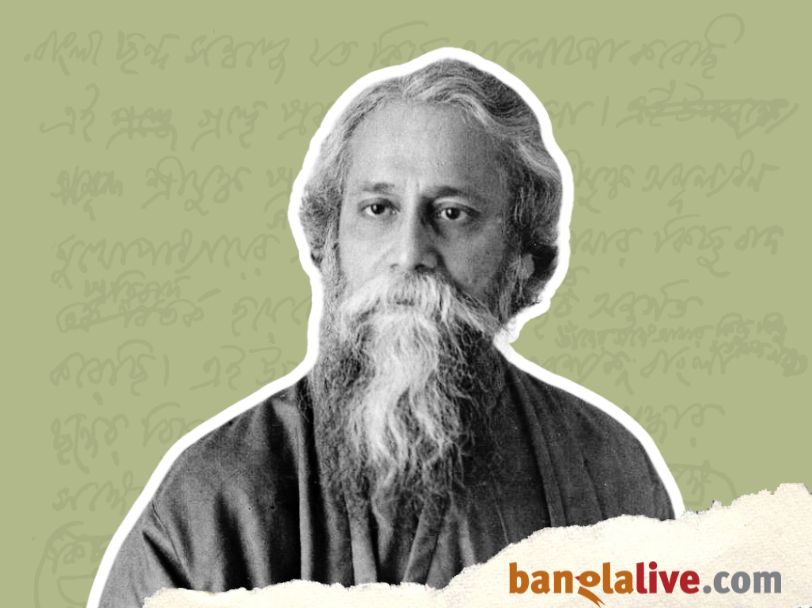
‘অভীক’ অর্থাৎ যার ভয় নেই। কুলধর্মকে অস্বীকার করলেও দুই নামের মূল ভাবটি কিন্তু এক, ভয়-হীন এক পরিস্থিতি, তবে কী না ভয়হীনতার হেতু পৃথক৷ প্রথম নামে ভয়হীনতার হেতু দেবীর চরণাশ্রয়, দ্বিতীয় নামে ব্যক্তির নিজস্ব স্ব-ভাব। অর্থাৎ, নায়কের দাবি এই যে, তার অন্তরের মানুষটি স্বতই ভয়হীন, কোনও এক দেবতার চরণে আশ্রয় নিয়ে ভয় থেকে অভয়ের দিকে যাত্রার গরজ তাঁর নেই। শেষ অসুখের সময়ে রাণী চন্দ ও অনিল চন্দকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি গান স্মরণে রাখতে বলেছিলেন, “বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে আমি না যেন করি ভয়।” রবীন্দ্রনাথের উক্তি, তাঁর এই গানটি (এবং তৎসহ আরও কিছু গান) “মন্ত্রের মতো”, তাই এগুলি স্মরণে রাখা প্রয়োজন। এই গানের প্রথম দুটি উদ্ধৃত চরণে কবির বক্তব্যের সঙ্গে অভয়াচরণ থেকে অভীক হয়ে ওঠার প্রয়াসী নায়কের বক্তব্যের আশ্চর্য মিল। (Rabindranath Tagore)
আরও পড়ুন: রবীন্দ্রনাথের কবিচেতনায় লক্ষ্মী ও সরস্বতীর দ্বন্দ্ব…
অভীকের নাম-পরিচয় থেকে শাস্ত্রীয় দেবীর বিসর্জন ঘটলেও, তার জীবনচর্যায় কিন্তু এক বিকল্প দেবীসত্তার আবির্ভাব ঘটেছে অতিব্যাপ্ত পরিসরে। গল্পের একেবারে শেষের চিঠিতে অভীক যে আত্মপরিচয় দিয়েছে, সেটি হল “তোমার নাস্তিক ভক্ত/ অভীক”। “তোমার” অর্থে গল্পের নায়িকার, বিভার। “নাস্তিক ভক্ত” কথাটির মধ্যে রয়েছে বিরোধাভাস অলঙ্কারের প্রয়োগ… যে নাস্তিক, সে আবার ভক্ত হয় কীভাবে? আসলে ‘নাস্তিক’ কথাটির অর্থ প্রসঙ্গভেদে পালটে পালটে যায়। সনাতনী হিন্দুর কাছে বৌদ্ধ নাস্তিক, কারণ বৌদ্ধ বেদের স্বতঃ প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। এমন একজন ‘নাস্তিক’ বলে দেগে দেওয়া বৌদ্ধও কিন্তু শাক্যমুনি বুদ্ধ এবং অন্যান্য বৌদ্ধশাস্ত্রোল্লিখিত বৌদ্ধ দেবতাদের প্রতি ‘ভজনশীল’, অতএব তাঁর ‘ভক্ত’ হতে বাধা নেই। অভীকের ‘নাস্তিক’ পরিচয়টি তার কুলধর্মগত আচারনীতির বিরোধজাত পরিচয়; আর ‘ভক্ত’ পরিচয়টি তাঁর আত্মধর্মগত ভজনশীলতার পরিচয়। তাঁর কাছে দুইই সত্য। (Rabindranath Tagore)
শেষ অসুখের সময়ে রাণী চন্দ ও অনিল চন্দকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি গান স্মরণে রাখতে বলেছিলেন, “বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে আমি না যেন করি ভয়।”
কিন্তু শাস্ত্রপরম্পরায় যিনি ঈশ্বর বলে, দেবতা বলে স্বীকৃত নন, তাঁর ‘ভক্ত’ হওয়া কি রবীন্দ্র-মনন-বিশ্বে স্বীকৃত? এর উত্তর, হ্যাঁ। রবীন্দ্রনাথের ‘জীবনদেবতা‘-র তত্ত্ব যে কাব্যে উজ্জ্বল হয়ে উদ্ভাসিত, সেই ‘চিত্রা’-র রচনাবলী সংস্করণের ভূমিকায় কবি লিখেছেন, “বস্তুত চিত্রায় জীবনরঙ্গভূমিতে যে মিলননাট্যের উল্লেখ হয়েছে তার কোনও নায়ক-নায়িকা জীবের সত্তার বাইরে নেই, এবং তার মধ্যে কেউ ভগবানের স্থানাভিষিক্ত নয়।” কবি এই কাব্যের নামকবিতা ‘চিত্রা’-য় বলেছেন, কবিকথকের দেশকালাতীত অন্তর্লোকের শান্তিময় বিরতির কেন্দ্রে নিত্যবিরাজিতা সেই জীবনদেবতা, এবং কবির অন্তরসত্তা সেখানে ভক্তরূপে নিত্যনীরাজনে ব্রতী… “একটি ভক্ত করিছে নিত্য আরতি।” সুতরাং, যে জীবনদেবতা ভগবানের স্থলাভিষিক্ত নন, যিনি জীবসীমার অন্তর্ভুক্ত, নিজের অন্তরসত্তাকে সেই অন্তরব্যাপিনীর ‘ভক্ত’ বলে ঘোষণা করতে কবি রবীন্দ্রনাথের আপত্তি ঘটেনি। (Rabindranath Tagore)
কবিমানসীকার জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন, “এক অর্থে রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীদাস-পন্থ প্রেমের কবি।” এখানে চণ্ডীদাস অর্থে তিনি বিবিধ সমনামী কবিগোষ্ঠীটির ইঙ্গিত করেছেন, যে গোষ্ঠীর রচনায় সহজিয়া বৈষ্ণব তত্ত্বও অন্তর্ভুক্ত৷ তাই, ‘বৈষ্ণবকবিতা’ রচনাটিতে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবির প্রেমকাব্যের অনুপ্রেরণা রূপে জাগতিক নরনারীর প্রেমযাপনের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। ‘পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি’ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক উদ্ধৃত হয়েছে সহজিয়া চণ্ডীদাসের রচনাংশ… “তুমি বেদবাদিনী, হরের ঘরনী/ তুমি সে নয়নের তারা–“। ‘রবিবার’ গল্পে দেখি, অভীকের বংশগত ধর্মাভ্যাস মূলত দুটি, একইসঙ্গে বিজড়িত প্রাচীন বৈদিক ব্রাহ্মণ্য এবং তীব্র শাক্ত আচার। এই দুটি প্রতিষ্ঠানকেই অভীক ত্যাগ করল, এবং বিভা হয়ে উঠল তার কাছে এই দুটি প্রতিষ্ঠানেরই বিকল্প– “বেদবাদিনী” অর্থাৎ ব্রাহ্মণের উপাস্য বৈদিক ব্রহ্মগায়ত্রী এবং “হরের ঘরণী” অর্থাৎ শাক্তের উপাস্য শিবগৃহিণী(তাদের গৃহদেবতা ছিলেন ভদ্রকালী)। (Rabindranath Tagore)
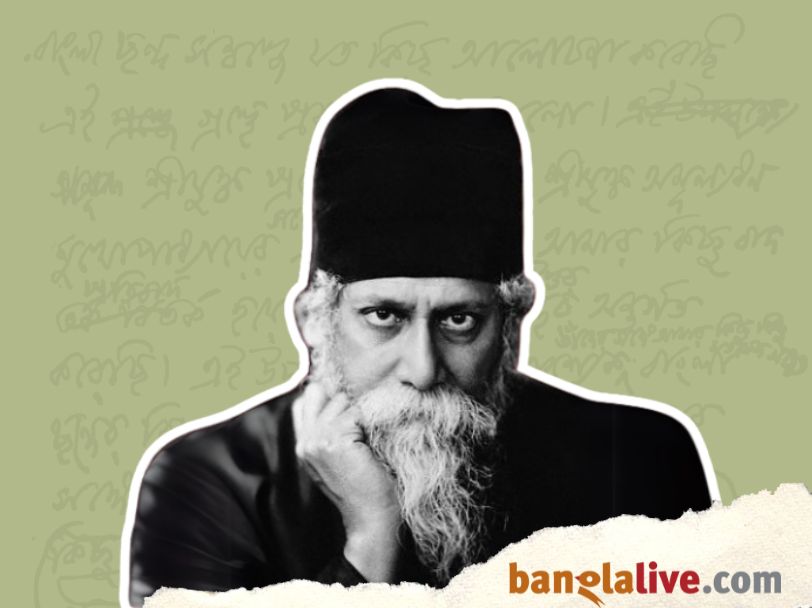
অভীক বিভাকে বলেছে, “সব দেবতার চেয়ে তুমি আমার কাছে প্রত্যক্ষ সত্য, এ কথা ভুলিয়ে দেবার মতো একটিও দেবতা নেই আমার সামনে।” অভীকের এই চিন্তার আড়ালে কোথাও কোনও পূর্বসূত্র নেই, তা বলতে পারি না। দেবতার বিগ্রহ, যন্ত্র, শিলা আদি আধারের মধ্যে প্রত্যক্ষ নারীই শক্তিসাধনার আধার হিসাবে সর্বোত্তম, এ কথা বীরাচারী তান্ত্রিক পরম্পরায় স্বীকৃত। অভীক বিভাকে যখন কোনও পরম্পরা-স্বীকৃত দেবতার সঙ্গে তুলনা করতে চেয়েছে, তখন তার মনে এবং মুখে প্রচলিত শক্তিদেবতার নামই এসেছে। অভীকের কথা অনুসারে, “আমার বেলায় তুমি মহামায়া, ভুলিয়ে রাখ; অধ্যাপকের বেলায় তুমি তারা, তরিয়ে দাও।” দেবীর মোহবন্ধনকারিণী স্বভাবটিই মহামায়া আর মোহমোচনকারিণী, ত্রাণদায়িনী স্বভাবটিই তারা… এই পরম্পরাগত বিশ্বাস অভীকের চিত্তলোক ত্যাগ করেনি। (Rabindranath Tagore)
এইখানে, অভীকের একটি প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম পাওয়া গেল, গণিতের অধ্যাপক অমরবাবু। এ নিয়ে আলোচনা সবিস্তার করার আগে মনে রাখতে হবে, অভীকের চিত্তলোকের মহামায়া-মূর্তি হওয়া ছাড়াও বিভার আরও একটি দেবীকল্প-মূর্তির কথা এ গল্পে উল্লেখ করা হয়েছে। সেটি হল চণ্ডীদাসের রাধা-মূর্তি। অভীকের প্রতি বিভার প্রেমের গভীরতা লক্ষ্য করে তার এক সখী পরিহাস করে বলেছিল, “মরি মরি, তোমারই গরবে গরবিনী আমি, রূপসী তোমারই রূপে।” এই উক্তি শ্রীরাধার উক্তি, চণ্ডীদাসের পদাবলীর দেবী-নায়িকার উক্তি। প্রচলিত কাব্যভাবনায় শ্রীরাধা মানবতী, বহুবল্লভ কৃষ্ণের অন্য-নায়িকা-বিলাসে তাঁর অতি প্রবল মান জন্মায়। অভীক অত্যন্ত সচেতনভাবে বিভার এই মানিনী স্বভাবটিকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছে তারই সামনে শীলা-সহ অন্যান্য সুন্দরীদের প্রতি নিজের আকর্ষণ তথা প্রশ্রয় ব্যক্ত করে। (Rabindranath Tagore)
আরও পড়ুন: শ্যামলী: রবীন্দ্রনাথের এক অভিনব গৃহ-পরিকল্পনা
পদাবলীর তত্ত্ববিশ্বের পরিভাষায় একে বলে ‘গোত্রস্খলন’… নায়িকার সম্মুখে নায়কের মুখে অন্য নারীর নামোচ্চারণে নায়িকার মান। কিন্তু বিভার মন টলেনি, অভীককে স্বীকার করতে হয়েছে যে বিভার মনে ঈর্ষা জাগিয়ে তোলা প্রায় অসম্ভব বটে। কিন্তু বিভা যেই অধ্যাপক অমরবাবুর বিলাতযাত্রায় আর্থিক সহায়তার সঙ্কল্পের কথা জানিয়েছে, অমনি, অমরবাবুর প্রতি বিভার কথায় বা আচরণে আদিরসাত্মক প্রশ্রয়ের চিহ্নমাত্র না থাকা সত্ত্বেও, অভীকের প্রবল ঈর্ষাজাত মান জন্মেছে। ‘গোত্রস্খলন’ লীলার এই বিপরীত চাল তো পদাবলীর পরম্পরায় বাহিত নয়। এ হল রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব জীবনসত্য। তাঁর কৈশোরে, কাব্য-কূজন আরম্ভ করার সময়ে কাদম্বরী দেবী তাঁরই সামনে বিহারীলাল চক্রবর্তীর কাব্যপ্রতিভার উচ্চ প্রশংসা করলে কবি-কিশোরের মনে যে প্রবল মান জন্মাত, অভীকের এই মানকে তারই দূরাগত প্রতিফলন বলে চিহ্নিত করতে চাইলে আশা করি ব্যাপারটা বেমানান ঠেকবে না! (Rabindranath Tagore)
‘রবিবার’ গল্পে বিভার সখীর সংলাপ অনুসরণে বিভার চরিত্রেও এই চণ্ডীদাস-বর্ণিতা রাধার ছায়াপাত ঘটেছে।
কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দূরত্বের হেতু মূলত দুইটি… এক, সামাজিক বাধার গণ্ডী পেরিয়ে তাঁর সঙ্গে দাম্পত্যযাপন ছিল অসম্ভব কল্পনা মাত্র; আর দুই, কাদম্বরীর আকস্মিক আত্মখণ্ডন। জগদীশ ভট্টাচার্য উল্লেখ করেছেন, “রবীন্দ্রমানসে কাদম্বরী দেবীর প্রথম মানসী-মূর্তি হল রাধামূর্তি।” ‘রবিবার’ গল্পে বিভার সখীর সংলাপ অনুসরণে বিভার চরিত্রেও এই চণ্ডীদাস-বর্ণিতা রাধার ছায়াপাত ঘটেছে। অভীকের সঙ্গে বিভার দূরত্বের হেতুও মূলত দুটি… এক, বিবাহের অসম্ভাব্যতা, আর দুই, অভীকের আত্ম-অপসারণ। বিভার অন্তর্গত এই রাধা-সত্তার উপস্থিতির ফলেই গল্পের যুগলের মধ্যে একের আত্ম-অপসারণ আর মৃত্যুজনিত ‘করুণ বিপ্রলম্ভ’ নয়, দূরদেশগমন-জনিত ‘প্রবাস বিপ্রলম্ভ’। প্রবাসগত অভীকের চিঠির মাধ্যমেই এই গল্পের অবসান। (Rabindranath Tagore)
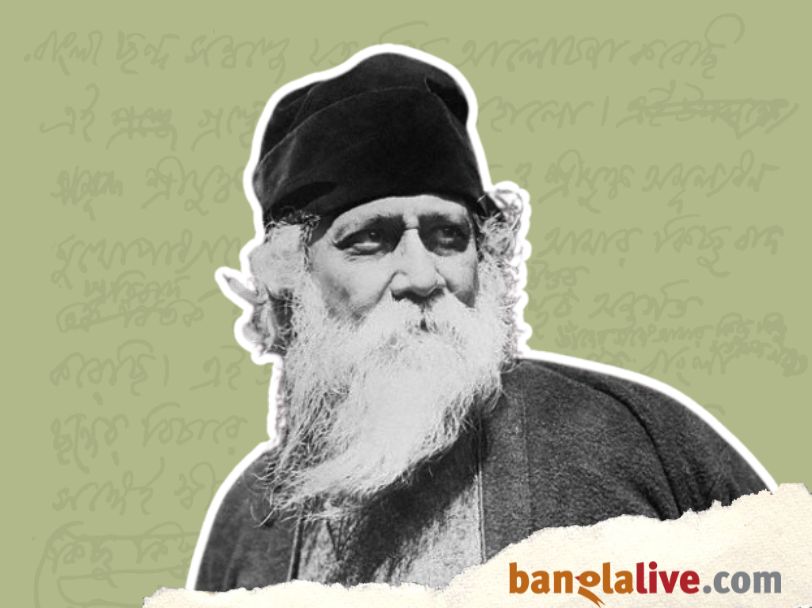
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা।”
(Rabindranath Tagore) যে নারীজাতি অভীকের কাছে “নাস্তিকের দেবতা”, তাদেরই মধ্যে সর্বপ্রধানার আসনে এই চিঠিতে বিভাকে স্থাপন করে অভীক লিখেছে, “কিন্তু নিশ্চয় তুমি জান যে, তারা নীহারিকামণ্ডলী, তার মাঝখানে তুমি একটিমাত্র ধ্রুবনক্ষত্র। তারা আভাস, তুমি সত্য।” এই উচ্চারণের মধ্যে গোপীযূথশিরোমণি শ্রীরাধার শ্রেষ্ঠত্বের অনুপ্রেরণা আছে৷ সেইসঙ্গে, ‘রবীন্দ্র-ছোটোগল্পের শিল্পরূপ’ গ্রন্থে তপোব্রত ঘোষ উল্লেখ করেছেন, বিভাকে ধ্রুবতারার সঙ্গে উপমিত করার মধ্যে লুকিয়ে আছে স্বয়ং কবির তরুণ বয়সের লেখা কবিতা “তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা”-র স্মৃতি। এই কবিতা প্রাথমিকভাবে কাদম্বরী দেবীর স্তুতি আকারে রচিত হলেও পরে ব্রহ্মসংগীতে পরিবর্তিত হয়, এমনটিই গবেষকদের সিদ্ধান্ত৷ (Rabindranath Tagore)
অভীকের চেতনায় ‘ঈশ্বর’ তাই প্রেমের ‘অসীম’ ও ‘সত্য’ এক অব্যক্ত হ্লাদৈকভাব, বিভার মানবীমূর্তির মাধ্যমেই ইন্দ্রিয়গোচর তথা হৃদয়গ্রাহী রূপে সেই ভাবের রসায়িত অভিব্যক্তি।
(Rabindranath Tagore) এই যে কান্তাভাব থেকে ব্রহ্মভাবে উত্তরণ, এরই প্রতিধ্বনি করে অভীক বলেছে, “এরই (বিভার অব্যক্ত ‘অলৌকিক’ প্রীতিরই) আকর্ষণে কোনো এক ভাবে হয়তো তোমার সঙ্গে সঙ্গে তোমার ভগবানেরই কাছাকাছি ফিরেছি।” অভীক বলেছে, “বী, আমার মধুকরী, জগতে সবচেয়ে ভালোবেসেছি তোমাকে। সেই ভালোবাসার কোনো একটা অসীম সত্যভূমিকা আছে বলে যদি মনে করা যায়, আর তাকেই যদি বল তোমাদের ঈশ্বর, তা হলে তাঁর দুয়ার আর তোমার দুয়ার এক হয়ে রইল এই নাস্তিকের জন্যে।” অভীকের চেতনায় ‘ঈশ্বর’ তাই প্রেমের ‘অসীম’ ও ‘সত্য’ এক অব্যক্ত হ্লাদৈকভাব, বিভার মানবীমূর্তির মাধ্যমেই ইন্দ্রিয়গোচর তথা হৃদয়গ্রাহী রূপে সেই ভাবের রসায়িত অভিব্যক্তি। তাই, সমুদ্রপথে প্রথম বিলাতযাত্রার প্রাক্কালে তরুণ রবীন্দ্রনাথের কাদম্বরী-স্তুতি এবং বিলাতের উদ্দেশ্যে সমুদ্রপথযাত্রী অভীকের বিভা-স্তুতি সহৃদয় সামাজিক পাঠকের চিত্তে একীভূত হয়। অসীম জলরাশির মধ্যে ভাসমান প্রাগাধুনিক নাবিকের উচ্চারণের মতোই দৃঢ়, সত্য, স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই গান…
(Rabindranath Tagore)
কখনো বিপথে যদি ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি
অমনি ও মুখ হেরি শরমে সে হয় সারা।।
তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা,
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা।
যেথা আমি যাই নাকো তুমি প্রকাশিত থাকো,
আকুল নয়নজলে ঢালো গো কিরণধারা॥
তব মুখ সদা মনে জাগিতেছে সংগোপনে,
তিলেক অন্তর হলে না হেরি কূল-কিনারা।
কখনো বিপথে যদি ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি
অমনি ও মুখ হেরি শরমে সে হয় সারা।।
তথ্যসূত্র:
১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘তিন সঙ্গী’।
২) জগদীশ ভট্টাচার্য, ‘কবিমানসী’ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)।
৩) তপোব্রত ঘোষ, ‘রবীন্দ্র-ছোটোগল্পের শিল্পরূপ’।
সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে সাম্মানিক বাংলা সহ স্নাতক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর ও এম ফিল, বর্তমানে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, কলকাতায় পিএইচডি গবেষণারত।