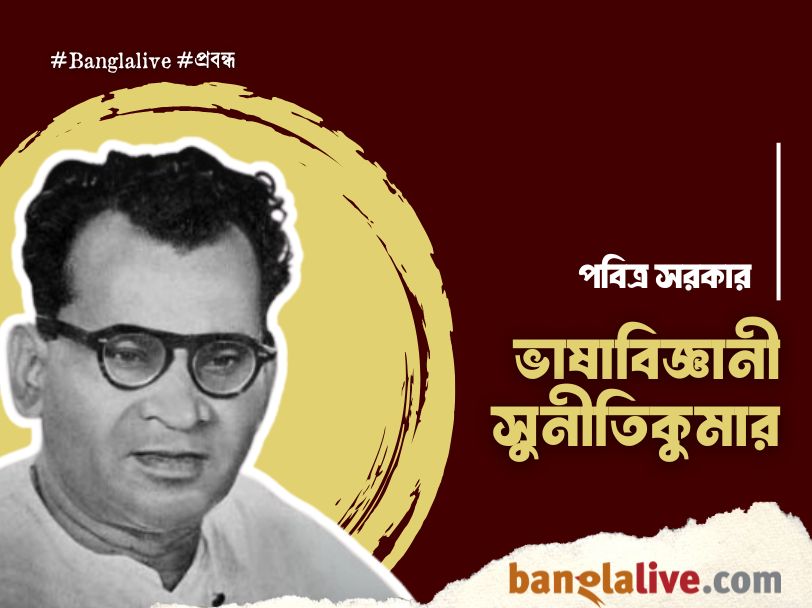(Suniti Kumar Chatterji) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭), তাঁর কাজের বিপুলতা, বিস্তার আর নানামুখী সামাজিক অস্তিত্বের গৌরবে এখনও ভারতের সর্বপ্রধান ভাষাবিজ্ঞানী, এবং বিশ শতকের এক শ্রেষ্ঠ শিক্ষক আর প্রজ্ঞাজীবী। যদিও ভাষাবিজ্ঞানীর পরিচয়ই তাঁর মুখ্য।
যেহেতু তাঁর চিত্রাঙ্কণে বিশেষ দক্ষতা ছিল, ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষাতেই তাঁর বর্ণনা ছিল খুবই চিত্ররূপময়। তাঁর লেখনী ছিল অজস্রপ্রসূ।
হাওড়ার শিবপুরের এই সন্তান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষা ও পরে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের (Comparative Philology) পাঠ শেষ করার পর ভারত সরকারের বৃত্তি পেয়ে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা করেন, যা পরে The Origin and Development of the Bengali Language, সংক্ষেপে ODBL নামে দুই বিশাল খণ্ড কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয়। (Suniti Kumar Chatterji)
আরও পড়ুন: লাইব্রেরি নিয়ে ব্যক্তিগত…
এই গবেষণা তাঁকে ভাষার ইতিহাসের এক শ্রেষ্ঠ গবেষক রূপে সারা পৃথিবীতেই সম্ভ্রম এনে দেয়। ভাষাবিজ্ঞানে তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাজ হল Indo-Aryan and Hindi (এর পরিশিষ্টে তাঁর ভারতীয় ভাষা রোমান লিপিতে লেখার একটি প্রস্তাব আছে), ‘বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা’ ইত্যাদি। তার বাইরেও অজস্র গ্রন্থের রচয়িতা তিনি। তার মধ্যে ভ্রমণ-সংক্রান্ত বইই বেশি, যদিও ভ্রমণের মধ্যে দেখা দেশের একটা বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিচয় তিনি সব সময় দিতেন। আর যেহেতু তাঁর চিত্রাঙ্কণে বিশেষ দক্ষতা ছিল, ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষাতেই তাঁর বর্ণনা ছিল খুবই চিত্ররূপময়। তাঁর লেখনী ছিল অজস্রপ্রসূ। (Suniti Kumar Chatterji)
সুনীতিকুমারের ভাষাবিজ্ঞান সংক্রান্ত রচনাকে বুঝতে হলে তিনি যে তত্ত্বপটভূমিকায় গবেষণা করেছিলেন তা বোঝা দরকার। সেটি হল ভাষাবিজ্ঞানের তুলনামূলক-ঐতিহাসিক পরম্পরা।
সুনীতিকুমারের ভাষাবিজ্ঞান সংক্রান্ত রচনাকে বুঝতে হলে তিনি যে তত্ত্বপটভূমিকায় গবেষণা করেছিলেন তা বোঝা দরকার। সেটি হল ভাষাবিজ্ঞানের তুলনামূলক-ঐতিহাসিক পরম্পরা। ১৭৮৬ সালে এই কলকাতাতেই যার প্রথম সূত্রপাত বলা যায়। তখনকার রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম জোন্স ওই প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় বর্ষে পদার্পণের স্মারক বক্তৃতায় জানান যে, তাঁর মনে হয়েছে, সংস্কৃত একটি অসামান্য ভাষা শুধু নয়, এর সঙ্গে জন্মসূত্র ইউরোপের প্রাচীন ভাষা গ্রিক, লাতিন, আর এশিয়ার প্রাচীন ভাষা পারসিকের গভীর আত্মীয়তা আছে। তাঁর এই বক্তৃতায় সারা পৃথিবীতে সাড়া পড়ে যায়, এবং সেখানে সংস্কৃত শেখার একটা উন্মাদনা দেখা যায়। (Suniti Kumar Chatterji)
সংস্কৃত একটি অসামান্য ভাষা শুধু নয়, এর সঙ্গে জন্মসূত্র ইউরোপের প্রাচীন ভাষা গ্রিক, লাতিন, আর এশিয়ার প্রাচীন ভাষা পারসিকের গভীর আত্মীয়তা আছে।
বিশেষত জার্মানদের মধ্যে, কারণ সংস্কৃতের মতো একটি সুপ্রাচীন ভাষাকে তাদের ভাষার প্রাচীন আত্মীয় জেনে তাদের জাতিসত্তার বোধ দৃঢ় হয়েছিল। এর ফলে প্রথম যে ভাষাবিজ্ঞানের জন্ম হল তা ওই তুলনামূলক-ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান, যার স্থিতিকাল মোটামুটিভাবে ঊনবিংশ শতাব্দী।
আরও পড়ুন: ভাষাদিবসের চর্চা : বাংলা ভাষার কিছু কাজকর্ম
এই ভাষাবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হল, এক ভাষার সন্তান হিসেবে অনুমিত কয়েকটি ভাষার মধ্যে ধ্বনি, শব্দখণ্ড, বাক্যগঠন ইত্যাদির তুলনা করে তাদের আত্মীয়তা আর পার্থক্য দেখানো, আর পার্থক্যের কারণ নির্দেশ করা। সেই সঙ্গে ওই তুলনার ভিত্তিতে তাদের মাতৃস্থানীয় ভাষাটি, যদি লুপ্ত হয়ে থাকে, তা কীরকম ছিল তার একটা ছায়ামূর্তি তৈরি করা। এর নাম পুনর্গঠন বা reconstruction. Reconstruction-এর সাহায্যেই গ্রিক, লাতিন, ইংরেজি ও জার্মান ইত্যাদির প্রাচীন রূপ টিউটনিক, চেক, পোলিশ রাশিয়ান ইত্যাদির প্রাচীন রূপ বালতোস্লাভিক, ফারসি, সংস্কৃত ইত্যদি সকলের মাতৃস্থানীয় ভাষা যে লুপ্ত ইন্দো-ইউরোপীয়, তা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছিল। (Suniti Kumar Chatterji)
আসলে একাধিক ভাষার তুলনা, আর ভাষাগুলির বিবর্তন বা বদলে-আসার ইতিহাস একটা আর-একটার উপর নির্ভরশীল বলেই।
ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই আত্মীয় ভাষাগুলির তুলনা করে ভাষাবংশের ইতিহাস রচনা থেকে সুনির্দিষ্ট ভাষার ইতিহাস রচনার দিকে ভাষাবিজ্ঞানীদের নজর পড়ে। আসলে একাধিক ভাষার তুলনা, আর ভাষাগুলির বিবর্তন বা বদলে-আসার ইতিহাস একটা আর-একটার উপর নির্ভরশীল বলেই। ফলে রাস্তা আলাদা পুরোপুরি হয়নি। তবু মনে রাখতে হবে এর মধ্যে হেগেলের ইতিহাস-দর্শন প্রচারিত হয়েছে, তার প্রভাবে ১৮৪৮ সালে মার্কস এঙ্গেলসের কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো মানুষের সভ্যতার দ্বন্দ্বময় ইতিহাস নির্মাণ করেছেন, ১৮৫৯-এ প্রকাশিত হয়েছে চার্লস ডারউইনের ‘দি অরিজিন অফ স্পিসিজ’। ইতিহাসের প্রতি মনোযোগে তীব্রতা এসেছে। (Suniti Kumar Chatterji)
সুনীতিকুমার লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর যে গবেষণা করলেন, তা এই ইতিহাসের দিকে নজর রেখে। বাংলা ভাষার সর্বাঙ্গীণ ইতিহাস।
সুনীতিকুমার লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর যে গবেষণা করলেন, তা এই ইতিহাসের দিকে নজর রেখে। বাংলা ভাষার সর্বাঙ্গীণ ইতিহাস। বলা বাহুল্য, সেই সাড়ে চার হাজার বছর আগেকার লুপ্ত ইন্দো-ইউরোপীয় থেকে ইন্দো- পারসিক, প্রাচীন ভারতীয় আর্য (বৈদিক ও সংস্কৃত), মধ্য ভারতীয় আর্য (পালি ও প্রাকৃত), অপভ্রংশ হয়ে বাংলায় বা নব্য ভারতীয় আর্যে পৌঁছোল, তার বিপুল ইতিহাস। বাংলা ধ্বনি, শব্দাবলির উৎপত্তি নিয়ে বারোশো পৃষ্ঠার বেশি আলোচনা। (Suniti Kumar Chatterji)
ইংরেজি ভাষার ইতিহাসে ইয়েসপার্সনের কাজ ছাড়া সারা পৃথিবীতেই এত বিশদ কাজের তুলনা নেই। এই ODBL সারা পৃথিবীর ভাষাবিজ্ঞানীদের কাছেই সমাদৃত ও সম্মানিত।
ইংরেজি ভাষার ইতিহাসে ইয়েসপার্সনের কাজ ছাড়া সারা পৃথিবীতেই এত বিশদ কাজের তুলনা নেই। এই ODBL সারা পৃথিবীর ভাষাবিজ্ঞানীদের কাছেই সমাদৃত ও সম্মানিত। এই ধরনের, অবশ্য আরও অনেক কম পরিসরে, সুনীতিকুমারের আর একটি কাজ Indo-Aryan and Hindi (১৯৪২)। এর পরিশিষ্টে আছে রোমান লিপিতে ভারতীয় ভাষাগুলি লেখার একটি প্রস্তাব, যা আমাদের কাছে সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। খানিকটা ইতিহাসের প্রেক্ষাপট বজায় রেখে তিনি Kiratajanakrti (1951), Dravidian (1965), রাজস্থানি ভাষার একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ ইত্যাদি বইও লিখেছেন। (Suniti Kumar Chatterji)
আরও পড়ুন: বাংলা ভাষা এবং ভাষা প্রযুক্তি
অর্থাৎ তাঁর মূল আদলটি ছিল ইতিহাসের। যখন তিনি এ কাজ শুরু করেছেন তার দশ-পনেরো বছর আগেই ভাষাবিজ্ঞানী ফেরদিনাঁ দ সোস্যুর (১৮৫৭-১৯১১) ভাষাবিজ্ঞানে নতুন পন্থা, ভাষার সংগঠন বিচারের সূত্রপাত করেছেন। কিন্তু তা হলেও সুনীতিকুমারের কাজের মূল্য এতটুকু কমে না। এই ইতিহাসের বাইরে সুনীতিকুমারের দ্বিতীয় বিশেষজ্ঞতার ক্ষেত্র ছিল ধ্বনিবিজ্ঞান বা ফোনিটিক্স। তিনি ছিলেন তখনকার এক শ্রেষ্ঠ ধ্বনিবিজ্ঞানী ড্যানিয়েল জোন্সের ছাত্র। ১৯২১ সালে তাঁর প্রবন্ধ Bengali Phonetics, বিপুলভাবে সমাদৃত হয়। (Suniti Kumar Chatterji)
এই ইতিহাসের বাইরে সুনীতিকুমারের দ্বিতীয় বিশেষজ্ঞতার ক্ষেত্র ছিল ধ্বনিবিজ্ঞান বা ফোনিটিক্স। তিনি ছিলেন তখনকার এক শ্রেষ্ঠ ধ্বনিবিজ্ঞানী ড্যানিয়েল জোন্সের ছাত্র।
পরে তিনি A Brief Sketch of Bengali Phonetics নামে যে ছোট বইটি প্রকাশ করেন(১৯২৮), তাতে উচ্চারণ তত্ত্বের চেয়ে বাংলাভাষার ধ্বনিতত্ত্ব বা ফোনিমিক্সই (কোনও ধ্বনি শব্দে কীভাবে ব্যবহৃত হয়, তা অন্য ধ্বনিকে কীভাবে প্রভাবিত করে ইত্যাদির বিচার) প্রধানভাবে আলোচিত হয়েছে। তাঁর এ বিষয়ে জ্ঞানের ব্যাপ্তির প্রমাণ পাওয়া যায় ব্যাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়ে Phonetics in the Study of Classical Languages in the East নামক বক্তৃতায়।
তাঁর ‘ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা’ বইটি ভারতের ভাষাগুলির রাজনৈতিক ভূমিকা কী হতে পারে তার একটি মনোজ্ঞ আলোচনা।
সুনীতিকুমারের বাংলা ভাষায় ভাষাতত্ত্বের বই একটিই, বলা চলে, ‘বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা’ (১৯২৯), যাতে তাঁর গবেষণার সংক্ষিপ্তসার ছাড়াও বাংলা ভাষার পরিবর্তনের কয়েকটি মূল সূত্র (অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি ইত্যাদি)র আলোচনা তিনি করেছেন। আমরা অন্যত্র এই সূত্রগুলির একটু সংশোধনের সুপারিশ করেছি। তা ছাড়া, তখনকার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীদের জন্য তিনি ‘ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ’ নামে একটি ব্যাকরণ-গ্রন্থও রচনা করেছিলেন, বা বাংলা লিখিত ভাষার একটি বর্ণনামূলক ব্যাকরণ বলা যায়। তাঁর ‘ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা’ বইটি ভারতের ভাষাগুলির রাজনৈতিক ভূমিকা কী হতে পারে তার একটি মনোজ্ঞ আলোচনা। (Suniti Kumar Chatterji)
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগে অধ্যাপনা আর বহুবিধ গ্রন্থরচনা ছাড়াও তিনি আজকাল যাকে ‘পাবলিক ইন্টেলেক্চুয়াল’ বলা হয়, তাও ছিলেন। তিনি রাজনীতিতেও কিছু ভূমিকা পালন করেছিলেন। পশ্চিম বাংলার বিধান পরিষদের অধ্যক্ষ(চেয়ারম্যান) হিসেবে দীর্ঘদিন নিয়োজিত ছিলেন, আবার কেন্দ্রীয় সাহিত্য অকাদেমিরও অধ্যক্ষ ছিলেন বহু বৎসর। এ ক্ষেত্রে তাঁর Languages and Literatures of India বইটি একটি স্থায়ী কীর্তি। (Suniti Kumar Chatterji)
তিনি রাজনীতিতেও কিছু ভূমিকা পালন করেছিলেন। পশ্চিম বাংলার বিধান পরিষদের অধ্যক্ষ(চেয়ারম্যান) হিসেবে দীর্ঘদিন নিয়োজিত ছিলেন
তাঁর অন্যান্য বেশিরভাগ ইংরেজি বাংলা বই শুধু ভাষা নয়, ভাষা ও সংস্কৃতিকে এক সঙ্গে ধরবার চেষ্টা করেছে। Iranianism, Dravidian, The People and Language of Orissa, Africanism—এই সব বই, আর বাংলায় ‘য়োরুবা দেশে’, ‘রবীন্দ্র-সঙ্গমে জাভা ও শ্যামদেশ ভ্রমণ’, ‘পথ চল্তি’ ইত্যাদি একাধিক ভ্রমণকাহিনিতে তাঁর চিত্রকরের(তিনি ভালো ছবি আঁকতে পারতেন) দৃষ্টি বিচিত্র সব দৃশ্যের সূক্ষ্মতা ও বিস্তারকে এমন অনায়সে ধরেছে যে দেখে বিস্মিত হতে হয়। (Suniti Kumar Chatterji)
আরও পড়ুন: বিস্মৃতপ্রায় কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ
১৯৩৬ সালে, আগের বছরে লেখা রবীন্দ্রনাথের অনুরোধপত্রের ভিত্তিতে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বানান সংস্কার সমিতি স্থাপন করেন, তখন সুনীতিকুমার হন তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। তার আগে ১৯১৪ সালে ‘সবুজ পত্র’ পত্রিকার জন্য সুনীতিকুমার একটি বানান-রীতি প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন, এই সমিতি তা সংশোধন করলে সুনীতিকুমার অত্যন্ত উদারচিত্তে তা মেনে নেন। (Suniti Kumar Chatterji)
বিদ্যাক্ষেত্রে কোনও কিছুই চিরস্থায়ী নয়, নিশ্চয়ই সুনীতিকুমারের কোনও কোনও সিদ্ধান্ত নতুন সময় ও তত্ত্বের দ্বারা সংশোধিত হবে। তা সত্ত্বেও তাঁর কাজের বিপুল মহত্ত্ব অম্লান থেকে যাবে। আমরা বিদেশে ভাষাবিজ্ঞানীদের মুখে সুনীতিকুমারকে giant বা দানবীয় প্রতিভা হিসেবে উল্লিখিত হতে শুনেছি। বাঙালিদের মধ্যে এমন বিশ্বন্ধর মনীষী খুব কমই এসেছেন। তাঁর জন্মদিনে তাঁর ছাত্রের ছাত্র হিসেবে আমি তাঁকে আভূমি নত হয়ে প্রণাম নিবেদন করি। (Suniti Kumar Chatterji)
পবিত্র সরকার বাংলা ভাষা ও চর্চার এক প্রতিষ্ঠানস্বরূপ। তাঁর শিক্ষা ও অধ্যাপনার উজ্জ্বল জীবন সম্পর্কে এই সামান্য পরিসরে কিছুই বলা অসম্ভব। তিনি প্রায় চারদশক অধ্যাপনা করেছেন দেশে ও বিদেশে। রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন সাত বছর এবং ছ'বছর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষা সংসদের সহ-সভাপতি। লেখাতেও তিনি অক্লান্ত ও বহুমুখী। ভাষাবিজ্ঞান ও ব্যাকরণ, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব, লোকসংস্কৃতি, ইংরেজি শিক্ষা, রম্যরচনা, শিশুদের জন্য ছড়া গল্প উপন্যাস রবীন্দ্রসংগীত, আত্মজীবনকথা— সব মিলিয়ে তাঁর নিজের বই সত্তরের উপর, সম্পাদিত আরও অনেক। গান তাঁর প্রিয় ব্যসন। এক সময়ে নান্দীকারে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় অভিনয়ও করেছেন।