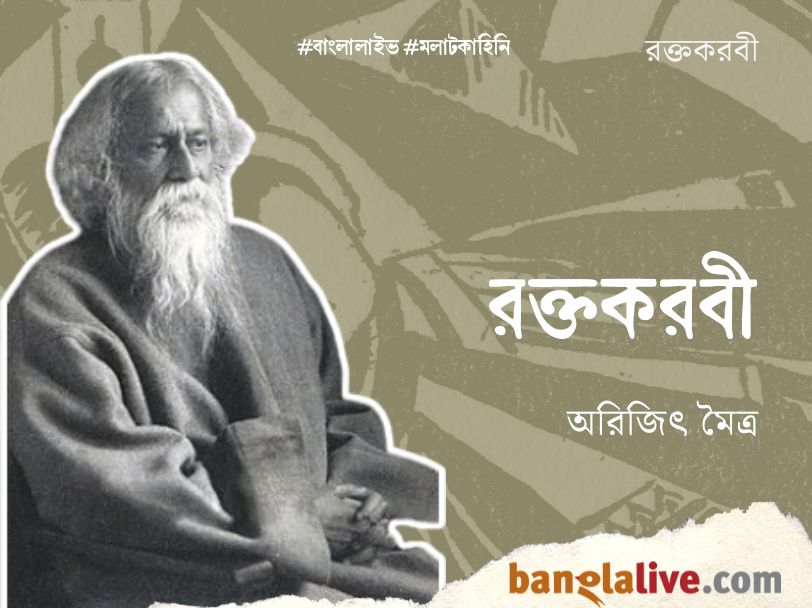(Raktakarabi)
রক্তকরবীর শতবর্ষ উপলক্ষে কবি রচিত এই নাটকটির প্রশংসা করে ধন্য হব, না বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে সমগ্র বিশ্বের অসহিষ্ণু আর ছন্নছাড়া পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাটকের বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা খুঁজব তাই ভাবছি! বছর পাঁচেক আগে বিশ্বব্যাপী মহামারির সময় বুঝতে পেরেছিলাম রাষ্ট্রযন্ত্রের কাছে আমরা সংখ্যা মাত্র। আজকের দিনেও সরকারের কাছে আমাদের অবস্থান মোটেই বদলায়নি বরং একই আছে। যক্ষপুরীর খোদাইকারদের অবস্থাও ছিল আমাদের মতো। মাঝে শুধু সময় বদলেছে কিন্তু রাষ্ট্রীয় শোষণ আর তা প্রয়োগের ধারা একই রয়েছে। পদ্মাপারে থাকাকালীনই কবির কল্পনায় এই নাটক অল্প অল্প করে রূপ পাচ্ছিল। এই নাটক লিখতে গিয়ে প্রায়ই পরিমার্জনা করতে হয়েছে রবীন্দ্রনাথকে। (Raktakarabi)
আরও পড়ুন: রক্তকরবী: বইয়ের শতবর্ষ, নাটকের নয়
রচনার সময় মোট ১১টি খসড়া করতে হয়েছিল তাঁকে! নামও বদলাতে হয়েছে একাধিকবার, প্রথমে, ‘যক্ষপুরী’ তারপর ‘নন্দিনী’ আর শেষে ‘রক্তকরবী’। নাটকটি কবি রচনা করেন প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে। পাশ্চাত্যের দানবীয় যন্ত্রসভ্যতা সেই সময় দ্রুতগামী। শোষকশ্রেণীর লক্ষ মুনাফা বৃদ্ধি আর শোষিত শ্রমিক শ্রেণী অবস্থা বিশুপাগল, ফাগুলালদের মতো। (Raktakarabi)
কিন্তু এসবের নেপথ্যে চালিকাশক্তি কোন অন্ধকারে বসে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, সেটা অজানা! অবস্থা খুব যে একটা বদলায়নি তা আগেই বলেছি। বিশ্বের বিশেষ কয়েকটি শাসকশ্রেণীর মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে সর্দার, গোসাঁই প্রমুখকে। আর সবার ওপরে দন্ডমুন্ডের কর্তা রাজা তো আছেনই। তবে রক্তকরবীর শতবর্ষকে উদযাপন করতে গিয়ে কয়েকজন অর্বাচীন নন্দিনীর মধ্যে, লেডি মুখার্জী অর্থাৎ রানু মুখার্জীকে খোঁজার চেষ্টা করেছেন! অবশ্য রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ বা রাবীন্দ্রিক কোনও বিষয় নিয়ে আলোচনার সময়, কবিকে তাঁরা নারীসঙ্গ থেকে স্বতন্ত্র করে দেখতে পারেন না! (Raktakarabi)
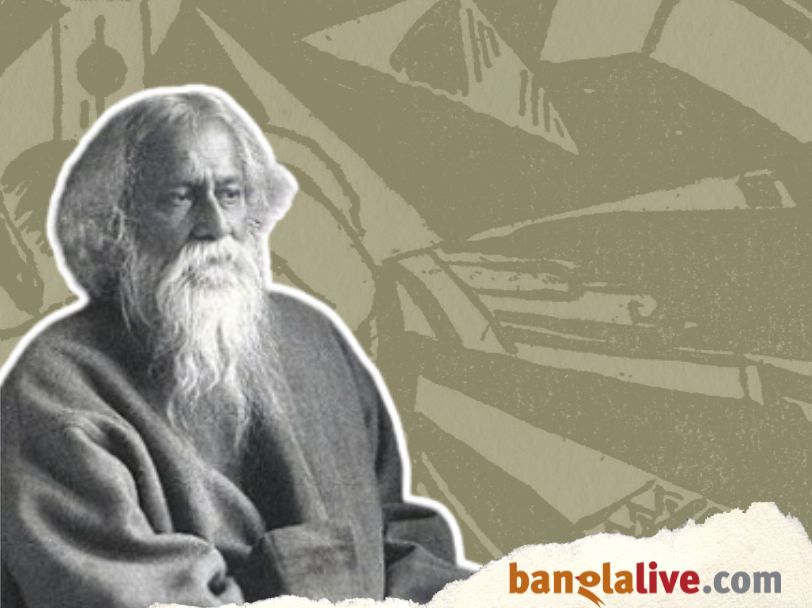
ইয়োরোপের ধোনিক সম্প্রদায় আর তাদের যান্ত্রিক সভ্যতা, জড়বাদের প্রভাব, বৈজ্ঞানিক সুবিধার অপব্যবহার মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে পশুত্বের সমসাময়িক স্তরে নিয়ে গিয়েছিল, তারই একটা স্বচ্ছ চিত্র প্রকাশিত হয়েছে ‘রক্তকরবী’ নাটকে। প্রকৃতির সঙ্গে সুন্দরের যে ছন্দবন্ধন, তা ছিন্ন হয়েছে অনেক আগেই, যত দিন যাচ্ছে, আমরা যান্ত্রিকভাবে উন্নত করছি নিজেদেরকে, ততই সম্পর্ক ছিন্ন হচ্ছে প্রকৃতির সঙ্গে, সহজ সুন্দরের সঙ্গে! আর এই বিশ্বচরাচরের সৌন্দর্য আর মানুষের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটাতে আসা নন্দীনিকেও নাটকের মতো বাস্তবে আমরা সহজ-সরল নিমন্ত্রণকে উপেক্ষা করে কবেই বর্ষার ফলা দিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছি তার কোমলতাকে। মানব সভ্যতার লক্ষ শুধুই মুনাফা অর্জন। (Raktakarabi)
“যান্ত্রিক সভ্যতা, সাম্রাজ্যবাদ এবং বিকৃত জাতীয়তাবোধ যে কীভাবে এবং কতভাবে মানুষকে পাশবিক নিম্নস্তরে নিয়ে যেতে পারে সেটা রবীন্দ্রনাথ মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন যুদ্ধত্তর কালে।”
পাশ্চাত্যের কবিদের মনকেও আচ্ছন্ন করেছিল বিশ্বযুদ্ধের কালোছায়া। পাউন্ড, এলিয়ট, অডেন, ম্যাকলিস প্রমুখের রচনার সঙ্গে রক্তকরবীর বিষয়বস্তুর তুলনামূলক সমালোচনা-হাক্সলির Ape and Essence এবং ও’লিনের The Hairy Ape। রক্তকরবী নাটকে রূপক এবং সংকেতের মিশ্রণ ঘটেছে। (Raktakarabi)
যান্ত্রিক সভ্যতা, সাম্রাজ্যবাদ এবং বিকৃত জাতীয়তাবোধ যে কীভাবে এবং কতভাবে মানুষকে পাশবিক নিম্নস্তরে নিয়ে যেতে পারে সেটা রবীন্দ্রনাথ মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন যুদ্ধত্তর কালে। বিভিন্ন দেশ ও রাষ্ট্রের আচার, ব্যবহার, আচরণ এবং দর্শনে। আত্মঘাতী উন্মত্ততা দেখে মানবতার কবি কলম ধরলেন আর তার ফলে আমরা পেলাম, ‘মুক্তধারা’ ও ‘রক্তকরবী’। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ওদেশের দুটি নাটক George Kaiser-এর ‘Gas’ এবং Karel Capek-এর ‘R. U. R’ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে রচিত Samuel Beckett-র ‘Waitting for Godot’ সম্পর্কে আলোচনা করলে দেখা যাবে ভাবধারার দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের নাটক ‘রক্তকরবীর’ সঙ্গে এই নাটকগুলির অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে। (Raktakarabi)
বিদেশী এইসব নাটকগুলির সম্পর্কে ধারণা থাকলে, ‘রক্তকরবী’-র অন্তর্নিহিত অর্থ বোঝা আরও সহজ হয়ে উঠবে। ‘Waiting for Godot’-এর নায়ক Tramp, প্রতিদিনই তার অপেক্ষায় প্রতিটি মুহূর্ত কাটায়, কিন্তু সে আসে না। তার অপেক্ষায় থাকে আশা আর থাকে ভয়। এই Godot-এর মধ্যে কি আমরা প্রত্যক্ষ করি নন্দিনীর রঞ্জনকে, যার ভালবাসার রঙ রাঙা… (Raktakarabi)
” ‘Red Oleanders’ বই হিসেবে ম্যাকমিলান থেকে প্রকাশিত হয় ১৯২৫ সালের জুন মাসে। তার আগে প্রবাসী ১৩৩১ সালের আশ্বিন এবং বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি ১৯২৪ সালের শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।”
রক্তকরবীর অনুবাদও করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ‘Red Oleanders’ বই হিসেবে ম্যাকমিলান থেকে প্রকাশিত হয় ১৯২৫ সালের জুন মাসে। তার আগে প্রবাসী ১৩৩১ সালের আশ্বিন এবং বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি ১৯২৪ সালের শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। (Raktakarabi)
সংলাপের মাধ্যমে কবি নাটকের বিভিন্ন অংশে রঞ্জনের উপস্থিতির ইঙ্গিত দিলেও নাটকের কোথাও কিন্ত রঞ্জনকে স্বশরীরে প্রকাশ করেননি। একেবারে শেষ পর্বে জালের আড়ালে থাকা রাজার ঘরে মৃত রঞ্জনকে আবিষ্কার করে নন্দিনী। এরপরেই আমরা শুনতে পাই রাজার আর্তনাদ আর আক্ষেপ, ‘আমার সর্বশক্তি দিয়ে যৌবনকে আমি মেরেছি।’ যেখানে যৌবনের অকালমৃত্যু ঘটে, সেখানকার ভবিষ্যৎ যে অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে, এ কথা বলাই বাহুল্য। (Raktakarabi)

অধ্যাপকের ভাষায় নন্দিনী হল যক্ষপুরীর মধ্যে আচমকা আলো। নির্মল প্রকৃতি নন্দিনীর রূপের মধ্যে দিয়ে যক্ষপুরীর সব অন্ধকার দূর করতে চায় কিন্তু সর্দারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, বর্বরতা সবসময় নখদন্ত বিস্তার করে বিভীশিখার আবরণে সব ঢেকে দেয়, কারণ রাষ্ট্রশক্তি মনে করে যন্ত্রের যন্ত্রণা, সবাইকে বিদ্ধ করে, দস্যু বৃত্তির দ্বারা মানবতাকে নিঃশেষ করে দেবে। সর্দার্নিদের ভোজে সাজ নিয়ে যাওয়া এক শ্রমিকের মুখের সংলাপ আজকের পৃথিবীতে ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক! সংলাপটি হল, ‘আমাদের কান দিয়ে যা ঢোকে, মুখে দিয়ে তা বেরোয় না, তাই টিকে আছি।’ (Raktakarabi)
আরও পড়ুন: রক্তকরবী: নব্যপুরাণ রক্তকরবী ও কিছু মেয়েলি ভাবনা
এই সংলাপের মধ্যে বর্তমান সময়ের দেশ এবং রাজ্যের শাসনব্যবস্থার ছবিটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি! রক্তকরবী নাটকে মকররাজ নিজেই স্বীকার করেছেন যে তাঁর মধ্যে আছে জোর আর রঞ্জনের মধ্যে আছে যাদু। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই, যে জোর আর যাদুর মেলবন্ধন কোনওদিনও, কোনওকালে, কোনও দেশেই হয় না! যদি হত তাহলে মেঘমুক্ত আকাশের নীচে মানুষের ভাতৃত্ব আর গঠনমূলক উদ্যোগ দেখা যেত কিন্ত তার বদলে আমরা দেখতে পাচ্ছি রাষ্ট্রশক্তির আস্ফালন, যন্ত্রের শক্তি দিয়ে ক্ষমতা দখল আর দস্যু বৃত্তির মাধ্যমে ধনসঞ্চয় যা মানব কল্যাণে ব্যবহারের পরিবর্তে রাষ্ট্রচালিকার সঙ্গে যুক্ত কতিপয় ব্যক্তির ভোগে ব্যায় করা হচ্ছে। ভাবতে অবাক লাগে যে একশো বছর আগে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে তাঁর দূরদৃষ্টি দিয়ে আজকের পৃথিবীর ছবি এঁকেছিলেন রক্তকরবীতে! (Raktakarabi)
মুদ্রিত ও ডিজিটাল মাধ্যমে সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
অরিজিৎ মৈত্র পেশায় সাংবাদিক। তপন সিংহ ফাউন্ডেশনের সম্পাদক অরিজিৎ পুরনো কলকাতা নিয়ে চর্চা করতে ভালবাসেন। নিয়মিত লেখালিখি করেন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। প্রকাশিত বই: অনুভবে তপন সিনহা, ছায়ালোকের নীরব পথিক বিমল রায়, চিরপথের সঙ্গী - সত্য সাই বাবা, বন্দনা, কাছে রবে ইত্যাদি।