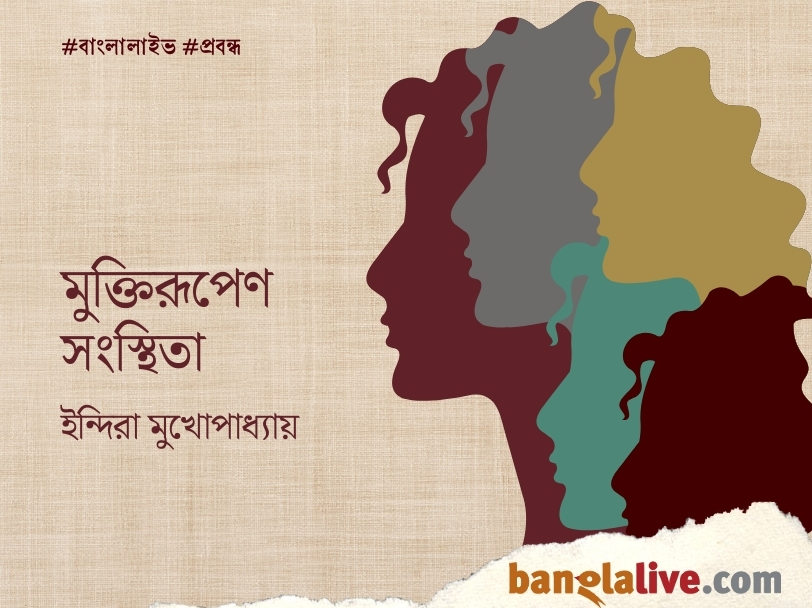(Women’s Day)
প্রাচীন যুগে মৈত্রেয়ী, গার্গী, ঘোষা, অপালা, বিশ্ববারা নামক দার্শনিক বিদুষী কন্যাদের চিনিয়েছে আমার দেশ। স্বাধীন মত প্রকাশের স্বাধিকারে সোচ্চার ছিলেন তাঁরা। মাতৃকাপুজোয় সরব পূর্বসূরিরা সেই আদিকাল থেকেই। মহাভারত আমাদের জানিয়েছে চিত্রাঙ্গদার কথা। পুরাণ বলেছে মনসা, বেহুলার ক্ষমতায়নের গল্প। চন্দ্রকেতুগড়ের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন চিনিয়েছে বাংলার মেয়ে (বধূ) খনাকে। আর আধুনিককালে মানে স্বাধীনতার আশেপাশে বাঙালি মেয়েদের জন্ম এবং বেঁচে থাকা ছিল কঠিন। নারী দিবসের আগে তাঁদের সবাইকে স্মরণ করি আরও একবার। (Women’s Day)
মৈত্রেয়ী ছিলেন প্রাচীন ভারতের বেদের পরবর্তী যুগের একজন দার্শনিক। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ অনুযায়ী, তিনি ছিলেন বৈদিক ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের দুই পত্নীর অন্যতমা। বৈদিক যুগে নারীজাতি যে শিক্ষার সুযোগ লাভ করে দার্শনিক সমাজে খ্যাতি অর্জনে সক্ষম হতেন, তার উদাহরণ মৈত্রেয়ী। ভারতীয় বিদুষীদের অন্যতম প্রতীক। ঋগ্বেদে প্রায় দশটি স্তোত্রের মন্ত্রদ্রষ্টা হিসেবে মৈত্রেয়ীর নাম। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ গ্রন্থের একটি কথোপকথনে হিন্দু দর্শনের আত্মা-সংক্রান্ত ধারণাটির ব্যাখ্যায় ‘মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ’ বিখ্যাত। (Women’s Day)
আরও পড়ুন: শ্রদ্ধাভরে শেষকৃত্য করান ‘শ্মশান বন্ধু’ টুম্পা দাস
উপনিষদের আরেক প্রধান নারী চরিত্র গার্গী। তিনিও বেদজ্ঞ। উপবীত ধারণ করার পাশাপাশি অংশ নিতেন যজ্ঞে। এমনকি অন্যান্য পণ্ডিতদের সঙ্গে শাস্ত্র নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করতেন সমান সুরে। এঁদের সবাইকে বলা হত ব্রহ্মবাদিনী। কীভাবে গার্গীর প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়েছিলেন যাজ্ঞবল্ক্য তাও আছে উপনিষদে। তাঁর অসামান্য ধীশক্তির কাছে পরাজিত হয়ে ঋষি এক সময় বলছেন, আর প্রশ্ন না করতে কারণ, তাঁর মাথা খসে পড়বে। তবে কি নারীর মেধা মনন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করে পুরুষের সাময়িক অস্তিত্ত্ব সংকট উপস্থিত হয়েছিল? (Women’s Day)
বৈদিক যুগের অপরূপা এক নারী ছিলেন অপালা। তাঁর বিদ্যা এবং বুদ্ধির কদর ছিল সর্বত্র। তেমনই ঘোষা, বিশ্ববারা, লোপামুদ্রাও অলঙ্কৃত করেছিলেন ভারতীয় নারীর আসন। দার্শনিক জ্ঞানে টইটুম্বুর সব বৈদিক যুগের নারী। সেসব নারীদের উপর নেমে এসেছে সামাজিক কোপ। (Women’s Day)
আরও পড়ুন: রঙেতে রাঙিয়া রাঙাইলে মোরে
মহাভারতের সেই দীপ্তিময়ী মণিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার কথা তুলে ধরা যাক। কথিত আছে, মণিপুররাজের ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে শিব বর দেন যে তাঁর বংশে কেবল পুত্রই জন্মাবে। তা সত্ত্বেও যখন চিত্রাঙ্গদার জন্ম হল রাজা তাকে পুত্রের মতই পালন করলেন। রাজকন্যা অভ্যাস করলেন ধনুর্বিদ্যা, যুদ্ধনীতি, রাজদন্ডনীতি। দ্বাদশ বৎসর ব্যাপী ব্রহ্মচর্য পালনের সময় দেশ ঘুরতে ঘুরতে অর্জুন তাঁর পাণিগ্রহণ করলেন। তাঁদের সন্তান হল বভ্রূবাহন। এক সময় অর্জুন ফিরে গেলেন তাঁদের ছেড়ে। চিত্রাঙ্গদা কিন্তু দমে যাওয়ার পাত্রী নন। পুরুষের পাশাপাশি মাথা তুলে দাঁড়ানোর জ্বলজ্যান্ত উপমা তিনি। (Women’s Day)
প্রবাদ বলে, স্বভাব যায়না ম’লে। সে যুগেও নারীরা খুব একটা সম্মানজনক কোনও অবস্থানে কিন্তু ছিলেন না। কয়েকজন বিদুষীর অবস্থান দেখিয়ে সমাজের সামগ্রিক অবস্থাটা বোঝা কখনওই সম্ভব নয়। প্রাবন্ধিক সুকুমারী ভট্টাচার্যের গবেষণার পরতে পরতে উন্মোচিত হয় প্রাচীন ভারতে নারীর ক্রমাগত অবদমনের ইতিবৃত্ত। আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকা শৃঙ্খলকে খুলতে চেয়েছেন বারবার।
সে যুগেও নারীরা খুব একটা সম্মানজনক কোনও অবস্থানে কিন্তু ছিলেন না। কয়েকজন বিদুষীর অবস্থান দেখিয়ে সমাজের সামগ্রিক অবস্থাটা বোঝা কখনওই সম্ভব নয়।
সেই আদিমতম শক্তিই বুঝি প্রকৃতি বা ধরিত্রী, ধাত্রীমাতা বা সর্বজনীন মাতৃশক্তি। প্রাচ্যই হোক বা পাশ্চাত্য সবখানেই মানুষের আদ্যিকালের বিশ্বাসেই বুঝি নারীশক্তির আরাধনা, উপাসনা এবং উত্থান। বারেবারে ধরিত্রী রূপিণী মাতার কাছে সারা বিশ্বের মানুষ তাই আজও নতজানু। এখনও বৃক্ষ, কাষ্ঠ, শিলাখন্ড, স্তূপ, মূর্তি, দেউল…এসব কল্পনায় মূর্ত হয়ে ওঠেন নারীশক্তিরা। কখনো তাঁর প্রকাশ শস্য বা কৃষিদেবী রূপে। কখনও প্রজননের দেবী ষষ্ঠী বা Fertility Cult রূপে। কখনও আবার কেবলি পৃথিবী-মাতা রূপে। (Women’s Day)
আমাদের দুর্গার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় পাশ্চাত্যের Earth Goddess Demeter কিম্বা অন্নপূর্ণার সঙ্গে মিল পাওয়া যায় মিশরের আইসিস ও গ্রীসের সিরিস দেবীর। আমাদের বাসন্তী দুর্গার সঙ্গে মিল পাই সেদেশের ইস্তারা দেবীর। যিনি একাধারে ওয়াইন গডেস অন্যদিকে রণের দেবী। ব্যাবিলনের নীনা বা ননাকেই বা ভুলি কেমনে? তিনিও তো সিংহবাহিনী দুর্গার অনুরূপ। আসলে সব নারীশক্তিই স্থান কাল পাত্রভেদে সেই জনজাতিকে খাইয়ে পরিয়ে, আদরে বাঁচিয়ে রাখেন, সন্তান দেন, প্রকৃতি গড়েন… তাই তিনিই আমাদের শস্যের অধিষ্ঠাত্রী Corn Goddess বা Vegetable Spirit শাকম্ভরী মা দুর্গা। (Women’s Day)
আরও পড়ুন: নীরবে নিতান্ত অবনত বসন্তের সর্ব-সমর্পণ।
প্রাচীন ভারতে নারীর এই অবনমন সবথেকে বেশি মাত্রায় তুলে ধরে ‘চাণক্য নীতি’। কিন্তু বদল ঘটে যুগের। “নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার। কেন নাহি দিবে অধিকার, হে বিধাতা?” বাংলায় ঠাকুরবাড়ির মেয়েরাই এগিয়ে চলেছিলেন একসময় আলোকবর্তিকা হয়ে। সে যেন এক অন্য নবজাগরণের ঢেউ এসেছিল বাংলায়। সেসময়টা ছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে বিংশ শতাব্দীর শুরু। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে কলাকৃষ্টি, শিল্প সাহিত্য, সঙ্গীত, ছবি আঁকার পাশাপাশি নাট্যচর্চার জোয়ার। ঠাকুরবাড়ির ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরাও সমান তালে উদ্যমী হয়ে পড়েন। রক্ষণশীলতার বেড়াজাল ডিঙিয়ে স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারে, প্রচারের আলোয় তাঁরাও হয়ে ওঠেন আলোকিত। ঠাকুর পরিবারে উন্মেষ ঘটতে শুরু করেছিল নারী ও পুরুষের প্রতিভা। (Women’s Day)
কিন্তু তবুও কোথায় ছিল মেয়েদের গলদ। এগিয়ে চলার পথে অন্তরায়। ‘লীলাবতীর নবদুর্গা’ লিখতে গিয়ে আমি দেখেছি একজন মেয়েকে পুরুষশাসিত সমাজের চাপা দেওয়ার কথা, আড়াল করার কথা। একদিকে পদার্থবিদ বিভা চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার ইলা মজুমদার ও প্রথম বাঙালি চিকিৎসক কাদম্বিনী গাঙ্গুলির কাঁধে এসে পড়েছে সামাজিক দায়ভার, অন্যদিকে জিন বিজ্ঞানী মহারাণী চক্রবর্তী বা মলিকিউলার বায়োলজিস্ট অর্চনা শর্মা’কে তাঁদের প্রথিতযশা স্বামীরা এগিয়ে দিয়েছেন আলোর দিকে। (Women’s Day)
জিন বিজ্ঞানী মহারাণী চক্রবর্তী বা মলিকিউলার বায়োলজিস্ট অর্চনা শর্মা’কে তাঁদের প্রথিতযশা স্বামীরা এগিয়ে দিয়েছেন আলোর দিকে।
বাংলার প্রথম ভূ-তাত্ত্বিক সুদীপ্তা সেনগুপ্ত’র স্বরচিত গ্রন্থ থেকে জানা যায়, তাঁর রন্টি অভিযান কালে হিমালয়ের ললনা শৃঙ্গ জয় করতে যাওয়ার সময় সরকারী ছাড়পত্র পেতে বেগ পেতে হয়েছে, অন্যদিকে অ্যান্টার্কটিকা অভিযানে পুরুষ সহযাত্রীদের মুখে শুনতে হয়েছে বক্রোক্তি। তাঁবুর মধ্যে সেই শীতলতম প্রতিকূল আবহাওয়ায় মেয়েরা সংখ্যাগুরু বলে পুরুষেরা “অ্যান্টার্কটিকায় এবার বিউটি পার্লার খোলা হবে” বলে দাগিয়েছেন। শুধু তাই নয়, ভালোমন্দ সুখাদ্য রেঁধে খাওয়ানোর বায়না জানিয়েছেন… (Women’s Day)
উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বাংলার মেয়েরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পেলেও তাদের বিজ্ঞান পড়ার অনুমতি ছিল না। বাঙালি মেয়েরা বিজ্ঞান পড়ে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হবে? কিন্তু অবগুন্ঠনা বাঙালি নারী বিজ্ঞানচর্চায় মেতে উঠে পুরুষের চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিলেন বটে। কারণ উনিশ শতক আর বিশ শতকে সে যেন ছিল যেন এক অলীক কল্পনা। ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেন পরামর্শ দিয়েছিলেন, মেয়েদের বিজ্ঞান পড়ার দরকার নেই। (Women’s Day)
শুধু ভারতীয় বিজ্ঞান কেন? বিশ্বের আনাচে-কানাচে এমন ঘটনাও ঘটেছে। আন্তর্জাতিক নারীদিবসে সেসব মনে পড়ে যায় বৈকি।
যদিও কিছুটা বিতর্কিত তবুও অনেকেই বলেন যে আইনস্টাইনের প্রথম পত্নী, Mileva Einstein-Maric তাঁর প্রথম জীবনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ পেপারগুলি লিখতে সাহায্য করেছিলেন । আইনস্টাইন প্রাথমিক ভাবে পদার্থ বিজ্ঞানী ছিলেন, অঙ্কের দিকটা তাঁর স্ত্রী করে দিতেন কিন্তু তিনি কোনওদিন সেভাবে স্বামীর আলোচনায় উঠে আসেননি। বরং নেপথ্যের নায়িকাই থেকে গেছেন।
ঠিক সেই ভাবেই ওয়াটসন এবং ক্রিক এই দুই সাহেব ডিএনএ-র ডাবল হেলিক্স আবিস্কার করার জন্য নোবেল প্রাইজ পান কিন্তু যে বিখ্যাত ‘ফোটোগ্রাফ ৫১’ ছবিটি তুলে Rosalind Franklin নামের সেই মহিলা বিজ্ঞানী প্রথম এই হেলিকাল স্ট্রাকচার জনসমক্ষে তুলে ধরেন তাঁর কথা সবাই ভুলে গেছেন। (Women’s Day)
আরও পড়ুন: রবীন্দ্রনাথের কবিচেতনায় লক্ষ্মী ও সরস্বতীর দ্বন্দ্ব…
‘লীলাবতীর নবদুর্গা’ গ্রন্থে উল্লিখিতি এমন ন’জন বাঙালি মেয়ে বিজ্ঞানীর মধ্যে সবার চলার পথ খুব মসৃণ ছিল না। মেধা, মনন, সাধনার সাফল্যের যথোচিত আলো তাদের কয়েকজনের মুখে বিশেষ পড়েনি, বরং সে আলো কেড়ে নিয়েছিল সমকালের পুরুষ-শাসিত সমাজ। মেয়েদের বিজ্ঞান সাধনার ইতিহাস বরাবরই বড় করুণ। একুশ শতকের মেয়ে বিজ্ঞানীরা সেদিক থেকে আশীর্বাদধন্যা। গবেষণার জন্য সে সুযোগ পাননি তাদের পূর্ব-মাতৃকারা। কয়েক দশক আগে, মহাকাশে কয়েক আলোকবর্ষ দূরের নক্ষত্র নামেই পরিচিত হওয়ার আগে পর্যন্ত বাংলার বহু মানুষই জানত না কে এই বিভা চৌধুরী? চিনত না প্রথম বাঙালি মেয়ে প্রকৌশলী ইলা মজুমদারের সংগ্রামের কথা।
একবার এক কাগজে বেরোলো পরনে পুরুষের পোষাক পরিহিতা ও সিগার ধূমপানরতা ডঃ কাদম্বিনী গাঙ্গুলির কার্টুন সম্বলিত হাস্যকর ছবি। যশ ও খ্যাতির শিখরে থাকা কাদম্বিনীকে কুড়োতে হয়েছিল ‘ধাইমানি’ খেতাব। ‘unclean midwife’ তকমাও জুটেছিল কপালে। অত পড়াশোনার পর ডাক্তার আর মিডওয়াইফ-কে একই আসনে বসানো হয়েছিল। এসবে অবিশ্যি কান দেননি তিনি বরং এসব কানাঘুষো এক ফুঁৎকারে উড়িয়ে দিয়েই কাদম্বিনী এগিয়ে চলেছিলেন নিজের লক্ষ্যে।
কয়েক আলোকবর্ষ দূরের নক্ষত্র নামেই পরিচিত হওয়ার আগে পর্যন্ত বাংলার বহু মানুষই জানত না কে এই বিভা চৌধুরী?
কিন্তু এসব নারীর জন্ম স্বাধীনতার আগে বা আশেপাশে। যুগ বদলেছে। যুগের ধর্ম বদলেছে। এখন নারীর ক্ষমতায়নের প্রকাশ তার কাজে, প্রতিবাদের ভাষায়, অধিকার কায়েম করায়। রবিঠাকুরের কথায় বলতে ইচ্ছে করে…
“সে কি রহিল লুপ্ত আজি সব জন পশ্চাতে? লউক বিশ্ব কর্মভার মিলি সবার সাথে।
নূতন যুগ সূর্য উঠিল, ছুটিল তিমির রাত্রি তব মন্দির অঙ্গন ভরি মিলিল সকল যাত্রী।।’’
তবে সমাজের পরিস্থিতি আজ অনেকটাই বদলেছে। লিঙ্গ বৈষম্য ভুলে আকাশের বাকী অর্দ্ধেকটা থেকে উড়ে যাচ্ছে সামিয়ানা। চাঁদের আলো পড়ছে আজ অন্ধকার আচ্ছন্ন বাকী অর্ধেক আকাশের গায়ে। এর নামই বুঝি উওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট। আমার নারী তার সম্পূর্ণ আকাশ জয় করে নিয়েছে আজ পুরুষের পাশাপাশি। (Women’s Day)
“নারী, তুমি নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী হে নন্দনবাসিনী উর্বশী”
“সুমঙ্গলী বধূ, সঞ্চিত রেখো প্রাণে স্নেহমধু। সত্য রহো তুমি প্রেমে, ধ্রুব রহো ক্ষেমে, দুঃখে সুখে শান্ত রহো হাস্যমুখে”
কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা যেন দৃপ্ত ভঙ্গীমায় নারীর ক্ষমতায়নের আয়না। নারীকে তিনি জ্বালাময়ী আগুনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। গানের কথায় বারেবারে প্রজ্জ্বলিত হয়েছে সেই বহ্নিশিখা স্বরূপিণী নারীশক্তির দীপ্তি। আর তাইতো ললাটে রক্ততিলক এঁকে সে দমন করার চেষ্টায় থাকে যা কিছু অশুভ, মন্দ, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে। অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যায়। শান্তির দূত হয়ে। আলোকবর্তিকা হয়ে। আজ নারীশক্তির জাগরণ অত্যন্ত জরুরী আর কল্যাণকর সমাজের পক্ষে। তার নিজস্ব মত প্রকাশ ও বিনিময়ের অধিকারের স্বাধীনতায় সে সরব থাক। “জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা! জাগো স্বাহা সীমন্তে রক্ত টীকা”।
রমণী বা যে শুধুই রমণ করে বা মহিলা যে শুধুই অন্দরমহলে থাকে তেমন সংজ্ঞা বদলে যাক। আজ নারী হয়ে উঠুক মুক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
সবখানেই স্থান, কাল, পাত্র ভেদে নারী ও পুরুষের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকবে। নিজেকেই জয় করে নিতে হবে যোগ্য সম্মান এবং অধিকার। সে তার কর্মস্থানেই হোক বা সংসারে। বাক স্বাধীনতায় নারীর জয় হোক। বিদ্যায়, শিক্ষায়, জ্ঞানলাভে তার জয় হোক। কন্যারূপেণ, মাতৃরূপেণ, বধূরূপেণ ছাড়াও স্বীকৃতি লাভ হোক কর্মের মাধ্যমে। স্বেচ্ছাচারিতায় নারী মুক্তি হয় না। আমার নারীর মুক্তি হোক সৎ কর্মরূপে। রমণী বা যে শুধুই রমণ করে বা মহিলা যে শুধুই অন্দরমহলে থাকে তেমন সংজ্ঞা বদলে যাক। আজ নারী হয়ে উঠুক মুক্তিরূপেণ সংস্থিতা। (Women’s Day)
রসায়নের ছাত্রী ইন্দিরা আদ্যোপান্ত হোমমেকার। তবে গত এক দশকেরও বেশি সময় যাবৎ সাহিত্যচর্চা করছেন নিয়মিত। প্রথম গল্প দেশ পত্রিকায় এবং প্রথম উপন্যাস সানন্দায় প্রকাশিত হয়। বেশ কিছু বইও প্রকাশিত হয়েছে ইতিমধ্যেই। সব নামীদামি পত্রিকা এবং ই-ম্যাগাজিনে নিয়মিত লেখেন ছোটগল্প, ভ্রমণকাহিনি, রম্যরচনা ও প্রবন্ধ।