পল্টু বলতে শুরু করল।
“তোরা তো সব্বাই আইনস্টাইনের রিলেটিভিটির কথা শুনেইছিস। আর তার মধ্যে দুটো ব্যাপার সম্পর্কে সবাই মোটামুটি অবগত।
এক E=mc2, অর্থাৎ মাস আর এনার্জির সমতা বা ইকিউভ্যালেন্স আর কনজারভেশন।
দুই কোনও জাগতিক বা মহাজাগতিক বস্তুর পক্ষে আলোর গতিতে চলা বা তাকে অতিক্রম করা সম্ভব নয়। (Bengali Story)
আরও পড়ুন: অদৃশ্য জগৎ: পর্ব – ১
কিন্তু আরও অনেক কিছুর সাথে আইনস্টাইন আরেকটা সাংঘাতিক কথা বলেন যে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স বা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বলে কিছু নেই। আসলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি একটা স্পেস-টাইমের ফ্যাব্রিক বা চাদর যা আমাদের মহাবিশ্বে ছড়িয়ে আছে আর তার উপরেই সব গ্রহ নক্ষত্রেরা বড় নক্ষত্রের টানে একে অন্যের থেকে ফিক্সড দূরত্ব বজায় রেখে ঘুরছে। নিউটন ভেবেছিলেন মহাবিশ্বে যে ভ্যাকিউম আছে তা ইথার দিয়ে ভরা। গ্রহ নক্ষত্রদের নিজেদের মধ্যেকার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সেই ইথারের মাধ্যমেই প্রবাহিত হয়। আইনস্টাইন বললেন ওসব ইথার টিথার কিছু না। এটা আসলে স্পেস-টাইমের একটা ফ্যাব্রিক বা চাদর। যার ওপরে বিভিন্ন ভরের গ্রহ নক্ষত্রেরা নিজের নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে বনবন করে ঘুরছে। এটা বলে উনি কিন্তু নিউটনের ইকোয়েশনকে বাতিল করেননি। শুধু বলেছেন নিউটনের থিওরির একটা লিমিটেশন আছে, যেটা পদার্থের ভর আর গতিতে সীমিত। আইনস্ট্যাইনের ইকোয়েশনে ভর আর গতি কমিয়ে দিলে তা একদম নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির তত্ত্ব মেনে চলে।” পল্টু এতটা বলে একটু থেমে একটা সিগারেট ধরাল, সাথে কাজলও।
সবাই চুপ। কারুর মুখে কোনও কথা নেই। চারপাশে শুধু ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক আর নদীর বয়ে চলার আওয়াজ।
কাজল একটু আড় ভেঙে বলল চল এবারে বাড়ি যাওয়া যাক।
সবাই চুপ। কারুর মুখে কোনও কথা নেই। চারপাশে শুধু ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক আর নদীর বয়ে চলার আওয়াজ।
কাজল একটু আড় ভেঙে বলল “চল এবারে বাড়ি যাওয়া যাক। আর মাথায় ঢুকছে না। নটা তো বাজেই! রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পরে আবার বসা যাবে।” এই বলে কাজল উঠে দাঁড়াল।
“দাঁড়া সিগারেটটা শেষ করি।” পল্টু উঠে বলল।
আরও পড়ুন: অদৃশ্য জগৎ: পর্ব – ২
শম্পা কিন্তু দারুণ রেঁধেছে। যেমন পোলাও তেমনিই মাংস। শেষে আবার কাঁচা আমের চাটনি। সব মিলিয়ে দারুণ খাওয়াদাওয়া হল। কাজল রিভু সবাই শম্পাকে বারে বারে থ্যাঙ্কিউ বলাতে পল্টু, বিল্টুও আর থ্যাঙ্কিউ না বলে পারল না।
খাওয়াদাওয়া সেরে রিভু, পল্টু, কাজল আর বিল্টু ছাদে গিয়ে বসল। রিভুর তো আর তর সইছিল না।
“পল্টুমামা তারপরে বলো কী হল!”
“হ্যাঁ কোথায় ছিলাম আমরা?” পল্টু জিজ্ঞাসা করল।
“ওই যে! আইনস্টাইনের নানান আবিস্কারের কথা!” রিভু ঝটপট জানিয়ে দেয়।
“রাইট!” পল্টু বলতে শুরু করে।
“আইনস্টাইন তাঁর জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটির ফিল্ড ইকোয়েশন ডিরাইভ করার সময় একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেন। তিনি দেখেন তাঁর ফিল্ড ইকুয়েশন স্ট্যাটিক ইউনিভার্সের কথা না বলে ইউনিভার্সের এক্সপ্যানশন বা সম্প্রসারণের কথা বলছে। যেটা আইনস্টাইন কিছুতেই মানতে পারছিলেন না। কারণ ওঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ইউনিভার্স স্ট্যাটিক এবং ফাইনাইট। তাই নিজের যুক্তি কায়েম করতেই ইউনিভার্সের এই সম্প্রসারণকে কাউন্টার করতে ওঁর জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটির ফিল্ড ইকুয়েশনে একটা কনস্ট্যান্ট (ফোর্স) জুড়ে দেন ল্যাম্বডা। এই ল্যাম্বডা জুড়ে অঙ্কে, আইনস্টাইন প্রমাণ করেন যে ওঁর প্রস্তাবিত ফিল্ড ইকুয়েশনে মহাবিশ্ব স্ট্যাটিক এবং ফাইনাইট! কিন্তু প্রশ্ন উঠতে থাকে মহাবিশ্ব যদি ফাইনাইটই হয় তাহলে তার বাউন্ডারির ওপারে কি আছে স্বর্গ না নরক?
এটা ছিল ১৯১৭ সালের ঘটনা।
বিজ্ঞানীদের মধ্যে তখন মহাবিশ্ব ফাইনাইট না ইনফাইনাইট এই নিয়ে প্রচন্ড বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। বিজ্ঞানীদের বক্তব্য ছিল অঙ্ক যদি বলেই দেয় মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে তাকে জোর করে আটকানোর কী দরকার।
বিজ্ঞানীদের মধ্যে তখন মহাবিশ্ব ফাইনাইট না ইনফাইনাইট এই নিয়ে প্রচন্ড বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। বিজ্ঞানীদের বক্তব্য ছিল অঙ্ক যদি বলেই দেয় মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে তাকে জোর করে আটকানোর কী দরকার। এইটুকু বলে পল্টু থামল।
এতক্ষণে কাজল মুখ খুলল “শুনেছি আইনস্টাইনের স্পেশাল আর জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি এতই কঠিন ছিল যে ১৯২১ সালে আইনস্টাইন ১৯০৫ সালের প্রকাশিত ফটো ইলেক্ট্রিক ইকুইয়েশনের জন্যে নোবেল পান। যদিও ১৯০৫ সালে স্পেশাল থিওরি অব রিলেটিভিটি আর ১৯১৫ সালে জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটি প্রকাশিত হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, শুনেছি ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী আর্থার এডিংটন পূর্ণ সূর্যগ্রহনের সময় আইনস্টাইনের এই কথাও প্রমাণ করে দেন যে লাইট সত্যিই সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে বেঁকে যায়।”
“তুই ঠিকই শুনেছিস কাজল। আসলে আইনস্টাইন তাঁর সমকালীন সব বিজ্ঞানীদের থেকে এতটাই এগিয়ে ছিলেন যে বাকিদের আইনস্টাইনকে বোঝা বেশ কঠিন ছিল। যেমন আইনস্টাইনের স্পেশাল থিওরি অব রিলেটিভিটি প্রথমে একমাত্র ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ছাড়া আর কেউই বোঝেননি।
যেমন আইনস্টাইনের নিজের প্রস্তাবিত কসমোলজিক্যাল কনস্ট্যান্ট বা ল্যাম্বডা।”
“কী এই ল্যাম্বডা? যদি একটু বুঝিয়ে বলো!” বিভু জানতে চাইল।
“এই ল্যান্বডা অর্থ্যাৎ কসমোলজিক্যাল কনস্ট্যান্ট ব্যাপারটা কিন্তু বেশ ইন্টারেস্টিং। ১৯১৭ সালে আইনস্টাইন এই ল্যাম্বডার কথা বলার পর তা নিয়ে বিশ্ব জুড়ে জোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে তোলপার শুরু হয়ে যায়। অনেকেই উঠে পড়ে লাগে এটাকে ভুল প্রমাণ করতে।
জ্যোতির্বিজ্ঞানি আলেক্সান্ডার ফ্রিডম্যান, কার্ল উইলহেম উইর্ডজ এমনকি বেলজিয়ামের এক ক্যাথোলিক পাদ্রি পদার্থবিদ জর্জেস লেমাইত্রে এরা সবাই আলাদা আলাদাভাবে অঙ্ক কষে প্রমাণ করেন যে সত্যিই মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে। এটা ঘটে ১৯২২ থেকে ১৯২৭’এর মধ্যে। লেমাইত্রে আবার আইনস্টাইনকে এই নিয়ে একটা চিঠিও লেখেন। লেমাইত্রের সেই চিঠি পেয়ে আইনস্টাইন তো বেজায় খেপে যান। চিঠির উত্তরে উনি লেমাইত্রকে বলেই ফ্যালেন যে ‘শোনো ভায়া!
অঙ্কটা তোমার সঠিক হলেও ফিজিক্সে তুমি বড়ই কাঁচা।’ পল্টু থামল।
“কিন্তু আইনস্টাইন মানছিলেনই বা কেন পল্টুমামা?”
আরও পড়ুন: কুট্টিদাদুর মিস্ট্রি : অরূপ দাশগুপ্ত
“ওটাই তো আত্মবিশ্বাস। নিজের অঙ্ককে আইনস্টাইন সাংঘাতিক ভরসা করতেন। সেইখান থেকেই এই গোঁয়ার্তুমিও বলতে পারিস। আইনস্টাইনের অঙ্ক ল্যাম্বডার প্রয়োজনিয়তা ঠিকঠাক চিহ্নিত করেছিলেন কিন্তু কারণটা ঠিক ধরতে পারেননি।
লেমাইত্রেও দমবার পাত্র নন। ১৯২৭ সালে প্রথমে নিজে আর ১৯২৯ সালে এডউইন হাবল দূরবিন দিয়ে দেখে এই সম্প্রসারণের কথা প্রমাণ করার পর হাবলের সাথে বিখ্যাত হাবল-লেমাইত্রের তত্ত্ব প্রকাশিত করেন। দুজনে মিলে দেখান যে গ্যালাক্সিরা নিজেরা সম্প্রসারিত না হলেও তাদের নিজেদের মধ্যের দূরত্ব বাড়ছে। আর এও বলেন যে আমাদের থেকে কোনও গ্যালাক্সি যত দূরে সে তত দ্রুত দূরে সরে যাচ্ছে। এই দূরত্বের সঙ্গে দ্রুততার সম্পর্ককেই হাবল-লেমাইত্রে সূত্র বলে। তবে এই সরে যাওয়াটা তখন ঘটে যখন ইন্টারগ্যালাক্টিক স্পেসে কোনও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব থাকে না।
এইসব ঘটনা ঘটাতে প্রবল অনিচ্ছা স্বত্বেও আইনস্টাইন আস্তে আস্তে নরম হন এবং মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের কথা মেনে নিয়ে ফিল্ড ইকোয়েশন থেকে ল্যাম্বডা বাদও দিয়ে দেন।”
“তাহলে আইনস্টাইন যদি ওই ল্যাম্বডা কনস্ট্যান্টটা না জুড়তেন সেক্ষেত্রে হাবলের আগেই উনি জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটিতেই এই সম্প্রসারণের কথা বলতে পারতেন! আচ্ছা পল্টুমামা এখন তো এই কসমোলজিক্যাল কনস্ট্যান্টও ওয়েল অ্যাক্সেপটেড তাই না!”
“তাই তো! কসমোলজিক্যাল কনস্ট্যান্ট ল্যাম্বডাই তো এখন মহাকাশ বিজ্ঞানে এক নতুন দিক খুলে দিয়েছে।”
“আচ্ছা পল্টুমামা এটা কি ঠিক যে এই কসমোলজিক্যাল কনস্ট্যান্ট ল্যাম্বডা ঘাটতে গিয়েই বিজ্ঞানীরা ডার্ক এনার্জি আর ডার্ক ম্যাটারের খোঁজ পেয়েছে!”
জোতির্বিজ্ঞানীদের মাথায় প্রথম সংশয় জাগল কোনও ফোর্স ছাড়া এই অ্যাক্সিল্যারেশন সম্ভব হচ্ছে কীভাবে। যদি এই অ্যাক্সিল্যারেশন সত্যি হয় তাহলে তো গ্যালাক্সিদের একে অন্যের থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে নিজেদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আওতার বাইরে চলে যাবে!
“কিছুটা তো বটেই! আসলে আইনস্টাইনের মৃত্যুর বহু বছর পর ১৯৯৮ সাল নাগাদ জোতির্বিজ্ঞানী সল পেরিমাটারের টিম আর ব্রায়ান স্কিম্ডটের টিম আলাদা আলাদা ভাবে সুপারনোভার কসমিক সিগন্যাল এ্যানালাইসিস করে দেখেন যে মহাবিশ্ব শুধুই যে সম্প্রসারিত হচ্ছে তা নয়, সাথে সাথে এই সম্প্রসারণ তরান্বিতও হচ্ছে। আর এতেই হয়ে গেল মুশকিল।
জোতির্বিজ্ঞানীদের মাথায় প্রথম সংশয় জাগল কোনও ফোর্স ছাড়া এই অ্যাক্সিল্যারেশন সম্ভব হচ্ছে কীভাবে। যদি এই অ্যাক্সিল্যারেশন সত্যি হয় তাহলে তো গ্যালাক্সিদের একে অন্যের থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে নিজেদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আওতার বাইরে চলে যাবে!” পল্টু থামল।
“সম্প্রসারণ হচ্ছে বলেই কি ১৩৮০ কোটি আলোকবর্ষ দূরের রেডিয়েশন এখন ৪৫০০ কোটি আলোকবর্ষ দূর থেকে আসছে?” বিভু জিজ্ঞাসা করল।
“ঠিক! আর এইজন্যেই মহাবিশ্বের এই অ্যাক্সিল্যারেটেড এক্সপ্যানশনকে জাস্টিফাই করতে বিজ্ঞানীরা আবার ল্যাম্বডাকেই যথাস্থানে ফিরিয়ে আনলেন।
ল্যাম্বডার একটা পজিটিভ ভ্যালু বসিয়ে দেখা গেল, ফিল্ড ইকোয়েশনে এই অ্যাক্সিল্যারেটেড এক্সপ্যানশনটা ব্যালেন্সড হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা এই ফোর্সের উৎস যে এনার্জি তাকে কোনওভাবেই ধরতে বা বুঝতে না পেরে নাম দিলেন ডার্ক এনার্জি। আমরা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যেসব এনার্জির প্রমাণ পাই এটা তার বাইরে।”
“তার মানে গ্র্যাভিটি যেখানে মহাজাগতিক বস্তুদের কাছে ধরে রাখছে সেখানেই এই ডার্ক এনার্জি তাদেরকে একে অন্যের থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।” পল্টু একটা সিগারেট ধরাল।
“তারমানে মহাবিশ্বের অ্যাক্সিল্যারেটেড এক্সপ্যানশনটা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আর ডার্ক এনার্জির মধ্যে একটা টাগ-অফ-ওয়ার! তাই না বলো পল্টুমামা!”
“তা ঠিক। কিন্তু এই রেট অফ এক্সপ্যানশনটা এতটাই স্লো যে গ্যালাক্সিরা প্রতি মিলিয়ন বছরে জাস্ট 0.007% দূরে সরছে। তাই এই চেঞ্জের এফেক্ট বোঝার আগে শুধু আমরা না পুরো মানব সভ্যতাই হয়তো হাওয়া হয়ে যাবে। অথচ এই ডার্ক এনার্জি মহাবিশ্বের সব ম্যাটার-এনার্জির ৬৮.৩%। আর এনার্জি সমস্ত মহাবিশ্বে সব জায়গায় ইভেনলি ডিস্ট্রিবিউটেড।” পল্টু থামল।
আরও পড়ুন: ফেসবুকের বেড়াল : সৌরভ হাওলাদার
“সেক্ষেত্রে তাহলে বাকি ৩২% আমাদের সব অবসার্ভেবল ম্যাটার আর এনার্জি?” রিভু জিজ্ঞাসা করল।
“ইয়েস অর নো! এই ৩২%’এর মধ্যে গ্র্যাভিটেশনাল এনার্জি, ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক এনার্জি আর নিউক্লিয়ার স্ট্রং আর উইক ফোর্স আর তার সাথে সব গ্রহ নক্ষত্র গ্যাস বা অন্যান্য দৃশ্যমান ম্যাটার মিলিয়ে যা হয় তা কেবল ৪.৭%।” পল্টু থামল।
“এ্যাঁ! কি বলছ পল্টুমামা! তাহলে বাকি ২৭%ই ডার্ক ম্যাটার?” রিভুরা তো অবাক।
“এই ডার্ক ম্যাটার বস্তুটা কি একটু বলবে পল্টুমামা?”
“তাহলে শোন!” পল্টু বলতে শুরু করল।
“ডার্ক ম্যাটার নিয়ে প্রথম সন্দেহ প্রকাশ করেন লর্ড কেলভিন ১৮৮৪ সাল নাগাদ। উনি অবশ্য সরাসরি ডার্ক ম্যাটারের কথাটা বলেননি। উনি সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যে আমাদের সূর্যের মতো হয়তো আরও অনেক নক্ষত্র আছে যা দৃশ্যমান নয়। অবশেষে ১৯৩৩ সালে ফ্রিৎজ জুইকি প্রথম গ্যালাক্সির শেষপ্রান্তে গ্রহ নক্ষত্রদের ঘোরার বেগ থেকে বুঝতে পারেন দৃশ্যমান গ্রহ নক্ষত্রের জন্যে যতটা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হওয়া উচিত আর তার জন্যে গ্যালাক্সির শেষপ্রান্তের গ্রহ নক্ষত্রদের যে বেগে ঘোরা উচিত তার থেকে বেশি বেগে ঘুড়ছে। অর্থাৎ ওই গ্যালাক্সিতে দৃশ্যমান পদার্থকে ধরে রাখার জন্যে যে পরিমান মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রয়োজন তার থেকে অনেক বেশি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বর্তমান।”
তার মানে এই এক্সট্রা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কাজ করছে কোনও অদৃশ্য পদার্থের উপরে। যা কিনা ওই ডার্ক ম্যাটার!” রিভু বলল।
“হয়তো! আমরা কিন্তু এই ডার্ক ম্যাটার সম্পর্কে কিছুই জানি না। আমরা এদের দেখতেও পাই না আর অনুভবও করতে পারি না। কারণ এরা গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড ছাড়া আর কোনও জানা ফিল্ড বা ম্যাটারের সাথে ইন্টারাক্ট করে না, এমন কি লাইটের সাথেও না। ফ্রিৎজ জুইকি এই পদার্থের নাম দেন ডাঙ্কল ম্যাটেরি বা ডার্ক ম্যাটার। সেই থেকে এর নাম ডার্ক ম্যাটার হয়ে যায়।” পল্টু জানাল।
অবিশ্বাস্য। তাহলে তো পুরো ব্যাপারটাই ঘেঁটে গেল পল্টুমামা! পিরিওডিক টেবিল ব্যাপারটাই তো ঘেঁটে গেল। আরও অনেক ধরনের ফোর্সও তো থাকতে পারে যা এই ডার্ক এনার্জির অংশ যা আমরা জানি না!
রিভু আর বিল্টু তো বিস্মিত। “তারমানে আমরা যা দেখি আর অনুভব করি সেটা মাত্র ৪.৭% তার বাইরে আরও ৯৫.৩% ম্যাটার আর এনার্জি আছে যা আমরা দেখতে বা অনুভব করতে পারি না? অবিশ্বাস্য। তাহলে তো পুরো ব্যাপারটাই ঘেঁটে গেল পল্টুমামা! পিরিওডিক টেবিল ব্যাপারটাই তো ঘেঁটে গেল। আরও অনেক ধরনের ফোর্সও তো থাকতে পারে যা এই ডার্ক এনার্জির অংশ যা আমরা জানি না! তারমানে ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরির ভিতটাই তো নড়ে গেল!”
রাত তখন সাড়ে বারোটা।
কাজল বলল “চল এবার শুতে যাই। আজ সবটা হজম কর! কাল সকালে আবার আলোচনা হবে।”
সারাটা রাত রিভুর মাথায় নানান প্রশ্ন ঘুরঘুর করতে লাগল। যেমন ডার্ক ম্যাটার যদি কোনওরকম ইলেক্ট্রোম্যাগন্টিক রেডিয়েশনের সাথে ইন্টারেক্ট না করে তাহলে তো মহাবিশ্বের বয়স বা ব্যাপ্তি নিয়ে আমাদের যে ধারনা তা ভুল। বিগ ব্যাং যে ১৩৮০ কোটি বছর আগে ঘটেছিল তা ঠিক নাও হতে পারে। হয়তো বিগ ব্যাংয়ের সময় যে এনার্জি আর ম্যাটার বিচ্ছুরিত হয়েছিল তার সবটাই ডার্ক এনার্জি আর ম্যাটার। তাই আমরা জানিই না এই অবসার্ভেবল ইউনিভার্সের বয়স কত! রিভুর মাথায় সব কেমন গুলিয়ে যেতে লাগল।
এইসব ভাবতে ভাবতে রিভু ঘুমিয়ে পড়ল।
(চলবে)
পড়াশোনা করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেডিয়ো ফিজিক্স বিভাগে। পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন তথ্য প্রযুক্তিকে। প্রায় এগারো বছর নানা বহুজাতিক সংস্থার সাথে যুক্ত থাকার পর উনিশশো সাতানব্বইতে তৈরি করেন নিজের তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা। বর্তমানেও যুক্ত রয়েছেন সেই সংস্থার পরিচালনার দায়িত্বে। কাজের জগতের ব্যস্ততার ফাঁকে ভালবাসেন গান-বাজনা শুনতে এবং নানা বিষয়ে পড়াশোনা করতে। সুযোগ পেলেই বেড়াতে বেরিয়ে পড়েন আর সেই অভিজ্ঞতা ধরে রাখেন ক্যামেরায়।




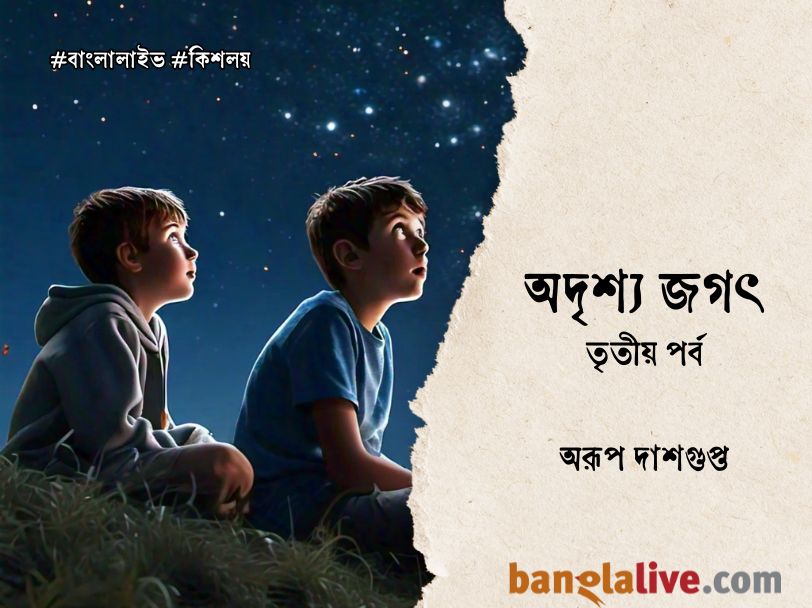





















One Response
Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam comments? If so how do you prevent it, any plugin or anything you can advise? I get so much lately it’s driving me crazy so any assistance is very much appreciated.