চেরিরেড
সিজারের পিছনে দাঁড়িয়েছিল কাসকা। ছুরির ঘা বসিয়ে দিল অতর্কিতে সিজারের বুকে। সিজার চেয়েছিলেন বাধা দিতে। কিন্তু নাহ। বড্ড দেরি হয়ে গেছে। প্রায় তেত্রিশটা ছুরির ঘা এসে পড়ল ষড়যন্ত্রকারীদের থেকে। আহত সিজার, রক্তমাখা সিজার- খুঁড়িয়ে, কষ্ট চেপে ব্রুটাসের কাছে গেলেন বাঁচার আর্তি নিয়ে। কিন্তু ব্রুটাসের আঘাত নেমে এল সিজারের মৃত্যু হয়ে! এ কী!
মৃত্যু? শেষ? ছেলেটার চোখে জল এসে গেল। এভাবে কেউ চলে যেতে পারে? চিরতরে?
অনলাইন ক্লাস হচ্ছে লকডাউনে। ছেলেটার মন চলে গেছে কোন সুদূরে। সারা শরীরে বর্ম এঁটে তার বাবা-মা লড়ে চলেছে হাসপাতালে। মুখ ঢাকা মাস্কে। কোনওভাবে যেন ভাইরাস এসে কাবু না করতে পারে। কতদিন সে বাবার সঙ্গে গলিতে ক্রিকেট খেলেনি। দাবার বোর্ড খোলেনি। কতদিন হয়ে গেল মায়ের গায়ের গন্ধ পায়নি ছেলেটা। মায়ের হাতের আলুপোস্ত খায়নি। আধোঘুমে কপালে হাত বোলায়নি একটা নরম হাত।
কিন্তু নাহ। মনখারাপ করলে চলবে না। তার থেকেও তার বাবা-মাকে এখন বেশি দরকার সমাজের। হাজার হাজার মানুষ অসহায় হয়ে তাকিয়ে আছে বাবা-মায়ের দিকে। কাতর দৃষ্টিতে। ওরা যে দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করছে সিজারের মতো। আর ছুরির পর ছুরি চালাচ্ছে ভাইরাসটা। ব্রুটাস! গতবছর ‘মাদার্স ডে‘-র দিনে ছেলেটা একটা দোকানে ঢুকেছিল। স্কুলছুটির পর। কসমেটিক্সের দোকান। লিপস্টিক আর নেলপালিশ চাইতেই দোকানি অবাক হয়ে তাকিয়েছিল।
– কার জন্য নেবে? গার্লফ্রেন্ড?
ইতস্ততভাবে প্রশ্নটা করেই ফেলেছিল দোকানি। তেরো বছরের কিশোরও আজকাল বান্ধবীর মন জোগাতে শপিং করে! কী দিনকাল এল!
– লাইট কালার নয়, আঙ্কল ঐ চেরি রেড লিপস্টিকটা দিন। আর ঐ গ্লসি নেলপালিশটা। মা একদম সাজগোজ করার সময় পায় না।
মা কী খুশি যে হয়েছিল সেদিন। নিজেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চটপট মেখে নিয়েছিল লিপস্টিকটা। অনেকদিন মা–কে দেখেনি ছেলেটা। পাছে সন্তানের কোভিড সংক্রমণ হয়, মা-বাবা এখন অনেক দূরে। সে রয়েছে দাদু দিম্মার জিম্মায়। তালাবন্ধ প্রাণহীন শহর। সন্ধ্যা হতেই টিমটিমে আলো। আজও মাদার্স ডে। আজ মা–কে কিছু দেওয়া হল না।
কিন্তু ছেলেটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, ফেসশিল্ড, মাস্কের মধ্যে মায়ের ঠোঁটে লেগে আছে দৃঢ়তার লিপস্টিক। গ্লাভসে ঢাকা আঙুলগুলো পরম যত্নে রোগীর হৃদয় আর ফুসফুস থেকে টেনে টেনে বার করছে এক একটা ছুরি। মায়ের নেলপালিশের রঙটা কী ছিল? মনে পড়ছে না।
ভালোবাসার কী রঙ?
চেরি রেড?
নন্দিনী নাইটিঙ্গেল
নন্দিনী আজ আর ফ্ল্যাটে ফিরতে পারবে না। গত তিনদিন ধরে আবাসনের লোকজন হল্লাবাজি করছে। নন্দিনী শক্তিনগর জেলা হাসপাতালের স্টাফ নার্স। এখন করোনা কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের দায়িত্বে। অতএব তাকে ঢুকতে দেওয়া যাবে না। নন্দিনী অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছে প্রতিবেশীদের। এভাবে সংক্রমণ ছড়ায় না। বরং নন্দিনীর থেকে তারা জেনে নিক কীভাবে প্রতিরোধ করতে হবে কোভিড আক্রমণকে। কিন্তু এইসব অন্ধরা আলো দেখতে অনিচ্ছুক। মাস্ক ছাড়া দিব্যি যাতায়াত, কেনাবেচা করছে। সবজিওয়ালা, দুধওয়ালা, মাছওয়ালা, যে কেউ করোনার কেরিয়ার হতে পারে। এমনকী লক্ষণ না-ও থাকতে পারে। মুখ দেখে তো আর রোগ বোঝা যায় না!

বহুবার অনুরোধ করেও আবাসনের কর্মকর্তাদের মন গলাতে পারেনি নন্দিনী। ভন্ডামিতে ভরা সমাজ। প্রয়োজনে এরাই পায়ে পড়ে। নিজের বুড়ো বাপ-মাকে হাসপাতালে ভর্তি করে চলে যায় ভুল ঠিকানা দিয়ে। যাতে ফেরত না নিতে হয়। বৃদ্ধাশ্রমের খরচটাও বাঁচল! কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করে একটা বিকল্প থাকার ব্যবস্থা আজ করতেই হবে। বিগ শপারে কিছু জামাকাপড়, অ্যাপ্রন, খাবারদাবার গুছিয়ে নিল নন্দিনী। মনের খাবার বলতে বই। কবিতা পড়তে ভালোবাসে নন্দিনী। করোনা ডিউটিতে কবিতা পড়া মাথায় উঠেছে। প্রাণভয় তো আছেই। মা মারা গেছে ছোটবেলায়। সে এক মেয়ে। বাবা একা গ্রামের বাড়িতে। বাবার জন্য অন্ততপক্ষে তাকে সুস্থ থাকতে হবে। কবি জয়দেব বসু নন্দিনীর খুব প্রিয়। আজ কবির জন্মদিন। আর একজনেরও। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল। বাবা মেয়ের নাম ‘নন্দিনী‘ রেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথের ‘রক্তকরবী‘ পড়ে। হতাশা, অবসাদের মধ্যে নন্দিনী এক মহাজাগতিক আলো। বাঁচার আশা।
জয়দেব বসুর দু’চার লাইন ভাবতে ভাবতে টোটোতে উঠে বসল নন্দিনী। টোটোচালক ছেলেটা বিএসসি পাস। সরকারি চাকরি পায়নি তাই টোটো চালায়। একমাত্র এর চোখেই মনুষ্যত্বের ভাষা দেখেছে নন্দিনী। মোবাইল নম্বরটা দিয়ে বলেছিল, “লাগলে ডাকবেন। যে কোনও দরকারে।” এখন হাসপাতালে যাচ্ছে নন্দিনী। তেরো নম্বর বেডের বুড়োটা এক্সপায়ার করেছে বোধহয়। একফোঁটা রক্ত নেই শরীরে। কাল জিজ্ঞেস করেছিল কাঁপা কাঁপা গলায়, “মা, আমি বাঁচব?” নন্দিনী স্মার্ট গলায় বেবাক মিথ্যে বলেছিল, “আলবাত।” অথচ রক্ত নেই ব্লাড ব্যাঙ্কে। অ্যানিমিয়া গোটা পাড়ায়। শহরে। দেশে। কোথাও সেবিকাদের একটুকুও সম্মান নেই। উল্টে অপমান, কটুক্তি। ফ্লোরেন্সকেও সহ্য করতে হয়েছিল নিশ্চয়ই।
“পেরিয়ে গেছি মেঝেনদের দেশ,
পেরিয়ে গেছি কুষ্ঠেখসা গ্রাম
জানো কি তুমি অনেকে এখানেও
ফিসফিসিয়ে বলে তোমার নাম।”
কবি জয়দেব বসুর এই পঙক্তিটা নন্দিনীর ভারি প্রিয়। হাসপাতালে পৌঁছে ভাড়া মেটানোর সময় টোটোচালক তরুণ বলে উঠল, “যদি কোথাও ব্যবস্থা না হয়, বলবেন। শক্তিনগর লেডিজ হোস্টেলে মামাতো দিদি থাকে। টিচার। বন্দোবস্ত হয়ে যাবে।” সুপারের অফিসে ঢোকার আগেই কান্নার রোল কানে গেল নন্দিনীর। তেরো নম্বর বেডের পেশেন্টপার্টি । গ্রীষ্মকালে এই এক কষ্ট। রক্ত পাওয়া যায় না। এবারে মহামারির জন্য রক্তের আরও আকাল।

ফ্লোরেন্সের কথা মনে পড়ল হঠাৎ। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে সেনাদের কী সেবাটাই না করেছিলেন। এলিজাবেথ কেনি! অস্ট্রেলিয়ায় পোলিওর বিকলাঙ্গ শিশুদের পাগুলো যিনি জলের মধ্যে নাড়িয়ে নাড়িয়ে সবল করতেন। ১৯৫০ সালে ইংল্যান্ডের একটা দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠল নন্দিনীর। শয়ে শয়ে নার্স একরত্তি নবজাতকদের কোলে নিয়ে বেরিয়ে আসছে ওয়ার্ড থেকে সূর্যের নীচে। চেঁচিয়ে বলছেন সিস্টার জেন ওয়ার্ড,
– রোদে নিয়ে যাও গো, রোদে নিয়ে যাও। বাচ্চাগুলো বেঁচে যাবে।
– ডাক্তাররা হাল ছেড়ে দিয়েছেন! রক্ত নেই
শব্দগুলো চাবুকের মতো আছড়ে পড়ল নন্দিনীর কানে। মনে হল তাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার করে দিচ্ছে আবাসনের লোকজন।
– আমি ব্লাড দিতে চাই তেরো নম্বরের জন্য। বি পজিটিভ। নাম লিখুন নন্দিনী জোয়ারদার।
সুপারের ঘরে হুড়মুড় করে ঢুকল সে। রক্ত দেওয়ার সময় আশেপাশে কলিগরা, ডাক্তাররা হাততালি দিচ্ছিল। টোটোচালক তরুণ কাছেই দাঁড়িয়ে। চলে যায়নি। অবাক হল না নন্দিনী। করোনা বড় শিক্ষক। রোজই কিছু না কিছু নতুন শেখাচ্ছে।
এখন যদি একটা খাতা আর পেন থাকত, অকালমৃত কবি জয়দেব বসুর জন্য একটা কবিতা লিখত নন্দিনী।
তোমার মতো মানুষ বড়ই বিরল,
শব্দ নিয়ে জাগলারিই কি কবিত্ব?
সময় যখন বদলায় রঙ বদল,
দুঃসময়ে চিনছি মানব চরিত্র।
*ছবি সৌজন্য: Pixabay, Yale Insights, Reuters
পেশায় ডাক্তার দোলনচাঁপা নতুন প্রজন্মের লেখকদের মধ্যে পরিচিত নাম। মূলত গল্প এবং উপন্যাস লেখেন বিভিন্ন ছোটবড় পত্রপত্রিকায়। 'চন্দ্রতালের পরীরা' এবং 'ঝুকুমুকু' তাঁর লেখা জনপ্রিয় কিশোরসাহিত্যের বই।










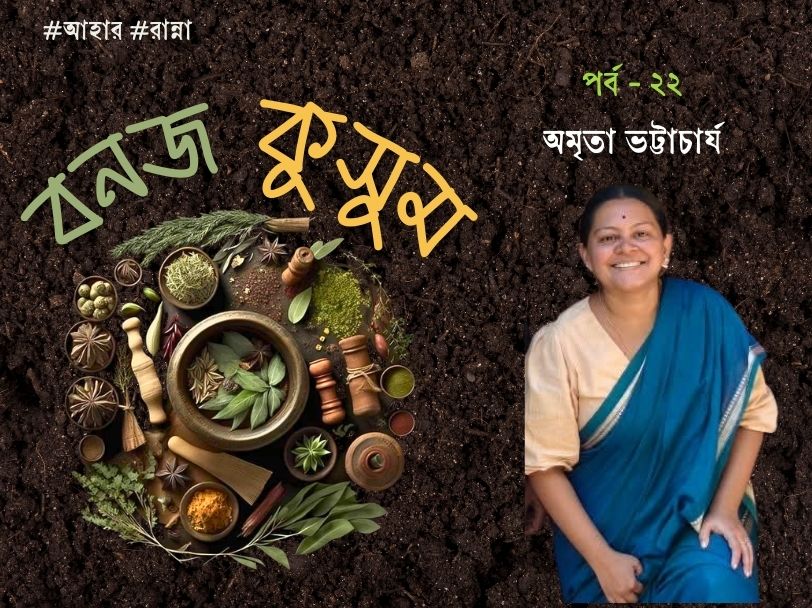













3 Responses
মন ছুঁয়ে গেল। সত্যি কতো মানুষ জন যে হারিয়ে গেল, কিন্তু হার না মানা মনোভাবাপন্ন ডাক্তার, নার্স ও সকলের সাহায্যে এগিয়ে আসা সাধারণ মানুষের সেবায়,যত্নে আমরা আবার ঘুরে দাঁড়াবো।
মনের না বলা অনেক কথা , অনেক অভিজ্ঞতা এখানে থাকুক সময়ের দলিল হিসেবে। আমরা ছিলাম আছি থাকব, সহমর্মী হয়ে সমব্যথী হয়ে।
চমৎকার লেখা । মন ভরে গেল !৬