‘জন্মভূমি — আমার স্বপ্নসঙ্গিনী’
জীবনের পথ-পরিক্রমায় যখন রঙের পরিবর্তন হতে থাকে— অর্থাৎ সবুজ, লাল, নীল ইত্যাদি থেকে শেষ পর্যন্ত ধূসর রঙে এসে পৌঁছয়, তখন মানুষ তার স্মৃতির মধ্যে আনন্দের সন্ধান করে বেড়ায়। আমিও আমার জীবনের পথচলায় যে সমস্ত অমূল্য সম্পদের সন্ধান পেয়েছি, তাকে নাড়াচাড়া করে আনন্দ পাবার চেষ্টায় আছি।
জন্মেছি ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে, গ্রামের নাম ‘কামারখাড়া’, ১৯৩২ সালের ২৪শে অক্টোবর। জন্মসূত্রে আমি পূববাংলার মেয়ে। যদিও ১৯৩৪ সালে আমার বাবা শ্রী সুধীর কুমার বসু কলকাতা চলে আসতে বাধ্য হন ইংরেজ পুলিশের তাড়নায়, স্বদেশি তকমা মাথায় নিয়ে। কেন জানি না, কোনও পূর্ববঙ্গীয় মানুষের সঙ্গে পরিচয় হলে তাকে আমার ভীষণ আপন মনে হয়—তার সঙ্গে পূর্ববঙ্গের ভাষায় কথা বলতে ইচ্ছে হয়— এটা হয়তো জন্মভূমির অদৃশ্য টানের ফল।
আমার সেই ফেলে আসা পূববাংলার গ্রামের কথা বলি— যে গ্রামের ছবি আমার মনের আরশিতে সততই দৃশ্যমান। প্রথমেই মনে পড়ে ছোট নদীটির কথা— নদীর পার অনেকটা চওড়া, নদীর পারে বসার জন্য বেঞ্চ, সামনে খোলা আকাশ। এই নদীটি পদ্মা কিংবা বুড়িগঙ্গায় মিশেছে— ঠিক জানি না। যখনকার কথা লিখছি তখন আমার বয়স মাত্র ৮ বছর। ১৯৪১ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বোমা পড়ার ভয়ে সবাই যখন কলকাতা ছেড়ে গ্রামে পালাচ্ছিল— আমাদের বাড়ির সব বাচ্চারা ও মহিলারা গ্রামে চলে যাই। দু’বছর গ্রামে থেকে ১৯৪৩ সালে কলকাতায় ফিরে আসি— সেটাই আমার শেষ গ্রামে যাওয়া।
‘কামারখাড়া’ গ্রামটি ছিল সবদিক থেকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ; সেখানে ইটের পাকা দালানওয়ালা ‘রাধানাথ হাই স্কুল’— সকালে মেয়েদের ও দুপুরে ছেলেদের ক্লাস; এই স্কুল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ছিল। গ্রামে পাকাপাকি একটা থিয়েটার মঞ্চ, সেখানে স্বনামধন্য ‘মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য’ গ্রামের ছেলে হিসেবে অনেক নাটকে অংশগ্রহণ করেছেন। বড় ফুটবল খেলার মাঠ। চৈত্র মাসে গাজনের সময় এই ফুটবল মাঠেই চারদিন ধরে মেলার আয়োজন হত।

কলকাতার ইট-কাঠের পরিবেশ থেকে গ্রামের সবুজের মধ্যে ছাড়া পেয়ে আমরা ছোটরা আনন্দে আত্মহারা। কত রকম গাছ, কত নানা রকমের পাখি। আমাদের বাড়িতে মস্ত একটা লিচু গাছ ছিল—পাখিরা ফল খেয়ে, না খেয়ে নষ্ট করে বলে গাছের ডগায় টিনের ঘণ্টা দড়ি দিয়ে বেঁধে পাখি তাড়াবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বেত গাছে যে ফল হয় সেটাও একটা মজার ব্যাপার। সেই ছোট ছোট সাদা ফলগুলো মোটেই সুস্বাদু নয়, সেই ফলই আমরা ছোটরা নারকেল-মালার মধ্যে রেখে নুন মেখে মহা আনন্দে খেয়েছি। নারকেল-মালাতে ঝাঁকানোর সময় সমস্বরে গান ধরেছি—
আম পাকে জাম পাকে
মামার বাড়ির বেথুন পাকে।।
বেতের ফলগুলিকে বলা হত বেথুন ফল।
পূর্ববঙ্গ নদীমাতৃক দেশ— সেখানে ঝড়-জল-বন্যা লেগেই থাকে, তাই সেখানকার ঘরগুলি উঁচু মাটির ভিতের উপরে টিনের দেওয়াল ও টিনের ছাদ দিয়ে তৈরি। যখন ঝড় উঠত আমাদের ভীষণ ভয় করত—এই বুঝি টিনের চাল উড়িয়ে নিয়ে যায়। বৈশাখ মাসের ঝড়ে আমাদের বাগানের একটা মস্ত আমগাছ পড়ে গিয়েছিল—সেই আম কুড়োবার মজাটাও আমরা ছোটরা উপভোগ করেছি।
বর্ষাকালে যখন পুকুর, নদী, খাল, বিল সব ভর্তি হয়ে জল বাড়ির উঠোন ভাসিয়ে দিত, তখন কাঠের পাঠাতন পেতে এ-ঘর ও-ঘর করতে হত। আমরা ছোটরা বাড়ির দাওয়ায় বসে কাগজের নৌকা জলে ভাসাতাম। জমি যখন জলে ডুবে যেত, অবাক হয়ে দেখতাম জল যতটা উপরে উঠত পাটগাছের ডগাগুলি ঠিক তার ওপরে মাথা তুলে জেগে থাকত।

এই গ্রামে পুকুরের ছড়াছড়ি— আমাদের নিজেদেরই ছিল দুটো পুকুর। গ্রীষ্মের রৌদ্রে যখন মাটি গরম হয়ে উঠেছে, ঘুঘু পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে, তখন বাড়ির বড়রা পুকুরপারে আমগাছের তলায় মাদুর পেতে আড্ডা জুড়েছে। বাড়িতে একটা গ্রামোফোন ছিল—সুটকেসের মতো হ্যান্ডেলওয়ালা, সেটাকে কখনও-সখনও পুকুরপারে নিয়ে যাওয়া হত— শচীনদেব বর্মনের ‘‘পদ্মার ঢেউরে/ আমার শূন্য হৃদয় পদ্ম নিয়ে যা/ যা রে…’’, সন্তোষ সেনগুপ্তের “জীবনে যারে তুমি দাওনি মালা/ মরণে কেন তারে দিতে এলে ফুল” ইত্যাদি নামকরা শিল্পীর রেকর্ড বাজিয়ে শোনা হত। যদিও আমি ছোট, তবু গানের প্রতি ভীষণ আকর্ষণে আমি প্রায়ই সেখানে উপস্থিত হতাম।
মাটি এমন উর্বরা যে আমের আঁটি যেখানে পড়েছে, কী সুন্দর কচি কচি পাতা নিয়ে গাছ গজিয়েছে—দেখে মুগ্ধ হতাম। কখনও-সখনও আমের আঁটি দিয়ে বাঁশি বানিয়ে বাজানো হত— আমি এটা একদমই পারতাম না। পুকুরপারে অনেক সময়ই সাপের খোলস পড়ে থাকতে দেখেছি, কিন্তু সাপ খুব নজরে পড়েনি।
কোনও কোনও দিন দুপুরে ঠাকুমাদের রামায়ণ-মহাভারত পাঠের আসরে ঢুকে পড়েছি— সেখানে রামায়ণের ‘তরণীবধ’ আখ্যান শুনে কেঁদে ভাসিয়েছি।
গ্রামে খুব বানরের উৎপাত ছিল। লালমুখো বানরগুলো তাদের বাচ্চা বুকে নিয়ে যখন টিনের চালের উপর দিয়ে লাফালাফি করত, রীতিমতো ভয় পেতাম।
বানরের কথা বলতে গিয়ে একটা ঘটনা মনে পড়ল। সবজি ইত্যাদি বাজারের পথ ছিল একটা বাঁশ-বাগানের ভিতর দিয়ে। সেই বাগানটায় আশিভাগই বাঁশ গাছ—বাঁশঝাড়ের মাঝখান দিয়ে বাজার যাবার পায়েচলা পথ। বড়রা আমাদের বলতেন ‘রাম’ নাম করলে বানরেরা কিছু করে না। কিন্তু আমার ১৪-১৫ বছরের দুই দাদা সেই পথ দিয়ে বাজার করে ফেরার পথে বানরেরা ছেঁকে ধরে আর আমার জেঠতুতো দাদার গালে চড় মেরে বাজারের থলি নিয়ে পালায়। সেই চড় খেয়ে আমার কুট্টিদা বেশ কিছুদিন গালের ব্যথায় কাবু ছিল।
মিত্ররা ছিল গ্রামের জমিদার। তাঁদের বাড়িতে একবার দু’দিন ধরে যাত্রার আসর বসেছিল। ‘জগাই-মাধাই উদ্ধার’ আর ‘নিমাই সন্ন্যাস’। যাত্রা দেখে আমার থেকে দু’বছরের বড় দুই দিদি সন্ন্যাস নেবে বলে সন্ধ্যার সময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে নদীর ধার পর্যন্ত গিয়ে ভয়ে আবার ফিরে আসে। ছোটবেলাটা এমনই—বাচ্চাদের চোখে মুগ্ধতা লেগেই থাকে। যা ভালো লাগে তাই হতে ইচ্ছা জাগে।
তখনকার দিনে মেয়েরা নানা ব্রত পালন করত। আমাদের বাড়ির কাছেই ছিল একজন গরিব ব্রাহ্মণ, তাঁর দুই মেয়ে মাঘমাসের শীতে ভোরবেলা পুকুরপাড়ে বসে একটা ব্রত পালন করত—তার নাম ‘মাঘ মণ্ডলের ব্রত’, আসলে এটা সূর্যের পুজো। ওরা যে গান গাইত তার দুটো লাইন—
ওঠো ওঠো সূর্যাই
ঝিকিমিকি দিয়া
তোমারে পূজিব আমি
বনফুল দিয়া।।
একমাস প্রতিদিন এই ব্রত পালন করার পর উঠোনে সূর্য এঁকে ও অন্যান্য আলপনা দিয়ে ফলমূল সহ পুজো দিয়ে ব্রতর পরিসমাপ্তি হত। এইসব ব্রতের মধ্যে যে নিষ্ঠা ও সহিষ্ণুতা থাকত— সেটা পরবর্তীকালে মেয়েদের ধৈর্যশীল ও কষ্টসহিষ্ণু হতে শেখাত। এই বয়সে এসে এটা উপলব্ধি করতে পারছি।
চৈত্র মাসে গাজনের সময় অনেক ছেলেরা বাড়ি বাড়ি আসত পয়সা রোজগারের জন্য— কখনও কালী, কখনও হর-পার্বতী ইত্যাদি সেজে। হাতের টিনের তলোয়ার নিয়ে যখন উদ্দাম নাচ দেখাতো=, তখন খুব মজা লাগত। এমনকী এরা নানারকম হালকা গানও শোনাত। তার মধ্যে একটা গান—
চুল নাই নেড়িবুড়ি
চুলের লইগ্যা কান্দে
কচুপাতার ঢিপল্যা দিয়া
খোপা ডাঙ্গর করে।
বুড়ি কোন গুণে।।
আমাদের বাড়িতে প্রতি বছরই দুর্গাপূজা ও কালীপূজা হত— তাই স্থায়ী পূজামণ্ডপ ছিল। তাছাড়া পূজামণ্ডপের পাশেই ছিল একটা ছোট ঠাকুরঘর। সেখানে মাটির কালো ‘হরি’ ঠাকুরের প্রতিমা। এই ঠাকুরঘরকে বলা হত হরির ঘর। পঞ্চবটি অর্থাৎ বট, অশ্বত্থ, আমলকী, বেল, অশোক গাছ দিয়ে ঘরটা ঘেরা ছিল, তাছাড়া শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় গাছ বলে প্রসিদ্ধ তমাল গাছটিও ছিল। প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় হরি ঠাকুরের পুজো হত, বিশেষ বিশেষ দিনে হরির লুট হেত বাতাসা ছড়িয়ে দিয়ে। আমরা সবাই ঠাকু্রঘর প্রদক্ষিণ করতে করতে গান গাইতাম—
লাগলো হরির লুটের বাহার
লুটট্যা নেরে তোরা।
চিনি সন্দেশ ফুল বাতাসা
মণ্ডা জোড়া জোড়া।।
পোলাপানে লুইট্টা নিল ঠইক্যা গেল বুড়া।।
যে গ্রামের ছবি আমার মানসচক্ষে আঁকা আছে, তার অস্তিত্ব এখন হয়তো একেবারেই নেই। আমার জন্মভূমি এখন আমার দেশ নয়—বিদেশ। ভাবতেও চোখে জল আসে। তবু আমার গ্রামের সেই ৮-৯ বছরের দেখা স্মৃতি রোমন্থন করে আনন্দ পাই।
সুব্রতা ঘোষ, ডাকনাম স্মৃতি। আবাসনের সকলের কাছে তাঁর পরিচয় মাসীমা নামে। ব্যক্তিত্বময়ী, হাস্যোজ্জ্বল এই মহিলা নব্বই বছর পার করেছেন। এক সময় আকাশবাণী কলকাতাতে গান গাইতেন। যেকোনও বয়সের মানুষের সঙ্গে সহজেই বন্ধুত্ব স্থাপন করার সহজাত ক্ষমতা আছে, তাই অসংখ্য তাঁর অনুরাগী। আশি বছর পার করে ফেসবুকে ঢুকে অনেকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছেন। অবসর সময়ে নানা বিষয়ের উপর লেখালেখি করতে ভালোবাসেন।




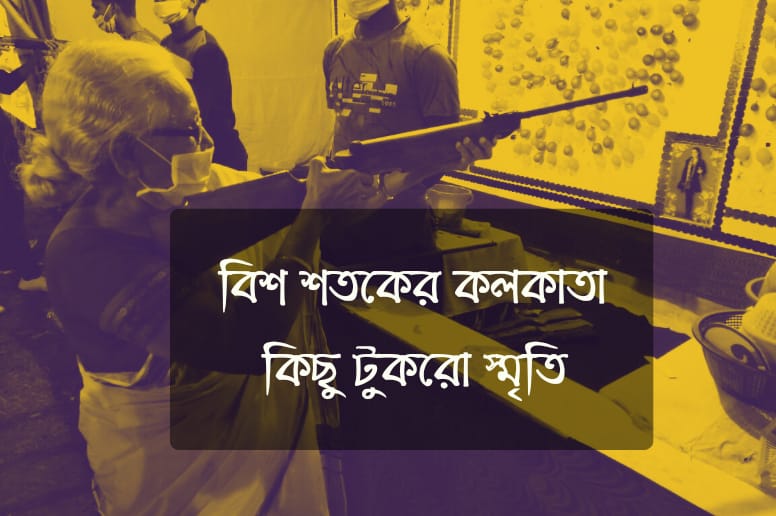






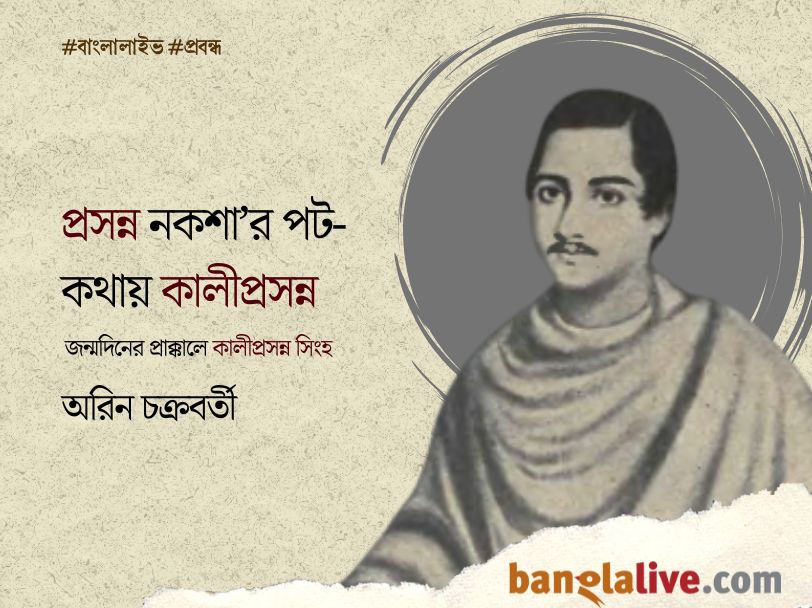














4 Responses
সত্যিই, ছোটবেলার স্মৃতি রোমন্থন সুখকর।
Khub bhalo Lekha Baro maima
Khub bhalo laglo mashima. Apnar lekha mon ta ke snigdha korlo. Aro likhun.
তোমার লেখা ছবির মতো,এত সহজ,এত সুন্দর লেখা মন ছুয়ে যায়। আসলে মনের সজীবতা অটুট।এভাবেই অমলিন হাসি নিয়ে খুব ভালো থেকো।