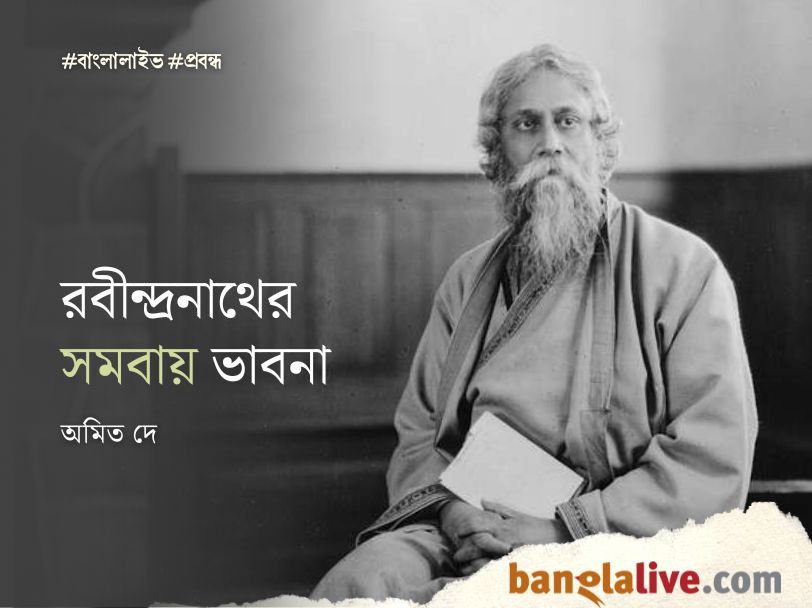(Rabindranath Tagore)
এই শিরোনামে কিছু লেখার অনুরোধ যখন আসে, আমার প্রাথমিক ভাবে মনে হয় মানুষকে ভালবাসার, ভাল রাখার নিবিড়, অতন্দ্র আবেগ থেকেই তো যাবতীয় সৃজন উৎসারিত হয়, আর সৃজক অবশ্যই চিন্তকও। সেই চিন্তা থেকেই সে সময়ের সাম্রাজ্যবাদ কবলিত সময়প্রেক্ষিতে স্বদেশবাসীকে ভাল রাখার উপায়সন্ধানে, সমবায়প্রথার কথা গভীরভাবেই ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এ কথা তাঁর জীবনেতিহাসই বলে। সুতরাং তার অনুসন্ধানে নামা যেতেই পারে। বিশেষত কবি ও কর্মীর আশ্চর্য সমন্বয়ে তাঁর জীবনের যে বিপুল ব্যাপ্তি, সে সত্য অনুধাবন আমাদের আত্মস্বার্থেই জরুরি। তারপর চমকিত হলাম আরেক ভাবনায়। আমার স্বল্প জ্ঞানে অনেক ভেবেও আর দ্বিতীয় কোনও কবির সন্ধান পেলাম না যিনি দেশের প্রাণকেন্দ্র যে গ্রাম, সেই গ্রামবাসীদের জীবন ধারণের মানোন্নয়নে এভাবে অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে রূপায়িত করে তুলতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সম্ভবত এখানেও তিনি অনন্য। (Rabindranath Tagore)
বদলের বিভিন্ন মাত্রা: রবীন্দ্রনাথ
বিশ্বজগত নিরববিচ্ছিন্নভাবে যে কান্না হাসির তরঙ্গে দোলায়িত হয়ে চলেছে, তার সমস্ত অভিঘাত কবিচিত্তে ঢেউ তুলুক, এই ছিল তাঁর কামনা। “যেথা তার যত ওঠে ধ্বনি/আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি।” কিন্তু জগতের যে দিকটি শিক্ষাবঞ্চনা, স্বাস্থ্যহীনতা, দৈন্য, অভাব, অনাহারে আঁধারাছন্ন, তার প্রত্যক্ষ পরিচয় ঠাকুরবাড়ির পড়ন্ত বৈভব আর আধুনিক ভাবনা ও সৃষ্টিশীলতার আলোকছটার পরিবেশে বড় হওয়া রবীন্দ্রনাথ প্রথম পেলেন প্রায় তিরিশ বছর বয়সে। সে প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে। (Rabindranath Tagore)
সমবায় বিষয়টি হল যৌথ শ্রমে, যৌথ বিনিয়োগে উৎপাদন উদ্যোগ এবং অংশীদারিত্বের হার অনুযায়ী লভ্যাংশের বন্টন
সমবায় বিষয়টি হল যৌথ শ্রমে, যৌথ বিনিয়োগে উৎপাদন উদ্যোগ এবং অংশীদারিত্বের হার অনুযায়ী লভ্যাংশের বন্টন। প্রাকৃতিকভাবে মানুষ যূথবদ্ধ প্রাণী, বস্তুত ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের আগে সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তার মধ্যে দেখা দেয়নি। সমবায় প্রথায় যেহেতু মুনাফা সমহারে বণ্টিত হয়, তাই অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা দূরে থাক, উদ্যমী শ্রমদানে উৎসাহ জাগ্রত হয়। ১৮৯০-৯১ খ্রিস্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথকে পূর্ব বাংলার শিলাইদহ, পতিসর সাজাদপুর (বর্তমানে বাংলাদেশ) প্রভৃতি অঞ্চলের জমিদারি দেখাশোনার কাজে পাঠালেন। (Rabindranath Tagore)

কবি সেই প্রথম ঠাকুরবাড়ির চকমেলানো বারান্দা ছেড়ে ধুলো কাদা ভরা বাংলার পল্লীগ্রামের মাটিতে পা রাখলেন। স্বাস্থ্যহীন, অনাহারী, সংস্কারআছন্ন, দারিদ্র্যক্লিষ্ট, শিক্ষাবঞ্চিত স্বদেশবাসী মানুষগুলোর বংশপরম্পরায় অসহায় জীবনযাপন প্রত্যক্ষ করে গভীরভাবে বিচলিত হলেন কবি। (Rabindranath Tagore)
তাঁর মনে হল, “এই সব নতশির, মূক, ম্লান মুখে ভাষা ফোটাতে হবে, শ্রান্ত, শুষ্ক, ভগ্ন বুকে আশা জাগাতে হবে” তবে ধন্য হবে মোর গান। “গ্রামোন্নয়নের অসংখ্য পরিকল্পনা নিয়ে শুরু হল তাঁর কর্মোদ্যোগ। লক্ষ্যণীয়, এই সময়ে প্রায় এক দশক সময়কাল জুড়ে তিনি গল্পগুচ্ছের যে গল্পগুলি লিখেছেন তার অধিকাংশই ফুটে উঠেছে এই পল্লীবাসী মানুষজনের জীবনচিত্রে, এ ছাড়া সমকালে রচিত ছিন্নপত্রের চিঠিগুলিতেও পল্লীপ্রকৃতির পটভূমিতে মানুষের জীবননির্বাহের নিখুঁত ছবি পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। (Rabindranath Tagore)
তিনি চাইতেন জীবিকা কেবল শক্তিসাধনার ক্ষেত্র না হয়ে মনুষ্যত্বসাধনার ক্ষেত্র হোক।
শনিবারের চিঠিতে (বৈশাখ,১৩৪৭) কবি যথার্থই লিখেছিলেন, “দেশের জন্য যত কিছু ভাবনা আকৈশোর আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, তা শুধু কাব্যেই প্ৰকাশ পায়নি। এর জন্য আমার সর্বস্ব পণ করেছিলাম। আমার সর্বস্ব খুব বেশি ছিল না, যতটুকু ছিল, ততটুকু নিঃশেষে উজাড় করে পরীক্ষার কাজ চালিয়েছি। দেশীয় বিদ্যালয় থেকে শুরু করে দেশীয় সমবায় ভান্ডার পর্যন্ত সবকিছুরই পত্তন করেছিলাম।” (Rabindranath Tagore)
বিদায়-অভিশাপ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন রাষ্ট্রনীতি যেমন নেশন স্বাতন্ত্র্যে আবদ্ধ থাকে, জীবিকাও সেভাবেই আবদ্ধ থাকে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে। তাই এত ঈর্ষা, প্রতারণা, প্রতিযোগিতা, হীনতা। অর্থাৎ তিনি চাইতেন জীবিকা কেবল শক্তিসাধনার ক্ষেত্র না হয়ে মনুষ্যত্বসাধনার ক্ষেত্র হোক। (Rabindranath Tagore)
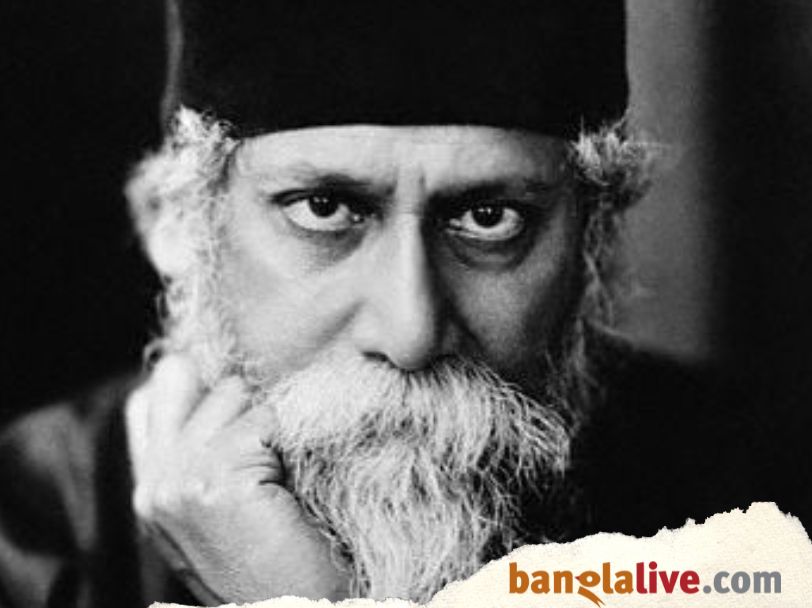
পরিশিষ্ট
জীবিকার ক্ষেত্রে শুধু অন্ন নয়, আপন সত্যকেও পেতে হবে মানুষকে। সমবায় প্রথায় সে সম্ভবনা থাকে। অসম্মিলনে মানুষ সর্বতোভাবে দরিদ্র হয়, আর সম্মিলনে হয় ধনী। তাঁর মতে সমবায় তত্ত্ব কেবলমাত্র একটা আচার নয়, এটি এক ‘আইডিয়া’। এ শুধু জীবিকাসাধনের আঁধা গলি নয়, এ হল অন্নপূর্ণার আগমন পথ। (Rabindranath Tagore)
কবির মন যখন দেশবাসীর দুর্দশা ঘোচানোর উপায় হিসাবে যৌথ কর্মনীতি, অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধীয় ভাবনায় আন্দোলিত হচ্ছে, এমন সময়ে তাঁর হাতে “ন্যাশনাল বিইং” নামে একটি বই আসে এবং সেই বইটি পড়ে তাঁর ভাবনা দৃঢ় ভিত্তি খুঁজে পায়। তবে তিনি অনুভব করেন যে, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ছাড়া ব্যক্তি বা কোনও গোষ্ঠীর উদ্যোগে এ কাজকে ব্যাপ্ত করে তোলা দুরূহ, কিন্তু একটি গ্রামকে ঘিরেও যদি এ কাজ করা যায়, তার ভবিষ্যৎ প্রসার অসম্ভব নয়। (Rabindranath Tagore)
তিনি কাজে নেমে পড়েন তাঁর কর্মীদলকে সঙ্গী করে। এ কর্মসাধনায় তাঁর প্রধান সহায়ক ছিলেন কালিমোহন ঘোষ, অতুল সেন প্রমুখ। অন্যদিকে সমবায়নীতি প্রয়োগের প্ৰয়োজনীয়তা বিষয়ে নানা প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। সময়টা ছিল বিশ শতকের প্ৰথম দশক। (Rabindranath Tagore)
কৃষি, শিক্ষা, সমাজ জীবন, সার্বিকভাবে গ্রামোন্নয়নের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয় তাঁর উদ্যোগ। পাতিসরে কালীগ্রামে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রথম কেন্দ্রীয় কৃষিসমবায় ব্যাংক স্থাপন করেন।
কৃষি, শিক্ষা, সমাজ জীবন, সার্বিকভাবে গ্রামোন্নয়নের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয় তাঁর উদ্যোগ। পাতিসরে কালীগ্রামে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রথম কেন্দ্রীয় কৃষিসমবায় ব্যাংক স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর তিনি লক্ষাধিক টাকা এই ব্যাংকে বিশ্বভারতীর নামে রাখেন। চাষিরা উপকৃত হয়েছিলেন তো বটেই, শোনা যায় মহাজনরাও অবশেষে এখানে টাকা গচ্ছিত রাখতে শুরু করেছিলেন। ১৯২১-এ প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রীনিকেতন। সেখানে সমবায় প্রথায় উৎপাদিত ধান রাখার জন্য স্থাপিত হয় ধর্মগোলা। এ ছাড়া রোগ নিবারণ ও চিকিৎসার আয়োজনও করা হয়েছিল। (Rabindranath Tagore)
শিক্ষা ক্ষেত্রে তিনি বিদ্যালয়ে ছাত্র সম্মিলনী গড়ে তুলেছিলেন। এখানে ছাত্ররা নিজেরাই দায়িত্ব ভাগ করে নিয়ে অঞ্চলভিত্তিক ভাবে গ্রামবাসীদের সেবাদান করতেন এবং একই সঙ্গে তাদের জানার সুযোগ পেতেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সহযোগিতা ঐক্যবন্ধনের মাধ্যমে সভ্যতার ধাত্রীভূমি গ্রামের বাসিন্দাদের সর্বস্তরীয় উন্নতিসাধন। (Rabindranath Tagore)
তাঁর এই ভাবনায় সমাজতান্ত্রিক প্রভাব ছিল মনে হয়। রাশিয়া ভ্রমণের পর সেখানকার যৌথ খামার ব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা তিনি করেছিলেন।সুইডেন পরিভ্রমণের পর সেখানকার সমবায় ব্যবস্থারও সপ্রশংস উল্লেখ করেছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন যে সাম্রাজ্যবাদী শাসনে আত্মপ্রত্যয়ী ও আত্মনির্ভর হয়ে ওঠার জন্য যে ঐক্যবন্ধন প্রয়োজন, তা সমবায় ব্যবস্থা এনে দিতে পারে। (Rabindranath Tagore)
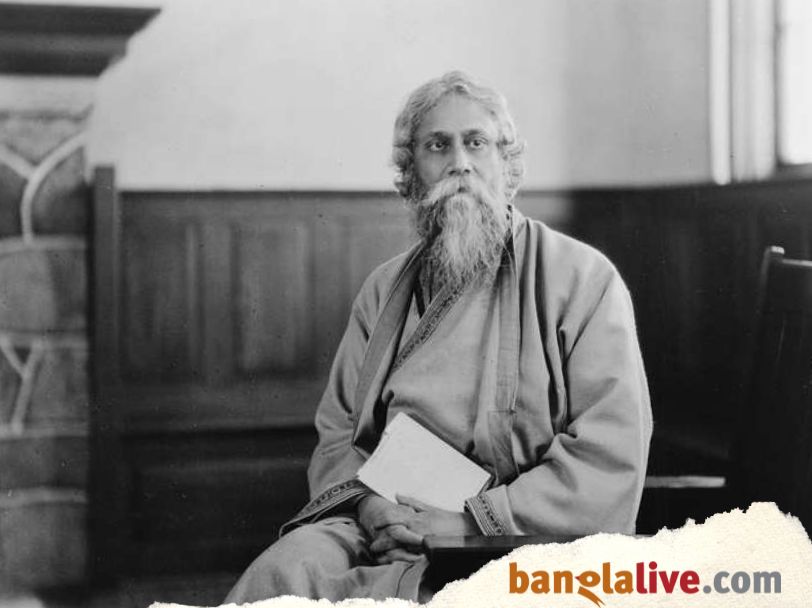
সে সময়ে অধিকাংশ পল্লীকুটিরে গো-পালন করা হত। সেই গো-দুগ্ধের সবটাই বাড়ির প্রয়োজনে লাগত না, কিছুটা বাড়তি হত। ঐ অল্প পরিমাণ দুধ বস্তুত নষ্ট হত। কিন্তু সকলের বাড়ি থেকে ওই অল্প পরিমাণ দুধ সংগ্রহ করলে তা অনেকটাই হবে এবং তা দিয়ে ঘি এর ব্যবসা করা সম্ভব। তিনি সুরুল অঞ্চলে ঋণ করে এইসব সমবায়িক ব্যবসার এক কেন্দ্র গড়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও জামাতা নগেন্দ্রনাথকে বিদেশে কৃষিবিজ্ঞান পাঠের জন্য পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে হঠাৎ মহামারী হয়ে দেখা দেয় ম্যালেরিয়া। সুরুলের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। রবীন্দ্রনাথ জানতেন একলা মানুষ খন্ডিত, সমাজসম্মিলনেই সে পূর্ণ। (Rabindranath Tagore)
পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া ও সুইডেন পরিভ্রমণ কালে তাদের সমবায় নীতির ব্যাপক প্রয়োগশীলতার প্রশংসা করেছেন।
বালি মাটিতে ফসল ফলে না, কারণ, সে মাটি আঁটো সাটো নয়, তাই ফসলের জন্য সে মাটিতে পলিমাটি মেশাতে হয়। মানুষও পারস্পরিক ভাবে বাঁধনে থাকলে জীবনের গোলা ঘর ফসলে ভরে ওঠে। সমবায় সর্বজনহিতায়। তাই সেখানে ব্যক্তিস্বার্থ সমাজিক কল্যাণকে ছাপিয়ে যেতে পারে না। ফলে গ্রামগুলি সমবায়ের মাধ্যমে স্বয়ম্ভর হয়ে উঠতে পারে। এই স্বয়ম্ভরতাই আত্মনির্ভরতার ভিত্তিভূমি। আর আত্মনির্ভর মানুষই স্বায়ত্বশাসনের যথার্থ অংশীদার হয়। অন্যথায় মূলধন ও মজুরির ভেদ বাড়তে থাকে এবং ধনী ও নির্ধনের পার্থক্য স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে চলে। গণতন্ত্র তখন পদে পদে ব্যাহত হয়। (দ্র:সমবায়নীতি -রবীন্দ্রনাথ) (Rabindranath Tagore)
পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া ও সুইডেন পরিভ্রমণ কালে তাদের সমবায় নীতির ব্যাপক প্রয়োগশীলতার প্রশংসা করেছেন। একাধিক অর্থনীতিবিদ সে সময়ে বাংলার প্রাণকেন্দ্র এই গ্রামগুলিকে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর এই ভাবনাকে সমর্থন জানিয়েছেন। দুর্ভাগ্য যে নানা কারণে তাঁর এই উদ্যোগ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। (Rabindranath Tagore)
কবি বলেছিলেন, “আমি তোমাদেরই লোক”। তাঁর এই দাবীর মধ্যে সামান্যতম অত্যুক্তিও নেই, কী বলেন?
আত্মপরিচয়ে ছাত্র, জীবিকা অধ্যাপনা। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। ভালোবাসেন শিক্ষার্থী যৌবনকে, বই পড়তে, মূলতঃ শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস আর হ্যাঁ, খেলাধুলা। অঙ্কটা কম জানেন বলে দাবি করেন, কিন্তু বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের গণিত বুঝে নেওয়ার আগ্রহ প্রবল।