বিশ্বরাজনীতির আঙিনায় বছরের শুরুতেই ঘটনার ঘনঘটা। গোটা দুনিয়াকে খানিকটা হতবাক করে আমেরিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ইমপিচমেন্ট প্রক্রিয়ার এর মধ্য দিয়ে যেতে হল। এই নিয়ে বারবার দু’বার, যা মার্কিনী ইতিহাসে অভূতপূর্ব। প্রথমবার ক্ষমতার অপব্যবহার করে তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ জোসেফ বাইডেনের নামে ভুয়ো খবর ছড়ানোর অভিযোগে, আর দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রদ্রোহিতার প্ররোচনায় উস্কানির দায়ে। যদিও একজন নাবালকও জানেন যে গত ৬ই জানুয়ারি, রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসির প্রাণকেন্দ্র ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ের উপর হামলা আর যাই হোক না কেন, ক্ষমতা দখলের কোনও বৈপ্লবিক আখ্যান নয়। বিদায়ী রাষ্ট্রপতি নিজে তো বটেই, অধিকাংশ হামলাকারীও জানতেন যে রাজপ্রাসাদ থেকে ট্রাম্পের বিদায় শুধু ছিল সময়ের অপেক্ষা। তবু কেন এই হামলা যার না আছে কোনও আপাত পরিণতি, না আছে কোনও সুনির্দিষ্ট দিশা? এর প্রভাব কি আদৌ সুদূরপ্রসারী? অন্যান্য দেশের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের, নির্বাচনী প্রেক্ষিতেও কি এহেন হামলা ঘটা সম্ভব? এই সমস্ত বিষয় বিশদে আলোচনা করাই এই নিবন্ধটির মূল উদ্দেশ্য।
উপরোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর একক ভাবে পাওয়া সমস্যাকর হলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উত্তর লুকিয়ে আছে গত দশকের মাঝামাঝি থেকে উদ্ভূত বিশ্বজোড়া এক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক মেরুকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে। সে প্রক্রিয়ায় ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে, সমমতাদর্শী মানুষেরা যুদ্ধং দেহি মনোভাব দেখিয়ে দল বেঁধে চড়াও হয়েছেন বিপরীত মতাদর্শের মানুষদের ওপর। এই দুই পক্ষের নেতাদের আস্ফালন এবং ক্রমাগত প্ররোচনামূলক উস্কানির ফলে ভেঙে গেছে এক অলিখিত সামাজিক চুক্তি যেখানে মতাদর্শগত বৈপরীত্যকে দেখা হত কিছুটা সহনশীলতার সঙ্গে। পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এবং বৈরিতার মাঝেও ছিল এক সামাজিক সহাবস্থানের বাতাবরণ। মতের অমিল হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন মতাবলম্বী মানুষদের প্রাত্যহিক জীবনে এহেন যুযুধান বৈরিতার অনুপ্রবেশ ছিল না এক-দু দশক আগেও। এই শতকের শুরুতেও তো বিশ্বায়নের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি ও তর্কের অভাব ছিল না। ছিল ভিন্ন ভাষা বা ধর্মের অনুসরণকারীদের সঙ্গে মতপার্থক্যও। কিন্তু, তখনও এই তার্কিকরা সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর বাসিন্দা হয়ে যান নি। কিন্তু এর কিছু বছরের মধ্যেই, খানিকটা আমাদের অগোচরেই, যেন পৃথিবীর কোনও এক বেখেয়াল মুহূর্তে শুরু হয়ে গেল ‘এজ অফ পোলারাইজেশন’ বা সার্বিক মেরুকরণের এক অস্থিরময় যুগ। নেমে এল একমাত্রিক মানসিকতার একচ্ছত্র আধিপত্য।

কেন বদলে গেল প্রেক্ষাপট? বিষয়টি অত্যন্ত জটিল বলেই হয়ত সম্যক গবেষণা এখনও ঘটেনি। তবুও কিছু মানুষ পথ দেখাচ্ছেন। যেমন অর্থনীতিবিদ দেবরাজ রায় এবং জোয়ান এস্তেবান। দেবরাজরা জানাচ্ছেন চূড়ান্ত এই মেরুকরণের ফলে মানুষ তাঁদের বৃত্তের বাইরের মানুষদের থেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করেন, আর সমমনস্কদের কাছে খুঁজে পান এক গভীর আত্মিক বন্ধন। বিচ্ছিন্নতাবোধ এবং আত্মীয়তার এক অহর্নিশ দ্বন্দ্ব সমাজে ছড়িয়ে দেয় পারস্পরিক ঘৃণা। সে ঘৃণা জন্ম দেয় হিংসার, আর হিংসা থেকে উদ্ভূত হয় গৃহযুদ্ধ।
কিন্তু গৃহযুদ্ধ একটি চরম পরিণতি। যেটা তখনই ঘটে যখন সমাজ ব্যবস্থা এবং তার প্রাতিষ্ঠানিক রক্ষাকবচ সমূহ মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে। কিন্তু গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় মেরুকরণের প্রভাব অন্যভাবেও আসতে পারে। একমাত্রিক মানসিকতা প্রভাব ফেলে যেতে পারে নির্বাচনী রাজনীতিতেও। একবিংশ শতাব্দীর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি, যেমন বিশ্বায়ন, উষ্ণায়ণ বা অভিবাসনের প্রসঙ্গে মানুষ দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করতে পারেন এবং তার আঁচ পড়তে পারে নির্বাচনের ফলাফলেও। বিষয়টি আর একটু খুঁটিয়ে দেখা যাক।
এখানে বলে রাখা ভাল যে আমরা বিভিন্ন ভোটারদের মধ্যে স্বাভাবিক মতপার্থক্যকে আদৌ অস্বীকার করছি না। মানুষের ব্যক্তিগত ইতিহাস ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির প্রভাবে গড়ে ওঠা জীবনদর্শন তাঁদের রাজনৈতিক মতাদর্শকে আলাদা আলাদা খাতে বইয়ে দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে বলাই যায় যে নিউইয়র্ক বা সানফ্রান্সিসকোর উচ্চশিক্ষিত, শহুরে মানুষ যারা একটি বিশ্বজনীন পরিবেশে জীবননির্বাহ করছেন তাঁদের আর্থসামাজিক মতামত যে পশ্চিম ভার্জিনিয়া বা দক্ষিণ ক্যারোলিনার গ্রামীণ, খেটে খাওয়া, বংশানুক্রমে রক্ষণশীল মানুষদের মতামতের থেকে আলাদা হবে সে কথা বলা বাহুল্য। কিন্তু একবিংশ শতকে এসে দেখা যাচ্ছে সময় সময় আর্থসামাজিক বিষয়গুলি এতই জটিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে উচ্চশিক্ষিত হোক কী স্বল্পশিক্ষিত, মানুষ কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গলদ্ঘর্ম হয়ে পড়ছেন।
যেমন অভিবাসন নীতি।
বিশ্বের অধিকাংশ ধনশালী দেশে উন্নয়নের জোয়াল বইতে হয় অভিবাসী শ্রমিকদের। ঐতিহাসিক ভাবেই একথা সত্য। তার উপর সাম্প্রতিক কালে প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির ফলে পশ্চিমী দেশের নানাবিধ পরিষেবার ভার চলে আসছে ভারতবর্ষের মতন বহু উন্নয়নশীল দেশে যেখানে শুধু মজুরি কম নয়, শিক্ষিত মানুষদের পরিশ্রমক্ষমতা এমনকি সময়বিশেষে কর্মদক্ষতাও পশ্চিমের মানুষদের তুলনায় বেশি। ধনতান্ত্রিক দেশের শিল্পপতিরা সে কথা জানেন বলেই আরও বেশি লাভের আশায় তাঁরা হয় উদার অভিবাসন নীতির পক্ষে সওয়াল করছেন অথবা কাজ পাঠিয়ে দিচ্ছেন এশিয়ার বিভিন্ন দেশে।

ফলস্বরূপ, বহু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ আমেরিকার মতন দেশে কর্মচ্যুত হচ্ছেন। বিপন্ন হচ্ছে তাঁদের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা, কারণ কর্মদক্ষতার তুলনায় এঁদের শ্রমমূল্য অত্যধিক। এই সমস্যার কোনও স্বল্পমেয়াদি সমাধান নেই। আউটসোর্সিং এর ফলে মার্কিনি গ্রাহক উন্নত পরিষেবা পাচ্ছেন, সঙ্গে বাড়ছে কোম্পানিগুলির মুনাফার পরিমাণ কিন্তু অপেক্ষাকৃত অদক্ষ মানুষ মূল জীবিকা হারিয়ে নিম্নমানের অন্য কোনও চাকরিতে যোগ দিচ্ছেন। এই সমস্যার আংশিক সমাধান হতে পারে যদি দেশের সরকার চেষ্টা করেন এই সমস্ত কাজ হারানো মানুষদের নতুন প্রযুক্তির জ্ঞানে দীক্ষিত করে তুলতে। দক্ষতা বাড়লে তাঁদের শ্রমের মূল্যও বাড়বে। কিন্তু এটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, এবং সে পরিকল্পনায় দরকার যথেষ্ট সরকারী বিনিয়োগ। অধিকাংশ সরকারই সে খরচে রাজি নন। রাজনৈতিক কারণে দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করতেও তাঁরা গররাজি।
কর্মচ্যুত মানুষজন কিন্তু এই বহুমাত্রিক সমস্যাটি তলিয়ে দেখছেন না। তাঁরা শুধুই দেখছেন নিজের দেশের শ্রমবাজারে তাঁদের কদর নেই, আর বিদেশী মানুষেরা ক্রমেই দখল করে নিচ্ছেন তাঁদের কর্মপরিসরটি। অর্থাৎ বিদেশীরাই তাঁদের দুর্দশার মূল কারণ। এই যে একমাত্রিকতার ফাঁদ, এরই ফায়দা তোলেন পোড় খাওয়া রাজনৈতিক নেতারা। তখন তাঁরা রাজনৈতিক স্বার্থে এক অদৃশ্য, বিদেশী জুজুকে তুলে ধরেন, আক্রমণ করেন ভিনদেশি ধর্ম-কৃষ্টি-সভ্যতাকে। ফলে সে দেশের মানুষরা ভুলে যান যে বিদেশী শ্রমিকদের শ্রম বিনা একবিংশ শতকের যুগোপযোগী জীবনযাত্রা সম্ভব নয়। শুরু হয় মেরুকরণ প্রক্রিয়া।
প্রাকৃতিক উষ্ণায়ন আর একটি উদাহরণ। একটি বৈজ্ঞানিক সত্য কিন্তু তার বিরুদ্ধে লড়তে গেলে যে কঠিন অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলি নিতে হবে সেগুলি তথাকথিত উদারচেতা মানুষরাও মেনে নিতে পারেন না, কারণ অদূর ভবিষ্যৎ-এ সেই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের জীবনযাত্রার মান ব্যাহত হতে পারে। বিলাসবহুল বড় গাড়ির কারখানাই হোক বা তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র, মাত্রাছাড়া গ্রিনহাউস গ্যাস উৎপাদনের ফলে বাতাসে বিষের পরিমাণ বাড়তে থাকে। কিন্তু যখনই গ্রিন ট্যাক্সের প্রস্তাব আসে, মানুষ অখুশি হন। সরকারী পরিবহণ মাধ্যমের ওপর ভরসা রাখতে বললে বা ফ্যাশন থেকে শুরু করে আমিষাশী খাদ্যসম্ভারে কাটছাঁট করার উপদেশ দিলে, অনেক মানুষই ভেবে বসেন এসব নেহাতই বৈপ্লবিক চিন্তাভাবনা।
এই যে একমাত্রিকতার ফাঁদ, এরই ফায়দা তোলেন পোড় খাওয়া রাজনৈতিক নেতারা। তখন তাঁরা রাজনৈতিক স্বার্থে এক অদৃশ্য, বিদেশী জুজুকে তুলে ধরেন, আক্রমণ করেন ভিনদেশি ধর্ম-কৃষ্টি-সভ্যতাকে।
উষ্ণায়ন হোক বা আগ্নেয়াস্ত্র আইন, বৈদেশিক বাণিজ্য হোক বা অভিবাসন নীতি,মানুষ সর্বদাই জটিল প্রশ্নের সরল, একমাত্রিক উত্তর খুঁজতে থাকেন। বিজ্ঞানী বা চিন্তাবিদদের পক্ষে এই একমাত্রিক উত্তর দেওয়া সম্ভব না হলেও বহু রাজনীতিবিদ এই উত্তর দেওয়ার ক্ষমতার মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন এক সফল ভবিষ্যৎ। তাঁরা চেষ্টা করছেন হ্যাঁ বা না, ভাল বা মন্দ, ঠিক বা বেঠিক জাতীয় সরাসরি এবং সরলতম উত্তরের মাধ্যমে ভোটারদের ধন্দ দূর করার। যারা জনসাধারণের এই ধন্দ ছলেবলেকৌশলে দূর করছেন, অ্যাডভান্টেজ সেই সব রাজনৈতিক নেতাদের। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এই ধন্দের নাম কগনিটিভ ডিসোন্যান্স (Cognitive dissonance)। সেই ধন্দকে অবৈজ্ঞানিকভাবে কমাতে গিয়ে তাই ফেসবুক, ট্যুইটার, হোয়াটসঅ্যাপ জাতীয় সোশ্যাল মিডিয়ায় ফেক নিউজের ছড়াছড়ি।
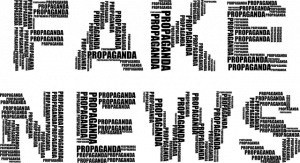
অল্পবিস্তর কগনিটিভ ডিসোন্যান্স আমাদের সবার মধ্যেই আছে। বহুমাত্রিক উত্তর নিয়ে আমাদের এই সমস্যা চিরকালীন। বুদ্ধিমান, যুক্তিবাদী মানুষও এই সমস্যার সম্মুখীন হন। কেন? অর্থনৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা দেখাচ্ছে যে আমাদের যুক্তিযুক্ত চিন্তাধারারও একটি পরিসীমা আছে। প্রবল আবেগ হোক বা অতিরিক্ত ঝুঁকির সম্ভাবনা, একাধিক কারণে আমাদের যুক্তিবাদী সত্তাটি দুর্বল হয়ে পড়ে। অনেক সময় আবার দীর্ঘমেয়াদী লাভ-ক্ষতির হিসেবনিকেশ এতই জটিল হয়ে পড়ে, আমরা একটি সরল উত্তরের জন্য হাপিত্যেশ করে বসে থাকি। আমাদের এই মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতার সুযোগটিই আজকের রাজনীতিবিদরা পূর্ণমাত্রায় নিচ্ছেন। তাঁরা জানেন ডাহা মিথ্যা কথা আজকের শিক্ষিত মানুষ শুনবেন না। ‘মানুষ চাঁদে কোনওদিন যায়নি’ বা ‘ইহুদীরা বাচ্চা ছেলেমেয়ের রক্ত চুষে খায়’ জাতীয় গতযুগের মিথ্যা কথা একুশ শতকে ভাইরাল হবে না। কিন্তু একমাত্রিক খবর বা কার্যকারণ সম্পর্কটিকে বিকৃত করে তোলা কোনও আপাতসত্য কিন্তু আদতে মিথ্যা খবর মানুষ বিশ্বাস করবেন। শুধু নিজেরাই পড়বেন না, পড়াবেন তাঁদের আত্মীয়-বন্ধু-পরিচিতজনদেরও। তাই দেখি মার্কিনী রাজনীতিবিদরা যুক্তি দেখান গত তিরিশ বছরে আমেরিকানদের হাতে থাকা আগ্নেয়াস্ত্রর সংখ্যা বেড়েছে বলেই ওই একই সময়ে অপরাধের সংখ্যাও কমেছে। যেটা তাঁরা বলেন না, ওই তিরিশ বছরেই কিন্তু অপরাধপ্রবণ এলাকাগুলিতে আমেরিকান সরকার শিক্ষা এবং সুরক্ষায় প্রভূত বিনিয়োগ করেছেন। ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতেও শুনতে পাই, ডিমানিটাইজেশনের দরুণ কালো টাকা ফিরে আসবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে। সুচতুর ভাবে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আড়াল করা হয় – ভারতীয় কালো টাকার অধিকাংশটাই বিদেশী ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখা, ডিমানিটাইজেশনের কোনও প্রভাবই সেই গচ্ছিত টাকার ওপর পড়বে না।
মেরুকরণের রাজনীতিকে মূর্ত করে তুলতে গত শতকের শেষ অবধি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের সমর্থকদের নিয়ে চালাত কিছু ধ্বংসকামী অভিযান, যার অধিকাংশই হত পূর্বপরিকল্পিত। হিটলারের আমলে ইহুদীনিধন হোক বা দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে কমিউনিস্টদের হত্যা বা ভারতে বাবরি মসজিদ ধ্বংস, এরকম বহু ইতিহাস সেই উগ্রতার সাক্ষ্য দেয়। একুশ শতকে প্রযুক্তির দৌলতে কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলিকে সবসময় পরিকল্পনা করে এহেন হিংসায় সামিল হতে হয় না। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভেসে আসা অফুরন্ত একমাত্রিক ফেক নিউজের দরুণ এহেন হিংসা যে কোনও মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়তে পারে। ফেসবুক, ট্যুইটার বা হোয়াটসঅ্যাপ তাই এক হিসাবে মেরুকরণের রাজনীতির পথ আরও প্রশস্ত করেছে। হিংসার মাত্রাটিকেও বাড়িয়ে তুলছে।
প্রযুক্তির দৌলত অগণিত সমমনস্ক মানুষ প্রায় একই সময়ে খবরগুলো পাচ্ছেন। মূহর্তের মধ্যেই, মানুষগুলির পূর্বনির্ধারিত মতামত সর্বসমক্ষে স্বীকৃতি পাচ্ছে, ফলে ব্যক্তিগত পক্ষপাত হয়ে দাঁড়াচ্ছে গোষ্ঠীগত বিশ্বাস।
সমস্যা আরও প্রকট হয়ে দাঁড়াচ্ছে কারণ সেই আদিম কাল থেকে মানুষের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তনির্ধারণে গোষ্ঠী একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। আপনি হয়ত ভাবেন যে কোনও পরিস্থিতিতেই সাধারণ মানুষের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র থাকা উচিত নয়। অথচ দিনভর বন্ধু, আত্মীয়, পরিচিতরা যদি ফেসবুক বা ট্যুইটারে জানাতে থাকেন ভিনদেশী, ভিনধর্মী আততায়ীদের হাত থেকে বাঁচতে হলে আগ্নেয়াস্ত্র রাখা ছাড়া গতি নেই তখন আপনার মনে একটা খটকা আসতে বাধ্য। এক অদৃশ্য বিপদ হয়ত আপনাকেও তাড়িত করে তুলবে। এবং এই একই ঘটনা দিনের পর দিন ঘটতে থাকলে এক সময় আপনি নিজের বিশ্বাসের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলে বেছে নিতে পারেন সেই মতটিই যা জনমানসে প্রাধান্য পাচ্ছে। শেষ এক দশক ধরে দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ ক্ষমতাসীন সরকার ও রাজনৈতিক দল অগুনতি টাকার বিনিময়ে জেনে নিচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের পছন্দ-অপছন্দের ইতিবৃত্তান্ত, আর তারপর আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সহায়তায় তাদের অ্যাকাউন্টে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পৌঁছে দিচ্ছে অজস্র ভুয়ো খবর যা জটিল সব প্রশ্নের একমাত্রিক এবং মিথ্যা উত্তরের জাল বুনে চলেছে। প্রযুক্তির দৌলত অগণিত সমমনস্ক মানুষ প্রায় একই সময়ে খবরগুলো পাচ্ছেন। মূহর্তের মধ্যেই, মানুষগুলির পূর্বনির্ধারিত মতামত সর্বসমক্ষে স্বীকৃতি পাচ্ছে, ফলে ব্যক্তিগত পক্ষপাত হয়ে দাঁড়াচ্ছে গোষ্ঠীগত বিশ্বাস। প্রযুক্তির অপব্যবহারের এখানেই শেষ নয় অবশ্য। সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখা যাচ্ছে হাজার হাজার মানুষ এসে কিছু নির্দিষ্ট খবরে ‘লাইক’ দিয়ে গেছেন বা শেয়ার করেছেন, জানাচ্ছেন ঘোরতর সমর্থন। কিন্তু আপনি ঘুণাক্ষরেও টের পাচ্ছেন না ওই হাজার হাজার প্রোফাইলের অনেক কটিই ভুয়ো। সৌজন্যে রাজনৈতিক দলগুলির আই-টি সেল। তারা শুধু প্ররোচনামূলক এবং মিথ্যা খবরই পরিবশন করছে না, উপরন্তু ভুয়ো প্রোফাইল বানিয়ে ছয়লাপ করে তুলছে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম। প্রযুক্তির প্রভাবে নিজের মতাদর্শ ভুলে মানুষ ঝুঁকে পড়ছেন সংখ্যাগরিষ্ঠের মতাদর্শের দিকে, অর্থনীতির পরিভাষায় যাকে বলা যায় ‘আর্টিফিশিয়াল হার্ডিং বিহেভিয়র’ (‘Artificial herding behaviour’)।
অর্থবান রাজনৈতিক দলগুলির মদতে প্রযুক্তির এই অপব্যবহার শুধু উন্নত দেশ নয়, উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্যও মারাত্মক বিপদ ডেকে আনছে। ভারতে ২০১৯-র লোকসভা নির্বাচনে বা বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের সময় দেখা গেছে সোশ্যাল মিডিয়া ছেয়ে যাচ্ছে ভুয়ো খবরে। সময় সময় সরকারী নীতিকে সমর্থন যোগানোর জন্য মূলধারার সংবাদপত্র বা টিভি চ্যানেল-ও পরিবেশন করছে উদ্ভট এবং বিপদজনক সব খবর। ২০১৬-য় ডিমানিটাইজেশনের সময় এরাই জানিয়েছিল নতুন নোট নিয়ে আসা হচ্ছে কারণ সেই নোটে লুকিয়ে থাকা মাইক্রোচিপ ব্যবহার করে সরকার অতি সহজেই কালো টাকার চোরাকারবারিদের পাকড়াও করবেন। এহেন গাঁজাখুরি খবর-ও কিন্তু বহু মানুষ মেনে নিয়েছিলেন এবং এক অন্ধ বিশ্বাসে শেয়ার করেছিলেন নিজেদের ফেসবুক টাইমলাইন বা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে। পশ্চিমবঙ্গেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। চলতি বিধানসভা নির্বাচনেও, এরকম অজস্র একমাত্রিক খবর পেশ করে মানুষকে দলে টানার চেষ্টা করে চলেছে রাজনৈতিক দলগুলি।
আন্তর্জালিক প্রযুক্তির প্রসারণের ফলে শেষ কয়েক দশকে বিশ্বের নানান প্রান্তের মানুষ পরস্পরের কাছে চলে এসেছেন, কিন্তু এই নতুন প্রযুক্তি বিগত দিনের উৎপাদন প্রক্রিয়াকে অনেক ক্ষেত্রেই অচল করে দিয়েছে। এর ফলে বহু মানুষ, যাঁরা পুরনো প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল ছিলেন, বর্তমানে কর্মহীন এবং চূড়ান্ত অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে ভুগছেন। অন্যদিকে উন্নয়নশীল দেশগুলির সামাজিক অসাম্য এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য বহু মানুষকে এখনও রেখে দিয়েছে এক মধ্যযুগীয় ঘেরাটোপের ভেতর। এই দিশেহারা মানুষগুলির অসহায়তা এবং ক্ষোভের সুযোগ পূর্ণ সুযোগ নিচ্ছেন উগ্র, মূলত দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক নেতারা। পূর্ববিশ্লেষিত ওই মেরুকরণ প্রক্রিয়ায় তাঁরা সমাজকে আরওই বিভাজিত করছেন। এবং এ কাজে বিশেষ ভূমিকা নিচ্ছে ফেক নিউজ। সোশ্যাল মিডিয়াগুলি ওপর ওপরে গণতন্ত্রের মুখোশটি রেখে দিলেও সেই মুখোশের আড়ালে কিন্তু কাজ করে চলেছে এক নয়া সামন্ততন্ত্র। প্রবল অর্থশালী নেতাদের হয়ে ভাড়া খেটে আই-টি সেল ছড়িয়ে দিচ্ছে একের পর এক ভুয়ো খবর।
উন্নয়নশীল দেশগুলির সামাজিক অসাম্য এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য বহু মানুষকে এখনও রেখে দিয়েছে এক মধ্যযুগীয় ঘেরাটোপের ভেতর। এই দিশেহারা মানুষগুলির অসহায়তা এবং ক্ষোভের সুযোগ পূর্ণ সুযোগ নিচ্ছেন উগ্র, মূলত দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক নেতারা।
এই ফাঁদ থেকে বেরনোর জন্য অবিলম্বে দরকার সোশ্যাল মিডিয়াগুলির নিরপেক্ষ এবং পেশাদারি মনোভাব। যদিও উপযুক্ত আইন প্রণয়ন না হলে সে মনোভাব নাও আসতে পারে। গত অগস্ট মাসে জানা গেছিল ফেসবুকের এক উচ্চপদস্থ কর্মীর মদতে তেলেঙ্গানার জনৈক রাজনৈতিক নেতা সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত বিষোদ্গার চালিয়ে গেছেন ফেসবুকে। প্রবল জনমতকে উপেক্ষা করে সেই কর্মী চাকরি টিঁকিয়ে রাখতে না পারলেও ফেসবুক এ ঘটনা থেকে আদৌ কোনও শিক্ষা নিয়েছে কিনা তা নিয়ে বিস্তর সংশয় রয়ে গেছে। বলা বাহুল্য যে সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিগুলোর জনমুখী চিন্তার ওপর আর আস্থা রাখা সম্ভব নয়, তাইi দরকার নির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন ও তার পালন। নির্বাচনের সময় যেহেতু ভুয়ো খবরের রমরমা বাড়তে থাকে তাই নির্বাচনী কমিশনকেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রতি প্রার্থীর জন্য বিজ্ঞাপনী বাজেট বেঁধে দেওয়া থাকলেও প্রতিটি দল সোশ্যাল মিডিয়ায় কত টাকা খরচ করতে পারবে বা দলগুলির প্রক্সি অ্যাকাউন্ট থেকে আদৌ বিজ্ঞাপন দেওয়া যাবে কিনা বা ভুয়ো খবর পরে তুলে না নিয়ে শুরুতেই কিভাবে আটকানো যায়, এধরনের বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় এসে গেছে।
আজকের আইন অবশ্য আগামীকাল কাজ নাই দিতে পারে। নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে সঙ্গে আসবে নতুন আইনি ফাঁকফোকর-ও। তাই আরও গভীরে যাওয়া প্রয়োজন। ভাবা দরকার নিজেদের মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতাগুলি নিয়ে। আমাদের মতাদর্শ নিরপেক্ষ হওয়ার দরকার নেই, কিন্তু পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট মতাদর্শে অনাবশ্যক গুরুত্ব দেওয়া আমরা বন্ধ করতে পারি। এক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যমগুলি বিশেষ ভূমিকা নিতে পারে। ব্যবসায়িক স্বার্থেই আজ বহু সংবাদপত্র ভুয়ো খবর ভাইরাল হতে দেখলেই তাঁদের পাঠকদের সতর্ক করে দিচ্ছেন। ফলে পাঠক এবং সংবাদপত্রের মধ্যে নতুন করে একটা বিশ্বাসের সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে। হাতে গোনা কিছু সংবাদপত্রের নতুন করে এক গ্রহণযোগ্যতাও তৈরি হচ্ছে। সামাজিক মাধ্যমগুলি এই একই পন্থা অনুসরণ করতে পারে। ট্যুইটারের মতন সামাজিক মাধ্যম এ কাজে অনেকটা সফল হয়েওছে। প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমশই দেখতে পাচ্ছে মিথ্যা কথার বেসাতি না করেও ব্যবসায়িক মুনাফা তোলা যায়। সত্যি এবং যুক্তিনিষ্ঠ খবরের সম্প্রচারও যে ব্যবসার মূলধন হয়ে দাঁড়াতে পারে সে কথা বুঝতে পারছে আরও অনেক সামাজিক মাধ্যম। ভুয়ো খবরের হাত ধরে যে মেরুকরণের রাজনীতি ক্রমেই জাঁকিয়ে বসছে তার থেকে মুক্তির আশা তাই করা যেতেই পারে, কিন্তু সে মুক্তিকে ত্বরান্বিত করতে দরকার এক সার্বিক সচেতনতা। সংবাদ উৎপাদক, সংবাদ উপভোক্তা এবং সরকার – সচেতন হওয়ার দায় আমাদের সবার।
ছবি সৌজন্য Pixabay
সঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় নটিংহ্যাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রবীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।
























One Response
যুক্তিপূর্ণ ও তথ্যনির্ভর বিশ্লেষণ। বহুদিন ধরে একটি ভালো নিবন্ধন প্রকাশ করার যে কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ।