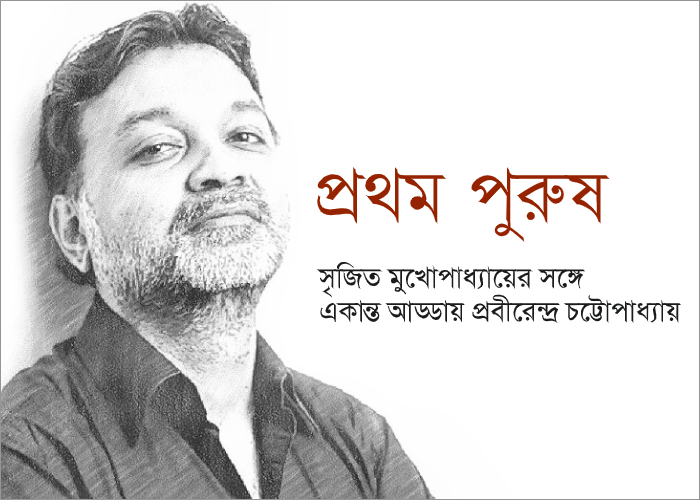শূূূন্য দশকের শুরুতে দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় একই সময়ে পড়াশোনা করেছিলেন সৃজিত মুখোপাধ্যায় এবং প্রবীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সৃজিত দু’বছরের সিনিয়র হলেও একসঙ্গে ক্যুইজ, নাটক ইত্যাদি অনেক কিছুই করেছিলেন দু’জনে। পেশায় কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রবীরেন্দ্র শেষ সতেরো বছর প্রবাসে কাটালেও খুব আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ করেছেন বাংলা চলচ্চিত্র জগতে সৃজিতের লাগাতার উত্থান। হয়তো সেই আগ্রহ থেকেই জমে উঠেছিল অনেক প্রশ্ন। এই বছরের ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সেই সব প্রশ্ন নিয়েই প্রবীরেন্দ্র আড্ডা জমিয়েছিলেন সৃজিতের সঙ্গে। ‘ফেলুদা ফেরত’ ওয়েবসিরিজ নিয়ে চূড়ান্ত ব্যস্ততার মধ্যেও সময় বার করেছিলেন সৃজিত। সেই আড্ডা ছাপার অক্ষরে রইল বাংলালাইভের পাঠকদের জন্য। বাংলা সিনেমার অন্যতম সফল পরিচালক নির্দ্বিধায় উত্তর দিয়েছেন সব প্রশ্নের। অনুপম রায়ের গানের মতোই গভীরে ঢুকে আত্মদর্শন করেছেন। নিজে ভেবেছেন। ভাবিয়েছেন প্রবীরেন্দ্রকেও।
শূূূন্য দশকের শুরুতে দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় একই সময়ে পড়াশোনা করেছিলেন সৃজিত মুখোপাধ্যায় এবং প্রবীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সৃজিত দু’বছরের সিনিয়র হলেও একসঙ্গে ক্যুইজ, নাটক ইত্যাদি অনেক কিছুই করেছিলেন দু’জনে। পেশায় কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রবীরেন্দ্র শেষ সতেরো বছর প্রবাসে কাটালেও খুব আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ করেছেন বাংলা চলচ্চিত্র জগতে সৃজিতের লাগাতার উত্থান। হয়তো সেই আগ্রহ থেকেই জমে উঠেছিল অনেক প্রশ্ন। এই বছরের ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সেই সব প্রশ্ন নিয়েই প্রবীরেন্দ্র আড্ডা জমিয়েছিলেন সৃজিতের সঙ্গে। ‘ফেলুদা ফেরত’ ওয়েবসিরিজ নিয়ে চূড়ান্ত ব্যস্ততার মধ্যেও সময় বার করেছিলেন সৃজিত। সেই আড্ডা ছাপার অক্ষরে রইল বাংলালাইভের পাঠকদের জন্য। বাংলা সিনেমার অন্যতম সফল পরিচালক নির্দ্বিধায় উত্তর দিয়েছেন সব প্রশ্নের। অনুপম রায়ের গানের মতোই গভীরে ঢুকে আত্মদর্শন করেছেন। নিজে ভেবেছেন। ভাবিয়েছেন প্রবীরেন্দ্রকেও।
প্রবীরেন্দ্রঃ ফিল্মমেকিং নিয়ে সত্যজিৎ বা তোমার ‘পেট্রোনাস’ তপন সিনহার লেখাপত্র পড়ে মনে হয়েছে একজন পরিচালকের টেকনিক্যাল নলেজটাও থাকা খুব দরকার। তপন সিনহা নিজেই জানিয়েছেন সত্যজিৎ একাধিকবার ওনার কাজ দেখে টেকনিক্যালি সন্তুষ্ট হতে পারেননি, সমালোচনা করেছেন। তো আলোই বলো বা শব্দ, তুমি টেকনিক্যাল নলেজটুকু আয়ত্তে কিভাবে আনলে?
সৃজিতঃ টেকনিকের ব্যাপারে আমি একেবারে ‘মাগল’। আচ্ছা, মাগল হয়তো নই, এতগুলো সিনেমা করে ফেলেছি যখন। কিন্তু মাডব্লাড তো বটেই। আমার পরিবারে না আছে কোনও উইজার্ড, না আছে কোনও উইচ। হগওয়ার্টস-এ আমি কোনও ক্লাসও করিনি। না পোশনস পড়েছি, না ডিফেন্স এগেন্সট ডার্ক আর্টস পড়েছি। আমার হাতে কিছুভাবে ২০১০ সালে একটা ম্যাজিক ওয়্যান্ড চলে এসেছিল। সেটা ঘুরিয়ে কিছু ভাবে একটা সিনেমা হয়ে গেছিল। কেন হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে সে নিয়ে কোনও আইডিয়া ছিল না……
প্রবীরেন্দ্রঃ কিন্তু তুমি যখন ক্যামেরায় চোখ রাখছ, লাইটটা কীভাবে পড়বে সে নিয়ে ন্যূনতম ভাবনাচিন্তা তোমাকে তো করতেই হবে। নয় কি?
সৃজিতঃ সেটা আমি বলে দিতে পারি। ওভার দ্য টাইম আমি শিখে গেছি। এখন আমি জানি HMI (Hydragyrum Medium-Arc Iodide) লাইট কাকে বলে। কখন স্টেডিক্যাম লাগবে আর কখন হ্যান্ডহেল্ড লাগবে সেটা বুঝতে পারি। কখন শ্যালো ফোকাস, কখন টপ লাইট আর কখন সিল্যুয়েট কাজ করবে সেটা ফিল করতে পারি। ডলি শট কোথায় ঢুকলে জমে যাবে আর কোথায়ই বা ফেসলাইট লাগবেনা সেটাও আস্তে আস্তে আয়ত্ত হচ্ছে। এটা খানিকটা ব্যাটিং এর মতন। কোন লেংথ আর লাইন এর বলে কী শট মারা উচিত এটা একটা সময়ের পর রিফ্লেক্সের পর্যায়ে পড়ে যায়।
প্রবীরেন্দ্রঃ এগুলো শিখলে কি অপর্ণা সেন বা অঞ্জন দত্তকে অ্যাসিস্ট করতে গিয়ে?
সৃজিতঃ ও বাবা, রিনা দি – অঞ্জন দা’দের পাগল করে দিয়েছিলাম। “রিনা দি, এটা কেন করছ?”, “অঞ্জন দা, এই শটটার কথাই কেন ভাবলে?”, প্রশ্নের পর প্রশ্ন। প্রশ্ন করলেই যে উত্তর সঙ্গে সঙ্গে পেতাম তা নয়। রিনাদি বল, “শোন ঋজু, আগে শটটা নিয়ে নি তারপর বলছি”। অঞ্জন দা হয়ত বললেন, “রাতের আসরে এক্সপ্লেন করব, এখন থাক”। কিন্তু উত্তরগুলো শুনেই ছাড়তাম। আর আমরা যারা একটা সায়েন্টিফিক ডিসিপ্লিনে পড়েছি তারা তো জানিই একটা নতুন ডিসিপ্লিনে কী করে দাঁত ফোটাতে হয় – প্রথমে একটা লিটারেচার রিভিউ করা দরকার, তারপর ডেটা কালেকশনের ব্যাপার, একটা মেথডলজি প্রোপোজ করতে হবে, শেষে একটা বিবলিওগ্রাফি দরকার। তো এখানেও একই ব্যাপার। লিটারেচার রিভিউ বলতে প্রচুর সিনেমা দেখেছি বা সিনেমা নিয়ে পড়েছি, হ্যান্ডস অন একটা ইন্টার্নশিপ করেছি অপর্না সেন বা অঞ্জন দত্তদের সঙ্গে, তারপর চাকরিতে নেমে নিজের কাজ নিজে করতে শুরু করেছি।

প্রবীরেন্দ্রঃ কিন্তু তোমারও নিশ্চয় সুব্রত মিত্ররা আছেন। বা তোমারও সুব্রত মিত্রদের দরকার পড়ে।
সৃজিতঃ অ্যাবসলিউটলি। আই ও আ লট টু সৌমিক হালদার। বোধাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকেও আমি প্রচুর সাহায্য পেয়েছি। অনেক কিছু জেনেছি।
প্রবীরেন্দ্রঃ সৌমিক বা বোধাদিত্যদের তুমি কি একেবারে ফ্রি-হ্যান্ড দিয়ে রাখো? সিনেমাটোগ্রাফি বা এডিটিং-এ তাঁরাই কী লিডিং রোল নিচ্ছেন?
সৃজিতঃ না, সবাই নিচ্ছেন না। এডিটিং একটা জায়গা যেখানে আমি ডমিনেট করি। আমি যদি প্রাইম মিনিস্টার হই, এডিটিং হল ডিফেন্স মিনিস্ট্রি, বা হোম মিনিস্ট্রি। সিনেমাটোগ্রাফি হয়ত রেলদপ্তর, সেখানে অনেকটা ফ্রী-হ্যান্ড দেওয়া যায়। অনেকে আমার সঙ্গে তাই কোলাবরেট করেন, অনেকে আবার আমার থেকে শেখেন-ও। অভিনেতাদের মধ্যেও সেই ব্যাপারটা আছে। অনেককে আমি ব্রিফ দিয়ে ছেড়ে দিই। তুমি তোমার মতন করো, আমি জানি সেখানে ভুল হওয়ার চান্স কম। আবার অনেককে হাতে ধরে শেখাতে হয়।
ভালো কথা, সৌমিক ছাড়া আরো কয়েকজনের নাম করতে চাই যাদের সঙ্গে কাজ করতে আমি ভালোবাসি। সুদীপ চ্যাটার্জী, গৈরিক সরকার। এডিটিং-এ আমি প্রণয় দাশগুপ্তর সঙ্গে কাজ করে খুব খুশি। অনুপম রায়ের মিউজিক নিয়ে তো আর বলারই কিছু নেই।
প্রবীরেন্দ্রঃ বেশ। প্রসঙ্গান্তরে যাই। তোমার থেকে কী নিটোল কমেডি আমরা কখনো আশা করতে পারি? ‘গল্প হলেও সত্যি’, ‘ধন্যি মেয়ে’ কী ‘শ্রীমান পৃথ্বীরাজ’ ধরণের? অফ কোর্স, ট্রীট্মেন্ট বা প্লট কনটেম্পোরারি হবে। কমেডিটা এই কারণেই আলাদা করে বলছি কারণ বাংলা সিনেমায় ভালো কমেডির অনেকদিন ধরেই বেশ আকাল। ‘ভূতের ভবিষ্যৎ’ এর মতন সিনেমা শেষ দশ-পনেরো বছরে আর ক’টাই বা বেরিয়েছে। শুধু সাটল কমেডি বলছি না, আমার ব্যক্তিগত ধারণা বাংলায় ফিজিক্যাল কমেডির স্বর্ণযুগটাও অনেকদিনই চলে গেছে। ফিজিক্যাল কমেডিগুলোর অধিকাংশই বড় স্থূলদাগের হয়, ভাঁড়ামোর পর্যায়ে চলে যায়। ফলে বুদ্ধিদীপ্ত দর্শকদের অধিকাংশই উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন।
সৃজিতঃ আমি না জানি না…
প্রবীরেন্দ্রঃ আমি আরোই তোমাকে প্রশ্নটা করছি কারণ আমি দেখেছি তোমার সিনেমায় হিউমর খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা নেয়।
সৃজিতঃ হ্যাঁ, খুবই ইম্পর্ট্যান্ট একটা রোল প্লে করে। গানেরও একটা বড় ভূমিকা থাকে। কিন্তু আশ্চর্যভাবে লোকে ভাবে আমি শুধু থ্রিলারই বানাই। কিন্তু পিওর কমেডি কোনওদিন বানাব কিনা জানি না। নেভার সে নেভার, কিন্তু এখনই কোনও প্ল্যান নেই। আমার ধারণা একজন পরিচালকের ব্যক্তিগত জীবন এই ডিসিশনগুলোর ব্যাপারে একটা ভূমিকা নেয়। যেমন ঋতুদা’র বাবা-মা চলে যাওয়ার পর ঋতুদার সিনেমা থেকে হিউমরটা আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। সিনেমাগুলো মৃত্যুমুখী হয়ে পড়ল। তখন ‘সব চরিত্র কাল্পনিক’ হচ্ছে, ‘দোসর’ হচ্ছে, ‘আবহমান’ হচ্ছে। তারপর যখন ঋতুদার সেক্সুয়াল ক্রাইসিসটা বেরিয়ে এল তখন এল ‘মেমোরিজ ইন মার্চ’, ‘আরেকটি প্রেমের গল্প’, ‘চিত্রাঙ্গদা’ ইত্যাদি। ক্লীয়রলি, ঋতুদার জীবনের বিভিন্ন ঘটনা তাঁর সিনেমাগুলোকে অ্যাফেক্ট করছে। একই ভাবে আমার জীবনে কী ঘটছে, তখন আমার মানসিকতা কী, সেগুলো আমার ফিল্মোগ্রাফিকে অ্যাফেক্ট করবে। তাই আমি কমেডি করব, না প্রচন্ড ডার্ক একটা থ্রিলার বানাব, নাকি পলিটিক্যাল সিনেমা বানাব নাকি কোনও স্যাটায়ার করব সেটা ডিপেন্ড করবে আমার নিজের জীবনের ওপর। তবে জেনারলি স্পীকিং একটা রোম্যান্টিক কমেডি ডিউ আছে, একটা সোশ্যাল স্যাটায়ার ডিউ আছে, বায়োপিক ডিউ ছিল কিন্তু গুমনামি এসেছে আর নটী বিনোদিনী আর চৈতন্যকে নিয়ে ডাবল বায়োপিকটা আসছে। ‘ফেলুদা’ আছে,’বহুরূপী’ আছে, ‘বিপিন চৌধুরীর স্মৃতিভ্রম’ আছে’। কাকাবাবু-ও আছে। বীণা দাসের বায়োপিক নিয়ে কাজ চলছে।
প্রবীরেন্দ্রঃ বাহ! বীণা দাসের বায়োপিক নিয়ে কী ওয়েবসিরিজ করছ?
সৃজিতঃ না, সিনেমা। এ ছাড়া একজন মা এবং দু’টো মেয়েকে নিয়ে একটি গল্পের কথা মাথায় আছে। ইট উইল বী আ রিভেঞ্জ স্টোরি।
প্রবীরেন্দ্রঃ তোমার ক্ষেত্রে প্রসেসটা কী? এই যে অফুরন্ত প্লট মাথায় আসছে, তুমি কী সেখান থেকে ঝাড়াইবাছাই করতে শুরু করো?
সৃজিতঃ সেটাও হয়। আবার ইম্প্রম্পটু-ও হয়ে যায়। যেমন এই কয়েকদিন আগেই অনুপমের বাড়িতে আমি – পরম – অনুপম আড্ডা মারছিলাম। কথায় কথায় ‘হেমলক ২’ চলে এল। সেই আলোচনা হতে হতেই একটা মিষ্টি প্লট বেরোলো। এই যে বেরোলো সেটা কিন্তু মাথায় রয়ে গেল। হয়ত তিন বছর পর একদিন সকালবেলা এই প্লটটাই মাথা চাগাড় দিয়ে উঠবে, আর আমি কাজ করতে বসে যাব।
প্রবীরেন্দ্রঃ আর তিন বছর পর যদি জেগে না ওঠে? তোমার কী খেরোর খাতা আছে যেখানে প্লটগুলো লিখে রাখো?
সৃজিতঃ (হাসি) খেরোর খাতা নেই, আমার আছে ম্যাকবুক। সেখানে ‘প্রোজেক্টস’ বলে একটা ফোল্ডার আছে। তবে অন্য অনেকের কিন্তু খেরোর খাতা আছে। অনুপমের ডায়েরিগুলো যেমন। এত এত গান লিখেছে, মোটা মোটা ডায়েরির সব পাতা শেষ। ব্যাঙ্গালোরেই প্রথম ডায়েরি শেষ হয়ে গেছিল। কলকাতায় আরো দুটো শেষ করে ফোর্থে ঢুকে গেছে। ও হাতেই লেখে।
প্রবীরেন্দ্রঃ ‘হেমলক ২’ যেহেতু এসে গেল, সিক্যুয়েল নিয়েই একটা প্রশ্ন করি। তুমি অনেকবারই বলেছ ‘নির্বাক’ তোমার খুবই প্রিয় সিনেমা। কিন্তু নির্বাকের বক্স-অফিস ব্যর্থতার পরেও কী তুমি ‘নির্বাক ২’ বানাবে?
সৃজিতঃ অবশ্যই। কোনও সন্দেহই নেই সে ব্যাপারে। ‘নির্বাক’ এর কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন কাল্ট ফলোয়িং। আমি তাদেরকে বলি “আপনারা হলে গেলেন না কেন? গেলে আরো ভালো লাগত”। (হাসি)
Bizzare ছবি বানাতে আমার খুব ভালো লাগে। আর ভাবতেও ভালো যে বাংলা সিনেমায় নেক্রোফিলিয়া নিয়ে কাজ হচ্ছে, সেলফ-লাস্ট নিয়ে কাজ হচ্ছে, একটা গাছ আর একটা মেয়ের মধ্যে প্রেম নিয়ে কাজ হচ্ছে। একটা গ্লাস সিলিং তো ভাঙ্গা হচ্ছেই, সেটা অস্বীকার করা যায় না। যদিও আমি খুব একটা অ্যানালাইজ করি না এই বিষয়গুলো নিয়ে।
প্রবীরেন্দ্রঃ সেক্স বা সেক্সুয়াল পলিটিকস কে তুমি আর কিভাবে বাংলা সিনেমায় আনতে চাও? ধরে ধরে যত ট্যাবু আছে সেগুলো ভাঙতে চাইবে? যে ট্যাবুর জন্য ‘ওল্ডবয়’ আমরা হিন্দিতে পুরোপুরি বানাতে পারি না, ‘জিন্দা’র মতন হাফ-ডান একটা সিনেমা হয়েই থেকে যায়।
সৃজিতঃ নির্বাক কিন্তু ট্যাবুকে অ্যাটাক করে না, বরং অডিয়েন্সকে এনগেজ করে। সেরকম সিনেমাই আমি বানাতে চাই। যখন নির্বাকের একটি চরিত্র মৃতদেহের প্রেমে পড়ছে, মৃতদেহ নিয়ে হ্যালুসিনেট করছে, বিয়ে করছে, তাকে নিয়ে হানিমুনে গেছে…এই সেক্সুয়াল পলিটিক্স, বা গাছের সেক্সুয়াল পলিটিক্স কিংবা অঞ্জন দত্তের চরিত্রটি যেমনভাবে নার্সিসিজমের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায় যেখানে সে নিজেই নিজের প্রতি ফিজিক্যালি অ্যাট্রাক্টেড এগুলো বিজার এবং এক্সট্রীম সেক্সুয়াল পলিটিক্স। আমি কিন্তু সেখানে সেক্সুয়াল পলিটিক্স নিয়ে একটা ডিসকোর্স লিখব ভেবে বসছি না। গল্পটাই আগে আসছে। রাজকাহিনী তে পার্টিশন পলিটিক্স নিয়ে যে তুমুল ফার্স আমি দেখিয়েছি সেখানেও ডিসকোর্স লেখার কোনও ইচ্ছে ছিল না।
প্রবীরেন্দ্রঃ গল্প তো প্রথমে থাকবেই। আমি যেটা জানতে চাইছি যে গল্পের খাতিরে যদি ইনসেস্ট আসে তুমি সেটা দেখাতে চাইবে বা পারবে?
সৃজিতঃ অবশ্যই দেখাব। যদি সিনেমায় দেখাতে নাও পারি, ওয়েবে তো হইহই করে দেখাব। থুড়ি, হইচই করে দেখাব (হাসি)। তুই কী ‘দ্বিতীয় পুরুষ’ দেখেছিস?
প্রবীরেন্দ্রঃ না , কলকাতায় এই অল্প কয়েকদিনের মধ্যে আর সময় বার করতে পারিনি।
সৃজিতঃ তাহলে আমি ডিটেইলসে কিছু বলছি না। এটকু বলতে পারি ‘দ্বিতীয় পুরুষ’ এর ক্লাইম্যাক্স দেখে কলকাতা অর্গানিক্যালি হাততালি দিয়ে উঠেছে। যে কটা শো আমি দেখেছি সব কটাতেই। পাঁচ বছর আগে এটা ভাবা যেত না।

প্রবীরেন্দ্রঃ ক্লাইম্যাক্সটা কি তাহলে তুমি আগে থেকেই ভেবে রাখো? নাকি ন্যাচারাল প্রসেসে শেষেই আসে?
সৃজিতঃ অনেক সময়েই ক্লাইম্যাক্সটা আগে আসে। মাঝে মাঝে পরে আসে। মাঝে মাঝে ক্লাইম্যাক্স থেকেই সিনেমাটা শুরু হয়। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেওয়ালে পিঠ থেকে যায়। তখন ভাবতে থাকি এবারে কী করে শেষ হবে (হাসি)! ‘দ্বিতীয় পুরুষ’ এর ক্ষেত্রে এটা একটা আলাদা, স্বতন্ত্র গল্প ছিল। পরে সেটাকে ‘বাইশে শ্রাবণ’ এর সিক্যুয়েল হিসাবে অ্যাডাপ্ট করা হয়। এতে অবশ্য ‘বাইশে ফ্যান ক্লাব’ এর সদস্যদের প্রভূত আপত্তি ছিল। আবার অনেকের আবদার-ও ছিল, ইনক্লুডিং মায় প্রোডিউসারস। তারা বহুবছর ধরে সিক্যুয়েল টার জন্য অনুরোধ করছিল। তাদের সাহ্যাযার্থে আর বহু মানুষের আবদার মেটাতে ঠিক করলাম গল্প দুটোকে ফিউজ করব। নিজের-ও ইচ্ছে ছিল অবশ্য। দেখতে ইচ্ছে করছিল অভিজিৎ পাকড়াশি কেমন আছে, সূর্য কেমন আছে। তার ওপর খোকা-র মতন একটা চরিত্র তৈরি করার প্রলোভন।
ন্যাচারাল প্রসেস প্রসঙ্গে এটাও বলে রাখা ভালো, আমার চরিত্ররা খুব অবাধ্য। আনন্দ কর যদি বলে “আমি প্রেম করব না। ভাঁড় মে যাও।“, আমাকে কাকুতিমিনতি করে বলতেই হবে, “তুমি এরকম করতে পারো না আমার সঙ্গে। আমি লেখক“। প্রবীর রায়চৌধুরীকে কিছুতেই বোঝাতে পারছি না বাংলা সিনেমায় স্ক্রীনে তুমি এরকম ভাবে কথা বলতে পারো না, এত গালাগালি দিতে পারো না! কিন্তু সে শুনবে কেন? সে তো এই ভাষাতেই কথা বলে অভ্যস্ত। চরিত্রগুলোর সঙ্গে আমার এই কন্টিনিউয়াস ডায়ালগ চলতেই থাকে।
প্রবীরেন্দ্রঃ প্রেসিডেন্সিতে তোমার থেকে দু’বছর জুনিয়র ছিল শমিত বসু। যে ‘সিমোকিন প্রফেসিজ’ সিরিজটা লিখে বেশ পপুলারিটি পেয়েছিল……
সৃজিতঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওর বই তো আছে আমার কাছে…
প্রবীরেন্দ্রঃ শমিতের একটা ইন্টারভিউতে পড়েছিলাম ও বলছে কোনও প্লট আসছেই না, আসছেই না, হঠাৎ একদিন দুম করে বলা নেই কওয়া নেই কোথা থেকে মাথায় বাল্ব জ্বলে উঠল…
সৃজিতঃ এপিফেনি। আমার হয় তো, ভয়ঙ্কর হয়। রাজকাহিনি ওয়জ এপিফেনাস। জয়া চ্যাটার্জীর ‘স্পয়েলস অফ পার্টিশন’ বলে একটা বই আছে। স্পয়েলস অফ পার্টিশনে একটা ডেঞ্জারাস লাইন আছে, যেটায় র্যাডক্লিফ লাইন একটা বা কয়েকটা বাড়ির মধ্যে দিয়ে গেছে বলা হচ্ছে। সেই জায়গাটা পড়তে পড়তেই আমার মাথায় ভিস্যুয়াল টা এসে গেছিল। হাফ অফ দ্য হোরহাউস ইজ ইন ইন্ডিয়া, দ্য আদার হাফ ইজ ইন পাকিস্তান। ‘উমা’-ও এপিফেনাস। একটা গোটা শহর একটা টার্মিনালি ইল বাচ্চার মুখে হাসি ফোটাবার জন্য ফেক ক্রিসমাসের আয়োজন করছে এই খবরটা পড়তে পড়তেই মাথায় খেলে গেল কলকাতা পারবে এরকম করতে? অমনি নকল দুর্গাপুজোর ইমেজটা চোখের সামনে চলে এল।
অন্যদের বললে ভাববে মিথ্যা কথা বলছি কিন্তু এপিফেনিগুলো যখন হয়, তারপর স্ক্রিপ্ট লিখতে সাত-আট দিনের বেশি সময় লাগে না। তারপর গোটা টীমকে শোনাতে একটু সময় লাগে। ফীডব্যাক নিই। হয়ত বলল, “এ জায়গাটা ভালো লাগছে না”, বা “এইখানটা কিচ্ছু হয়নি”।
প্রবীরেন্দ্রঃ এরকম কী হয়েছে যে তুমি পড়লে কিন্তু বাকিদের ফীডব্যাক এতটাই নেগেটিভ ছিল যে কাজটাই আর করলে না?
সৃজিতঃ (চিন্তামগ্ন) না, রিজেক্টেড হয়নি। তবে বিস্তর কাটাছেঁড়া অনেকবারই করতে হয়েছে। আবার উল্টোদিকে ‘জাতিস্মর’ বা ‘রাজকাহিনী’র স্ক্রিপ্ট শোনার পর সবাই চুপ করে বসেছিল। নড়াচড়াও করেনি বিশেষ। জাস্ট জিজ্ঞাসা করেছিল, “কবে করব? প্রি-প্রোডাকশন শুরু করে ফেলি?”। আমি আবার গণতন্ত্রে বিশ্বাস করলেও নিজেও স্ক্রিপ্ট নিয়ে খুব পজেসিভ।
প্রবীরেন্দ্রঃ ভেঙ্কটেশ-ও নিশ্চয় ফীডব্যাক দেয়? নাকি এখন তুমি যাই নিয়ে যাও সেটাকেই গ্রীন সিগন্যাল দিয়ে দেয়, অ্যাজ ইট ইজ?
সৃজিতঃ ফীডব্যাক দেয়। সবসময়ই দিয়ে এসেছে। কিন্তু সেটা আমি ঢোকাচ্ছি কী ঢোকাচ্ছি না সেটা আমার ওপরেই ডিপেন্ড করে, মানে আমি সেই ফীডব্যাকের সাথে এগ্রি করছি কিনা সেই ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। হ্যাঁ, সময় সময় তুমুল ঝগড়াও হয়ে গেছে। তিন দিন, চার দিন, ছ দিন ধরে নেগোশিয়েশন চলছে। তাতে আমারই আখেরে লাভ। স্ক্রিপ্টিং লজিক গেটস শার্পার।
আমার অ্যাসিস্ট্যান্টদের সাথেও যে এ ব্যাপারটা হয় না তা নয়। আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর সৌম্য এত সিনিক্যাল যে ওকে আমার স্ক্রিপ্ট শোনাতেই ভয় লাগে (হাসি),বলেও দেয় “তোমার না এটা একদম হয়নি, আবার লেখো”! কিন্তু ইউ নীড সাচ পীপল! আজ তুই মন্দারমণি ঘুরতে গিয়ে একটা ব্লগ লিখলি, নিজের খেয়ালেই লিখলি। তখন সেটার ভাষা বা সাহিত্যগুণ নিয়ে কিছু ভাবিস নি। কিন্তু সেই লেখাটাই ছেপে বার হওয়ার সময় তোর ভাষা বা সাহিত্যগুণ নিয়ে ফীডব্যাক দরকার, তাই না? এমনকি বানান ভুল হয়ে থাকলে সেটাও ধরিয়ে দেওয়ার লোক দরকার। ফিল্মটা এক ব্লগ বা র্যাদার ভ্লগের মতন।
তবে লেখার সময়ে অত ভাবনাচিন্তা করলে চলবে না। লিখতে হবে জে-কে-রাউলিং এর মতন। আনইন্টারাপ্টেড।
প্রবীরেন্দ্রঃ আমাদের এই লম্বা আড্ডাটা শেষের দিকে এসে গেছে। কিছু কনক্লুডিং প্রশ্ন করি। সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের কাছে অনেক সাফল্যই এসেছে। আমার ব্যক্তিগত মত, তোমার জন্য যে বাংলা রিমেক সিনেমার জায়গাটা চলে গেছে সেটাই তোমার সবথেকে বড় সাফল্য। তুমি বাংলা সিনেমায় আসার পর আর দক্ষিণী সিনেমার রিমেক টলিউডে প্রায় দেখাই যায় না। আমার এই অ্যাসেসমেন্টের সঙ্গে তুমি কি একমত হবে?
সৃজিতঃ হ্যাঁ, আনডাউটেডলি। আয়্যাম ভেরি হ্যাপি অ্যাবাউট দ্যাট। বাংলা রিমেকের সঙ্গে যারা জড়িয়ে ছিল, সে পরিচালক হোক কী অভিনেতা-অভিনেত্রী হোক কী টেকনিশিয়ানস হোক, তারা সবাই কিন্তু এখন মৌলিক বাংলা সিনেমা নিয়েই কাজ করছে। সব কটা ছবি সাকসেস্ফুল হচ্ছে না কিন্তু আমরা সবাই চেষ্টা করছি কনটেন্ট-ড্রিভন, মীনিংফুল সিনেমা করার। ওই ভিশাস ট্রোপ অফ সিন টু সিন রিমেক অফ সাউথ ইন্ডিয়ান মুভিজ থেকে বেরোনো গেছে।
প্রবীরেন্দ্রঃ আর প্রযোজকরাও সেই চেষ্টাটাকে সমর্থন যোগাচ্ছেন?
সৃজিতঃ হ্যাঁ। ফোকাসটাই এখন ডিরেক্টরদের দিকে ঘুরে গেছে। আজকে কিন্তু সৃজিতের সিনেমা বা কৌশিক গাঙ্গুলির সিনেমা বা শিবপ্রসাদ-নন্দিতার সিনেমা বা অরিন্দম শীলের সিনেমা বলেই লোকে চিনছে। কোনও সুপারস্টারের নামে নয়।
প্রবীরেন্দ্রঃ তুমি আগেই বলেছ বিশেষ কিছু ভেবে তুমি টলিউডে সিনেমা করতে আসোনি। কিন্তু এই রিমেকের ট্রেন্ডটা কে সরাতে হবে বা বাংলা সিনেমার ফোকাসটা পরিচালকদের দিকে ঘোরাতে হবে এরকম কোনও স্বপ্ন কি ছিল তোমার? তেত্রিশ বছর বয়সে তুমি সিনেমা বানাতে এলে, তার আগের এক-দু বছরে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে কোনও ভাবনাচিন্তা করেছিলে?
সৃজিতঃ একত্রিশ বছরে আমার স্বপ্ন ছিল আমার বত্রিশের জীবনটাকে কেন্দ্র করে। তখন হয়ত স্বপ্ন দেখছি আমার বত্রিশ বছর বয়সে ফেলুদা নিয়ে একটা নাটক মঞ্চস্থ করতে হবে, সাকসেস্ফুলি। যে নাটকটা মিনিংফুল হবে, কর্পোরেট মডেলকে ফলো করে টাকা আনবে, এবং আমাকে সৃষ্টিশীলতার আনন্দ দেবে। ‘ফেলুদা ফেরত’ হ্যাপেনড। তারপর স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম আমাকে সেলফ-এমপ্লয়েড হতে হবে। চাকরিটা ছেড়ে দিলাম। কিন্তু দেখলাম নাটকে গল্প বলতে কিছু অসুবিধা হচ্ছে, তখন স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম সিনেমা বানাতে হবে……
প্রবীরেন্দ্রঃ বুঝতে পারছি যে রিমেকের ট্রেন্ডটা সরাতে হবে এরকম কোনও স্বপ্ন তুমি দেখোনি। কিন্তু সমসাময়িক বাংলা সিনেমার একজন দর্শক হিসাবে এই গাদা গাদা রিমেক দেখে তোমার মধ্যে কী কোনও হতাশা আসত বা রাগ?
সৃজিতঃ না, কোনও হতাশা ছিল না। কোনও রাগ ছিল না। কোনও বিপ্লবী চিন্তাভাবনা ছিল না। হ্যাঁ, সিনেমাগুলো মোটের ওপর হতাশ করছিল হয়ত কিন্তু ব্রিলিয়ান্ট কিছু টেলিফিল্ম হচ্ছিল তখন। সেগুলো দেখে খুব ইন্সপায়ারড হতাম। কৌশিক গাঙ্গুলি বা অঞ্জন দত্তর সেই সব টেলিফিল্মে তখন দাপটের সঙ্গে অভিনয় করছেন কৌশিক সেন, চূর্ণী গাঙ্গুলি বা রজতাভ দত্তের মতন অভিনেতারা। ঋতুদা তখনও সিনেমা বানাচ্ছেন, অঞ্জন দা ‘বং কানেকশন’ বানাচ্ছেন, সেগুলো দেখেও ইন্সপায়ারড হচ্ছি। কিন্তু এর বাইরে আর কোনও কারণ ছিল। তারপর জাস্ট হয়ে গেল, হয়ে গেল, হয়ে গেল। এটাও জানি একদিন আসবে যেদিন হবে না, হবে না, হবে না। সেদিন অন্য কিছু হবে। (হাসি) আমি জানি শুক্রবারের ম্যাজিকটা একটা শুক্রবার থেকে আর আসবে না। আমি সেই শুক্রবারের জন্য মানসিক ভাবে প্রস্তুত।
প্রবীরেন্দ্রঃ তুমি যখন শুরু করেছিলেন তখনকার হিসাবে ইন্ডাস্ট্রির পাথ টা শিফট করে গেছে। সেটা তোমার নিজের ম্যাজিকেই হতে পারে বা তোমার সমসাময়িক সমস্ত ভালো পরিচালকদের সমষ্টিগত প্রচেষ্টার কারণে হতে পারে। কিন্তু দর্শকের প্রত্যাশাটাও বেড়ে গেছে। এটা নিয়ে নিশ্চয় কিছু ভাবনাচিন্তা করো তুমি?
সৃজিতঃ জানি। কিন্তু আমি আলাদা করে কিছু করার চেষ্টা করব না। যেটা আগেই বলেছি, আই সিম্পলি ওয়ান্ট টু হ্যাভ ফান। এই দশ বছরে অনেক আনন্দ পেয়েছি, অনেক মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, অসংখ্য জায়গায় গেছি। পরের দশ বছরেও এগুলোই করে যেতে চাই। এমনকি নিজের শহরকেই অনেক বেশি জানতে পেরেছি, ভালোবাসতে পেরেছি। প্রচুর ভালোবাসা পেয়েছি, প্রচুর হেট্রেড-ও পেয়েছি। তবে আমার ধারণা শেষ পর্যন্ত ভালবাসার দিকেই পাল্লা ভারি।
প্রবীরেন্দ্রঃ শেষ টপিক। আ টপিক দ্যাট কানেক্টস আস – দ্য ইন্টারভিউয়ার অ্যান্ড দ্য ইন্টারভিউয়ি। জে-এন-ইউ, জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটি। তুমি সাউথ পয়েন্টে পড়েছ, প্রেসিডেন্সিতে পড়েছ……
সৃজিতঃ আমার প্রথম স্কুল কিন্তু দোলনা। সাউথ পয়েন্টে ইলেভেন-টুয়েলভ।
প্রবীরেন্দ্রঃ রাইট। কিন্তু তোমার কিছু ইন্টারভিউতে দেখছি জে-এন-ইউ এর কথা বারবার ফিরে এসেছে। দোলনা, সাউথ পয়েন্ট বা প্রেসিডেন্সির তুলনায়। সেটা কেন? আমি আরোই প্রশ্নটা তুললাম কারণ আজ জে-এন-ইউ সারা ভারতের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণে-অকারণে, ভালো খবরের জন্য হোক বা খারাপ খবরের জন্য, জে-এন-ইউ নিয়ে মিডিয়ায় আলোচনার বিরাম নেই। সেই প্রেক্ষিতে হয়ত আমাদের পাঠকরা জে-এন-ইউ নিয়ে তোমার এগজ্যাক্ট সেন্টিমেন্টটা বুঝতে চাইবেন। জে-এন-ইউ কী দিয়েছে তোমাকে?
সৃজিতঃ জে-এন-ইউ আমাকে ক্রোমোজোম দিয়েছে, আমাকে টিস্যু দিয়েছে, আমাকে সেরেবেলাম দিয়েছে। যা দেওয়ার সব আমাকে জে-এন-ইউ ই দিয়েছে। জে-এন-ইউ হ্যাজ ফ্যাশনড মি। জে-এন-ইউ র পাঁচ বছরই আমাকে গড়ে দিয়েছে। আমি আজকে যাই হই না কেন তার সব কৃতিত্বই জে-এন-ইউ’র। হ্যাঁ , প্রেসিডেন্সির-ও অল্প কৃতিত্ব থাকবে।
প্রবীরেন্দ্রঃ কিন্তু প্রেসিডেন্সিতে যখন পড়ছ তখনও তোমার সমসাময়িকরা দেখছে সৃজিতের মধ্যে ট্যালেন্ট আছে। তুমি ক্যুইজ করছ, নাটক করছ, সাংস্কৃতিক ভাবে খুবই অ্যাকটিভ। অফ কোর্স, তখন কেউ জানত না যে তুমি আজকের সৃজিত মুখার্জী হবে। কিন্তু তোমার ট্যালেন্টের ব্যাপারে মোর অর লেস ওয়াকিফ-হাল ছিল। জে-এন-ইউ আলাদা করে ঠিক কী দিল তোমাকে? বা তোমার যে ট্যালেন্ট ছিলই সেটাকে আলাদা করে কিভাবে নার্চার করল?
সৃজিতঃ ফার্স্ট অফ অল, জে-এন-ইউ ইজ ইন্ডিয়া। আমার ভারতবর্ষের সঙ্গে দেখা হয়েছে জে-এন-ইউ গিয়েই।
প্রবীরেন্দ্রঃ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় নোবেল পাওয়ার পর ঠিক এই কথাটাই বলেছিলেন।
সৃজিতঃ ওহ, তাই নাকি! হ্যাঁ, জে-এন-ইউ ইজ দ্যাট। সে নিয়ে কোনও সন্দেহই নেই। ভাষা-সংস্কৃতি-রাজনীতি সব কিছুর যে মেল্টিং পট জে-এন-ইউ সেটার মধ্যে না পড়লে জে-এন-ইউ কী সেটা বোঝানো একটু মুশকিল। জে-এন-ইউ বাঁচতে শেখায়, ভাবতে শেখায়, স্বাবলম্বী হতে শেখায়।
প্রবীরেন্দ্রঃ জে-এন-ইউ তোমার দৃষ্টিভঙ্গিকে বদলেছে, তোমার দর্শন বা মতবিশ্বাসকে শেপ দিয়েছে। এই ইমপ্যাক্ট তোমার কোনও সিনেমায় দেখা যায়?
সৃজিতঃ হ্যাঁ। জে-এন-ইউ আমাকে নিজের টার্মসে কাজ করতে শিখিয়েছে। এটা আগেও বলছিলাম বোধহয়। আমি কখন পড়াশোনা করব আর কখন করব না সেটা যে আমাকেই ঠিক করতে হবে এবং সেটা আমার অধিকার এটা জে-এন-ইউ যাওয়ার আগে তো বুঝতে পারিনি। যখন সেটা বুঝলাম, আমার সঙ্গে সেই বোধটা রয়ে গেল সারা জীবনের জন্য। আমার গল্প, আমার স্ক্রিপ্ট বদলাব শুধু আমার টার্মসেই। এই আত্মবিশ্বাসটা জে-এন-ইউ না গেলে আসত না। আমার যখন ইচ্ছে হবে তখনই আমি সিনেমা দেখব, বা আমার যখন ইচ্ছে হবে তখনই আমি ক্যান্ডল মার্চ-এ যাব। তাতে আমার বন্ধুরা অসন্তুষ্ট হলেও আমার কিছু এসে যায় না। সেই বোধটা এখনো রয়ে গেছে। এবং সারাজীবনই থাকবে।
প্রবীরেন্দ্রঃ এই কনফিডেন্সটা কলকাতায় থেকে গেলে আসত না, তাই তো? আমিও সেটা ফিল করতে পারি। ম্যাক্রো লেভেলে, মাইক্রো লেভেলে-ও। যেমন ধরো, কলকাতায় মাধ্যমিকের আগে থেকে যে প্রাইভেট টিউশন নেওয়া শুরু হয়েছিল সেটা থেকে গেছিল ব্যাচেলর্স প্রোগ্রামের থার্ড ইয়ার অবধি। জে-এন-ইউ গিয়ে প্রথম মুক্তি পেলাম আমরা। অথচ যে বন্ধুরা কলকাতায় থেকে গেল তাদের অনেককেই দেখেছি মাস্টার্সেও টিউশনে যাচ্ছে।
সৃজিতঃ অ্যাবসলিউটলি। অ্যাবসলিউটলি। এত কমপ্লেক্স একটা দেশের মাইক্রোকজম হচ্ছে জে-এন-ইউ। সেই প্রথমবার আমরা আমাদের দেশের ভাস্টনেসটা বুঝতে পারছি। তখন পারস্পেকটিভটাই চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। অগুন্তি ছোটোখাটো ব্যাপার নিয়ে আর মাথাই ঘামাতে ইচ্ছে করছে না।

প্রবীরেন্দ্রঃ তুমি দেখছ রাজস্থান থেকে মীনা রা পড়তে আসছে বা হরিয়ানার প্রত্যন্ত গ্রামের ছেলেমেয়েরা আসছে। নাগাল্যান্ড-মণিপুর-মিজোরামের ছেলেমেয়েরা আসছে। তাদের পৃথিবী আর আমাদের পৃথিবীর মধ্যে অনেক তফাত, এক দেশের বাসিন্দা হয়েও।
সৃজিতঃ সেই তো। নর্থইস্টের ছেলেরা হয়ত বলছে, “ইন্ডিয়াতে এরকম হয় বুঝি?”, আর সেটা শুনে আমাদের চোখ গোল্লা হয়ে যাচ্ছে। তাহলে কী ওরা নিজেদের ইন্ডিয়ান বলে ভাবে না? এই প্রশ্নটা আসছে বলেই পরের প্রশ্নটাও ভাবতে হচ্ছে – কেন নিজেদের ইন্ডিয়ান ভাবে না? তখন তারা মণিপুরে মিলিটারি শাসনের কথা বলছে। সেই নিয়ে রাজনৈতিক তর্ক শুরু হচ্ছে। কিন্তু একইসঙ্গে বুঝতে পারছি এটাই আমার ভারতবর্ষ। শুধু ভারতবর্ষ নয়, আমার পৃথিবীও। ভারতবর্ষের মধ্যে দিয়েই আমি পৃথিবীটাও দেখতে পাচ্ছি। তাই জে-এন-ইউ নামে এই যে পরশপাথর, এই যে সোনার কাঠি, এর কোনও বিকল্প নেই। আজও ভোররাতে আমি ইস্ট গেটের রাস্তাটা দেখি, এই লেক গার্ডেন্সের বাড়িতে দাঁড়িয়েও ক্যাম্পাসের মধ্যে ময়ূরের ডাক শুনতে পাই। জে-এন-ইউ উড কন্টিনিউ টু হন্ট মী টিল আয়্যাম ডেড। আর হ্যাঁ, আমার রাজনৈতিক মতাদর্শ যাই হোক না কেন আই উড ডিফেন্ড জে-এন-ইউ টিল দ্য কাউজ কাম হোম (পান নট ইনটেন্ডেড)।
(যৌথ অট্টহাস্য)
প্রবীরেন্দ্রঃ ব্যক্তিগত ভাবে, এবং বাংলালাইভের পাঠকদের পক্ষ থেকে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই সৃজিত দা। হয়ত এই ইন্টারভিউটা অনেকের কাছেই এক অচেনা সৃজিত মুখোপাধ্যায়কে চেনাবে। বা সেটা না হলেও অনেক বিষয় নিয়ে ভাবাবে। পাঠকদের প্রশ্ন বা মন্তব্য থাকলে তোমার কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব। ভালো থেকো, আর ফেলুদা ওয়েবসিরিজের জন্য অনেক শুভেচ্ছা রইল।
আগের পর্বের লিঙ্ক https://banglalive.com/first-person-part-3/
প্রবীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ব্রিটেনের কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যানেজমেন্ট সায়েন্সের অধ্যাপক। অর্থনীতি ও রাজনীতি নিয়ে বিশেষ আগ্রহ। বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন সংবাপত্রে অর্থনীতি, রাজনীতি ও বিজ্ঞান বিষয়ক একাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন প্রবীরেন্দ্র। এছাড়াও লিখেছেন একাধিক কল্পবিজ্ঞান ও রহস্যকাহিনী। তাঁর প্রকাশিত বইগুলি হল 'বাইট বিলাস', 'ক্যুইজ্ঝটিকা', 'পরিচয়ের আড্ডায়', 'আবার ফেলুদা, আবার ব্যোমকেশ', এবং 'চার'।