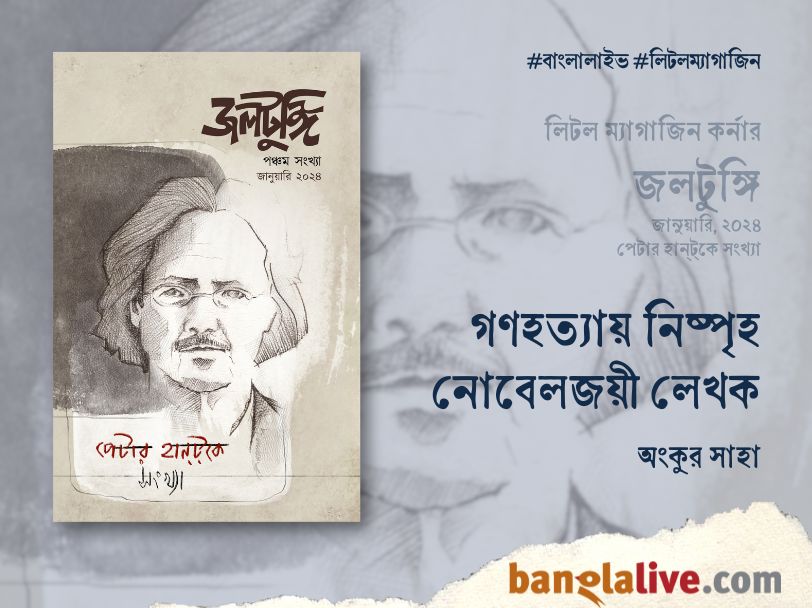(Little Magazine)
১
বিতর্কিত লেখক
বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জার্মান ভাষার এক প্রধান সাহিত্যিক পেটার হান্ট্কে। ৬ ডিসেম্বর ১৯৪২ তাঁর জন্ম; জন্মস্থান হিটলারের জার্মান রাইখের গাউ কোরিন্থিয়া প্রদেশের ছোট্ট শহর গ্রিফেন, (লোকসংখ্যা ৩৬০০), এখনকার ভূগোল অনুযায়ী সেটি অস্ট্রিয়া দেশের অন্তর্ভুক্ত। তিনি ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, অনুবাদক, সিনেমা পরিচালক, কবি এবং চিত্রনাট্যকার। ২০১৯ সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন— “for an influential work that with linguistic ingenuity has explored the periphery and the specificity of human experience.” তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি জনপ্রিয় কিন্তু বিতর্ক তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফেরে বহুকাল ধরে।
তাঁর পারিবারিক পটভূমিটিও এখানে সংক্ষেপে জেনে নেওয়া ভালো। তাঁর জার্মান বাবা এরিখ স্কোনেমান ছিলেন ব্যাংকের কেরানি এবং যুদ্ধের সময় পরিবারকে ত্যাগ করে যোগ দিয়েছিলেন নাৎসি ফৌজে। অন্তঃস্বত্বা মা মারিয়া স্লোভেনিয়ার মেয়ে, তিনি আবার বিয়ে করেন বার্লিনের ট্রাম কন্ডাক্টর ব্রুনো হান্ট্কেকে— তিনিও যোগ দেন ভেরমাখট সেনাবাহিনীতে। যুদ্ধের পরে পরিবারটি বাস করতেন সোভিয়েত রাশিয়া অধিকৃত বার্লিনে। সেখানে তাঁর সৎ-ভাই আর সৎ-বোনের জন্ম। ১৯৪৮ সালে তাঁরা ফিরে আসেন মায়ের জন্মস্থান গ্রিফেনে। (Little Magazine)
অন্তঃস্বত্বা মা মারিয়া স্লোভেনিয়ার মেয়ে, তিনি আবার বিয়ে করেন বার্লিনের ট্রাম কন্ডাক্টর ব্রুনো হান্ট্কেকে— তিনিও যোগ দেন ভেরমাখট সেনাবাহিনীতে।
জন্মদাতা পিতাকে তিনি চোখেও দেখেননি শৈশবে আর কৈশোরে; সৎ-পিতা মদ্যপান করতেন প্রচুর আর প্রহার করতেন মা ও ছেলে, দু-জনকেই। এগারো বছর বয়েছে পেটার গেলেন ক্যাথলিক বোর্ডিং স্কুলে; সেখানকার সংবাদপত্রে তাঁর কৈশোর সাহিত্যজীবনের সূচনা। তারপর হাই স্কুল, কলেজ এবং ১৯৬১ সালে অস্ট্রিয়ার গ্রাৎস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনশাস্ত্রের ডিগ্রির পাঠ আরম্ভ করেন। লেখক ঘর ছেড়ে বেঁচেছিলেন, রেহাই পেয়েছিলেন সৎ-পিতার প্রহার থেকে, কিন্তু তাঁর মায়ের ওপরে চলল নিয়মিত অত্যাচার। মারিয়া আর সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করলেন ১৯৭১ সালে। লেখকের স্মৃতিচারণে রয়েছে তাঁর প্রতিফলন— ১৯৭২ সালে প্রকাশিত ‘স্বপ্নের অধিক বিষাদ— একটি জীবনকাহিনি’। একজন বিশিষ্ট সমালোচকের মতে বইটি— “as short and loaded a book as possible: no fat, no longueurs, no self-indulgent melodrama.” নিজের মায়ের বিষয়ে এমন আবেগহীন সত্যকথনের উদাহরণ বিরল।
বেশ কয়েকজন তরুণ, প্রতিভাবান লেখক-লেখিকা তখন গ্রাৎস বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী। তাঁরা ‘মানুসক্রিপ্টে’ নামে একটি ক্ষুদ্রপত্র প্রকাশ করতেন। সেখানে প্রকাশিত হয় হান্ট্কের কম বয়সের অনেক লেখা। ১৯৬৫ সালে যখন ‘সুরক্যাম্প ভেরলাগ প্রকাশনা’ সংস্থা তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘ভীমরুল’ (‘The Hornets’) প্রকাশনার জন্য নির্বাচন করলেন, হান্ট্কে তখন লেখাপড়ার পথ চুকিয়ে পুরো সময়ের লেখক হলেন। উপন্যাসটি হান্ট্কের ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’— একেবারেই সফল হয়নি; পাঠকরাও ভুলে গেছেন। যতদূর জানি বইটির ইংরেজি অনুবাদেরও অনুমতি দেননি লেখক। কিন্তু এই উপন্যাসের কিছু কিছু থিম তাঁর সঙ্গে থেকে যাবেই। এক অন্ধ মানুষের জবানিতে তাঁর ও তাঁর কুয়োর জলে ডুবে অকালমৃত ভাইয়ের জীবনযাপনের খণ্ড-ছিন্ন বর্ণনা এবং চিন্তাভাবনার বহমান স্রোত। নামহীন অন্ধ মানুষটি কি লেখকের অলটার ইগো? সেটাও এখানে পরিষ্কার নয়। (Little Magazine)
এক অন্ধ মানুষের জবানিতে তাঁর ও তাঁর কুয়োর জলে ডুবে অকালমৃত ভাইয়ের জীবনযাপনের খণ্ড-ছিন্ন বর্ণনা এবং চিন্তাভাবনার বহমান স্রোত।
গল্প-উপন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে তিনি চেষ্টা করছিলেন নাটক লেখারও। ১৯৬৬ সালে তাঁর প্রথম নাটক ‘দর্শকদের মনে আঘাত দেওয়া’ (‘Offending the Audience’) অভিনীত হল ফ্রাঙ্কফুর্টের একটি অভিজাত থিয়েটারে; পরিচালক: ক্লাউস পেমান (১৯৩৭-)। সফল এই প্রযোজনাটি কি নাটক অথবা প্রতিনাটক? সেই নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলল। আর তখন থেকেই প্রবাদপ্রতিম স্যামুয়েল বেকেট (১৯০৬-১৯৮৯)-এর সঙ্গে তাঁর তুলনা। পরের বছর তাঁর দ্বিতীয় নাটক ‘কাসপার’ প্রকাশিত ও অভিনীত হলে সেই তুলনা হয়ে উঠল আরও জোরদার। কাসপার হাউজার (১৮২১-১৮৩৩) এক রহস্যময় জার্মান অভিজাত যুবক, যিনি নাকি সারাজীবন কাটিয়েছেন নুরেমবার্গের এক দুর্গের ভূগর্ভের জেলখানায়; তাঁকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন পোল ভেরলেন (১৮৪৪-১৮৯৬) এবং গেয়র্গ ট্র্যাকল (১৮৮৬-১৯১৪); হান্ট্কে লিখলেন এক রূপকধর্মী নাটক। হান্ট্কের সফল সাহিত্যজীবনের সেই সূচনা।
এক হিসেবে হান্ট্কের কোনো দেশ নেই: গ্রাৎস ছেড়ে আসার পরে তিনি পশ্চিম জার্মানির বিভিন্ন শহরে বসবাস করেন: ডুসেলডর্ফ, বার্লিন, ক্রোনবার্গ; সেখান থেকে প্যারিস; তারপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দু-বছর (১৯৭৮-১৯৭৯) কাটিয়ে আবার অস্ট্রিয়াতে এক দশক (১৯৭৯-১৯৮৮)। ১৯৯০ সাল থেকে তাঁর স্থায়ী বসত প্যারিসের উপকণ্ঠে শাভিল মহল্লায়।
উপন্যাস ও নাটক ছাড়াও তিনি লিখেছেন বেশ কয়েকটি চিত্রনাট্য এবং পরিচালনা করেছেন চলচ্চিত্র। ১৯৭৮ সালে মুক্তি পায় তাঁর পরিচালিত ‘বাঁ-হাতের মহিলা’ এবং সে-বছরের কান চলচ্চিত্র উৎসবে উচ্চ-প্রশংসিত এবং সোনালি তালপাতা পুরস্কারের তালিকায় ওঠে। (Little Magazine)
গল্প, উপন্যাস আর স্মৃতিচারণ মিলিয়ে কুড়িটির বেশি গ্রন্থ তাঁর। কবিতাও লিখেছেন তিনি পত্রপত্রিকায়, তাঁর কাব্যগ্রন্থও আছে কয়েকটি সেসব ইংরেজিতেও অনুবাদ হয়েছে। সেইসঙ্গে আধ ডজন নাটক ও চিত্রনাট্য। তিনি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেছেন শেক্সপিয়রের নাটক; ১৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর রচনাসমগ্র: প্রথম থেকে নবম খণ্ডে কথাসাহিত্য, নাটক, চিত্রনাট্য; দশম আর একাদশ খণ্ডে প্রবন্ধ ও ব্যক্তিগত গদ্য; দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ খণ্ডে ডায়েরি আর দিনলিপি।
১৯৭৮ সালে মুক্তি পায় তাঁর পরিচালিত ‘বাঁ-হাতের মহিলা’ এবং সে-বছরের কান চলচ্চিত্র উৎসবে উচ্চ-প্রশংসিত এবং সোনালি তালপাতা পুরস্কারের তালিকায় ওঠে।
আমেরিকার ওয়েসলিয়ান কলেজের জার্মান সাহিত্যের অধ্যাপক কৃষ্ণা উইনস্টন (১৯৪৪-) হান্ট্কের সাম্প্রতিক কয়েকটি গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ করেছেন। সাম্প্রতিকতম অনুবাদটি প্রকাশিত হয়েছে ২০২২ সালে (মূল রচনা ২০১৭); গ্রন্থের নাম ‘ফলচোর অথবা, অভ্যন্তরে একমুখী যাত্রা’ (‘The Fruit Thief Or, One-Way Journey Into the Interior’)।
আমাদের এই নিবন্ধের আলোচ্য লেখকের একটি কৃশকায় নন-ফিকশন গ্রন্থ। কিন্তু তার আগে সে-অঞ্চলের সামগ্রিক ইতিহাস এবং রাজনৈতিক পরিমণ্ডলটি জেনে নেওয়া ভালো। (Little Magazine)
২
যুগোস্লাভিয়া নিয়ে কিছু কথা
বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের মানচিত্রে নানান যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটেছে, বিশেষ করে প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমাপ্তির পরে। উনবিংশ শতকের শেষপ্রান্তে ইউরোপে পাশাপাশি অনেকগুলি সাম্রাজ্য এবং তাদের মধ্যে নিয়মিত যুদ্ধবিগ্রহ। পূর্ব আর দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের উত্তরে জারের সাম্রাজ্য রাশিয়া; মধ্যে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির সাম্রাজ্য; আর এড্রিয়াটিক সাগরের পূর্বপ্রান্ত থেকে শুরু করে ভূমধ্যসাগরের সীমানা ঘিরে সারা মধ্যপ্রাচ্যব্যাপী বিস্তৃত তুর্কি অটোমান সাম্রাজ্য।
স্লাভ জাতিগোষ্ঠীর মানুষেরা পূর্ব ইউরোপে বসবাস করছেন খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে। এদের অনেকেই খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে অর্থোডক্স চার্চের সুসমাচার অবলম্বন করে। এই জাতিগোষ্ঠীর একটা বড়ো অংশ বাস করত জার শাসিত রাশিয়ায়— এরা হলেন পূর্বদেশের স্লাভ। বাকিরা থাকত সার্বিয়া, রোমানিয়া, পোল্যান্ড, বোহেমিয়া, মোরাভিয়া ইত্যাদি দেশে— এরা হল দক্ষিণ দেশের ও পশ্চিম দেশের স্লাভ। স্লাভ জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা হয়েছে বেশ কয়েকবার, কিন্তু রাশিয়ার জারের তীব্র বিরোধিতায় সেগুলি সফল হয়নি। ইউরোপে কেবল স্লাভ জাতির জন্যে একটি দেশ গড়ে তোলা কোনোভাবেই সম্ভব হয়নি। (Little Magazine)
উনবিংশ শতকের শেষপ্রান্তে ইউরোপে পাশাপাশি অনেকগুলি সাম্রাজ্য এবং তাদের মধ্যে নিয়মিত যুদ্ধবিগ্রহ।
১২৯৯ সালে তুর্কোমান উপজাতির নেতা ওসমান অটোমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন বর্তমানকালের তুরস্কে। সেই সাম্রাজ্য ছড়িয়ে পড়ে পূর্ব আর দক্ষিণ ইউরোপে, উত্তর এশিয়ায় আর মধ্যপ্রাচ্যে। অটোমান সম্রাটেরা ছিলেন মুসলমান এবং চতুর্দশ শতাব্দী থেকে শুরু করে ইউরোপের এই গুরুত্বপূর্ণ অংশে কোণঠাসা হয় খ্রিস্টধর্ম এবং দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে ইসলামধর্ম। সম্রাটেরা খ্রিস্টধর্মীদের ওপরে অতিরিক্ত কর ধার্য করেন এবং খ্রিস্টধর্মের আয়োজন সীমাবদ্ধ থাকে গির্জায়, কনভেন্টে এবং ছড়ানো-ছেটানো আশ্রমে। পরবর্তী চার-পাঁচ শতাব্দীতে এই অঞ্চলে দু-টি ইসলামি গোষ্ঠী গড়ে ওঠে: শ্বেতকায় মুসলমান যারা সংখ্যায় বেশি এবং তুর্কি অথবা এশিয়ার মুসলমান, যারা সংখ্যায় কম। (Little Magazine)
প্রথম মহাযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮) স্লাভ জাতির মানুষেরা লড়েছিলেন মিত্রশক্তির পক্ষে এবং অটোমান সম্রাটের বিপক্ষে। যুদ্ধে অটোমানদের পরাজয় হলে সাম্রাজ্যটি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। ‘যুগোস্লাভিয়া’ শব্দটির অর্থ ‘দক্ষিণের স্লাভদের দেশ’, কিন্তু ইহুদিদের প্যালেস্তাইনের মতন সেটি ছিল কেবল এক স্বপ্নের রাজ্য। স্লাভরা বাস করত বিভিন্ন অঞ্চলে: সার্বিয়া, মন্টেনেগ্রো, ক্রোয়েশিয়া, স্লোভেনিয়া, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্য, ইত্যাদি। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষদিকে যখন অটোমানদের পরাজয় আসন্ন, এইসব দেশগুলির স্লাভ নেতারা সমবেত হলে গ্রিসের করফু দ্বীপও এবং ২০ জুলাই ১৯১৭ একটি চুক্তিতে সই করলেন যে দক্ষিণের স্লাভদের জন্য একটি নতুন দেশ গড়ে তোলা হবে। দেশটি হবে স্বাধীন এবং অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্যের আওতার বাইরে। সেই বিখ্যাত চুক্তির নাম ‘করফুর ঘোষণা’ (‘The Corfu Declaration’)।
‘যুগোস্লাভিয়া’ শব্দটির অর্থ ‘দক্ষিণের স্লাভদের দেশ’, কিন্তু ইহুদিদের প্যালেস্তাইনের মতন সেটি ছিল কেবল এক স্বপ্নের রাজ্য। স্লাভরা বাস করত বিভিন্ন অঞ্চলে: সার্বিয়া, মন্টেনেগ্রো, ক্রোয়েশিয়া, স্লোভেনিয়া, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্য, ইত্যাদি।
প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে গড়ে তোলা হল এমন একটি দেশ, ১৯১৮ সালের অক্টোবর মাসে: অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্যের অন্তর্গত সার্বিয়া রাজ্যের সঙ্গে অটোমান সাম্রাজ্য এবং প্রাশিয়ার হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যের স্লাভবহুল প্রদেশগুলি জুড়ে দিয়ে। দেশটির নাম হল ‘স্লাভ, ক্রোয়েট ও স্লোভেনদের রাষ্ট্র’ (‘State of Slovenes, Croats and Serbs’); দেশে থাকবেন একজন ‘সাংবিধানিক সম্রাট’ (‘Constitutional Monarch’), কিন্তু দেশে থাকবে সংসদীয় গণতন্ত্র, অনেকটাই ব্রিটেনের মতন ব্যবস্থা। সার্বিয়ার রাজা প্রথম পিটার (১৮৪৪-১৯২১) হলেন এই নতুন দেশের রাজা; ১৯২১ সালে তাঁর মৃত্যুর পরে নতুন রাজা তাঁর পুত্র আলেকসান্দার কারাজোরজেভিক (১৮৮৮-১৯৩৪)। ১৩ জুলাই ১৯২২, প্যারিসে ইউরোপের রাষ্ট্রদূতদের সমাবেশে রাজনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়া হল দেশটিকে এবং ১৯২৯ সালে দেশটির নতুন নামকরণ ‘যুগোস্লাভিয়া রাজ্য’ (‘Kingdom of Yugoslavia’)। ১৯৩৪ সালে ফ্রান্সে সরকারি সফরের সময় এক বিদ্রোহী ঘাতকের গুলিতে রাজা আলেকসান্দারের অকালমৃত্যু। (Little Magazine)
প্রথম মহাযুদ্ধের শেষদিকে যখন অটোমানদের পরাজয় আসন্ন, এইসব দেশগুলির স্লাভ নেতারা সমবেত হলে গ্রিসের করফু দ্বীপও এবং ২০ জুলাই ১৯১৭ একটি চুক্তিতে সই করলেন যে দক্ষিণের স্লাভদের জন্য একটি নতুন দেশ গড়ে তোলা হবে।
এর পর সিংহাসনে বসলেন রাজার এগারো বছর বয়সি সন্তান দ্বিতীয় পিটার (১৯২৩-১৯৭০)। পাঁচ বছর পরে (সেপ্টেম্বর ১৯৩৯) আবার বাজল যুদ্ধের দামামা: এবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ; যুগোস্লাভিয়ার সরকার নিয়মিত সহযোগিতা চালিয়ে গেলেন মিত্রশক্তির সঙ্গে। ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাস নাগাদ পুরো অঞ্চলটির প্রায় সব দেশগুলি খুব সহজেই চলে এল হিটলারের ও মুসোলিনির নাৎসিবাহিনীর কবলে। তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন হাঙ্গেরির নাৎসিরা। বিপাকে পড়ে ১৮ বছর বয়সি রাজা দ্বিতীয় পিটার পালিয়ে গেলেন দেশ ছেড়ে: গ্রিস → প্যালেস্টাইন → মিশর → ব্রিটেন। সেখানে গড়ে উঠল নির্বাসনে যুগোস্লাভিয়ার সরকার। যুগোস্লাভিয়ার মানুষ দল বাঁধলেন নাৎসিদের বিপক্ষে, গড়ে তুললেন গেরিলা বাহিনী। নাৎসি সেনাদলের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তাদের প্রতিরোধী আক্রমণে। রাশিয়ার সমর্থনে তারা প্রতিষ্ঠা করল এক সাময়িক সরকার: গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় যুগোস্লাভিয়া; এই সরকারের যিনি নেতা হলেন তিনি পার্টিজান সেনাবাহিনীর প্রধান এবং ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে সুপরিচিত, তাঁর নাম জোসিপ ব্রজ টিটো (১৮৯২-১৯৮০)। তিনি পরে জওহরলাল নেহেরুর ঘনিষ্ঠ সুহৃদ এবং দু-জনেই জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতা। তিনি আদতে কমিউনিস্ট হলেও স্তালিনের অত্যাচার, গুপ্তহত্যা আর অপশাসনের বিরোধী ছিলেন। নিজের দেশে তিনি এতটাই জনপ্রিয় যে সোভিয়েত রাশিয়া যখন হাঙ্গেরিতে (১৯৫৬) এবং চেকোস্লোভাকিয়ায় (১৯৬৮) বলপূর্বক স্থানীয় স্বাধীন সরকারের পতন ঘটিয়ে রাশিয়ার তাঁবেদার সরকার স্থাপন করেছিল, যুগোস্লাভিয়াতে তেমন কিছু করতে সাহস পায়নি। (Little Magazine)
পাঁচ বছর পরে (সেপ্টেম্বর ১৯৩৯) আবার বাজল যুদ্ধের দামামা: এবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ; যুগোস্লাভিয়ার সরকার নিয়মিত সহযোগিতা চালিয়ে গেলেন মিত্রশক্তির সঙ্গে।
তা ১৯৪৪ সালে গড়ে উঠল নতুন দেশ ও সরকার; ১৯৪৫ সালে বিলুপ্ত করা হল রাজার পদ— উইনস্টন চার্চিলের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও। চার্চিল চেয়েছিলেন যুগোস্লাভিয়ায় রাজতন্ত্র এবং ব্রিটিশ প্রভাব বজায় রাখতে। কিন্তু আমেরিকা দেখল যে টিটোকে যদি রাশিয়ার বৃত্তের বাইরে রাখা যায়, তাতেই পশ্চিম ইউরোপের সুবিধে। ১৯৪৮ সালে দ্বিতীয় পিটার চলে গেলেন আমেরিকায় এবং পরের বাইশ বছর অপেক্ষায় রইলেন যুগোস্লাভিয়ার রাজা হয়ে তিনি আবার দেশে ফিরবেন। ১৯৫৩ সালে দেশটির নতুন নামকরণ হল ‘প্রজাতন্ত্রী সমাজতন্ত্রী যুগোস্লাভিয়া যুক্তরাষ্ট্র’ (‘Socialist Federal Republic of Yugoslavia’) সংক্ষেপে SFRY.
১৯৪৩-১৯৪৫ সালেই দেশটির বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে এবং ইসলামি ও খ্রিস্টধর্মী মানুষদের মধ্যে কলহ-বিবাদের সূচনা হয়েছিল, কিন্তু টিটো কড়া হাতে তাদের দমন করেন। ছয়টি রিপাবলিক নিয়ে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল যুগোস্লাভিয়া দেশটির:
১. বসনিয়া এবং হার্টজেগোভিনা (রাজধানী: সারায়েভো)
২. ক্রোয়েশিয়া (রাজধানী: জাগ্রেব)
৩. মাসেডোনিয়া (রাজধানী: স্কোপিয়া, মা তেরেসার জন্মস্থান)
৪. মন্টেনেগ্রো (রাজধানী: টিটোগ্রাদ)
৫. সার্বিয়া (রাজধানী: বেলগ্রেড)
৬. স্লোভেনিয়া (রাজধানী: লুবলিয়ানা, অমিয় চক্রবর্তীর একটি বিখ্যাত কবিতার বিষয় এই শহর)
সার্বিয়ার অন্তর্গত ছিল দু-টি স্বশাসিত প্রদেশ: কসোভো (রাজধানী: প্রিস্টিনা) এবং ভয়ভোদিনা (রাজধানী: নোভি সাদ)।
জাতি-ধর্ম-বর্ণের এই তপ্ত কটাহে মোটামুটি শান্তি বজায় রাখতে পেরেছিলেন টিটো তাঁর সুশাসনে। জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন ক্রোয়েশিয়ার মানুষ, কিন্তু ছয়টি রিপাবলিকের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিল সার্বিয়া। জাতিগোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক কলহ ও হানাহানি, ছাত্র এবং শ্রমিকদের মিছিল লেগেই থাকত, কিন্তু টিটো তাদের মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে দেননি এবং বশে রাখতে পেরেছিলেন আর দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির কারণে তিনি ছিলেন ভীষণ জনপ্রিয়। কমিউনিস্ট শাসনে ধর্মের প্রভাব ছিল কম এবং টিটো বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভেতর মেলামেশা এবং বিবাহবন্ধনে উৎসাহী দিতেন, যাতে যুগোস্লাভিয়া নামে একটি জাতিসত্তা তৈরি হয়। (Little Magazine)
১৯৭০-এর দশকে খনিজ তেলের মূল্যবৃদ্ধির ফলে দেশে অর্থনৈতিক সংকট ঘনিয়ে আসে এবং তার সঙ্গে জাতিবিদ্বেষ ও ধর্মবিদ্বেষ বেড়ে চলে। ৪ মে ১৯৮০: টিটোর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেই সংকট ঘনীভূত হয়। সার্বিয়ার নেতা স্লোবোদান মিলোশেভিচ (১৯৪১-২০০৬) এই সংকটের সুযোগ নিয়ে সার্বিয়াতে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে সচেষ্ট হন। তিনি সার্বিয়ার একচ্ছত্র নেতা হবেন এবং কসোভো আর ভয়ভোদিনা প্রদেশদু-টিকে নিজের কুক্ষিগত করবেন। তারা অবশ্যই প্রতিবাদ জানাল। দেশের প্রধান পার্লামেন্টে ছয়টি রিপাবলিক আর দু-টি প্রদেশ মিলে মোট আটটি ভোট, মিলোশেভিচ চান তিনটি ভোট তাঁর দখলে আনতে। এইভাবে চলল কয়েক বছর; ১৯৮৯ সালে কসোভোর আলবেনিয়া জাতির খনি শ্রমিকেরা যখন ধর্মঘট করলেন, সেটা হয়ে দাঁড়াল আলবেনিয়া জাতির শ্রমিক এবং অন্য শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষের কারণ। ওই একই সময়ে পূর্ব ইউরোপের দেশে দেশে কমিউনিজমের পতন ঘটলে সংযুক্ত যুগোস্লাভিয়া দেশটির পতন হয়ে দাঁড়াল অনিবার্য। (Little Magazine)
সার্বিয়ার অন্তর্গত ছিল দু-টি স্বশাসিত প্রদেশ: কসোভো (রাজধানী: প্রিস্টিনা) এবং ভয়ভোদিনা (রাজধানী: নোভি সাদ)।
জাতি-ধর্ম-বর্ণের এই তপ্ত কটাহে মোটামুটি শান্তি বজায় রাখতে পেরেছিলেন টিটো তাঁর সুশাসনে।
১৯৯১ সালে স্লোভেনিয়া এবং ক্রোয়েশিয়ার রিপাবলিক দু-টি যুগোস্লাভিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করে। পরের বছর স্বাধীনতার স্বপক্ষে গণভোট চালু করে বসনিয়া এবং হার্টজেগোভিনা রিপাবলিক। সেই দেশের শতকরা ৪৪ শতাংশ মানুষ মুসলমান, ৩২.৫ শতাংশ মানুষ অর্থোডক্স খ্রিস্টধর্মী সার্ব এবং ১৭ শতাংশ মানুষ ক্যাথলিকধর্মী ক্রোয়েট; স্বাধীন হলে এই রিপাবলিকটি হবে মুসলিমপ্রধান এবং সার্বরা সেটিকে মেনে নিতে কোনোমতেই রাজি নয়। বসনিয়ার সার্বদের কট্টরপন্থী নেতা রাদোভান কারাদিচ (১৯৪৫-) একটি জঙ্গি মিলিশিয়া গড়ে তুললেন সার্বিয়ার মিলোসেভিচের প্রত্যক্ষ সমর্থনে। তাদের লক্ষ্য সংখ্যাগুরু মুসলমানদের দমিয়ে রাখা এবং বসনিয়ার ভেতরে সার্বদের জন্য একটি এনক্লেভ গড়ে তোলা। (Little Magazine)
বসনিয়ার গণহত্যা
রাদোভান কারাদিচের বাবা হলেন সামান্য মুচি এবং মা হলেন দরিদ্র কৃষককন্যা। কিন্তু তিনি নিজেকে জাহির করতেন অভিজাত বলে; তিনি জীবনে কোনো যুদ্ধে একটি বন্দুকের গুলিও ছোড়েননি, মিলিটারি সংগঠন চালানোর কোনো অভিজ্ঞতাই তাঁর নেই, কিন্তু তিনি হতে চান সামরিক নেতা। ১৯৮৯ সালে তিনি গঠন করলেন সার্ব গণতান্ত্রিক পার্টি (সার্ব ভাষায় সংক্ষেপে SDS)— পার্টির লক্ষ্য অন্য রিপাবলিকগুলির সার্ব অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি নিয়ে সার্বিয়ার সঙ্গে বৃহত্তর সার্বিয়া গঠন করা এবং মুসলমানদের ভয় দেখানো যাতে তারা দেশ ছেড়ে চলে যায়।
৩ এপ্রিল ১৯৯২ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯৫ বসনিয়াতে গৃহযুদ্ধ চলে; এক লক্ষেরও বেশি মানুষকে হত্যা করা হয়, যাদের বেশিরভাগই ধর্মে মুসলিম। ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯৫ প্যারিসের শান্তিবৈঠকে যুদ্ধমান শক্তিগুলি রাজি হয় যুদ্ধবিরতিতে; এক হপ্তা পরে ওহাইওর ডেটন শহরে স্বাক্ষরিত হয় শান্তিচুক্তি।
বিভিন্ন গণকবরে মৃতদের সমাহিত করা হয় হেলাফেলায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী অর্ধশতকে ইউরোপে এই প্রথম গণহত্যা। ১১ জুলাই এখনও সেই শহরে শোকের দিবস।
বসনিয়ার পূর্বপ্রান্তে একটি মফস্সল শহরের নাম স্রেব্রেনিৎসা— শব্দটির অর্থ স্থানীয় ভাষায় ‘রুপোর খনি’; হয়তো কোনোকালে রুপো পাওয়া যেত সেখানে— এখন রয়েছে কয়েকটি নুনের খনি এবং ঊষ্ণ জলের প্রস্রবণ। ১৯৯৫ সালের ১১ জুলাই সেখানে এসে নাম SDS-এর জঙ্গিবাহিনী; শহরটির জনসংখ্যা মুসলিমপ্রধান: তাদের নিরাপত্তার জন্য ছিল জাতিসঙ্ঘের অল্প কিছু প্রহরী ওলন্দাজ সেনা। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাদের দমন করে সার্ব মিলিশিয়া নির্বিচারে খুন করতে থাকে মুসলিম পুরুষ ও বালকদের; নারীদের গণধর্ষণের পরে গণহত্যা। পরবর্তী তিন সপ্তাহে মৃত মানুষের সংখ্যা ৮৩৭২। বিভিন্ন গণকবরে মৃতদের সমাহিত করা হয় হেলাফেলায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী অর্ধশতকে ইউরোপে এই প্রথম গণহত্যা। ১১ জুলাই এখনও সেই শহরে শোকের দিবস।
১৯৯৫ সালের জুলাই মাসে এই শহরে থাকতেন ২৭,৫৪২ জন মুসলিম নাগরিক (৭৫.১২%) এবং ৮৩১৫ জন সার্ব। ২০১৩ সালে পরবর্তী আদমশুমারিতে দেখা যায় মুসলিমের সংখ্যা কমে ৭২৪৮ (৫৪.০৫%) এবং ৬০২৮ জন সার্ব (৪৪.৯৫%)। এখনও সেখানে আবিষ্কৃত হচ্ছে নতুন নতুন মৃতদেহ। (Little Magazine)
রাতকো ম্লাদিচ (১৯৪২-) ছিলেন এই গণহত্যা ও গণধর্ষণের নেতা। ২০১১ সালের ৩১ মার্চ তাঁকে গ্রেফতার করে সুইৎজারল্যান্ডের হেগ শহরে পাঠানো হয় আন্তর্জাতিক আদালতে বিচারের জন্য। বিচার আরম্ভ হয় পরের বছর এবং তাঁর শাস্তি হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। ৮২ বছর বয়সে তিনি এখনও জেলে বন্দি, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য।
বিচার আরম্ভ হয় পরের বছর এবং তাঁর শাস্তি হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। ৮২ বছর বয়সে তিনি এখনও জেলে বন্দি, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য।
রাদোভান এবং রাতকো— পশ্চিমের সংবাদপত্রে দু-জনেরই নতুন নামকরণ হয় ‘বসনিয়ার কশাই’ (‘Butcher of Bosnia’); রাদাভান কারাদিচেরও বিচার হয়েছে আন্তর্জাতিক আদালতে এবং তিনিও জেলে বন্দি থাকবেন যাবজ্জীবন।
যুদ্ধ সমাপ্ত হলেও যুদ্ধের রেশ থেকে যায় বহুকাল। ১৯৯৫ সালের যুদ্ধবিরতির পরেও ছোটোখাটো বিবাদ লেগেই থাকে এবং দু-তিনটি নতুন দেশের জন্মও হয়। ১৯৯১ সালে অখণ্ড যুগোস্লাভিয়ার জনসংখ্যা ছিল ২ কোটি ৩২ লক্ষ। বর্তমানকালে সেই ভূমিতে রয়েছে সাত-সাতটি স্বাধীন দেশ:
১. বসনিয়া এবং হার্টজেগোভিনা (রাজধানী: সারায়েভো)
২. ক্রোয়েশিয়া (রাজধানী: জাগ্রেব)
৩. কসোভো (রাজধানী: প্রিস্টিনা)
৪. মন্টেনেগ্রো (রাজধানী: পদগোরিকা)
৫. উত্তর মাসেডোনিয়া (রাজধানী: স্কোপিয়া)
৬. সার্বিয়া (রাজধানী: বেলগ্রেড)
৭. স্লোভেনিয়া (রাজধানী: লুবলিয়ানা)।
সব মিলিয়ে দেশগুলির জনসংখ্যা এখন ২ কোটি ১১ লক্ষ।
রাদোভান এবং রাতকো— পশ্চিমের সংবাদপত্রে দু-জনেরই নতুন নামকরণ হয় ‘বসনিয়ার কশাই’
এই অন্যায় যুদ্ধের সূচনা করেছে সার্ব জাতিগোষ্ঠী, সেই নিয়ে পশ্চিমের দেশগুলি সহমত। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে এক কুম্ভ পেটার হান্ট্কে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর মতে অন্যায় হয়েছে সার্বদের বিরুদ্ধে। সেই কারণে তিনি জাতীয় বীরের সম্মান পান সার্বিয়াতে। গণহত্যা এবং যুদ্ধ-অপরাধের জন্য আন্তর্জাতিক আদালতে বিচার চলাকালীন ২০০৬ সালে মিলোশেভিচের মৃত্যু হয়; হান্ট্কে ছিলেন তাঁর প্রধান সমর্থক এবং গুণকীর্তনকারী ভাষণ দেন তাঁর স্মরণ সভায়। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লেখক সার্বিয়ার সর্বোচ্চ জাতীয় সম্মানে ভূষিত হন, “সার্বিয়ার সত্যকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরার জন্যে”। এহ বাহ্য। (Little Magazine)
৩
নদীগুলির দিকে অভিযাত্রা— সার্বিয়ার জন্য ন্যায়বিচার
[‘A Journey To the Rivers: Justice For Serbia’— Written by Peter Handke; Translated from the original German by Scott Abott; First Published by Viking in 1997; xii+83 pages; ISBN: 0-670-87341-1.]
১০ মাস ২ দিন সময়কালে (২৫ জুন ১৯৯১ থেকে ২৭ এপ্রিল ১৯৯২) যুগোস্লাভিয়া দেশটি রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধের পরে ভেঙে ৬-৭ টুকরো হয়ে যায়। সেই ধ্বংসাত্বক যুদ্ধ আর গণহত্যার প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিম ইউরোপ আর উত্তর আমেরিকার রাজনীতিক আর বুদ্ধিজীবীরা প্রায় সকলেই ছিলেন সহমত। বিশেষ করে ক্রোয়েশিয়া আর বসনিয়ার গৃহযুদ্ধ অনেক ঐতিহাসিক আর প্রতিবেদককে মনে করিয়ে দিয়েছিল তার অর্ধশতাব্দী পূর্বের স্পেনের গৃহযুদ্ধের কথা। (Little Magazine)
দুই গৃহযুদ্ধের সময়কালে পৃথিবীর শক্তিশালী দেশগুলি ছিল সন্ত্রাসবাদীদের পক্ষে (১৯৩৬ সালে ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিবাদী সেনাদল, ১৯৯২ সালে বসনিয়ার সার্ব মিলিশিয়া) অথবা অথবা পালন করেছিল গা-বাঁচানো নিরপেক্ষতা, যার অর্থ হল যাতে সরকারি পক্ষ (স্পেনের গণতান্ত্রিক রিপাবলিকান শাসকদল, সারায়েভোতে বসনিয়ার সরকার) তাদের আত্মরক্ষার জন্য যথাযোগ্য অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতে না পারে। কিন্তু ওইসব দেশের সাংবাদিক, লেখক আর শিক্ষিত মানুষেরা ছিলেন তাদের সরকারের কড়া সমালোচক এবং তাঁরা পক্ষ নিয়েছিলেন আইন শৃঙ্খলার (১৯৯২-এর সারায়েভো এবং ১৯৩৬ সালের মাদ্রিদ)। কিন্তু স্পেনে যেরকম ‘আন্তর্জাতিক ব্রিগেড’ যুদ্ধ করেছিল ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে, বসনিয়াতে তেমন কিছু ছিল না। থাকলে হয়তো ভালোই হত, কিছু নিরপরাধ মানুষের প্রাণ বাঁচত। কিছু সাংবাদিক অবশ্য প্রাণের ভয় না করে সারায়েভোতে গিয়েছিলেন যুদ্ধের সময়ে এবং অন্য বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের নিজেদের দেশে বসনিয়ার স্বপক্ষে জনমত গড়ে তুলতে। (Little Magazine)
১৯৩৬ সালে যেমন ফ্রাঙ্কোর স্বপক্ষে সাফাই গাওয়ার জন্যে ইউরোপে উপস্থিত ছিলেন টি.এস. এলিয়ট (১৮৮৮-১৯৬৫), উইন্ডহ্যাম লুইস (১৮৮২-১৯৫৭) এবং এজরা পাউন্ডের (১৮৮৫-১৯৭২) মতন লেখকেরা, ১৯৯০-এর দশকের সূচনায় রাশিয়া দেশটির বাইরে বসনিয়ার সার্বদের পক্ষ নেওয়ার মতন তেমন কোনো বিখ্যাত মানুষ ছিলেন না। একমাত্র ব্যতিক্রম অস্ট্রিয়ার ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার, আমাদের আলোচ্য পেটার হান্ট্কে। তাঁর মতে সার্বরা যদি অপরাধ করেও থাকে, তারা সেটা বাধ্য হয়েই করেছে। আর আসল দোষ জার্মানির— সেই দেশটি স্বাধীন স্লোভেনিয়া আর ক্রোয়েশিয়াকে আগেভাগেই রাজনৈতিক স্বীকৃতি দিয়ে বসেছিল, তারাই এই ঘটনার আসল খলনায়ক।
কিছু সাংবাদিক অবশ্য প্রাণের ভয় না করে সারায়েভোতে গিয়েছিলেন যুদ্ধের সময়ে এবং অন্য বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের নিজেদের দেশে বসনিয়ার স্বপক্ষে জনমত গড়ে তুলতে।
(Little Magazine) গৃহযুদ্ধ যত ঘনীভূত হয়, হান্ট্কের গাত্রদাহ ততটাই বেড়ে চলে; বিশেষ করে প্যারিসের ‘লা মোন্দ’ এবং ফ্রাঙ্কফুর্টের কয়েকটি সংবাদপত্রের প্রতিবেদকদের বিপোর্টাজ এবং মতামত নিয়ে। তাঁর সতীর্থ লেখকেরা প্রায় সকলেই সার্বদের বিরুদ্ধে, সেই নিয়ে হান্ট্কের বিরক্তির সীমা নেই। ১৯৯৫ সালের হেমন্তে তিনি সার্বিয়া ভ্রমণে গেলেন: তাঁর ফলশ্রুতি এই গ্রন্থটি।
হয়তো এই যুদ্ধের একটি সংশোধনবাদী ইতিহাসের প্রয়োজন ছিল, যাতে সার্বদের অভাব-অভিযোগগুলি সহানুভূতির আলোকে বিবেচনা করা যেতে পারে। বসনিয়ার সার্বদের কিছু সাংবিধানিক অধিকার ছিল যুদ্ধের আগে, যেগুলি সঠিকভাবে পালন করা হয়নি। কিন্তু হান্ট্কে সেই কর্মে সফল হননি। তিনি ইচ্ছেমতো মন্তব্য করে গেছেন, কিন্তু যুক্তিতর্ক দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। (Little Magazine)
পেটার হান্ট্কে তাঁর এই ভ্রমণকাহিনি/নিবন্ধটি লেখেন ১৯৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর থেকে ১৯ ডিসেম্বর। পরের বছর (১৯৯৬) জানুয়ারি মাসে মিউনিখের প্রধান সংবাদপত্রে সেটি দুই খণ্ডে প্রকাশিত হলে বিতর্কের ঝড় ওঠে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিবন্ধটির ইংরেজি অনুবাদ করেন আমেরিকার ইউটা প্রদেশের ব্রিগহ্যাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্মান সাহিত্যের অধ্যাপক স্কট অ্যাবট (১৯৫৫-)। সমসাময়িক বিতর্ক আর সমালোচনার জবাব দিতে লেখক একটি ভূমিকা জুড়ে দেন বইটির মার্কিন সংস্করণে:
মার্কিন সংস্করণের ভূমিকা
প্রিয় পাঠক/পাঠিকা,
এই নিবন্ধটির প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৯৯৬ সালের সূচনায় মিউনিখ শহরের ‘সুডডয়েচ ৎসাইটুং’ সংবাদপত্রের পাতায় দু-টি উইকেন্ড জুড়ে (জানুয়ারি ৫-৬ এবং ১৩-১৪) এবং লেখাটি ইউরোপের প্রেসে ঝড় তোলে।
(Little Magazine) প্রথম কিস্তিটি প্রকাশের পরে ইতালির ‘কোরিয়েরে দেলা সেরা’ দৈনিক পত্রিকাটি আমাকে ‘আতঙ্কবাদী’ আখ্যা দেয় এবং প্যারিসের ‘লিবারেশোঁ’ কাগজটি পাঠকের দৃষ্টিগোচর করে যে প্রথমত, ১৯৯১ সালের স্লোভেনিয়ার যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা কম বলে আমার মজা পেয়েছিল এবং দ্বিতীয়ত, পশ্চিমের সংবাদমাধ্যমে যুগোস্লাভিয়ার যুদ্ধের এক বা অন্য শিকারের আমি যে-বর্ণনা দিয়েছি তাতে আমার ‘সন্দেহজনক রুচি’-র প্রকাশ হয়েছে। তারপর ‘লা মোন্দ’ কাগজে লেখা হয়েছে যে আমি ‘সার্বিয়ার দালাল’ এবং ‘জর্নাল দ্যু দিমন্স’ সাময়িকপত্রে আলোচিত হয়েছে আমার ‘সার্বিয়া-পন্থী আন্দোলন’-এর বৃত্তান্ত। এইভাবেই চলতে থাকে যতক্ষণ না মাদ্রিদের ‘এল পাইস’ নামক খবরের কাগজ আমার নিবন্ধে স্রেব্রেনিৎসা হত্যাকাণ্ডের সমর্থন খুঁজে পায়। (Little Magazine)
পেটার হান্ট্কে তাঁর এই ভ্রমণকাহিনি/নিবন্ধটি লেখেন ১৯৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর থেকে ১৯ ডিসেম্বর। পরের বছর (১৯৯৬) জানুয়ারি মাসে মিউনিখের প্রধান সংবাদপত্রে সেটি দুই খণ্ডে প্রকাশিত হলে বিতর্কের ঝড় ওঠে।
এবার আমার রচনাটি ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে এবং আপনারা সেটি সরাসরি পড়বেন আমি যেমনটি লিখেছিলাম; আমি একবিন্দু সাফাই গাইব না অথবা একটি অক্ষরও ফিরিয়ে নেব না। আমি যেভাবে আমার প্রতিটি বই লিখেছি, যেভাবে এতদিন আমি সাহিত্যচর্চা চালিয়েছি, ঠিক সেইভাবেই আমি সার্বিয়া দেশটিতে আমার ভ্রমণের বর্ণনা করেছি: ধীরগতি এবং অনুসন্ধিৎসু আখ্যানবর্ণন; প্রতিটি অনুচ্ছেদ তুলে ধরেছে একটি কাহিনি কিংবা একটি সমস্যার বিবরণ, একটি প্রতিনিধিত্বের, শিল্পরূপের, ব্যাকরণের— তাদের নান্দনিক যথার্থতা; এইভাবেই আমার চিরকালের সাহিত্যসৃষ্টি— প্রথম পর্যায় থেকে অন্তিম পর্যায়।
প্রিয় পাঠক, এটাই এবং একমাত্র এটাই আমি আপনাদের পাঠের জন্য নিবেদন করছি। পেটার হান্ট্কে
এপ্রিল ১৯৯৬।
কেবল যে বইটি নিয়েই বিতর্ক তা নয়, ফরাসি ও জার্মান ভাষার সংবাদমাধ্যমে সেই বিতর্কের ফায়দা তুললেন হান্ট্কে। মেতে উঠলেন বিভিন্ন ফোরামে বক্তৃতা দিয়ে এবং বইয়ের সমালোচকদের সঙ্গে ডিবেট করে— তাঁর তর্কযুদ্ধের বিশেষ লক্ষ্য ছিলেন বামপন্থী, প্রগতিশীল জার্মান লেখক পেটার স্নাইডার। বইটিতে না রয়েছে ভ্রমণ বৃত্তান্ত, না রয়েছে ভ্রমণের বিস্ময়, অথবা স্থানীয় মানুষের সঙ্গে হার্দিক আদানপ্রদান। কেবল রয়েছে আত্মপ্রচার এবং সার্বিয়ার পক্ষ নিয়ে রাজনৈতিক পোলেমিক। এই নিরর্থক কর্মে তিনি তাঁর সৃজনশীল সাহিত্যকর্ম বন্ধ রাখলেন এক বছরেরও বেশি সময়।
তিন পরিচ্ছেদের এই বইটি সুপাঠ্য নয়, সুখপাঠ্য তো নয়ই। যেখানে হান্ট্কের মতন খ্যাতি আর গুণমানের অন্যসব লেখক বসনিয়ার সার্বদের পক্ষ নিয়েছেন, সেখানে তিনি যে নির্লজ্জভাবে খুনি সার্বদের গুণগান গাইলেন, সেটাই এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয়। কুকুর মানুষকে কামড়ালে, সেটা সংবাদপত্রের শিরোনাম হয় না, কিন্তু মানুষ কুকুরকে কামড়ালে সেটা উল্লেখযোগ্য খবর, এটাও অনেকটা সেইরকম। তিনি বেলগ্রেড শহরে গেলেন কিন্তু গণহত্যার কোনো চিহ্নও খুঁজে পেলেন না। (Little Magazine)
তিনি গৃহযুদ্ধের কোনো রিপোর্ট লিখলেন না, মানুষজনের দুঃখদুর্দশা নিয়েও তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই, কেবল যাঁরা সেই কাজগুলি দায়িত্ব নিয়ে পালন করছেন তাঁদের প্রতি নির্বিচার আক্রমণ। ‘লা মোন্দ’ তাঁর মতে “a demagogic snoop sheet”, ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরের একটি অভিজাত সংবাদপত্র “a central European Serb-swallowing rag”। নোবেলজয়ী কবি জোসেফ ব্রডস্কিও রেহাই পেলেন না তাঁর নিন্দামন্দ থেকে।
যুদ্ধ হয়েছে বসনিয়ায়, কিন্তু হান্ট্কে ভ্রমণ করলেন সার্বিয়া। ধরুন আমেরিকার ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় কোনো মার্কিন লেখক অথবা সাংবাদিক ব্যাংকক ভ্রমণ করে সেই যুদ্ধের রিপোর্ট লিখতেন অনেকটা সেইরকম।
যুদ্ধ হয়েছে বসনিয়ায়, কিন্তু হান্ট্কে ভ্রমণ করলেন সার্বিয়া। ধরুন আমেরিকার ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় কোনো মার্কিন লেখক অথবা সাংবাদিক ব্যাংকক ভ্রমণ করে সেই যুদ্ধের রিপোর্ট লিখতেন অনেকটা সেইরকম। তিনি খোদ বসনিয়াতে গেলেন না, কিন্তু দুই দেশের মধ্যে দ্রিনা নদীর যে-সীমান্ত (পূর্ব দিকে সার্বিয়া, পশ্চিমপারে বসনিয়া)।
গ্রন্থটির শেষ পর্বে লেখক একটি সার্বিয়ান শব্দবন্ধ ব্যবহার করেছেন: ‘জেবি গা’, যার ইংরেজি করলে দাঁড়াবে ‘ফাক হিম’। সুধী পাঠক যদি বইটি পড়া সমাপ্ত করে লেখকের প্রতি সেই একই শব্দবন্ধ ব্যবহার করে, তাহলে অন্যায় কিছু হবে না। গ্রন্থের সাব টাইটেল ‘সার্বিয়ার জন্য ন্যায়বিচার’: সেটিও এক কপটতাপূর্ণ ভণ্ডামি; যদি ভিয়েতনাম বা ইরাকের যুদ্ধ নিয়ে কোনো বইয়ের যদি সাবটাইটেল হয় ‘আমেরিকার জন্য ন্যায়বিচার’, সেরকমই অশোভন লাগবে।
‘সার্বিয়ার জন্য ন্যায়বিচার’ না কি ‘অন্ধের হস্তিদর্শন?’ পাঠকই তার বিবেচনা করবে। (Little Magazine)
তথ্যসূত্র:
১. The Serbs: History, Myth and the Destruction of Yugoslavia; by Tim Judah; third edition; Yale University Press; 2009.
২. The History of Serbia; by John K Cox; Greenwood Press; 2002.
৩. সমসাময়িক মার্কিন সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র।
(বানান অপরিবর্তিত)
বাংলালাইভ একটি সুপরিচিত ও জনপ্রিয় ওয়েবপত্রিকা। তবে পত্রিকা প্রকাশনা ছাড়াও আরও নানাবিধ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে থাকে বাংলালাইভ। বহু অনুষ্ঠানে ওয়েব পার্টনার হিসেবে কাজ করে। সেই ভিডিও পাঠক-দর্শকরা দেখতে পান বাংলালাইভের পোর্টালে,ফেসবুক পাতায় বা বাংলালাইভ ইউটিউব চ্যানেলে।