১৯০১ সাল। জুন মাসে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে এসেছেন। গরমের দিনে পুণ্যাহ উৎসব মহাসমারোহে সমাপ্ত হবার পর শিলাইদহের কুঠিবাড়ি জনশূন্য। খাঁ খাঁ করছে। অনেকদিন ধরে নানাবিধ ব্যস্ততার পর কবি ভেবেছিলেন নির্জনে একলা আরাম করবেন। তবু ফাঁকা বাড়িতে তাঁর বড্ড একা লাগল। পড়তে চেষ্টা করলেন, মন বসাতে পারলেন না। বাগানে গেলেন, আবার ফিরে এসে শূন্যতা অনুভব করতে লাগলেন। কিছুতেই সুবিধা হল না। শেষে স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে চিঠি লিখতে বসলেন। লিখলেন,
‘তোমার শাকের ক্ষেত ভরে গেছে। কিন্তু ডাঁটা গাছগুলো বড্ড বেশি ঘন ঘন হওয়াতে বাড়তে পারচেনা। কুমড়ো অনেকগুলো পেড়ে রাখা হয়েছে। নীতু যে গোলাপ গাছ পাঠিয়েছিল সেগুলো ফুলে ভরে গেছে কিন্তু অধিকাংশই কাঠগোলাপ — তাকে ভয়ানক ফাঁকি দিয়েছে। রজনীগন্ধা, গন্ধরাজ, মালতী, ঝুমকো, মেদি খুব ফুটেচে। হাস-নু-হানা ফুটচে কিন্তু গন্ধ দিচ্চে না, বোধ হয় বর্ষাকালে ফুলের গন্ধ থাকে না।’
এই চিঠিটি পাঠ করতে করতে স্বভাবতই মনে হতে পারে এই বাগানের যাবতীয় দায়িত্ব মৃণালিনী দেবীরই ছিল। কিন্তু যদি একটু গভীরভাবে মনোযোগ দেওয়া যায় চিঠির প্রতিটি ছত্রে, বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ কতটা ওয়াকিবহাল ছিলেন বাগান পরিচর্যার ব্যাপারে। তা না হলে এতটা খুঁটিনাটি বিষয়ে আলোকপাত করতেন না।
শিলাইদহ কুঠিবাড়ির অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল ফুলের আর ফলের বাগান। এই বাগানেই দেখা যেত স্থলপদ্ম, রঙ্গন, জবা, বা অপরাজিতা ফুটে আলো করে আছে। ফুলের পাশাপাশি আলু, মটরশুঁটি, পেঁয়াজ, কপি, চিনেবাদাম এই সমস্তও ফলত সেখানে। ‘শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থে শচীন্দ্রনাথ অধিকারী জানিয়েছেন ‘প্রথম যুগের কুঠিবাড়ি ছিল দোতলা, প্রাচীরবেষ্টিত একটি বৃহৎ পুষ্পবাটিকা সমন্বিত। প্রাচীরের মধ্যে প্রকাণ্ড গোলাপবাগান, অন্যান্য বহুপ্রকার ফুলে পাতায় সুসজ্জিত অপরূপ কুঞ্জকানন।’ এছাড়াও এই বাগানে গুটিপোকা পালন হত, আঙুরের ক্ষেত ছিল, তুঁতের চাষ হত। এমনই সে বাগানের আকর্ষণ যে, একবার রবীন্দ্রনাথ রথীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতনে ডেকে পাঠালে কতটা বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিলেন তা জানা যায় তাঁর ‘পিতৃস্মৃতি’ পড়লে।
‘সেই শিলাইদহ— যার কুঠিবাড়ির চারদিকে গোলাপ ফুলের বাগিচা, একটু দূরে সুদূরবিস্তারী খেত, যা বর্ষার দিনে কচি ধানে সবুজ, শীতকালে সরষে ফুলের হলদে রঙে সোনালি;…সেই-সব ছেড়ে আমায় চলে যেতে হল বীরভূমের ঊষর কঠিন লাল মাটির প্রান্তরে।’

বোঝাই যায় শিলাইদহে কুঠিবাড়ির বাগানেরও কত কদর ছিল। শুধু তো শিলাইদহ নয়, সাজাদপুরের দিকে তাকালেও দেখা যাবে এক দৃশ্যপট। ১৮৯৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের পাঁচ তারিখে সাজাদপুর থেকে কবির লেখা একটি চিঠি পড়া যাক। দোতলার ঘর থেকে লিখছেন, ‘যেদিকে চেয়ে দেখি সেই দিকেই গাছের সবুজ ডাল চোখে পড়ে এবং পাখির ডাক শুনতে পাই — দক্ষিণের বারান্দায় বেরোবা-মাত্র কামিনী ফুলের গন্ধে মস্তিষ্কের সমস্ত রন্ধ্রগুলি পূর্ণ হয়ে উঠে।’ সাজাদপুরের কুঠিবাড়ির বারান্দা বসে কবি হয়তো কোনও মধ্যাহ্নে ‘শৈশবসঙ্গীত’-এর “কামিনী ফুল” কবিতা পাঠ করতেন,
‘ছি ছি সখা কি করিলে, কোন্ প্রাণে পরশিলে
কামিনীকুসুম ছিল বন আলো করিয়া—
মানুষপরশ-ভরে শিহরিয়া সকাতরে
ওই যে শতধা হয়ে পড়িল গো ঝরিয়া।
জান ত কামিনী সতী, কোমল কুসুম অতি
দূর হ’তে দেখিবারে, ছুঁইবারে নহে সে—
দূর হ’তে মৃদু বায়, গন্ধ তার দিয়ে যায়,
কাছে গেলে মানুষের শ্বাস নাহি সহে সে।…’
রবীন্দ্রনাথের বাগানবিলাসিতা ঠিক এমনই।
রবীন্দ্রজীবনের ইতিহাস বলে বাল্যকাল থেকেই বাগানের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। ‘জীবনস্মৃতি’তে বাগান সম্পর্কে লিখছেন এমন, ‘বাড়ির ভিতরে আমাদের যে-বাগান ছিল তাহাকে বাগান বলিলে অনেকটা বেশি হয়’। পঞ্চাশ বছরে কবি সেই ছেলেবেলার বাগানকে বর্ণনা করেছিলেন, ‘একটা বাতাবি লেবু, একটা কুলগাছ, একটা বিলাতি আমড়া ও একসার নারিকেলগাছ তাহার প্রধান সংগতি। মাঝখানে ছিল একটা গোলাকার বাঁধানো চাতাল।’ এই বাগানেই শরতের শিশিরভেজা সকালে ঘাসপাতার গন্ধ বালক-রবিকে মাতাল করে তুলত। এমনতর বাগান দেখে বালক মনে সাধ জেগেছিল বাগান করার। দেখা যাক তাঁর সেই বাগান করার স্মৃতি। ‘বেশ মনে পড়ে, দক্ষিণের বারান্দার এক কোণে আতার বিচি পুঁতিয়া রোজ জল দিতাম। সেই বিচি হইতে যে গাছ হইতেও পারে, একথা মনে করিয়া ভারি বিস্ময় এবং ঔৎসুক্য জন্মিত।’ এছাড়াও বালক-রবির মনে আরও নানারকমের ইচ্ছে জাগত। যেমন, গুণেন্দ্রনাথের বাগানের থেকে পাথর চুপিচুপি না বলে এনে নিজেদের পড়ার ঘরের এককোণে নকল পাহাড় বানিয়ে সেখানে মাঝে মাঝে ফুলগাছের চারা পুঁতে সেবা করার চেষ্টা করতেন।

মনে আছে, শিলাইদহের কুঠিবাড়ির বাগান দেখে অবাক হতে হয়েছিল, কারণ এই সেই কবি এবং কবিপত্নীর হাতে গড়া গোলাপবাগ। এছাড়া আরও নানারঙের ফুল ছিল সে বাগানে। তন্ময় হয়ে দেখতে দেখতে শান্তিনিকেতনের আশ্রম এবং কবির আবাসের চারপাশের বাগানের সৌন্দর্য ভেসে উঠেছিল। লাল মাটির ঊষর প্রান্তরে কবি গোটা আশ্রমকেই নন্দনকানন বানিয়ে তুলেছিলেন। একসময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই রুক্ষ জমিতে ঊর্বর মাটি ফেলার ব্যবস্থা করেছিলেন। বহু অর্থ ব্যয় করতে হয় তাঁকে। আম, জাম থেকে আমলকী, দেবদারু, শাল, সেগুন গাছ লাগিয়েই ক্ষান্ত হননি, মহুয়া, বকুল, কদম, ছাতিম ফুলেরও গাছ লাগিয়ে সফল হন। রবীন্দ্রনাথ ১৮৯০ সালেই কবুল করেছিলেন প্রমথ চৌধুরীর কাছে এই বলে, ‘এই মরুভূমির মাঝখানে আমাদের বাগানটি গাছে ছায়ায় ফলে ফুলে আচ্ছন্ন হয়ে, পাখীর গানে মুখরিত হয়ে, তরুপল্লবের অন্তরাল হতে দৃশ্যাগ্রশিখর প্রাসাদের দ্বারা মুকুটিত হয়ে নিভৃতমহিমায় বিরাজ করচে।’ এবং দীপ্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন ‘এই বোলপুরের বাগান আমাদের ভারি ভাল লাগে।’ মনে হতে পারে এই বাগান তো কবি তৈরি করেননি! কিন্তু তাতে কি কিছু যায় আসে? বাগানকে যিনি ভালোবাসেন, ভালোবাসতে জানেন, তাকে নিজেহাতেই বাগান বানাতে হবে এমন তো দায় থাকার কথা নয়। প্রকৃতিপ্রেমী হবার জন্য কি হাতে গড়ে প্রকৃতি তৈরি করতে হয়?

শান্তিনিকেতনে ‘কোনার্ক’ বাড়িতে থাকাকালীন জানা যায় রবীন্দ্রনাথ একবার বর্ষার শেষে লাল বারান্দার সামনে একটি শিমূল গাছের চারা দেখে তার গোড়ায় সার দিয়ে জল দিয়ে লালন করতেন। ঠিক তার পরের বর্ষায় শিমূলের নীচে দেখা যায় একটি মাধবীলতা। তিনি মাধবীলতাটি তুলে শিমূলের গায়ে জড়িয়ে দেন। আজও সেখানে শিমূল গাছটি মাধবীলতাকে গায়ে জড়িয়েই দাঁড়িয়ে আছে। ‘কোনার্ক’-এর পর কবির থাকার জন্য ‘শ্যামলী’ তৈরি হয়েছিল। ভেবেছিলেন এই বাসাটাই তাঁর শেষবেলাকার ঘর হবে। কবিতায় লিখেওছিলেন সেকথা। চন্দননগরের মোরান নামে এক সাহেবের বাড়িতে থাকাকালীন কবি একটি মাটির ঘর দেখে মুগ্ধ হয়ে সুরেন্দ্রনাথ করকে বলেছিলেন শান্তিনিকেতনে অমন একটি বাসা বানিয়ে দিতে।
কবির ইচ্ছেমতো ঘর তৈরির সঙ্গে সঙ্গে ‘শ্যামলী’র আশেপাশে অনেক লেবু গাছ লাগানো হল। এর মধ্যে পাতিলেবু যেমন ছিল, বাতাবি লেবুর গাছও পোঁতা হল। লেবুফুলের গন্ধ কবি খুব পছন্দ করতেন। এছাড়া সামনের মাটির উঠোনে দুটো গুলঞ্চ ফুলের গাছও বেড়ে উঠেছিল। ‘শ্যামলী’কে ঘিরে আম, জাম, কাঁঠাল, শিরীষ, তেঁতুল, আতা, কুর্চি আর ইউক্যালিপটাস গাছ ছিল। জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ আমগাছের নীচে বসতেন। কখনও কুর্চির তলায় বসে চা খেতেন। কখনও আবার গুলঞ্চের তলায় ছড়ানো সাদা ফুলের মাঝে বসে বই পড়তেন। ‘শ্যামলী’র পর কবি এসে উঠলেন ‘পুনশ্চ’তে। ‘পুনশ্চ’র সামনে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আসা ফুল বোগেনভিলিয়ার ঝাড় সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছিল। রবীন্দ্রনাথ এই ফুলের নামকরণ করেছিলেন ‘বাগানবিলাস’। বোগেনভিলিয়া কবির দৌলতে বাংলা নাম অর্জন করল। ‘পুনশ্চ’ আর ‘উদীচী’র মাঝে এই বাগানবিলাসের সমারোহ।
প্রতিমা দেবীর ‘নির্বাণ’ গ্রন্থে জানা যায় রবীন্দ্রনাথ মনে মনে কল্পিত বাসভবন গড়তেন। এমন একটি কল্পনার কথা রবীন্দ্রনাথ জার্মানি থেকে প্রতিমা দেবীকে লিখেছিলেন। ১৯৩০ সালের ১৮ অগস্ট।
‘থেকে থেকে মনে আসছে তোমার সেই স্টুডিয়োর কথাটা। ময়ুরাক্ষী নদীর ধারে, শালবনের ছায়ায় খোলা জানলার কাছে। বাইরে একটা তালগাছ— খাড়া দাঁড়িয়ে, তারি পাতাগুলোর কম্পমান ছায়া সঙ্গে নিয়ে রোদ্দুর এসে পড়েচে আমার দেয়ালের উপর— জামের ডালে বসে ঘুঘু ডাকচে সমস্ত দুপুরবেলা; নদীর ধার দিয়ে ছায়া-বীথি চলে গেছে— কুড়চি ফুলে ছেয়ে গেছে গাছ, বাতাবি নেবুর ফুলের গন্ধে বাতাস ঘন হয়ে উঠেচে, জারুল পলাশ মাদারে চলেচে প্রতিযোগিতা, সজনে ফুলের ঝুরি দুলচে হাওয়ায়; অশথগাছের পাতাগুলো ঝিলমিল ঝিলমিল করচে— আমার জানলার কাছ পর্যন্ত্য উঠেচে চামেলি লতা।’

এক নিঃশ্বাসে পড়ে গেলে প্রকৃত বাগানবিলাসীর স্বপ্ন বলেই মনে হয়। আসলে বাস্তবের পাশাপাশি তাঁর করিমনে একটি এমন রমণীয় বাগান যে সর্বত্র বিরাজমান ছিল, তা এই চিঠির ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। প্রসঙ্গক্রমে ‘পুনশ্চ’ কাব্যগ্রন্থের ‘বাসা’ কবিতাতেও এই স্বপ্নের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়।
‘…নদীর উপরে বেঁধেছি একটি সাঁকো,
তার দুই পাশের কাচের টবে
জুঁই বেল রজনীগন্ধা শ্বেতকরবী।
গভীর জল মাঝে মাঝে
নীচে দেখা যায় নুড়িগুলি।…’
রবীন্দ্রনাথের কাছে ফুলের অস্তিত্ব ছিল এক অনাবিল আনন্দের প্রতীক। কত যে ফুলের নাম রেখেছিলেন তিনি। অমলতাস থেকে নীলমণি লতা আছে যেমন, আবার বনপুলক থেকে নিমচামেলিও আছে। জানা যায় রবীন্দ্রনাথ ঝোপঝাড়ের জঙ্গল থেকে একটি বুনোফুল এনে বাগানে লাগানোর আদেশ করেছিলেন। পরে এই বুনোফুলেরই নাম দিয়েছিলেন বনপুলক। ইংরেজি অ্যালামন্ডা ফুলকে আদর করে ডাকলেন অলকানন্দা বলে। প্রকৃতিপ্রেমী কবি যে কাননের ফুলফল গাছপালাও পছন্দ করতেন, তা কি আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে?
তথ্যসূত্র:
চিঠিপত্র -১ – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ছিন্নপত্রাবলী – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
পিতৃস্মৃতি – রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
নির্বাণ – প্রতিমা দেবী
শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ – শচীন্দ্রনাথ অধিকারী
গুরুদেব – রানী চন্দ
সব হতে আপন – রানী চন্দ
কবির আবাস ১ – সুরঞ্জনা ভট্টাচার্য
ছবি সৌজন্য: Wikimedia Commons, সমকাল, OneIndia
প্রাক্তন সাংবাদিক। পড়াশোনা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। ষোলো বছর বয়স থেকে কলকাতার নামী পত্রপত্রিকায় লেখালেখির হাতেখড়ি। ছোটোদের জন্য রচিত বেশ কিছু বই আছে। যেমন 'বিশ্বপরিচয় এশিয়া', 'ইয়োরোপ', 'আফ্রিকা' সিরিজ ছাড়া 'দেশবিদেশের পতাকা', 'কলকাতায় মনীষীদের বাড়ি', 'ঐতিহাসিক অভিযান', 'শুভ উৎসব' ইত্যাদি। এছাড়া বর্তমানে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নানা গবেষণার কাজে নিবেদিত। ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। 'রবীন্দ্র-জীবনে শিক্ষাগুরু' এবং 'রবীন্দ্র-গানের স্বরলিপিকার'। বর্তমানে একটি বাংলা প্রকাশনা সংস্থায় সম্পাদক।



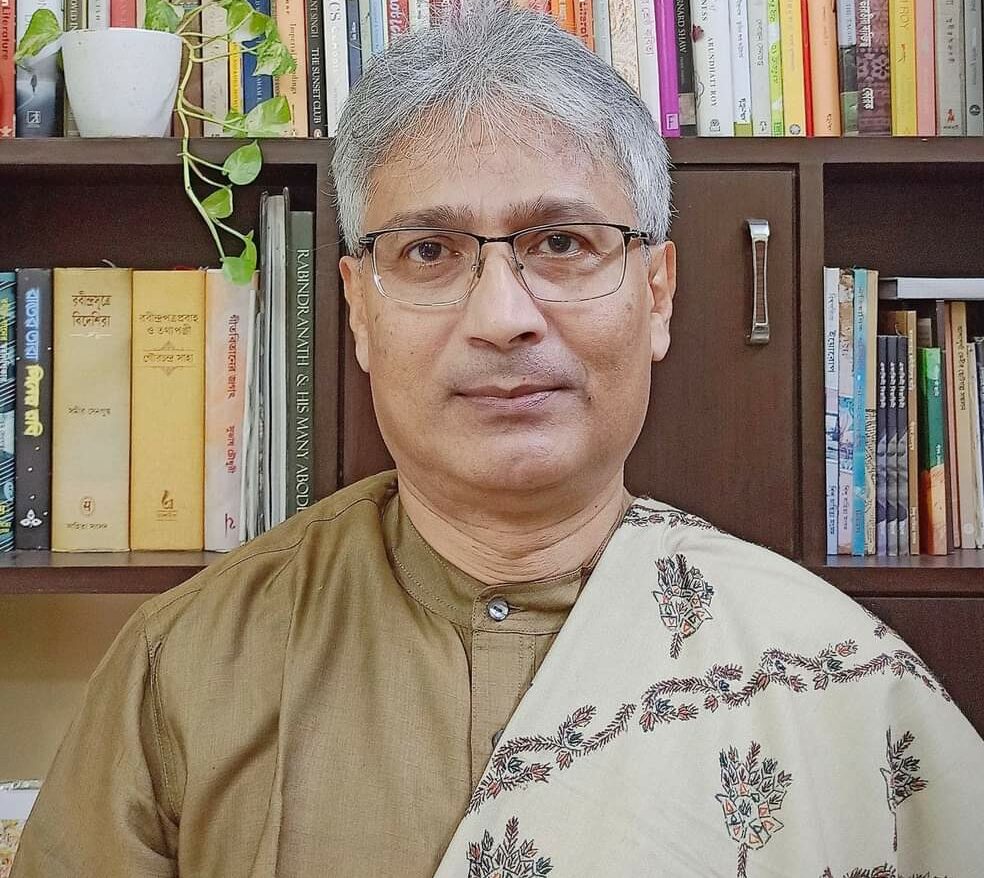






















One Response
স্বপন গুপ্তে’র পরিচয় লিপি পড়ে পঞ্চান্ন ষাট বছরের পুরোনো বাল্যকাল শৈশবের স্মৃতি আবার উজ্জ্বল হয়ে ধরা দিল!
মনে পড়ে গেল ,সেই অধীর আগ্রহে আকাশবাণী কলকাতার শুক্রবার রাত সাড়েন’টার রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুরোধের আসরের প্রতিক্ষা করা, কখন প্রিয় শিল্পী স্বপন গুপ্তে’র কন্ঠস্বরে ওই দুটি গানের কোনো টি শুনতে পাবো।