১৯৭৩-এই উস্তাদ হাফিজ আলি খাঁ (Hafiz Ali Khan) মেমোরিয়াল মিউজিক ফেস্টিভাল হল কলকাতায়। উফ্! অত অসাধারণ সংগীত মহোৎসব দেখিনি এ জীবনে। ১৫ ডিসেম্বর থেকে পাক্কা সতেরো দিন ধরে চলল সেই যজ্ঞ সদ্য উঠে আসা কলামন্দির হলে, যার মধ্যে তিনটে সারারাতের অনুষ্ঠান। উদ্বোধনের সন্ধ্যায় বাজালেন হাফিজ আলি খাঁ সাহেবের সুপুত্র আমজাদ আলি খাঁ। তারপর নানা সন্ধ্যায় রবিশঙ্কর, আলি আকবর, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিলায়েত খাঁ, হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়া, ইমরাত খাঁ তাঁদের সেতার, সরোদ অথবা বাঁশি নিয়ে। নাচের আসরে এলেন বিরজু মহারাজ, যামিনী কৃষ্ণমূর্তি। আর গানের জলসা ভরিয়ে তুললেন আমির খাঁ, সিদ্ধেশ্বরী দেবী, ভীমসেন যোশী, প্রসূন ও মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়, সালামৎ আলি খাঁ, মুনাব্বর আলি খাঁ— কে নয়! ৩১ ডিসেম্বরের শেষ অনুষ্ঠানে ভোরের দিকে গাইতে বসলেন আমির খাঁ সাহেব, আর ধরে নিলেন ললিত! আর হায়, হায়, সে কী গান! ললিতে তখনও গান ভরে আছে যখন শ্রোতার অনুরোধে ধরে নিলেন ভটিয়ার। ভটিয়ার তার আগেও বহু শুনেছিলাম, কিন্তু সেদিনের ভটিয়ার যেন স্বর্গ থেকে অবতীর্ণ! খাঁ সাহেবের এই খেয়াল দুটির রেকর্ডিং পরেও কয়েকবার শুনেছি ওর শিষ্যা পূরবী মুখোপাধ্যায়ের সংগ্রহ থেকে এবং প্রতিবারই পূর্বের মতোই বিস্ময়ে বোবা মেরে গেছি। ওই স্পুলেই ধরা ছিল খাঁ সাহেবের আরও কয়েকটা হোম রেকর্ডিং। যার একটিতে খাঁ সাহেব মজা করে গাইছেন বেগম আখতারের বাংলা গান ‘এ মৌসুমে পরদেশে যেতে তোমায় দেব না’! Oh my God! Oh my God! সে যে কী ঠুংরি rendering তা জন্মেও ভোলার না। পূরবীদির সঙ্গে একেক দফায় পাঁচ-সাতবার করে শোনা হত খাঁ সাহেবের ‘এ মৌসুমে’ আর দু’জনেই আমরা গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসতাম—আর এই মানুষটাই জীবনে ঠুংরি গাইলেন না!
আমির খাঁ সাহেবের কণ্ঠে রাগ ভাটিয়ার
তো, যে কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম সেখানেই ফিরি। হাফিজ আলি খাঁ সংগীত সম্মেলনের উদ্যোক্তা আমজাদ আলি খাঁর বল ও ভরসা ছিলেন আমারই কোম্পানির কর্তা অরূপ সরকার। তিনি তখন তাঁর মনের মতো কাজ এলেই আমাকে ধরিয়ে দেন, হাত ভরে টাকা দিয়ে। তো এই কনফারেন্সের প্ল্যান হচ্ছে যখন, ওঁর মাথায় খেলল একটা অসাধারণ ব্রোশিওরের আইডিয়া। শুধু সম্মেলন নয়, ফেস্টিভালের সুভ্যেনিরও হতে হবে ঐতিহাসিক। হাফিজ আলি খাঁ সাহেবের (Hafiz Ali Khan) জীবন, কাজ, সংগীতে অবদান ও তাঁর সরোদের সুর, লয়, ছন্দ, তালও সর্বোপরি। সে যন্ত্রের অপরূপ আওয়াজের কথাও তুলে আনতে হবে লেখায় লেখায়। আর সে জন্য প্রয়োজন দুটি মানুষের দীর্ঘ আলাপ— বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও রাইচাঁদ বড়াল।
পণ্ডিত বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ছিলেন অসামান্য ধ্রপদিয়া, যে ধ্রুপদজ্ঞান তিনি ধারণ ও বিস্তার করতেন বীণ ও সুরশৃঙ্গারে। তিনি অতি উত্তম পর্যায়ের রবাবিয়াও ছিলেন। আমার বন্ধু সুব্রতদা (সেতারি সুব্রত রায়চৌধুরী) মাঝেমধ্যেই বীরেনবাবুর কাছে সুরশৃঙ্গারের পাঠ নিতে যেতেন এবং আমাকে সঙ্গে নিয়ে। শেখাটা মৌখিকই হত। বীরেনবাবু তখন চোখে দেখতে পান না, কিন্তু বড় কালো চশমায় চোখ ঢেকে মাঝে মাঝে বীণে আঙুল চালিয়ে মুখে মুখেই বলে ও গেয়ে যেতেন ধ্রুপদের অঙ্গ। তাতে থেকে থেকেই গায়ে কাঁটা দিত আমাদের।

শিষ্য সুব্রতর জন্য বীরেনবাবুর দুটি বিশদ শিক্ষা জীবনেও ভোলার নয়। ধ্রুপদের চার বাণীর মধ্যে গৌহর ও নৌহর বাণী। রামপুরের মহৎ বীণকার উজির খাঁ’র নাতি উস্তাদ দবির খাঁর কাছে তালিম নিয়েছিলেন বীরেনবাবু। যে উজির খাঁ ছিলেন তানসেনের কন্যা, সরস্বতীর সাক্ষাৎ বংশধর। বীরেনবাবু শিক্ষা করেছিলেন বাবা আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের কাছে, পাঠ নিয়েছিলেন সেতারি বিলায়েত খাঁর পিতামহ এমদাদ আলি খাঁর কাছে এবং উস্তাদ হাফিজ আলি খাঁর কাছেও। নানান সাগর যেন এসে মিশেছে এই এক বীণগুরুর ধ্যানে ও ধনে। ধ্রুপদের চার বাণীর নামকরণ, চরিত্র ও চলন নিয়ে যেদিন বলছিলেন সেই স্মৃতি আজও ছেয়ে আছে মনে। এক-এক করে বুঝিয়েছিলেন গৌহর বাণী, খণ্ডর বাণী, নৌহর বাণী ও ডাগর বাণীর চিন্তা, চরিত্র ও বিশেষত্ব। নৌহর বাণীর নদী ও জলযানের চলন বোঝাতে ওঁর খাটের ওপর আঙুল খেলিয়ে নৌকার ভঙ্গি দেখালেন। তারপর ডাগর বাণী ক্রিয়া বোঝাতে তুলে নিলেন বীণ। সুব্রতদাও তখন সেতার ধরলেন। আমার মনে হতে লাগল আমরা কলকাতার বালিগঞ্জ পাড়া নয়, চালান হয়ে গেছি কোনও ধ্রুপদ আশ্রমে।
বড় পরিতাপের বিষয় যে হাফিজ আলি খাঁ সংগীত সম্মেলনের জন্য বীরেনবাবুর সঙ্গে নতুন করে আলাপচারিতায় বসা গেল না। কারণ তার সামান্য আগেই তিনি দেহরক্ষা করেছেন। হাফিজ আলি খাঁকে নিয়ে তাঁর আগের কোনও লেখা ব্যবহার করতে হয়েছিল বলে মনে হয়। তবে হাফিজ আলি খাঁর স্মৃতি নিয়ে বলার জন্য তখনও দিব্যি বিরাজমান ওঁর সরোদের সঙ্গে দিনের পর দিন রেওয়াজে বসে সাথসঙ্গতে বিশাল দিগগজ হয়ে ওঠা রাইচাঁদ বড়াল। সেসময় তিনি দিনের পর দিন জলসায় সঙ্গত করে গেছেন নানা শিল্পীর সঙ্গে লখনউ, এলাহাবাদ, বেনারসে। তবলা শিল্পী হিসেবে যখন দেদার নাম ছড়াচ্ছে দেশে রাইচাঁদ সরে গেলেন সিনেমা জগতে। তাঁর সুর করা দেড়শোর মতো হিন্দি ও বাংলা ছবির গান দিনে দিনে ইতিহাস হয়ে উঠল। এত এত স্মরণীয় গানের নির্মাতার খ্যাতির আড়ালে প্রায় চাপা পড়ে গেল তাঁর তবলা সঙ্গতের জীবনকথা।

বলা বাহুল্য, কয়েকদিন ধরে তাঁর গুরু হাফিজ আলি খাঁ’র গল্প ও কাজের কথা শুনছি যখন, রাইবাবু বাস্তবিকই আহ্লাদে আটখানা। মুহুর্মুহু চা আর সিঙারা আসছে দু’জনার সামনে আর শুনতে হচ্ছে ‘পেটে চা না পড়লে কথা আসবে কোত্থেকে? খাও খাও।’ বলেই চা তুলছেন ঠোঁটে।
হাফিজ আলি খাঁ একসময় কলকাতা এলে রাইবাবুদের বাড়িতেই উঠতেন। সেই ঘরটাও দেখালেন আমাকে। ‘খাঁ সাহেবের রেওয়াজের রকম কী ছিল জানো?’
জিজ্ঞেস করতেই হল, ‘কী রকম?’
বললেন, ‘সারারাত ঘরে মোমবাতি জ্বলত। একেকটা মোমবাতি দেড় ফুট লম্বা। ওঁর রাতের রেওয়াজের সময় বার করা হত ক’টা মোমবাতি জ্বলেছে তা দিয়ে। কোনও রাতে রেওয়াজ হত তিন বাতি, কোনও দিন চার, আবার কোনও দিন পাঁচ বা ছয়। ‘ছে বাতিকে রিওয়াজ’ মানে সারারাত। আমার সৌভাগ্য যে এরকম ওঁর অনেক রেওয়াজেই সঙ্গত করে কাটিয়েছি, শিখেছি।’
‘এত জোরালো, ভরাট আওয়াজ ওস্তাদের, অথচ কী সুরেলা মধুর। একবার তড়াং করে স্ট্রোক পড়লেই কান, মন জুড়িয়ে যেত। জ্ঞানগম্যি, পাণ্ডিত্য তো পরে আসবে। আর এরকম এক মানুষকে সেকালের এক লড়াকু তবলিয়া চ্যালেঞ্জ করে বসল। দেখা যাক, লড়ন্ত সঙ্গে কে কদ্দুর বোলে, তালে, লয়ে ছুটতে পারে। আমার ওস্তাদ সে লড়াইয়ে ঢুকতেই চাননি। কিন্তু সে তবলিয়া নাছোড়। শেষে সেই লড়াই চড়তে চড়তে এমন এক চড়ায় উঠল যে তবলার ওপরই হার্ট ফেল করে মারা পড়ল ছোকরা। খাঁ সাহেবের তখন কী যে দুঃখ, কেন আমি বাজনা থেকে সরে গেলাম না!’
হাফিজ আলি খাঁ’র বাজনা
হাফিজ আলি খাঁকে নিয়ে কথাবার্তা, লেখালিখির পর্ব যেদিন শেষ হল সেদিন এক তাজ্জব করা ঘটনাও ঘটল। দোতলায় আমাদের কাজের জায়গা থেকে নেমে রাইবাবু আমাকে একতলার হলের পাশে এক থামের সামনে নিয়ে দাঁড় করালেন। থামে এক বড় ফ্রেমে বাঁধানো এক অতীব রূপসী মহিলার ছবি। রাইবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ‘ইনি কে জানো?’
আমি মাথা নাড়তে রাইবাবু বললেন, ‘দ্য ওয়ান অ্যান্ড ওনলি মুশতারি বাই!’
আমি যথেষ্ট চমকেছি দেখে ফের বললেন, ‘তোমরা নামই শুনেছ, গান তো শোনোনি। কয়েকখান রেকর্ড ওঁর আছে, পরে একদিন এসে শুনিয়ে দোবখন। ও জিনিস, খোকা, হয় না, হয় না। আর বলব কী, এই বাড়িতেই জলসায় সেবার গাইতে এলেন। হেন বড় গাইয়ে বাজিয়ে নেই যিনি আসরে শুনতে বসলেন না। কী মিষ্টি আওয়াজ আর সুরেলা, গভীর কারুকাজ। দুটো না তিনটে খেয়াল গেয়েছিলেন। তার আগে যা শুনেছি সব কান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ শুনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আমায় ফোনে ডাকছেন। ছুটে গিয়ে ফোন ধরতে বললেন, ‘এ দেবীর সন্ধান কোথায় পেলে, রাই?’
আমার তখনই খেয়াল হল জলসার এই প্রোগ্রাম অল ইন্ডিয়া রেডিওর প্রথম ওবি অর্থাৎ আউটসাইড ব্রডকাস্টিং। তাই জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বসে রেডিওয় এই অনুষ্ঠান শুনেছেন। বললাম, গুরুদেব, বললে কালই আপনার কাছে নিয়ে আসব ওঁকে।
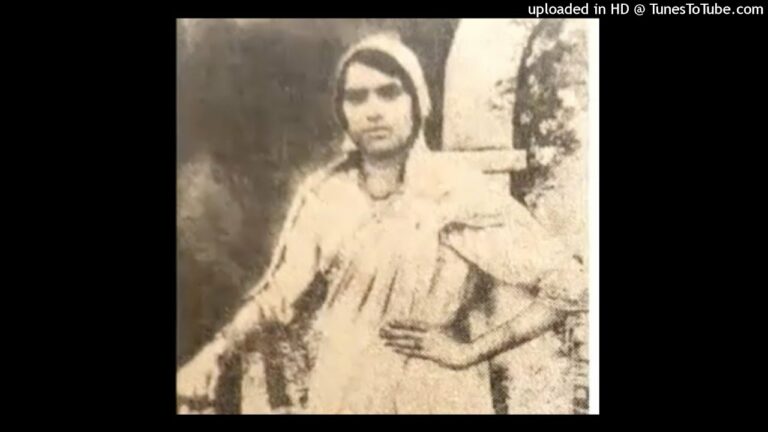
গান শেষ হবার পর মুশতারিকে এ কথা বলতে সেও তো প্রায় মূর্চ্ছা যায়। বললেন, ঠাকুর সাহাবের ভাল লেগেছে আমার গান! আরও শুনতে চান? আমি কাল সকালেই ওঁর দর্শন নিতে যাব।
যেই বললাম, ‘চলুন তাহলে’ মুশতারি বললেন, তাহলে দশ সের সন্দেশ আর দশ ফুটের একটা মালা তৈরি করে আনান। শুনেছি ঠাকুর সাহাব লম্বা মানুষ। আর উনি যা গাইতে বলবেন আমি গাইব। আর উনি চাইলে ওঁর কিছু গানও তালিম নিয়ে শিখে ওঁকে শোনাব কোনওদিন।’
এই সব কথা হচ্ছিল মুশতারি বাইয়ের সুন্দর ছবিটার সামনে। কথা শেষ করে স্মৃতিমগ্ন রাইবাবু দেখি একদৃষ্টে চেয়ে আছেন ছবিটার দিকে। এক সময় আমার হাত দুটো জড়ো হয়ে কপালে উঠে এল প্রণামের ভঙ্গিতে।
*ছবি সৌজন্য: Facebook
*পরের পর্ব প্রকাশ পাবে ডিসেম্বর, ২০২৩
শংকরলাল ভট্টাচার্যের জন্ম ১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট, কলকাতায়। ইংরেজি সাহিত্যে স্বর্ণপদক পাওয়া ছাত্র শংকরলাল সাংবাদিকতার পাঠ নিতে যান প্যারিসে। তৎপরে কালি-কলমের জীবনে প্রবেশ। সাংবাদিকতা করেছেন আনন্দবাজার গোষ্ঠীতে। লিখেছেন একশো ত্রিশের ওপর বই। গল্প উপন্যাস ছাড়াও রবিশংকরের আত্মজীবনী 'রাগ অনুরাগ', বিলায়েৎ খানের স্মৃতিকথা 'কোমল গান্ধার', হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিমালা 'আমার গানের স্বরলিপি'-র সহলেখক। অনুবাদ করেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা থেকে সত্যজিৎ রায়ের চিত্রনাট্য পর্যন্ত।

























