‘মায়ের আদর’ বললেই যেন একটা ভারী সুন্দর সুঘ্রাণ নাকে এসে লাগে। তাতে কখনও মিশে থাকে নারকেল তেলের গন্ধ, কখনও গরমের বিকেলে জুঁইফুলের সুবাস, কখনও পন্ডস ট্যালকম পাউডারের ফিনফিনে সৌরভ, আবার কখনও বা স্রেফ সদ্য-ফোটা গোবিন্দভোগ চালে গাওয়া ঘিয়ের আকুল করা আঘ্রাণ। এরমধ্যে কোনটা যে আলাদা করে মা মা গন্ধ, বোঝা ভারী শক্ত। কোনটার মধ্যে যে মিশে আছে মায়ের আদর, ঠাহর করা যায় না আলাদা করে। কেবল ‘মা’ বলে ডাকলেই যে একটা গালভরা ভালোবাসার শালিকপাখির ‘কুইচ’ করে লাফিয়ে ওঠা বুকের মধ্যে, সেটাই যেন ফিরে ফিরে আসে এই গন্ধবাসনার অনুষঙ্গে।
প্রসঙ্গত জানানো যাক, এই মাতৃদিবস পালনের শুরু কিন্তু মার্কিনদেশে, উনিশ শতকের শেষে। গৃহযুদ্ধে আমেরিকা তখন ক্ষতবিক্ষত। সেইসময় মায়েদের নিয়ে, মায়েদের অধিকার নিয়ে লড়াই শুরু করেছিলেন অ্যান রিভজ জারভিস। অন্তঃসত্ত্বা মায়েরা যাতে একত্রিত হয়ে নিজেরাই নিজেদের সাহায্য করতে পারেন, তাই শুরু করেছিলেন প্রাথমিক জনস্বাস্থ্য আন্দোলন। সংগঠনের নাম দিয়েছিলেন ‘মাদার্স ওয়র্ক ক্লাব’। যুদ্ধ থেমে যাবার পরেও বিজয়ী এবং বিজিত, দু’পক্ষের মায়েদের জন্যই নানারকম কাজ করে গিয়েছেন অ্যান। পরে সেই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যান তাঁর কন্যা অ্যান মারি জার্ভিস। তিনিই মার্কিনদেশে মাদার্স ডে পালনের সূচনা করেন, ফি বছর মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে, নিজের মায়ের স্মৃতিরক্ষার্থে। ক্রমে আমেরিকা থেকে বিশ্বের ৪৬টি দেশে ছড়িয়ে পড়ে মাদার্স ডে-র ধারণা, যদিও দেশভেদে পালনের সময় হয়তো আলাদা। ভারতে মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই মাদার্স ডে পালিত হয়।
সেই ঘরে-বাইরে কর্মরতা, নিঃস্বার্থ ভালোবাসার উৎস, যত্ন-পরিচর্যা-সাহচর্যের যে রূপটি ‘মা’ বলতেই মনে জেগে উঠত, তার বাইরের চেহারায় অনেকটা বদল হয়েছে নিশ্চয়ই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। মা মানেই সারাদিন কাজ সেরে আঁচলে ঘাম মুছতে মুছতে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়ানো, এলোখোঁপা আর সিঁদুরটিপ, এখন আর নেই বললেই চলে। তা নিয়ে আধুনিকা মায়েদের কম সমালোচনা শুনতে হয় না আগের প্রজন্মের কাছে। তা সত্ত্বেও নতুন প্রজন্মের মায়েরা নতুন করে লিখে চলেছেন মাতৃত্বের সংজ্ঞা। ‘মায়ের আদর’ মানেই যে জ্বরের সময় রাতজেগে জলপটি কিংবা দিনভর রান্নাঘরের আঁচে খুন্তি নাড়া, এ ধারণা অতীত করবার সময় এসেছে। ‘মায়ের আদর’ মানে হয়ে উঠুক না, অফিস থেকে ফিরে ফুড ডেলিভারি অ্যাপে আনানো আইসক্রিম খেতে খেতে একসঙ্গে টিভিতে সিনেমা দেখা কিংবা উইকেন্ড ট্রিপে গাড়ি চালিয়ে মন্দারমণি? তাতে কি আদর কিছু কম পড়বে? মনে তো হয় না!
তবুও মাতৃদিবসে পাঁচজন লেখকের কাছে আমরা জানতে চেয়েছিলাম তাঁদের মায়ের হাতের রান্না বলতে প্রথমেই কোন স্বাদের কথা মনে পড়ে– এঁরা হলেন, কবি মন্দার মুখোপাধ্যায়, খাদ্য-ইতিহাস গবেষক পিনাকী ভট্টাচার্য, লেখক ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় ও আলপনা ঘোষ এবং শিক্ষিকা শ্রুতি গঙ্গোপাধ্যায়। শ্রুতি ছাড়া বাকি সকলেই মাতৃহারা হয়েছেন। মা-কে কাছে না-পাওয়ার দুঃখ ভুলে তাঁরা জানালেন মায়ের হাতের সেই বিশেষ পদটির কথা, যার স্বাদগন্ধ এখনও তাঁদের রসনায় অমলিন। বাংলালাইভের উদ্দেশ্য, এক আধদিন শখের রাঁধুনে মায়েদের হাতে হাতে গরমাগরম রেসিপি তুলে দিয়ে তাঁদের কাজ সহজ করা! আর কী, হ্যাপি মাদার্স ডে!

সংসারে প্রতিদিন রান্না করলেও, এ ব্যাপারে আমাদের মায়ের উৎসাহ ছিল প্রায় ‘নাস্তি’। আসলে রান্না নয়, তিনি ভালোবাসতেন মিটিং এবং নিটিং। তবে দুটি রান্নায় বেশ কোমর বেঁধে লেগে পড়তেন। একটি হল আমার দিদিমার ছাঁদে রান্না পদ– বড়ার ঝাল আর অন্যটি হল, নিজের পছন্দের পেয়ারার জেলি।
ঘটিবাড়ির বড়ার ঝাল
মটরডাল আগের রাতে এক চিমটে সোডা দিয়ে ভিজিয়ে পরদিন ধুয়ে জল ফেলে, গোটা ডাল অল্প একটু সরিয়ে রেখে, বাকিটা শিলে বাটা; কিন্তু মিহি করে নয়। মানে একটু কচকচে– দানা দানা। সঙ্গে কাঁচালঙ্কা, আদা আর দু’তিনটে গোলমরিচ। ডালবাটার শিলটা না ধুয়ে তাতেই শুকনোলঙ্কা, সরষের তেল ও নুন দিয়ে জল ছাড়া বেটে নিতে হবে। সাদা ও কালো সরষের পেস্ট; সাদা একভাগ তো, কালো তিনভাগ। এবার মশলা দেওয়া কচকচে করে বাটা ডালের সঙ্গে সরিয়ে রাখা ভেজা ডাল ভালো করে মেখে, হাত আন্দাজ বড় বড় ডালের বড়া ছাঁকা তেলে ভেজে একটু জল ছিটিয়ে দিতে হবে। আরও ভাল হয় ভিজে ন্যাকড়ায় মুড়ে দিলে।

এরপর শুকনোলঙ্কা, পাঁচফোড়ন আর হিঙের ছোঁক দিয়ে, তাতে লম্বা লম্বা করে কাটা আলু এবং দু’ফালা পটল আবার তেরছা করে চারফালায় কেটে নুন ও বাটা হলুদে কষা; কষতে কষতে একটু লালচে রঙ ধরলে সামান্য জল হাতে করে ছিটিয়ে ঢাকাচাপা দিয়ে নরম করে নিতে হবে। এরপর বড়াগুলো নেড়ে চেড়ে আরও একটু ডুবো জল। ফুটে উঠে জল কমে গেলে সরষের পেস্ট দিয়ে মাখামাখা এবং এক চিমটে চিনি দিয়ে নাড়া। নামাবার আগে ছোট্ট বাটিতে সরিয়ে রাখা আন্দাজ মতো বাটা আদা, বাটা হলুদ, সরষের পেস্ট আর দু’পলা সরষের তেল ভাল করে মিশিয়ে কড়ায় দিয়ে নাড়লে ঝাঁঝ উঠবে। খুন্তি ঘোরালেই, কড়ার গা থেকে এমন মাখনের মতো ছেড়ে আসবে মাখা মাখা ডালবড়ার ঝাল যে কড়াখানি দেখলে মনে হবে সদ্য মাজা। ডাল বাটার অসুবিধে থাকলে, একইভাবে বেসনের বড়া দিয়েও করা যায়।
পেয়ারার জেলি
আমার মেমসাহেবি ধাঁচের মা ভাল বাসতেন কেক, পুডিং, স্যুপ আর স্যান্ডুইচ। বাবার সাহেব ধাঁচার সহযোগে ছিল বালির তাতে বানানো ঘরোয়া কেক এবং ধোঁওয়া ওঠা এগ নুডলস; আর ছিল নিজের এয়ারগান দিয়ে শিকার করা বটের তিতির রোস্ট। শিমলায় বড় হওয়া মায়ের স্বাদেও বিদেশি জ্যাম, জেলি আর মেয়োনিজ়। পরে শিলংয়ের বন্ধু মুক্তিমাসির কাছে শিখেছিলেন পেয়ারার জেলি বানানো। সারাজীবন জেলি বানিয়েছেন প্রবল আহ্লাদে। কেজিখানেক পাকা পেয়ারা সেদ্ধ করে, জল ছেঁকে তুলে, নতুন গামছায় ফেলে সে এক পর্ব। অনেকটা যেন সেই পুকুরে মাছ ধরার মতো। বাবা আর মা লম্বা করে টেনে, দু’দিক দু’জনে ধরে আছেন। আর ঠাকুমা মধ্যিখানে মোড়া নিয়ে বসে একটা কাঠের ডালঘোঁটনা দিয়ে পেয়ারা কাঁচিয়ে রস বের করে চলেছেন। নীচে রাখা বড় একটা পাথরের বাটিতে, কাপড়ে ছাঁকা সেই রস ঝরঝর করে ঝরে পড়ছে।

আগে থেকে করে রাখা প্রায় দেড় কেজি চিনির রস তাতে মিশিয়ে এবার এলুমিনিয়ামের সসপ্যানে সেটা ফুটিয়ে গাঢ় করা হল। নামাবার সময় একটু জিলেটিন আর সোনালি আভার সামান্য সবুজ রঙও মেশানো হল। ইতিমধ্যে আমাদের দু’বোনের কাজ হল, খানদশেক এক মাপের ধোয়া কাচের শিশিতে একটা করে চামচ দিয়ে হাঁ করে মুগ্ধ তাকিয়ে থাকা। ইতিমধ্যে বাবা আবার শিশির লাল ঢাকনাগুলোর ভেতরে মোম গলিয়ে পলেস্তারা করে দিতেন। ফাইনালি বড় হাতায় করে সার দেওয়া শিশিগুলোতে জেলি ঢেলে ঠান্ডা করতে দেয়া হত। একেবারে ঠান্ডা হয়ে গেলে চামচগুলো বের করে মোম মাখানো ঢাকা দিয়ে শিশিগুলো সিল করা হতো। শিশিগুলোর গায়ে স্টিকার লাগিয়ে এক দুই তিন করে নম্বর এঁকে দিতেন, যাতে একসঙ্গে সব শিশি খোলা না হয়। নরম পাঁউরুটির একপিঠে মাখন আর অন্যপিঠে ওই জেলি লাগালেই আমাদের এমন খিদে পেত যে, অন্তত ছয়মাসের জন্য বানানো জেলির শিশি ফাঁক হতে মাস দুয়েকও লাগত না।
*ছবি সৌজন্য: Stockfood, Youtube
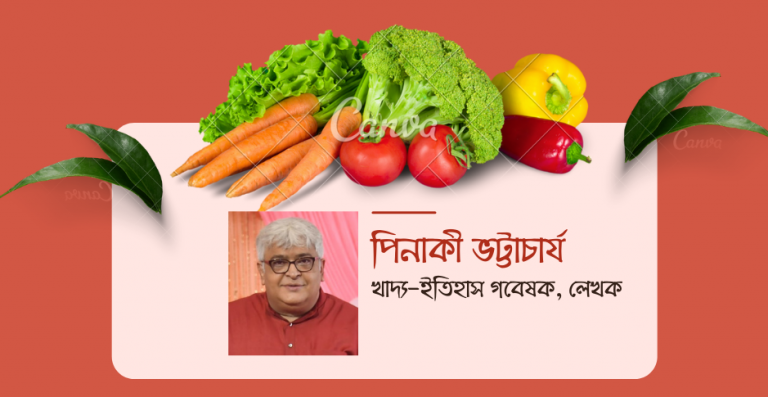
বেশ কিছুদিন আগে বাংলালাইভে ফিউশন খাবার নিয়ে লেখার সময় বোহেমিয়ানের শ্যেফ জয় বলেছিল, রান্না হচ্ছে একটা অর্কেস্ট্রার মতো– কোনও উপাদান বেশি অথবা কম হলেই সুর কাটবে। মায়ের রান্নার কথা মনে করলে আমার কিন্তু অর্কেস্ট্রা নয়, ভারতীয় মার্গসঙ্গীত মনে পড়ে। সেই সময়টা– যখন তবলা, হারমোনিয়াম আর সারেঙ্গি, বা কখনও বীণা, শুধু এই কয়েকটা বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে আবদুল করিম খাঁ, ফৈয়াজ খাঁ, মৈজুদ্দিনরা নীল দিগন্তে ম্যাজিক ছড়িয়ে দিতেন। অমিয় সান্যাল থেকে কুমারপ্রসাদ, সবাই এ ব্যাপারে এক সুরে গেয়েছেন যে সেকালে সারেঙ্গিবাদকরা সুরের জগতে যদিও কৌলীন্য পেতেন না, কিন্তু পাকা সারেঙ্গির সঙ্গত ছাড়া নামী ওস্তাদদের গানের জৌলুস ফিকে হয়ে যেত।

মায়ের রান্না পায়েসও অনেকটা এমনই। কাজু-কিশমিশ লাগত না সুস্বাদু করার জন্যে। সেই পায়েসের সুরে সারেঙ্গিবাদক হিসেবে থাকত চাল, এক্কেবারে দুধের তালে সঙ্গত করার জন্যেই যেন সে রান্নাঘরে এসেছিল। চিনি অথবা খেজুরগুড় অনেক নামী তবলিয়াদের মতো ঢক্কানিনাদ করত না, শামতাপ্রসাদ বা হিরুবাবুর মতো নিজেকে উজাড় করে দিত পায়েসের দুধের মধ্যে। মায়ের রান্না চাপড়িঘণ্টতে পেতাম এক বিসমিল্লা খাঁ আর ভি জি জোগ-এর ডুয়েট- পাকা উচ্ছে আর মটরডাল বাটা স্রেফ মূর্ছনা সৃষ্টি করত থালার ওপর। কেউ কাউকে ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা না করে এক সুরে বেজে চলত। মায়ের রান্না পোলাওতে পেতাম পরিমিতিবোধ– চাল ধোয়া থেকে শুরু করে আদার পরিমাণ, সমস্ত কিছুতে এক তাল, এক সুর মিশে থাকত। নবদ্বীপের গোঁড়া গোস্বামী পরিবার থেকে বেথুন কলেজ হয়ে ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়- সবিতা ভট্টাচাের্যর এই মহাপ্রস্থান-সদৃশ বন্ধুর পথ সাফল্যের সঙ্গে পাড়ি দেওয়ার রহস্য সম্ভবত সময়ের কাজ সময়ে করা আর পরিমিতিবোধ। তাই পোলাও হোক, কি চাপড়িঘণ্ট– আদার পরিমাণ ঠিক কী হবে, বা কখন দিলে স্বাদ খোলতাই হবে, মা জানতেন।

শাশুড়ি মায়ের রান্না কালচে রঙের কষা মাংস আমার খুব প্রিয় আর একটা পদ। তাতে বোঝা যেত মাংস কষার কেরামতি। জল সেখানে থাকত নামমাত্র, শুধু মাঝেমাঝে একটু জল আঁজলা করে ছিটিয়ে দেওয়া। সেই পরিমিতিবোধের গল্প। নিরামিষের মতো আমিষ রান্নাতেও একইভাবে প্রযোজ্য। কেউ একজন বলেছিল, রান্নায় চা-পাতা ভেজানো জল দিলে কালচে রঙটা সহজে আসে। উনি তাকে দাবড়ে বলেছিলেন, ভালো রান্না ফাঁকিবাজি করে আর রঙ মিশিয়ে হয় না।
মফসসল থেকে এসে কলকাতায় বাস করা পরিবারে আত্মীয়ের ঢল লেগেই থাকত। পরীক্ষার আগে পড়া ছেড়ে বৈঠকখানায় গিয়ে আড্ডা দিতে দেখলে পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মা একটা ভয়ানক চিমটি কাটতেন সবার চোখ বাঁচিয়ে। আজকে এই বয়েসে মায়ের হাতের রান্নার মতোই মিস্ করি সেই চিমটিটা- পরিমিতিবোধ আজও তৈরি হল না আমার। সময়ের কাজ যে কোনদিনই সময়ে করে উঠতে পারলাম না!
পুনশ্চ: মা চলে গেছেন বেশকিছু বছর হয়ে গেল। শাশুড়ি-মা আছেন। তবু পুরো লেখাটা অতীত-কথন হল, কারণ উনি বহুবছর আমাকে আমার প্রিয় কালচে রঙের কষা মাংস খাওয়াননি।
*ছবি সৌজন্য: Unfoldbangla, Betterbutter
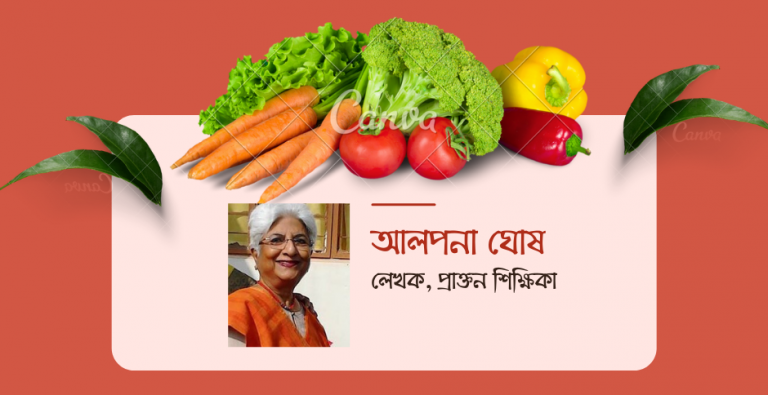
লক্ষ্মীপুজোর ভুনি খিচুড়ি
বিজয়া দশমীর রেশ কাটতে না কাটতেই আমাদের বাড়িতে শুরু হয়ে যেত কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর প্রস্তুতি। পুজোর আগের দিন পুজোর কাজ গোছানো শুরু হয়ে যেত। বাবা কাকারা বাজার, ঠাকুর কেনা, পুজোর জায়গা চাঁদমালা আর কাগজের ফুল দিয়ে সাজানো, ইত্যাদি কাজ সেরে ফেলতেন। তবে সব কাজের মধ্যমণি ছিলেন আমার ছোট্টখাট্ট লক্ষ্মীমন্ত চেহারার মা। পুজোর দিন সকাল থেকে নিরম্বু উপোস। সারা বাড়ি জুড়ে ধানের শিষের আলপনা আর মা লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ, ফল কাটা, নৈবেদ্য, সব যে কী করে মা একা হাতে করতেন, আজ এই ৭৬ বয়সে পৌঁছেও আমার কাছে এক পরমাশ্চর্য ব্যাপার বলে মনে হয়। কিন্তু এসব বাদ দিলে, এ পুজোর মুখ্য আকর্ষণ ছিল আমার মায়ের হাতের রান্না ভুনি খিচুড়ি। লক্ষ্মীপুজোর ভোগ। এখনও মনে পড়ে, আমাদের দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের কথা। তিনি ছিলেন মার্ক্সবাদী কট্টর বামপন্থী, ঘোর নাস্তিক। অথচ যথাকালে পুজো শুরু হবার ঠিক আগেই তিনি বাড়িতে হাজির। কেন? কারণ আর কিছুই নয়, মায়ের হাতের ভুনিখিচুড়ির অমোঘ আকর্ষণ।

যতদিন বাড়িতে কয়লার উনুনের চল ছিল, আমার মা উনুনের সামনে পিঁড়ি পেতে বসে রান্না করতেন। পুজোর দিন মাঝদুপুরে শুরু হত ভুনি খিচুড়ি রান্না। ঝকঝকে পিতলের ডেকচিতে মা রাঁধতেন। উনুনের আঁচে মায়ের মুখে লাল আভা। লালপাড় শাড়িতে ঘোমটা টানা মা-কে যে কী সুন্দর দেখাত। কী পরিপাটি করে রাঁধতেন। খিচুড়ির গন্ধে সারা বাড়ি ম’ ম’ করত। রান্নার শেষে ভোগ নিবেদন। আমরা সবাই অধীর অপেক্ষায়, কখন আমাদের পাতে পড়বে স্বাদে গন্ধে অপূর্ব সেই সেই ভোগের খিচুড়ি।
রাঁধতে লাগবে: গোবিন্দভোগ চাল এক কাপ, সোনামুগ ডাল এক কাপ, গোটা কাঁচালঙ্কা ৫-৬টা, তেজপাতা দুটো, গোটা গরমমশলা এক চা চামচ, কাজু-কিশমিশ তিন টেবিলচামচ (দুটি মিলিয়ে), আদাবাটা এক টেবিলচামচ, জিরেগুঁড়ো হাফ টেবিলচামচ, হলুদগুঁড়ো এক চা চামচ, লঙ্কাগুঁড়ো স্বাদমতো, কুচনো নারকেল আধ টেবিলচামচ, নারকেলকোরা ৩/৪ টেবিলচামচ, চালডালের দ্বিগুণ মাপের জল, নুন-চিনি স্বাদমতো, ঘি তিন টেবিলচামচ, সাদা তেল এক টেবিলচামচ।
প্রণালী: গোবিন্দভোগ চাল বেছে ধুয়ে জল ঝরিয়ে রাখতে হবে। ওই একই পরিমাণ ডাল কম আঁচে শুকনো খোলায় ভেজে ধুয়ে জল ঝরিয়ে রাখতে হবে। তারপরে পেতলের ডেকচিতে দু’ টেবিলচামচ ঘি এবং পুরোটা তেল গরম করে তাতে কুচনো নারকেল ও কাজু–কিশমিশ ভেজে তুলে রাখতে হবে। এবারে তেজপাতা, থেঁতো করা গরমমশলা ফোড়ন। ফোড়নের হালকা গন্ধ বেরুলে আদাবাটা পড়বে। কম আঁচে নাড়তে হবে। একটু ভাজা হলে হলুদ, লঙ্কা, জিরেগুঁড়ো সামান্য জলে গুলে ঢেলে দিয়ে কষবার পালা।

এবারে জল ঝরানো চাল, ডাল দিতে হবে। নাড়াচাড়া থামালে চলবে না। অর্ধেকটা কোরানো নারকেল মেশাতে হবে। পুরোটা ভাজা মতো হলে গরমজল। ফুটে উঠলে নুন। মাঝারি আঁচে ঢাকা দিয়ে রান্না করতে হবে। মাঝেমাঝে নাড়তে হবে। ভাজা নারকেলকুচি, কাজু-কিশমিশ দিয়ে ফের ঢাকা। চাল-ডাল সেদ্ধ হয়ে এলে স্বাদমতো চিনি দিতে হবে। জল শুকিয়ে খিচুড়ি ঝরঝরে হয়ে এলে বাকি ঘি ছড়িয়ে আঁচ বন্ধ করে ঢাকা অবস্থায় খানিকক্ষণ রেখে নামাতে হবে। উপর থেকে বাকিটা নারকেলকোরা ছড়িয়ে গরমাগরম পাতে!
*ছবি ও রান্না সৌজন্য: লেখক

থালাভরা ভর্তা
‘তুমি যাচ্ছ পালকিতে মা চড়ে/ দরজাদুটো একটুকু ফাঁক করে/ আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার পরে/ টগবগিয়ে তোমার পাশে পাশে…’
এই না বলে, হারে রেরে রেরে করে মায়ের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়তেই হাত ধরে টেনে কোলে। আদর করতে নয়, শীতসন্ধ্যের শেষে একটু দূরেই উনুনে তখন নিভু নিভু আঁচে কয়েকটা আলু পুড়তে দেওয়া, সে আঁচ থেকে আগলে রাখতে! আমি জন্মানোর পর আত্মীয়রা কেউ কেউ বলেছিল, ‘প্রথমেই মেয়ে হল!’ আবার ক’মাস যেতে না যেতেই- ‘মেয়ে হয়ে এত দস্যি??’ মা শুনে গেয়ে উঠতেন, ‘সব দুষ্টু ছেলেরাই লক্ষ্মী/ তারা বাঁধনছাড়া পক্ষী/ যদি সঙ্গে থাকে ভয় কী..’
সারাদিন কয়লা ভাঙা, গুল পাকানো, বাজার করা, উনুন ধরিয়ে রান্না করা, অসুস্থ বাবার যত্ন করা, আর বাকি সব কাজ সেরে, নিভু আঁচে শেষ কুড়ন্তি কিছু একটা বসিয়ে, মেঝেতে একটু দূরে মা বসতেন মেয়েকে নিয়ে। পায়ের ওপর বসিয়ে কখনও সুকুমার সমগ্র, কখনও গীতবিতান গুনগুনিয়ে, কখনও শিশু ভোলানাথ… কতই বা বয়েস তখন, চার? পাঁচ? ছয়? ওই যে কবিতাটা, ‘আমার মা না হয়ে তুমি আর কারো মা হলে…’ ওর চেয়ে বীরপুরুষ ঢের ঢের ভালো। গলা জড়িয়ে জিজ্ঞেস করত ছোট্ট মেয়ে, ‘কবে আমি বড়ো হব?’ ওই নিভু আঁচে সেদ্ধ হওয়া আলু মাখা দিয়ে ফ্যানভাত গোল্লা পাকিয়ে মুখে ভরে দিতে দিতে উত্তর আসত, ‘পুরো ভাতটা খেলে তবেই তো…’

আহা! মায়ের হাতের ফ্যানভাত আলুসেদ্ধ, আজও সব চেয়ে প্রিয়। আর সেই কাঠের আর কয়লার আঁচে রান্নার কী স্বাদ! নিভু আঁচে সেদ্ধ হত কখনও আলু, কখনও কপি, কখনও বেগুন বা অন্য নানান সবজি। তা দিয়ে সামান্য আয়োজনে মা বানাতেন ভর্তা। সেই ভর্তার গল্প বলব আজ, যে ভর্তা প্রধানত সারাদিন খেটে খাওয়া নিম্নবিত্তের হেঁসেলে জন্মিয়ে আজ নামীদামি রেস্তোরাঁতেও জায়গা করে নিয়েছে। জাঁকজমকের রান্না ছেড়ে আজ হোক সাদামাটা ভর্তার কথা, মায়ের হাতের ছোঁয়া আর ভালোবাসা যে সবচেয়ে বেশি খুঁজে পাই এতেই! তবে সে কথা বলার আগে, যাই মায়ের সঙ্গে বাজারে। ছোটবেলায় ওই ছোট্ট ছোট্ট খেলনবাটি কখনও কিনে না দিলেও, একটু বড় হতেই সঙ্গে করে সবজি বাজার চিনিয়েছিলেন মা। এই সুযোগে, বাজারের হিসেব নিকেশটাও শেখানো হয়ে যেত। ঘুরতে ঘুরতে শুনতাম…
– হাত দিয়ে না দেখে কি বাজার করা যায়? এই দেখ! ভেন্ডির ডগাটা এরকম ভেঙ্গে দেখবি কচি কিনা। বেগুন দেখবি হালকা আর নিটোল কিনা। মাছের কানকো তুলে লাল টুকটুকে রঙ হলে তবেই তো, আবার কখনও গন্ধ শুঁকে চিনবি!
টাটকা সবজি মাছ কিনে এনে রান্না চাপত। কিছু সবজি রেখে দিলে একটু বুড়ো হয়ে গেলেই বানাতেন ছেঁচকি। আর সবজি শেষ হবার দিকে, হয়তো এটা একটু ওটা একটু পড়ে আছে, তখন হতো ভর্তা। ভর্তা বানানোর জন্যে পেঁয়াজ লম্বা কুচি করতে করতে মা বলতেন, খাবারের স্বাদ অনেকাটা নির্ভর করে সবজি কাটার ওপর। পারফেকশনিস্ট মা পেঁয়াজ কাটতেন সরু সরু লম্বা লম্বা করে, সব এক মাপে। ভর্তা বানানোর জন্যে দেখতাম, এই কটা জিনিস মোটের ওপর সব কিছুতেই দিত:
১. পেঁয়াজ সরু লম্বা করে কেটে ভাজা (হালকা গোলাপি করে) বেরেস্তার মতো ব্রাউন নয় কিন্তু।
২. রসুন লম্বা লম্বা কেটে হালকা ভাজা
৩. শুকনোলঙ্কা ভাজা, সেটা নুন দিয়ে মেখে ভালো করে চটকে গুঁড়ো করে নেওয়া
৪. কাঁচা সর্ষের তেল
বাকি রইল ভর্তার স্বাদ। সে তো হাতের স্পর্শে যে ভালোবাসা মেশে, তার মোড়কে তৈরি। গরম গরম ভাতের পাতে যে যে ভর্তা মায়ের কাছে খেয়েছি সেগুলো বলি।

১. আলু ভর্তা: আলু সেদ্ধ করে ভালো করে মেখে ওপরের চারটে উপকরণ পড়বেই। এ ছাড়াও কখনো আলুতে জিরেভাজা, বড়িভাজা, বা কখনও টমেটো পোড়া, বা অনেকটা ধনেপাতা কুচিও মিশিয়ে দিতেন মা। আবার কখনও আলু ডিম টমেটো মিশিয়ে ভর্তা! আলুটা আসলে একটা বড় ক্যানভাসের মতো, যাতে বা যার সঙ্গে নানান জিনিস মিশিয়ে ভর্তা করা যায়।
২. মুগ ডাল/ মুসুর ডাল ভর্তা: ওপরের চারটে উপকরণ ছাড়াও, ধনেপাতাকুচি দিয়ে ভালো করে মাখা। একটু শক্ত করে ডাল সেদ্ধ হবে। এক বড়ো বাটি ডাল হলে তিনটে পেঁয়াজ আর ৭-৮ কোয়া রসুন লাগবে।
৩.কাঁচালঙ্কার ভর্তা: এতে স্রেফ ওই ওপরের থেকে পেঁয়াজ, রসুনভাজা আর সঙ্গে ধনেপাতাকুচি, আর এক চামচ লেবুর রস মেশাতে হবে। একশো গ্রাম লঙ্কায় দুটো পেঁয়াজ, ৭-৮ টা রসুন, স্বাদমতো লঙ্কা।
৪. কাঁচা আমের ভর্তা: এক বাটি কাঁচা আম কুরিয়ে, সেই ওই দুটো পেঁয়াজ চারকোয়া রসুন আর লঙ্কা ভাজার সঙ্গে একটু মিষ্টি আর অল্প সর্ষেবাটা দিলেই হবে।
৫. বড়া ভাজা ভর্তা: এক বড়ো বাটি বড়া ভাজা একটু গরম জলে ভিজিয়ে জল চিপে তার সঙ্গে তিনটে পেঁয়াজ, ৭-৮ কোয়া রসুন, লঙ্কাভাজা স্বাদমতো, আর বেশ কিছুটা ধনেপাতা কুচি ভালো করে মেশানো।
৬. ডিম: সেদ্ধ করে চটকে, ওই চারটে উপকরণ স্বাদমতো মেশানো। ছ’টা ডিম হলে ওই ধরো, দুটো পেঁয়াজ আর ৩-৪ কোয়া রসুন।
৭. চিংড়ি/ রুই মাছ ভর্তা: মাছ ভেজে নিয়ে খোসা বা কাঁটা ছাড়িয়ে চটকে নেওয়া। এটা মা যা করেন, তেল গরম করে অল্প এক চামচ পেঁয়াজ-রসুনবাটা আর হাফ চামচ আদাবাটা কষে এক বাটি চটকে নেওয়া মাছ দিয়ে নাড়িয়ে তারপর তাতে পেঁয়াজ, রসুন, শুকনোলঙ্কা ভাজা আর অল্প ধনেপাতা কুচি মিশিয়ে নেন।
৮. কালোজিরের ভর্তা: খুব সাবধানে ঢিমে আঁচে কালোজিরে ভেজে নিয়ে, সেটা বেটে ফেলতে হবে। তারপর ওই পেঁয়াজ, লঙ্কা আর রসুনভাজা দিতে মাখা, এতে রসুন একটু দু’চার কোয়া বেশি হলে আমার ভালোলাগে। তবে সাবধান! কালোজিরে বেশি ভাজলেই এটা তেতো হয়ে যায়!
৯. সাদা তিলের ভর্তা: কম আঁচে হালকা গন্ধ আসা পর্যন্ত নাড়িয়ে নিয়ে, এক বাটি তিলের সঙ্গে দুই বড়ো চামচ নারকেলকোরা মিশিয়ে বেটে নেওয়া। তাতে আবার ওই পেঁয়াজ-রসুন-লঙ্কাভাজা মেশানো। মা কে দেখি দু’চার দানা চিনি মিশিয়ে দিতে এর সঙ্গে।
১০: বেগুন/ সিম/ কাঁচকলার ভর্তা: বেগুন পুড়িয়ে নিয়ে, সিম আর কাঁচকলাটা সেদ্ধ করে নিয়ে, ওই চারটে উপকরণ দিয়ে মেখে নেওয়া। বেগুন ভর্তাতে সঙ্গে কাঁচালঙ্কা কুচি, আর ধনেপাতা কুচি এক্সট্রা। কখনও মা টমেটো পোড়াও মেশাতেন চটকে। কাঁচকলা ভর্তাতে ধনেপাতা কুচি আর সিম ভর্তাতেও তাই..

১১. পটলের খোসার ভর্তা: মিহি করে বেটে নিয়ে, তেল গরম করে তাতে ভেজে নিতে হবে শুকনো করে। ভাজতে ভাজতে অল্প মিষ্টি আর স্বাদমতো নুন দিয়ে নামিয়ে সেই ওই চার উপকরণ দিয়ে মাখা।
১২. কপি পাতার ভর্তা: এটাও বেটে নিয়ে অল্প তেল গরম করে ভেজে নিতে হবে শুকনো করে, কম আঁচে। সঙ্গে নুন আর অল্প মিষ্টি। এটা দু’রকম করেন মা। একটায় কালোজিরে কাঁচালঙ্কা ফোড়নের সঙ্গে ওই চার উপকরণ মেশানো। আর একটায় কালোজিরে কাঁচালঙ্কা ফোড়নের সঙ্গে নারকেলকোরা আর সর্ষেবাটা মেশানো। ওই একবাটি পাতাবাটায় আধ বাটি নারকেল আর দেড় চামচ মতো সর্ষে বাটা।
এগুলোর যে কোনও একটা হলেই আমি তো পুরো ভাত সাবড়ে ফেলি। ওহ! আর একটা ভর্তা তো বলাই হলো না, আমার শাশুড়ি মায়ের প্রিয় শুঁটকি মাছের স্পেশাল ভর্তা। সে গল্প অন্য দিনের জন্যে তোলা রইল। আজ যখন তিন প্রজন্ম একসঙ্গে ভর্তা বানাচ্ছি, দিদার কাছে নাতি শিখছিল রান্নার খুঁটিনাটি। ভুল করতেই সত্তরোর্ধ শিক্ষিকা বেশ কড়া চোখে তাকালেন, অমনি ফচকেটা বলে উঠল, ” উরিব্বাবা, দেবী যে আজ রান্নারূপেণ সংস্থিতা!” রাগ বদলে গেল হাসিতে…
মাতৃ দিবসে মনে মনে প্রার্থনা করলাম, মায়ের আঁচলের এই শাসন আর ভালোবাসা বহু বহু বছর দীর্ঘজীবি হোক!
*ছবি ও রান্না সৌজন্য: লেখক
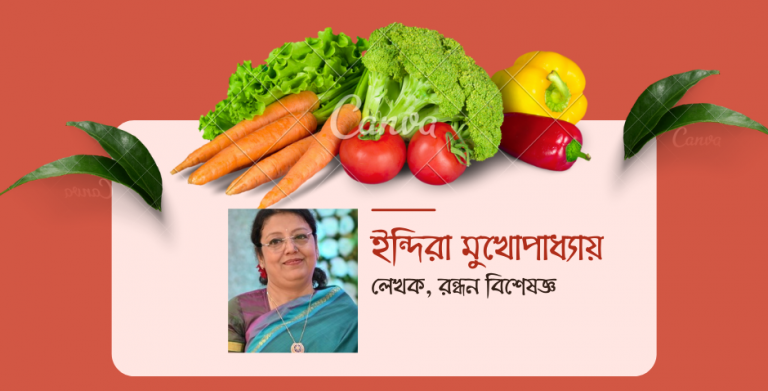
মাতৃদিবসে ক্রোকে-কাহিনি
আমার দিদিশাশুড়ির কাছেই ফিশ ক্রোকের নাম প্রথম শুনি। সেই জেনেছিলাম আলুর সঙ্গে চটকে নেওয়া মাছের পুর দিয়ে ডিপ ফ্রায়েড স্ন্যাক্স হল ফিশ ক্রোকে আর আলুসেদ্ধর বাটির মধ্যে মাছের পুর ভরলেই তা হয় ফিশচপ।
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং তাঁর স্ত্রী বাসন্তীদেবীর সঙ্গে দিদিশাশুড়ির প্রগাঢ় বন্ধুতা ছিল। রন্ধনপটিয়সী বাসন্তীদেবী মাঝেমধ্যেই নিজেহাতে রান্না করে পাঠাতেন তাঁদের বাড়ি। ওই দাশবাড়ির খানসামা ও বাবুর্চির কাছেই দিদিশাশুড়ি মা শিখেছিলেন রুইমাছের ক্রোকে। তিনি মারা যাবার আগে পর্যন্ত প্রতি রবিবার রান্নার ঠাকুরকে বলতেন রুইমাছ নুন হলুদ আর সামান্য ভিনিগার দিয়ে সেদ্ধ করে কাঁটা বেছে রাখতে। আলুসেদ্ধ করে, পিঁয়াজ, আদা, রসুন, কাঁচালংকা সব রেডি হলে দিদিশাশুড়ির তত্ত্বাবধানে সেই ক্রোকের পুর হত। একসঙ্গে আলু দিয়ে মেখে সামান্য ঘি, গরমমশলা আর গোলমরিচ ছড়িয়ে ক্রোকের পুর তৈরি হলে ডিমের গোলায় চুবিয়ে বিস্কুটের গুঁড়োয় গড়িয়ে নিতেন। নানারকম আকারের ফিস ক্রোকে গড়তেন তিনি। কোনওটা হৃদয়াকৃতির, কোনওটা গোল আবার কোনওটা রোলের মতো।
পারিবারিক ঘনিষ্ঠতার কারণে দেশবন্ধু এবং বাসন্তীদেবীর কন্যা কল্যাণীদেবী আমার শাশুড়িমায়ের খুব প্রিয় ছিলেন। অবিভক্ত বাংলার সুপরিচিত রাজনৈতিক মুখ এবং সুবক্তা স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় জামাতা কর্নেল ইউ এন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ভাস্কর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল রন্ধনশিল্পী কল্যাণীদেবীর। আমার শাশুড়ি মা সুযোগ পেলেই বাসন্তীদেবী এবং তাঁর প্রিয় কল্যাণী জ্যাঠাইমার কাছ থেকে অসাধারণ সব রান্নার রেসিপি লিখে রাখতেন নিজের ডায়েরিতে। সেই ডায়েরি উত্তরাধিকারসূত্রে এখন আমার দখলে।

দুই শাশুড়িমায়ের দেখে ক্রোকে শেখা হয়েছিল আমার। পরে ক্রোকে নিয়ে চর্চা করে জেনেছি, নানান আকৃতির ডিপ ফ্রায়েড এই মুখরোচক জলখাবারের মূলে কিন্তু আলু। বাংলার আদি অকৃত্রিম আলুর চপ, অবাঙালিদের আলু টিকি, বিদেশের হ্যাশ ব্রাউন, চিন, তাইওয়ানের ম্যাশড প্যোট্যাটো ও ভুট্টার দানা সেদ্ধ দেওয়া কেলে বিং (kělè bǐng), ইন্দোনেশিয়ার সেদ্ধ আলুর মধ্যিখানে মুরগির কিমা দেওয়া ‘ক্রকেট’ (kroket), আলুর সঙ্গে আনাজ, মাংস কিম্বা সিফুড মেশানো জাপানের ফ্ল্যাট প্যাটি (korokke), সাউথ কোরিয়ার গোরোকে (goroke) আদতে একই আলুর রূপভেদ।
বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়ের ‘পাকপ্রণালী’ বইতে সে যুগে বিলিতি চপ কাটলেট ইত্যাদি ভাজা জলখাবারের হিন্দু সমাজে গ্রহণযোগ্যতার কথা পাই। প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর বইতে জেনেছি, বিদেশি চপের অন্যতম ধারক ও বাহক হিসেবে ফরাসি রেসিপি ক্রোকে বা (croquette) বনেদি বাঙালির অন্যতম ‘পার্টি স্ন্যাক্স’ হয়ে ঢুকে পড়েছিল এককালে। শুরুতে যা ছিল ফরাসি আলুর ক্রোকে, তা ক্রমশ উন্নত হতে থাকল আনাজ এবং আলুর মিশেলে। তবে ফ্রেঞ্চ ক্রোকের গড়ন ছিল দিদিশাশুড়ির চোঙাকৃতি ক্রোকের মতোই। ঠাকুরবাড়ির রান্নায় পাই ‘রাঙালুর ক্রোকে’ আর প্রজ্ঞাসুন্দরীর নিরামিষ আহারে ‘ডুমুরের কুর্কিট’-এর রেসিপি। পরে উত্তরণ হল মাংসের কিমা এবং আলুসেদ্ধর অদ্ভুত মাখামাখিতে। বাঙালির মাছে নাড়ী কাটা। তাই একদিন মৎস্যপ্রেমী বাঙালি নিজেই আবিষ্কার করে নিল সেদ্ধ মাছের সঙ্গে আলুর মিশ্রণে ক্রোকে বানানোর পদ্ধতি।
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং তাঁর স্ত্রী বাসন্তীদেবীর সঙ্গে দিদিশাশুড়ির প্রগাঢ় বন্ধুতা ছিল। রন্ধনপটিয়সী বাসন্তীদেবী মাঝেমধ্যেই নিজেহাতে রান্না করে পাঠাতেন তাঁদের বাড়ি। ওই দাশবাড়ির খানসামা ও বাবুর্চির কাছেই দিদিশাশুড়ি মা শিখেছিলেন রুইমাছের ক্রোকে। তিনি মারা যাবার আগে পর্যন্ত প্রতি রবিবার রান্নার ঠাকুরকে বলতেন রুইমাছ নুন হলুদ আর সামান্য ভিনিগার দিয়ে সেদ্ধ করে কাঁটা বেছে রাখতে।
অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই ফরাসি ক্রোকের রোমান বানান ছিল croquet। শব্দটির উৎপত্তি croquer থেকে, যার অর্থ ‘to crunch’। ক্রোকের জন্ম সপ্তদশ শতকে, ফ্রান্সে। সেই থেকে মধ্যিখানে সেদ্ধ আলু অথবা আলুর মধ্যে আখরোট কিম্বা ট্রুফল, সেদ্ধ ডিম আর বাইরে ডিম, চিজ আর বিস্কুটের গুঁড়োর খোল– এই হল ক্রোকের আদি সূত্র। এই ক্রোকে ফ্রান্স থেকে স্পেনে পৌঁছে হয়েছিল সামান্য ভিন্নধর্মী croquetas হয়ে। এ তথ্য গুগল করে জেনে আমার শাশুড়িমা-কে জানাতে তিনি অভিভূত হয়ে আবারও শুনিয়ছিলেন বাসন্তীদেবীর ক্রোকে কানেকশন। আজ মায়েদের দিনে নতজানু হয়ে ক্রোকের নাড়িনক্ষত্রের স্বাদ-গন্ধমাখা গল্প ছবি-সহ ভাগ করে নিলাম বাংলালাইভের পাঠকদের জন্য।
*ছবি ও রান্না সৌজন্য: লেখক
মৌলিক‚ ভিন্নধর্মী ও সময়োপযোগী - এমনই নানা স্বাদের নিবন্ধ পরিবেশনের চেষ্টায় আমরা। প্রতিবেদন বিষয়ে আপনাদের মতামত জানান 'কমেন্ট' বক্সে | নিয়মিত আপডেট পেতে ফলো করুন - https://www.facebook.com/banglaliveofficial

























2 Responses
খুব সুখপাঠ্য এবং উপভোগ্য লেখাগুলোর জন্য অনেক ধন্যবাদ | এ তো শুধু রান্নার রেসিপি নয় , স্নেহ ভালোবাসার আরকে চোবানো , অনেকখানি মন কেমন করা কিছু স্মৃতি আর হারিয়ে যাওয়া সময়কে চোখের সামনে ফিরিয়ে আনা | বড় ভালো লাগলো পড়ে !Subhasrer
ইতিহাসে আবেগে একাকার এক সুস্বাদু সাহিত্যপদ। রান্নার রসায়নে সমীকরণের মতো মিশে থাকে কত ভালবাসা আর আদরের অতীত, এই লেখা তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর।