১২
– আচ্ছা মাম্মা! তুমি কি বিয়ে হয়ে এসে কখনও শুনেছ ছোটকুর কথা?
রোহিনী নোট নিতে নিতে হঠাৎ থেকে জিজ্ঞেস করে৷
‘ছোটকু!’ সীমন্তিনী বেকিং গ্লাভস্ পরে অ্যাপল পাই-টা কতটা হয়েছে পরখ করছিল৷ রোহিনীর প্রশ্নে একটু থমকেছে৷
– ছোটকু নামটা চেনা চেনা লাগছে না তো? কেন রে? কী হয়েছে? বাবাইকে জিজ্ঞেস করে দেখ্? ওদের ফ্যামিলির সবাইকে তো আমি চিনিই না৷ বিয়ে হয়ে সোজা চলে এলাম এদেশে৷ এক্সটেনডেড ফ্যামিলিকে আর চেনার সুযোগ হল কই?
মাম্মার গলায় কি একটু আক্ষেপ মিশে আছে? রোহিনী ঠিক ধরতে পারে না।
– না, আর একটু হবে মনে হচ্ছে পাইটা৷ তুই ওয়াশিংটা এক লট একটু দিয়ে আসবি? আজ খুব ভাল রোদ ৷ বেডকভার-টভারগুলো একটু মেলে দিতে হবে৷
মাম্মার এই এক অবসেশন৷ খটখটে ড্রাই হয়ে গেলেও মনে হয় দেশের মতো খটখটে রোদে না শুকোলে যথেষ্ট জীবাণুমুক্ত হল না৷ প্রথম প্রথম রোহিনী তর্ক করত৷ এখন হাল ছেড়ে দিয়েছে৷ রোহিনী খুব অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেসমেন্টে গেল৷ বেসমেন্টে বিরাট বড় ওয়াশিং মেশিনটায় কাপড়চোপড় লোড করছে৷ দিন দিন পরিষ্কার পরিষ্কার বাতিকটা বাড়ছে মাম্মার৷ কোনও দরকার নেই, তাও মাঝে মাঝেই বেডকভার বেডশিট সব নামিয়ে দেবে কাচার জন্য৷ যেখানে যা আছে সব জড়ো করবে৷ সব নাকি নোংরা হয়ে গেছে৷ নিকি সপ্তাহে একদিন ওয়াশিং করে যায়৷ তাতে মাম্মার পোষায় না৷ দেশে থাকলে এটাকেই বলত শুচিবায়ু৷ এখানে এটার একটা গালভারি নাম আছে৷ ইন্টারনেটে দেখেছে রোহিনী৷ জার্মোফোবিয়া৷ রণোকে বলেওছিল৷ রণো ওর মাকে বেশি ঘাঁটায় না৷ কিছু বলতে গেলেই মাম্মা কেঁদেকেটে একশেষ করবে৷
রণো ওর মাম্মার এই অতিরিক্ত ইমোশনাল স্বভাবটা জানে৷ বিশেষ করে রণোর ব্যাপারে মাম্মা ভীষণ টাচি৷ একটু থেকে একটু হলেই মুখ হাঁড়ি হয়ে যায়৷ একজন সন্তানের মা হলেই বোধহয় এরকম মারাত্মক রকমের পজেসিভ হয়? বাংলায় এক সন্তানের মা-দের কি যেন একটা জম্পেশ নাম আছে৷ বহু চেষ্টা করেও ঠিক মনে পড়ল না রোহিনীর৷ একটা ভালো বাংলা ডিকশনারি এখন ওর নিত্যসঙ্গী৷ রণোর দাদুর খাতাটা সাধুভাষায় লেখা বেশিরভাগটাই৷ রোহিনীর মধ্যবিত্ত বাঙালি বাড়িতে বাংলার চর্চা রয়েছে৷ নিয়মিতভাবে ওর বাবা-মা ওকে আর ওর দাদাকে বাংলা পড়তে বাধ্য করেছেন৷ তার সুফল ও এখন বুঝতে পারছে৷ আইএসসি পাশ করার পরই আন্ডারগ্র্যাড পড়তে এদেশে চলে এসেছিল৷ পরে কখনও বাংলার দরকার হবে ভাবেওনি কোনওদিন৷ কিন্তু পরে যখন পার্টিশন নিয়ে কাজ করল, তখন বিস্তর বাংলা সোর্স পড়তে হয়েছিল ওকে৷ আর এখন তো জ্যোতির্ময় সেনের এই খাতাটা দৈবাৎ খুঁজে পেয়ে যেন জীবনটাই পাল্টে গেছে৷ খাতাটা নিয়ে এখন সত্যিই গভীর অবশেসন জন্মেছে ওর৷ রোহিনী অনলাইনে অর্ডার করে একটা ভালো ডিকশনারি আনিয়েছে৷ কোনও শব্দে হঠাৎ আটকে গেলে, বা খটোমটো লাগলে ও ডিকশনারির শরণাপন্ন হয়৷
ওয়াশিং চাপিয়ে ও উপরে উঠে দোতলায় নিজের ঘরে গেল৷ ওর মানে ওর আর রণোর ঘর৷ নামেই ওদের ঘর৷ রণো এখন বিশেষ আসার সময় পায় না৷ রোহিনী বরং ইদানিং বেশি আসার চেষ্টা করে৷ খাতাটা পড়তে পড়তে ওর মনে অনেক প্রশ্ন৷ তার উত্তরগুলো এবাড়ির কারোর জানা নেই৷ রণো আর বাবাই দুজনেই নিজের নিজের কাজের জগতে বুঁদ হয়ে থাকে৷ পিসিমণি নিজের মতো করে নিজের সমস্যাগুলোর সঙ্গে যোঝে৷ বেচারি পিসিমণি কী-ই বা করবে? জন্মেছে ইংল্যান্ডে৷ দু’বছর বয়স হতে হতেই আমেরিকায়৷ পিসিমণি চলনে বলনে কথাবার্তায় একদম অ্যামেরিকান– রোহিনী যতটুকু দেখেছে৷ ও এখন ডিভোর্সি, তার উপর ছেলের জন্য একটা অতিরিক্ত চাপ সব সময়ই রয়েছে যদিও বিয়াট্রিস রুণকে সবসময় আগলায়৷ রুণ কখনই আর পাঁচটা বাচ্চার মতো স্বাভাবিক সুস্থ জীবনযাপন করতে পারবে না৷ সবসময় ওকে বাইরের লোকের কাছ থেকে সাহায্য নিতে হবে জীবনযাপনের জন্য৷ তাও এদেশে এধরনের স্পেশাল নিড ছেলেমেয়েদের জন্য অনেকরকম ব্যবস্থা৷ দেশে হলে কি করত পিসিমণি?
দাদুর খাতাটা নিয়ে বাবাই বা পিসিমণির উৎসাহ থাকার কথা নয়৷ ওরা তো বাংলা পড়া দূরস্থান, বাংলা বলতেও পারে না তেমন৷ বাবাই তাও একটু একটু বলে, কিন্তু ওদের মাতৃভাষা ইংরেজি৷ রণোরও যেমন৷ ডিকশনারিটা হাতে নিয়েই সাঁ করে শব্দটা মনে পড়ল রোহিনীর৷ যে নারীর একটিমাত্র সন্তান তাকে বলে কাকবন্ধ্যা৷ পুরনো দিনে ওনলি চাইল্ডের মাকেও প্রায় সন্তানহীনাই ভাবা হত৷ বন্ধ্যা নয়, সামান্য একটু কোয়ালিফায়ার৷ কাকবন্ধ্যা৷ আশা করা হত নারীদের বেশ কটি সন্তান থাকবে৷ সেই হিসেবে মাম্মা, পিসিমণি সবাই কাকবন্ধ্যা৷ রোহিনীর নিজের তিরিশ বছর বয়স হয়ে গেল৷ এখনও তারা সন্তানের কথা ভাবেনি৷ রণো চাকরি জীবনে উন্নতির বেশ উঁচু ধাপের সিঁড়িতে না উঠে বাচ্চা চায় না৷ রোহিনী নিজে কী চায়, তাও এখন ওর নিজের কাছে খুব স্পষ্ট নয়৷ যেন বিয়ের পর থেকে রণোর ইচ্ছেতেই ওর ইচ্ছে৷ অথচ ওদের দুটো স্বাধীন স্বতন্ত্র জীবন৷ কেউ কারোর ইচ্ছে অন্যের উপর চাপাবে না– এই অলিখিত পূর্বশর্ত থেকেই ওদের একত্র বাস৷ রোহিনীও কি তাহলে ভিতরে ভিতরে মেনে নিচ্ছে! রণোর ইচ্ছেতেই সম্মতি দিচ্ছে? সেরকম কি কথা ছিল? রোহিণীর নিজের উপর রাগ হতে থাকে কেন যেন৷ টেবিলে রাখা খাতাটার দিকে তাকায় ও৷ এই খাতাটা এখন ও যেখানে যায় সঙ্গে নিয়ে যায়৷ এটা যেন ওর নিজস্ব একটা সম্পদ৷ অথচ এ বাড়ির সবাই খাতাটা নিয়ে যাকে বলে লিস্ট বদারড৷ যে একমাত্র খাতাটা উৎসাহ নিয়ে পড়তে পারত, সেই মাম্মারও এ বিষয়ে কোনও উৎসাহ নেই৷ একবার-দুবার খুব আলগাভাবে বলেছে বটে,
– বাবা, এরকম যে একটা মেমোয়ার উনি লিখছিলেন, জানতামই না৷
কিন্তু তার বেশি কোনও উৎসাহ দেখায়নি৷ খাতাটা দেখতেও চায়নি নেড়েচেড়ে৷

আর দিদান? অরুণলেখার এখন একটু একটু করে স্মৃতিবিভ্রম বাড়ছে৷ ‘শি হ্যাজ হার গুড ডেজ অ্যান্ড ব্যাড ডেজ’৷ বাবাই সেদিন পিসিমণিকে স্কাইপ কলে বলছিল৷ ঠিকই কথাটা৷ দিদানের কোনও কোনও দিন পুরনো কথাগুলো খুব ভালো মনে পড়ে, কখনও কখনও স্মৃতির উপর সরের মতো আস্তরণ পড়ে৷ সেদিন একটু অসংলগ্ন কথা বলে৷ তবু, খেয়াল করেছে রোহিনী৷ নতুন স্মৃতিগুলো যত তাড়াতাড়ি ভুলে যায় দিদান, পুরোনগুলো ততটা নয়৷ ‘সিলেক্টিভ মেমারি ল্যাপ্স’ বাবাই বলেছিল৷ দিদানের একটা ভালো দিনে, যখন দিদানের চোখ মুখ দেখেই বোঝা যায় যে, পুরনো কথা নাড়াচাড়া করছে মাথার মধ্যে, তখন একদিন সুযোগ নিয়েছিল রোহিনী৷
– দিদান, দাদু একটা নোটবুকে নিজের জীবনের সব গল্প লিখে রেখেছেন৷ আমি খাতাটা খুঁজে পেয়েছি৷ তোমাকে আস্তে আস্তে পড়ে শোনাব?
রোহিনী ঠিক বুঝতে পারছিল না অরুণলেখার প্রতিক্রিয়া কি হবে। নীল চামড়ার বাঁধানো খাতাটা অরুণলেখা শীর্ণ হাত দু’খানিতে তুলে দিয়েছিল রোহিনী৷ অরুণলেখা ফাউলার্স বেডে আধশোয়া হয়ে বসেছিলেন৷ খাতাটা হাতে দিতে অনেকক্ষণ হাত বুলিয়েছিলেন খাতার উপরটায়৷ যেন অনেকদিন আগেকার একটা চেনা অভিজ্ঞানকে আলতোহাতে অনুভব করেছিলেন৷ কিন্তু খোলেননি খাতাটা৷ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অবশেষে খুব ক্লান্তভাবে বলেছিলেন,
– দিদিভাই! এইটা যখন উনি লিখতে শুরু করেন, গোড়া থেকেই আমার কৌতূহল ছিল খুব। কী লিখছেন জানার জন্য৷ একবার ঝুঁকে দেখেও ফেলেছিলাম, বাংলায় লিখছেন উনি৷ কিন্তু যতবারই জিজ্ঞেস করেছি, বলেছেন, জীবনের গল্পগুলো লিখছি৷ যখন জিজ্ঞেস করেছি, ‘আমাকে দেখাবে না?’ বলেছেন ‘যখন সময় হবে, তখন দেখাব৷’ সেই সময় আর আসেনি৷ তারপর তো স্ট্রোক হল৷ প্যারালাইজড্ হয়ে গেলেন৷ তখন ওঁকে নিয়েই চিন্তা ছিল৷ খাতার কথাটা মনেও ছিল না৷ তারপর যখন উনি চলে গেলেন, ওখানেই তো ছিলাম৷ একা থাকতাম৷ কিন্তু কখনও মনে হয়নি খাতাটা দেখি, কারণ ওটা তো উনি আমার জন্য লেখেননি, নিজের জন্যই লিখেছিলেন৷ হয়তো ইচ্ছে ছিল পরের জেনারেশনের কেউ পড়ুক৷ তুমি পড়ছ, দাদুকে তো দেখনি সেভাবে! এই খাতাটার মধ্যে দিয়ে উনি হয়তো তোমার মতো কারোর সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন৷ সেটাই তো ভালো৷
অরুণলেখার এই কথার পর আর কখনও জোর করেনি রোহিনী৷ শুধু একবার অনুমতি নিয়েছে৷ হ্যাঁ, ওর কিছু করার দরকার হলে, বা কোনও অসম্পূর্ণ ন্যারেটিভকে সম্পূর্ণ করতে ও দরকার মতো অরুণলেখার কাছে আসবে৷ একটা অসম্পূর্ণ বয়ানকে সম্পূর্ণ গোল আকার দেবার জন্য ওর দিদানের কাছে অনেক কিছু জানা দরকার৷
– মাম্মা! ড্রায়ার থেকে কাপড়গুলো বের করেছিস?
সীমন্তিনী হেঁকে জিজ্ঞেস করছে৷
– ডোন্ট ওয়ারি মাম্মা৷ আই উইল ডু ইট ইন মাই ওন টাইম৷
রোহিনী শান্ত সমাহিত গলায় বলছে৷
– রোদ থাকতে থাকতে কাপড়গুলো একটু শুকিয়ে নে সোনা৷ আর তারপর যদি অ্যাপেল পাই টেস্ট করতে চাস, তাহলে আয়৷
সীমন্তিনীর গলায় সবসময় একটা ব্যস্ততা, যেন খুব তাড়াহুড়ো রয়েছে খুব৷ রোহিনী ঠিক করেছে মাম্মার কোনও কথায় তেমন পাত্তা দেবে না৷ মাম্মার মধ্যে একটা কন্ট্রোল ফ্রিক সত্তা আছে৷ সবসময় মাম্মা চেষ্টা করে সমস্ত কাজ নিখুঁতভাবে চলবে, ঘরবাড়ি একেবারে ধুলোহীন হয়ে সাজানো থাকবে৷ সবাই রোবটের মতো নিজের কাজগুলো করে ফেলবে৷ যদিও রোহিনী এতদিনকার অভ্যেসে দেখেছে এদেশে ঘরবাড়ি এমনিতেই পরিষ্কার থাকে৷ দেশের মতো রোজ রোজ ডাস্টিং করার দরকার হয় না৷ বিশেষ করে সীমন্তিনীদের বাড়ির মতো সব ঘরেই চমৎকার ওয়াল টু ওয়াল কার্পেট থাকলে৷ মাম্মা ওসব শুনলে তো! নিকি এখন সপ্তাহে তিনদিন এসে সমস্ত ঘরের ডাস্টিং করে৷ ঘরে হুভার চালিয়ে, ওয়াশিং করে, ইন্ডোর প্লান্টগুলোর ব্যবস্থা করে, বাসন ধুয়ে সব কিছু ঝকঝক করে দেয়৷ ভালই ডলার খরচ হয় নিকির জন্য, তবে ও যে ওর কর্তব্যকর্মগুলো বেশ ভালোভাবেই করে এ বিষয়ে অন্ততঃ রোহিনীর কোনও সন্দেহ নেই৷
সীমন্তিনীও নিকির ওপর বিরূপ নয়, কিন্তু নিকি যখন থাকে না, সপ্তাহের সেই দিনগুলোও ও ধরে নেয় ওকে এই কাজগুলো করতেই হবে৷ ফলে সকাল থেকে টি-শার্ট আর প্যান্টের উপর একটা হাল্কা জোব্বার মতো অ্যাপ্রন পরে, কাঁধ অবধি চুল ঝুঁটি করে বেঁধে ও নেমে পড়ে অদৃশ্য ধূলিকণাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে৷ অরুণাভ ঠিক উল্টো, ব্যস্ত ডাক্তার৷ কিন্তু একই সঙ্গে বহুবিধ শখ ওর৷ সময় পেলেই সাঁতার কাটতে যায়, গল্ফ খেলে, সামারে কায়াকিং করতে চলে যায়৷ প্রথম প্রথম রোহিনীর দেখে খুব অবাক লাগত৷ বস্টনের যে সাবার্বে রণোদের বাড়ি, সেখানে থ্রি-কার গ্যারাজে একটা জায়গা নির্দিষ্ট, অরুণাভর কায়াক রাখার জন্য৷ সামারে অবধারিতভাবে বাবাই সপ্তাহান্তে কায়াক বড় গাড়ির সঙ্গে লাগিয়ে নিয়ে কায়াকিং করতে যেত৷ ইদানিং কয়েক বছর ধরে অরুণাভর ছটফটে স্বভাবটা একটু কমেছে৷ মাউন্টেনিয়ারিং বা ট্রেকিংয়ে ইদানিং প্রায় যায়ই না বাবাই, তবে যে কোনওরকম স্পোর্টস ওর এখনও প্রিয়৷ সন্ধ্যেবেলা সময় পেলেই বেসমেন্টের ঘরের আরামকেদারায় আধশোয়া হয়ে ফুটবল দেখতে ভালোবাসে৷ ফুটবল মানে অ্যামেরিকান ফুটবল৷
এইটা যখন উনি লিখতে শুরু করেন, গোড়া থেকেই আমার কৌতূহল ছিল খুব। কী লিখছেন জানার জন্য৷ একবার ঝুঁকে দেখেও ফেলেছিলাম, বাংলায় লিখছেন উনি৷ কিন্তু যতবারই জিজ্ঞেস করেছি, বলেছেন, জীবনের গল্পগুলো লিখছি৷ যখন জিজ্ঞেস করেছি, ‘আমাকে দেখাবে না?’ বলেছেন ‘যখন সময় হবে, তখন দেখাব৷’ সেই সময় আর আসেনি৷ তারপর তো স্ট্রোক হল৷ প্যারালাইজড্ হয়ে গেলেন৷ তখন ওঁকে নিয়েই চিন্তা ছিল৷ খাতার কথাটা মনেও ছিল না৷
বাড়ির কোনও ব্যাপারে কখনও সময় দেয় না বাবাই, নাকও গলায় না৷ বস্টন সাবার্বের এই জায়গাটা খুব শান্ত৷ অথচ শহর থেকে খুব একটা দূরে নয়৷ রোহিনীর এখন এটা শ্বশুরবাড়ি৷ কে জানে যদি দিল্লিতেই থেকে যেত, তাহলে জীবনের গতিটা কীরকম হত? হয়তো সে দিল্লি ইউনিভার্সিটি কিংবা জেএনইউ-তে পড়ত, প্রচণ্ড ছাত্র-রাজনীতি করত, তারপর হয়তো জাঠ কি পাঞ্জাবি বামপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী কোনও ছেলেকে বিয়ে করে সে দিল্লিতেই থাকত, কোনও একটা ভালো কলেজে পড়াত, চাইলে তনিকা সরকারের কাছে গবেষণা করতে পারত৷ চিত্তরঞ্জন পার্কে এক প্রতিবেশীর আত্মীয় উনি৷ ওই বাড়িতেই তনিকা সরকারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল রোহিনীর৷ তনিকা সরকারের কাছে দাদুর এই খাতাটা দেখাতে খুব ইচ্ছে হল রোহিনীর৷ উনি দেখলে হয়তো অনেককিছু বলতে পারতেন খাতাটার বিষয়ে৷
সীমন্তিনী আবার ডাকল রোহিনীকে৷ নাঃ! মাম্মাকে বুঝতে হবে যে ওর পেট ভর্তি৷ খাওয়ার ব্যাপারে খুব সচেতন রোহিনী৷ সে ঠিক করেছে ভালো করে ব্রেকফাস্ট করলে সে লাঞ্চ খাবে না৷ আর যতই ইনসিস্ট করক মাম্মা, ওইসব অ্যাপল পাই-টাই ছুঁয়েও দেখবে না৷ রোহিনী একটা ফিটনেস রেজিম চালু করেছে নিজের জন্য৷ একটা নিজস্ব রুটিন থাকা দরকার ৷ একটা শৃঙ্খলায় বাঁধা দরকার জীবনকে৷ জ্যোতির্ময় সেনের জীবনকে ছুঁতে গেলে আরও গভীরে যেতে হবে৷ কী ভেবে একজন লোক প্রথমে ইংল্যান্ডে, তারপর আমেরিকায় এসে সেটল করল, ছেলেমেয়ের মধ্যে দিয়ে ঠিক কী স্বপ্ন সে দেখতে চেয়েছিল, কেমন ছিল তার জার্নিটা, সব কিছু জানা দরকার৷
১৩
দেশভাগ এবং স্বাধীনতা– দুটি শব্দ বহু বাঙালির জীবনে সমার্থক হইয়া গিয়াছে৷ যাঁহারা ভুক্তভোগী তাঁহারা বিলক্ষণ জানেন স্বাধীনতার অমৃতফলের সহিত একই সঙ্গে দেশভাগের বিষফলও আস্বাদন করিতে হইয়াছিল৷ আমাদের পরিবারের মতো কিছু কিছু হতভাগ্য প্রস্তুত হইবারও সময় পায় নাই৷ বস্তুতঃ খুলনায় ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগস্ট ভারতের পতাকা উত্তোলিত হইয়াছিল৷ একদিনের ব্যবধানে ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়া যায়৷ স্থির হয় মুর্শিদাবাদের পরিবর্তে খুলনা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইবে৷ বাবা পূর্ব হইতেই মনস্থির করিয়া কলিকাতায় আসাই স্থির করেন এবং সেন্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে যোগ দেন৷ সেই অনুযায়ী মা এবং আমরা তিনটি ভাই বোন (ছোটকু তখনও জন্মায় নাই) বাবার সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়া উত্তরের শহরতলিতে বাসা লইলাম৷ কিন্তু জ্যাঠামশাইরা, যাঁহারা মোটামুটি নিঃসংশয় ছিলেন যে খুলনা সদর এবং নিকটস্থ সেনহাটি গ্রাম ইত্যাদি ইন্ডিয়াতেই রহিবে, স্বাধীনতার একদিন পরে সেই সিদ্ধান্ত বদল হওয়ায় তাঁহাদের মস্তকে বজ্রাঘাত হয়৷ অনতিবিলম্বেই তাঁহারা বুঝিতে পারেন, বিষয়-সম্পত্তি, ভদ্রাসনটুকু রক্ষা করা তো বটেই, পাকিস্তানি সরকারের জমানায় দৈনন্দিন জীবনাচরণই কঠিন হইয়া পড়িতেছে৷ বড় দুই জ্যাঠামশায় সেনহাটি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন৷ বড় জ্যাঠামশাই প্রধান শিক্ষক হিসাবে অত্যন্ত সম্মানীয় ব্যক্তি ছিলেন৷ কিন্তু তিন-চার বৎসর পরেই দু’জনেই অনুভব করিতেছিলেন যে, তাঁহাদের প্রাপ্য সম্মান আর বজায় থাকিতেছে না৷
পারিবারিক দুর্গোৎসব বেশ কয়েক বৎসর বন্ধ হইয়া গিয়াছিল৷ পূর্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত স্বপ্নবাসুদেবের মন্দিরের নিত্যপূজাও কোনওক্রমে নমো নমো করিয়া চলিতেছিল৷ কিন্তু যে বিদ্যালয় আমার ঠাকুর্দার প্রতিষ্ঠিত, সেখানে অন্তর্নিহিত রাজনীতি ও কোন্দল এত জটিল হইয়া উঠিল, যে ১৯৫২ সন নাগাদ জ্যাঠাদের পরিবার কলিকাতা আসিতে একপ্রকার বাধ্য হন৷ ইতিমধ্যে পাসপোর্ট চালু হয়৷ দুই দেশে যাতায়াত আর অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত রহিল না৷ যতদূর মনে আছে দুই জ্যাঠামশায় প্রায় সর্বস্বান্ত অবস্থায় কলকাতা পৌঁছান৷ স্কুল হইতে প্রাপ্য টাকা পয়সার খুব অল্প অংশই তাঁহারা পাইয়াছিলেন৷ বাকি পরে পাওয়া যাইবে বলিয়া আশ্বস্ত করা হইয়াছিল৷ সেই অর্থ আর কখনই পাওয়া যায় নাই৷ পৈত্রিক বাটিও ‘এনিমি প্রপারটি’ তকমা লইয়া বেদখল হইয়া যায়৷

জ্যাঠারা যখন কলিকাতায় আসেন, তখন বিজয়গড়, আজাদগড় ইত্যাদি এলাকাগুলির সমস্ত জমি রেফ্যুজিদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা হইয়া গিয়াছিল৷ বাস্তুহারা উন্নয়নের মধ্যেও বহু চোরাস্রোত ছিল৷ জ্যাঠারা মাঝে মধ্যে হা-হুতাশ করিতেন– যাদবপুর, বাঘাযতীন অঞ্চলের তথাকথিত ভালো এলাকাগুলি এর মধ্যে অন্যদের মধ্যে বিতরণ করা হইয়া গিয়াছে বলিয়া৷ প্রায় নামমাত্র মূল্যে সেই জমিগুলি রেফ্যুজিরা পান৷ সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের গ্রামের কতিপয় মুরুব্বি ব্যক্তি মিলিয়া বেহালা অঞ্চলে একটি স্বতন্ত্র কলোনী স্থাপন করিয়াছিলেন৷ জ্যাঠারাও ওই অঞ্চলে পাশাপাশি দুইটি জমি কিনিয়া বাড়ি করিতে সক্ষম হন৷ সেনহাটির লোকের সংখ্যাধিক্যের দরুণ ওই নতুন পাড়াটির পত্তন করিয়া নাম দেওয়া হয় সেনহাটি কলোনি৷ জ্যাঠাদের বাড়ি যখন হইতেছিল, তখন ওইসব অঞ্চল একেবারে নীচু এবং জলাজমি ছিল৷ রাতবিরেতে শিয়াল ডাকিত৷ আশ্চর্যের বিষয়, তাহার পনেরো-ষোলো বৎসর পরেই ওইসব স্থানের কেমন আমূল পরিবর্তন হইল৷ গা ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া কত বাড়ি মাথা তুলিল৷ বহু দোকানপাট-বাজার, রিক্সা, স্কুল, কলেজ সমস্ত মিলিয়া বেহালা অঞ্চল কলিকাতার দক্ষিণে একটি অত্যন্ত জনবসতিপূর্ণ এলাকা বলিয়া পরিগণিত হইল৷
দেশভাগ এবং শরণার্থী হইয়া চলিয়া আসা, এই বিরাট ঘটনার প্রভাব যে সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই৷ রেফ্যুজি পরিবারগুলিকে বহু বিড়ম্বনার শিকার হইতে হইয়াছিল৷ ভাগ্যের বিড়ম্বনায় তাহাদের বহু পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল৷ ছিন্নমূল মানুষের বেদনা এবং সংগ্রাম লইয়া সাহিত্য, বিশেষ করিয়া ফিল্ম কম হয় নাই৷ নূতন নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত হওয়া একটি জটিল প্রক্রিয়ার অংশ৷ সেই প্রক্রিয়ার ঘূর্ণনে আবর্তিত হইতে হইতে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত মানুষরা জীবনের সঙ্গে নতুনভাবে বোঝাপড়া করিতে সমর্থ হয়৷ তাহাদের মানসিকতায়ও কিছু পরিবর্তন হয়৷ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান– যেগুলি একসময় জলহাওয়ার মতোই স্বাভাবিক এবং সহজলভ্য বলিয়া মনে হইত, সেই বস্তুগুলি পঞ্চাশের দশকের রেফ্যুজিদের নিরন্তর সংগ্রামের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়৷ পুরুষদের পাশাপাশি এই সংগ্রামে মেয়েরাও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে৷ হয়তো স্বাধীনতার বিশ বৎসর পূর্বে নারী স্বাধীনতার ভূমিটি তৈরি হইয়াছিল৷ তবে ত্রিশ-চল্লিশের দশকে যে সব নারীরা লাইমলাইটে আসেন, তাঁহারা ব্যতিক্রমী৷
রোহিনী ঠিক করেছে মাম্মার কোনও কথায় তেমন পাত্তা দেবে না৷ মাম্মার মধ্যে একটা কন্ট্রোল ফ্রিক সত্তা আছে৷ সবসময় মাম্মা চেষ্টা করে সমস্ত কাজ নিখুঁতভাবে চলবে, ঘরবাড়ি একেবারে ধুলোহীন হয়ে সাজানো থাকবে৷ সবাই রোবটের মতো নিজের কাজগুলো করে ফেলবে৷ যদিও রোহিনী এতদিনকার অভ্যেসে দেখেছে এদেশে ঘরবাড়ি এমনিতেই পরিষ্কার থাকে৷ দেশের মতো রোজ রোজ ডাস্টিং করার দরকার হয় না৷ বিশেষ করে সীমন্তিনীদের বাড়ির মতো সব ঘরেই চমৎকার ওয়াল টু ওয়াল কার্পেট থাকলে৷
স্বাধীনতা এবং দেশভাগের পরবর্তী বিশ বৎসর ধরিয়া নারী স্বাধীনতার ক্ষেত্রটি যে বাংলায় বহুলাংশে বিস্তৃত হইল, এ বিষয়ে কোনও সংশয়ের অবকাশ নাই৷ আমার জেঠতুতো দিদিদের দেখিতাম, বৈদ্য পরিবারের এই মেয়েদের লড়াকু মানসিকতা আমাকে বিস্মিত করিত৷ খেঁদি, বুঁচি, আন্না, শেফালি– আমার দিদিরা প্রত্যেকে নিজ চেষ্টায় প্রাইভেটে বিএ বা এমএ পাশ করিয়াছিলেন৷ সেনহাটি কলোনিতে আমাদের পরিবারের লতায় পাতায় জ্ঞাতিগুষ্টির মধ্যেই তাঁহাদের বিবাহ হয়। কিন্তু প্রত্যেকটি মহিলা স্বাধীন উপার্জনক্ষম ছিলেন৷ ইঁহাদের কেহ বেহালায় স্কুলে পড়াইতেন, কেহ বা নার্সিং শিখিয়া হাসপাতালে নার্সের কাজ করিতেন৷ আবার জেঠিমারা সেলাই মেশিন কিনিয়া শেলাই শিখিয়া পাড়া-প্রতিবেশিনীর ব্লাউজ, পেটিকোট সেলাই করিয়া স্বামীদের সংসারের ব্যয় আংশিক নির্বাহ করিতেন৷ জ্যাঠারা চাকরিজীবনের উপান্তে ইন্ডিয়ায় আসেন৷ নতুন করিয়া আর চাকরি জোগাড় করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না৷ কিন্তু বাড়িতে নিয়মিতভাবে তাঁহারা ছাত্র পড়াইতেন৷ বেশ কয়েক ব্যাচে ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁহাদের কাছে ইংরাজি, সংস্কৃত এবং অঙ্ক শিখিতে আসিত৷
আমাদের পরিবারটি জ্যাঠামহাশয়দের তুলনায় সচ্ছল ছিল৷ আমাদের নিজস্ব লড়াই ছিল, কিন্ত বোধকরি পার্টিশনের কিঞ্চিৎ পূর্বে স্থানান্তরিত হইবার দরুণ লড়াইয়ের প্রকৃতি কিছু ভিন্ন ছিল৷ বাবা কলকাতায় আসিয়াও সরকারি কলেজে অধ্যাপনা করিতেন৷ স্বাধীন ভারতবর্ষে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের স্মরণে সেন্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজের নামকরণ করা হয় মৌলানা আজাদ কলেজ৷ এই কলেজটিতে আমিও আইএসসি পড়ি৷ সে ৫২-৫৩ সালের কথা৷ কলেজটিতে ঢুকিবার মুখে একটি মহুয়া গাছ ছিল৷ অর্বাচীন ছাত্ররা প্রায়ই গাছের তলায় পড়িয়া থাকা ফুলগুলি কুড়াইয়া মহুয়ার স্বাদ আস্বাদন করিত৷ যেমন ছাত্রদের ভিতর, তেমনি শিক্ষকদের ভিতর মিশ্র গোষ্ঠী ছিল৷ অধিকাংশই মুসলমান ছাত্র৷ কলেজে যেমন একদিকে বাংলা ও সংস্কৃত পঠন পাঠনের ব্যবস্থা ছিল, তেমনি আরবি, ফারসি, উর্দু ইত্যাদি ভাষাও অধ্যয়নের ব্যবস্থা ছিল৷ স্টাফরুমেও হিন্দু ও মুসলিম ধর্মাবলম্বী শিক্ষকদের একধরনের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ছিল৷ পার্টিশনের পরবর্তী বছরগুলিতেও এই সৌহার্দ্য কখনও ক্ষুণ্ণ হয় নাই৷
এইবার আমার ইমিডিয়েট ফ্যামিলির বিষয়ে কিছু বলা প্রয়োজন৷ পূর্বেই বলিয়াছি আমার ভগিনীদ্বয় হাসি ও খুশি শান্তিনিকেতনে পড়িতে যায়৷ হাসি ও খুশির মধ্যে তফাৎ আড়াই বৎসরের৷ হাসি ও খুশি শৈশব হইতে কলাবিদ্যায় প্রভূত পারদর্শী ছিল৷ দু’জনেরই গানের গলা ছিল চমৎকার৷ সেজন্য প্রি-ইউনিভার্সিটির পর বাবা হাসিকে শান্তিনিকেতনে সঙ্গীতভবনে ভর্তি করাই সমুচিত বলিয়া বিবেচনা করেন৷ খুশি তাহার দুই বৎসর পরে কলাভবনে যোগ দেয়৷ উহারা শান্তিনিকেতনে আবাসিক ছাত্রী হিসাবে পড়িত৷ সেইখানে কোনও একবার ভগ্নীদের গ্রীষ্মের ছুটির গোড়ায় আনিতে গিয়া অরুণের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়৷ আমার সহিত যে তখনই প্রথম দেখা, অরুণের স্মৃতিতে সেই ঘটনা ধরা নাই৷ প্রথম দর্শনেই সেই তরুণীকে দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল– বাঃ! বেশ মেয়েটি তো! ভিতরে ভিতরে একটু চিত্তচাঞ্চল্য টের পাইতেছিলাম৷ আমিও তখন পঁচিশ বৎসরের যুবকমাত্র৷ সেই পরিচয় গভীরতর হয় ১৯৬১-র বসন্তোৎসবে৷ সেই ঘটনায় হয়তো বা হাসিরও কিছু হাত ছিল৷ হাসি অরুণের ঘনিষ্ঠতম বান্ধবীও বটে৷ অরুণকে সে সর্বদা আমার সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করিত৷

হাসি ও খুশি দুইবোন শান্তিনিকেতনের যে কোনও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অগ্রবর্তী ভূমিকায় থাকিত৷ খুশি অঙ্কনের পাশাপাশি নৃত্যশিল্পেও পারদর্শী ছিল৷ শান্তিদেব ঘোষের নাচের ট্রুপের সঙ্গে সে পরে জাভা, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি পরিদর্শন করিয়াছিল৷ সে রাত্রে বৈকালিকে ‘আমাদের শান্তিনিকেতন’ গানের মাদকতায় আমি তখনও আচ্ছন্ন ছিলাম৷ রাতে অরুণলেখাদের বাড়িতে ওর কয়েক বন্ধুর নিমন্ত্রণ ছিল৷ হাসির দাদা ও অভিভাবক হিসাবে সেই রাত্রে সেখানে আমিও আমন্ত্রিত ছিলাম৷ অরুণ এবং তাহার দাদা মোহন শান্তিনিকেতনের জল-বাতাসে মানুষ৷ তাহাদের ব্যবহারে কোনও জড়তা ছিল না৷ রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর অরুণদের সীমান্তপল্লির একতলার ছাদে গানের আসর বসিয়াছিল৷ হাসি ও অরুণ শুধু নয়, আরও অনেকে সে রাত্রে গান গাহিয়াছিল৷ খোলা আকাশের তলায় চাটাই বিছাইয়া একের পর এক গান৷ কখনও এসরাজ বাজাইয়া, কখনও খালি গলায়৷ একেবারে শেষ পর্যায়ে হাসি বলিয়াছিল
– অরুণ! তুই ওই জ্যোৎস্নারাতের গানটা গা৷
আর একবারও সাধিতে হয় নাই৷ এক ঢাল চুল খোলা, সামনে কোথাও একটা বকুল গাছ হইতে তীব্র মাদকতাময় গন্ধ আসিতেছিল৷ অরুণ গাহিতেছিল বসন্তের এই মাতাল সমীরণে৷ আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে৷
সেই গান যেন অন্য কোনও কল্পলোক হইতে ভাসিয়া আসিয়া সেদিনের ছাব্বিশ বছরের যুবক আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া দিতেছিল৷ অরুণলেখার সঙ্গে জীবনের এই খেলাঘরে পঞ্চাশ বছরেরও বেশি কাটাইলাম৷ মান অভিমান, ঝগড়াঝাঁটি সব দাম্পত্যের মতোই আমাদেরও দাম্পত্যের অংশ ছিল৷ মাঝে মাঝে মনে হইয়াছে, এই অরুণলেখাকে যেন চিনিতে পারি না৷ কী জানি অরুণেরও হয়তো আমাকে দেখিয়া মাঝে মাঝে এই একইরকম অচেনা ঠেকে৷ কিন্তু চক্ষু বুজিয়া মনের মধ্যে যদি সেদিনকার সেই বসন্তোৎসবের দৃশ্য মনে করি, তবে সব যেন একইরকম আছে মনে হয়৷ বাহান্ন বছর আগের সেই ছাদ, অরুণের একঢাল কালো চুল, জাদুকরী জ্যোৎস্না, দোলপূর্ণিমার সেই মায়াচাঁদ, সব কিছু অবিকল তেমনই আছে৷ মনে মনে সেই স্বপ্নজীবন তার তীব্র মাদকতাময় বকুলগন্ধ লইয়া ফিরিয়া আসিতে থাকে৷
১৪
সীমন্তিনীর আজকাল খুব ভালো লাগে৷ তাদের বাড়িটা আবার অনেককাল বাদে বেশ ভরে উঠেছে৷ অরুণলেখা আসার পর বাড়িটা বেশ ভরা ভরা লাগছিল প্রত্যেকবারের মতোই৷ সীমন্তিনী লক্ষ করেছে, ওর শাশুড়ির একটা শান্ত স্নিগ্ধ উপস্থিতি রয়েছে৷ একেবারেই উচ্চকিত নয়, কিন্তু একটা হালকা সুগন্ধের মতো বাড়িটাকে ঘিরে রাখে৷ হয়তো পুরোটাই ওর মন গড়া৷ কিন্তু বাড়িতে অরুণলেখা থাকলেই ওর মনে হয় মাথার উপরে একটা ছাতা খোলা রয়েছে৷ এক ধরনের প্রোটেকশন৷ রোহিণীর মা বাবা এসে কদিন খুব হৈ হৈ হল৷ সেই সময়েই জিনিয়ারও ইস্ট কোস্টে কাজ পড়ে যাওয়ায় বেশ একটা ফ্যামিলি রি-ইউনিয়ন মতো হয়ে গেল৷ পরের বছর কলকাতায় বেশ কিছুটা সময় নিয়ে যেতে হবে৷ রোহিণীর দাদার বিয়েতে রণো আর রোহিণী তো বটেই, সীমন্তিনী আর অরুণাভকেও যেতে হবে৷ ওরা অনেকবার করে বলেছে অরুণলেখাকেও নিয়ে যাবার জন্য৷ কিন্তু মামণির শরীর কি অতদূরে যাবার ধকল সইতে পারবে?
পূর্বেই বলিয়াছি আমার ভগিনীদ্বয় হাসি ও খুশি শান্তিনিকেতনে পড়িতে যায়৷ হাসি ও খুশির মধ্যে তফাৎ আড়াই বৎসরের৷ হাসি ও খুশি শৈশব হইতে কলাবিদ্যায় প্রভূত পারদর্শী ছিল৷ দু’জনেরই গানের গলা ছিল চমৎকার৷ সেজন্য প্রি-ইউনিভার্সিটির পর বাবা হাসিকে শান্তিনিকেতনে সঙ্গীতভবনে ভর্তি করাই সমুচিত বলিয়া বিবেচনা করেন৷ খুশি তাহার দুই বৎসর পরে কলাভবনে যোগ দেয়৷ উহারা শান্তিনিকেতনে আবাসিক ছাত্রী হিসাবে পড়িত৷ সেইখানে কোনও একবার ভগ্নীদের গ্রীষ্মের ছুটির গোড়ায় আনিতে গিয়া অরুণের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়৷
ভাবতে ভাবতে ঝম ঝম করে বৃষ্টি এল৷ কাচের বড় বড় জানলা দিয়ে বৃষ্টি দেখতে খুব ভাল লাগে সীমন্তিনীর৷ ওর ছোটবেলায় কলকাতায় বৃষ্টি এলে ঠাকুমার ঘরে গিয়ে গুটিশুটি হয়ে শুয়ে পড়ত।
– ঠাম্মা, একটা গল্প বলো৷
ঠাম্মা গল্পের ঝুলি খুলে বসতেন৷ ঠাম্মার কাছে শুনেছিল ওর দাদু নাকি ভাগ্যান্বেষণে বর্মায় গিয়ে ছিলেন কিছুদিন৷
– আমার তখন পাঁচ মাস চলছে৷ তোমার পিসি ছোট, আর তোমার বাবা আমার পেটে, তখন তোমার দাদু পাড়ি দিলেন বার্মা৷
– তুমি কোথায় ছিলে?
– কেন, এই বাড়িতেই৷ তখন আমার শ্বশুর, শাশুড়ি, ননদরা, চাকরবাকর– বাড়ি একেবারে গমগম করত৷
– বাবা যখন জন্মাল,তখন?
– তখন তো লোকে কথায় কথায় অত হাসপাতালে ছুটত না৷ মেডিকেল কলেজ ছিল৷ কিন্তু খোকা হয়েছিল বাড়িতে৷
ভবানীপুরের বাড়ির ভিতরদিকের একটা ঘর ছিল আঁতুড়ঘর৷ সীমন্তিনীর বাবা অম্বিকাচরণের জন্ম সেখানে৷ বিয়ের পর রোহিণীকে নিয়ে যখন কলকাতায় এসেছিল সীমন্তিনী, তখন আঁতুড়ঘরটা দেখে খুব অবাক হয়েছিল রণো আর রোহিণী৷ রণো বেশ কয়েকবার গেছে কলকাতায়,কিন্তু সীমন্তিনীর বাবার জন্ম যে বাড়িরই একটা ঘরে, সেটা ওকে বলা হয়নি কখনও৷ ওই বাড়িতেই অম্বিকার জন্ম৷ মৃত্যুও৷ অম্বিকা খুব বেশিদিন বাঁচেননি৷ বাবা আর একটু বেশিদিন থাকলে সীমন্তিনী ওর ঘরসংসার দেখাতে পারত বাবাকে৷ সীমন্তিনীর হঠাৎ মনে হল, বাবার মৃত্যুর খবর পেয়ে অরুণাভ ছুটে গেছিল চটজলদি টিকিট কেটে৷ কিন্তু কী পরিস্থিতিতে বাবা ঘুমের মধ্যে হঠাৎ চলে গেলেন, গিয়ে অরুণাভ কী দেখেছিল এসব আর কখনও জানা হয়নি অরুণাভর কাছ থেকে৷ তখন সীমন্তিনী হেভিলি প্রেগন্যান্ট৷ ওকে যতটা সম্ভব ঢেকে, প্রোটেক্ট করে চলতেন শুধু অরুণাভ নয়, অরুণলেখা আর জ্যোতির্ময়ও৷ ওই সময়ে শ্বশুর শাশুড়ির সাহচর্য আর উপস্থিতি ওর কাছে ছিল আর্শীবাদের মতো৷ মা-বাবা যেভাবে সন্তানকে রক্ষা করে, ওঁরা ঠিক সেভাবেই সব ঝড় ঝাপটা থেকে চিরকাল ঢেকে এসেছেন সীমন্তিনীকে৷ অম্বিকার আকস্মিক মৃত্যুর বেশ কিছুদিন পরে অরুণাভকে বেশ কয়েকবার জিজ্ঞেস করেছে সীমন্তিনী,
– তুমি গিয়ে কী দেখেছিলে?
অরুণাভ বার বার এড়িয়ে গেছে৷
– কী হবে সীমন ওসব মনে করে? যিনি গেছেন, তিনি তো আর ফিরবেন না৷ তার চেয়ে শেষ যেমন দেখেছ, সেই হাসিখুশি জীবন্ত মানুষটাকেই মনে রেখে দাও৷
অরুণাভ খুব আস্তে আস্তে সীমন্তিনীর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলেছিল৷
‘কিছু কিছু গল্প অজানাই থেকে যায়৷ অজানাই থাক না…’ যেমন বলেছিলেন বিক্রম৷ ওঁর প্রথম উপন্যাস তখন সদ্য বেরিয়েছে৷ বিশালকায় উপন্যাস রুদ্ধশ্বাসে কয়েকদিনের মধ্যে পড়ে ফেলেছিল সীমন্তিনী৷ তার দু-একমাসের মধ্যে বস্টনের বার্নস অ্যান্ড নোবলের দোকানে বুক ট্যুরের অংশ হিসেবে একটা আলোচনাসভায় এসেছিলেন উনি৷ তখন যুবক৷ অরুণাভরই আশপাশে বয়স৷ রোগা পাতলা চেহারা৷ মাথার সামনের দিকটা আস্তে আস্তে পাতলা হয়ে আসছে৷ ওঁকে দেখার জন্য দোকানে প্রায় দেড়শো লোকের আসন সব কানায় কানায় ভরা৷ উজ্জ্বল কিন্তু নরম আলোর বৃত্তে বসে লেখক খুব মৃদস্বরে পাঠ করলেন উপন্যাসের স্বনির্বাচিত কয়েকটি অংশ৷ তারপর প্রশ্নোত্তরের পালা৷ উৎসাহী পাঠকরা একের পর এক প্রশ্নের ডালি সাজিয়ে জবাব জানতে চাইছিলেন লেখকের কাছে৷ উনি একটুও ব্যস্ত বা বিব্রত হচ্ছিলেন না৷ যেন প্রতিটি প্রশ্নই অনুমান করেছিলেন– এরকমভাবে হেসে থেমে থেমে জবাব দিচ্ছিলেন৷ সেই সময়ই সীমন্তিনীর মনেও বইটা পড়ার সময়ই যে প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল, সেটাই একটু অন্য ভাষায় করেছিলেন এক পাঠক৷ গল্পের নায়িকার তার প্রেমিকের সঙ্গে কেন বিয়ে না হয়ে অন্য একজনের সঙ্গে কেন বিয়ে হল? তার ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে বিয়ে হলে কি হত? লেখক একটু বিষণ্ণ হাসি হেসেছিলেন৷ পাতলা হয়ে আসা চুলে আঙুল চালাতে চালাতে বলেছিলেন,
– ওর সঙ্গে বিয়ে হলে কী হত, আমি জানি না৷ কারণ বিয়েটা হয়নি৷
আবার কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে উনি বলেছিলেন,
– আসলে জান তো, কিছু কিছু গল্প অজানাই থেকে যায়৷ অজানাই থাক না!
সীমন্তিনীর হঠাৎ মনে পড়ে গেল কথাটা৷ সব গল্প নিটোলভাবে শেষ হয় না৷ আবার কিছু কিছু গল্প এক একজনের জীবন পরিধির মধ্যে ঘটে শেষ হয়ে যায়৷ কত গল্প আছে, যেগুলো সময় থাকতে কখনও ঠিকমতো শোনা হয় না৷ রোহিণী এইজন্যই পুরনো গল্পগুলোকে ধরে রাখতে চায়৷ জ্যোতির্ময়ের ডায়েরির মধ্যে যে পুরনো সময় উঁকি মারে, চেনা মানুষদের ঘরোয়া কথায় যে হারিয়ে যাওয়া পরিবারগুলোর ছবি ভেসে ওঠে, ও সেগুলোকে খুঁজে বেড়ায় পুরনো সময়টাকে বুঝতে৷
অরুণলেখা এখনও জীবনের যে ঘটনাগুলো মনে করতে পারেন, তার অনেকগুলো হয়তো সীমন্তিনীর জানা৷ কিন্তু অরুণলেখার জীবনের অনেক খুঁটিনাটিই তো ও জানে না৷ উনি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেসব গল্পও হারিয়ে যাবে চিরকালের মতো৷ এসব ভাবতে ভাবতে সীমন্তিনীর একটু অস্থির লাগল৷ কী ভেবে ও তাড়াতাড়ি বাড়ির চটিটা গলিয়ে অরুণলেখার ঘরে এল৷ দুপুর থেকেই রীতিমতো ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে৷ অরুণলেখা জানলার পাশে রাখা বেতের গোল চেয়ারে বসে বৃষ্টি দেখছেন৷ ঘরের মিউজিক সিস্টেমে বর্ষার গান বাজছে৷ ‘যায় দিন শ্রাবণ দিন যায়’ সংকলনটার নাম৷ রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গান ও কবিতার সুগ্রন্থিত একটি সংকলন৷ অরুণলেখা এখন নিজে গান চালাতে পারেন না৷ উনি ফিলাডেলফিয়ার বাড়িতে পুরনো দিনের টার্ন টেবল রেকর্ড প্লেয়ার আর পরের দিকে ক্যাসেট প্লেয়ারে অভ্যস্ত ছিলেন৷ রোহিণী নিশ্চয়ই চালিয়ে দিয়ে গেছে৷ এরকম ছোট ছোট জিনিসগুলো রোহিণী সবসময় খেয়াল রাখে বাড়িতে থাকলেই৷ সীমন্তিনী মনে মনে তারিফ না করে পারে না৷ সীমন্তিনীরই তো খেয়াল করা উচিত ছিল৷ ও এলো চুলগুলো একটা আলগা হাত খোঁপা করতে করতে অরুণলেখার কাছে এসে বলল,
– ঠিক দেশের মতো বৃষ্টি পড়ছে আজ, তাই না মামণি?
অরুণলেখা হাসলেন। বললেন,
– এদেশে বৃষ্টি হলে মাটির সোঁদা গন্ধ পাওয়া যায় না৷ আমাদের ওখানে বৃষ্টি হলেই ওই যে সুঘ্রাণটা উঠত, ওটা এদেশে আসার পর খুব মিস করতাম৷ তারপর আস্তে আস্তে অভ্যেস হয়ে গেল৷
– দেশে যেতে ইচ্ছে করে মামণি?
সীমন্তিনী আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল৷
– নাঃ, এখন আর করে না৷ দেশে আর কতবছর ছিলাম বল! জীবনের বেশিটাই তো এখানেই কাটল, ইংল্যান্ডে চার বছর বাদ দিলে৷
– এখন এটাই তোমার দেশ, কী বল দিদান?
রোহিণী সুড়ুৎ করে কখন ঘরে ঢুকে এসেছে খেয়ালই করেনি সীমন্তিনী৷ ও হাসিমুখে বলল,
– আরে, তুই কখন চলে এলি?
– হাঁউ মাঁউ খাঁউ, গল্পের গন্ধ পাঁউ…
রোহিণী মজা করে বলছে৷
– যেই দেখেছে আমার ঘরে তুমি আসছ, অমনি ও এসেছে৷ পুরনো গল্প পেলে আর কিছু চায়না মেয়েটা৷
– একেবারে ঠিক কথা৷ দিল্লিতে এরকম বৃষ্টি হলে আমার মা মাসিরা গোল হয়ে বসে গল্প করার জন্য, কিন্তু উইথ চা অ্যান্ড পাঁপড়ভাজা৷ এনিবডি ফর চা অ্যান্ড পাঁপড়? হাত তোল৷
– গুর্মুখের দেওয়া আগের পাঁপড়গুলোও ফুরোয়নি এখনও৷ চা কি চাইনিজ টি টা করবি? তাহলে দ্যাখ প্যানট্রিতে সেকেন্ড তাকে আছে৷
সীমন্তিনী বলছে৷
– নো ওয়ে৷ পিওর লপচু চা ইন দিস্ ওয়েদার৷ আমি জানি কোথায় আছে৷
বলে রোহিণী হুড়মুড় করে চলে গেল চা আর পাঁপড়ের জোগাড় করতে৷ অরুণলেখা সীমন্তিনীকে বললেন,
– মেয়েটা সত্যিই খুব আন্তরিক৷ আমাদের বাড়ির উপযুক্ত।
সীমন্তিনীও সায় দিল।
– ওর বাড়িতেও খুব ঘরোয়া পরিবেশে বড় হয়েছে তো! সেটা বোঝা যায়৷ শিপ্রাদিরা সকলেই এত চমৎকার৷ আমাদের সঙ্গে ওয়েভলেংথে খুব মেলে৷

সীমন্তিনীদের শোবার ঘরগুলো সব উপরতলায়৷ ঘরের লাগোয়া একটা ছোট প্যানট্রি আছে চটজলদি চা জলখাবার করার জন্য৷ সকালের বেড টি আর বিকেলের চা স্ন্যাক্স সব এখান থেকেই হয়৷ অরুণলেখার স্যুপ অবধি৷ সন্ধ্যেয় বেশিরভাগ দিনই অরুণলেখা স্যুপ আর এক পিস টোস্ট খান৷ বাইরের লোক বা গেস্ট না থাকলে ছোটখাট খাবারের জন্য নীচের বড় কিচেনে যাবার দরকারই পরে না৷ রোহিণী বেশ চট করে চা আর পাঁপড় সেঁকে এনেছে৷
– হ্যাভ আই মিস্ড্ এনিথিং?
– নো, উই আর ওয়েটিং ফর ইওর গ্রেসাস কম্পানি৷
সীমন্তিনী বলল৷ অরুণলেখা পাঁপড়ের দিকে তাকিয়ে বললেন,
– আমাদের দমদমের বাড়ির ওখানে খুব বড় রথের মেলা বসত৷ পাঁপড়ভাজা ছিল মাস্ট৷
– বাড়িতে ভাজতে, না মেলায় কিনতে?
রোহিণী জিজ্ঞেস করল৷
– মেলায় তো বটেই৷ আমরা দফায় দফায় মেলায় গিয়ে ঘুরে আসতাম৷
– কার সঙ্গে যেতে?
এবার সীমন্তিনী৷
– যখন যার সঙ্গে হয়৷ শাশুড়ির সঙ্গে যেতাম৷ শাশুড়ির খুব গাছের শখ ছিল৷ বেছেবুছে চারা কিনে নিয়ে আসতেন দমদমের বাড়ির সামনে জমিতে লাগানোর জন্য৷ ওই করে লেবু লঙ্কা, ধনেপাতা, কত কী হয়েছিল৷ এমনকি ছোট ছোট টমেটো অবধি৷ দুটো আমগাছও লাগিয়েছিলেন৷ তবে সেই আম আর আমাদের খাওয়া হয়নি৷
– কেন?
– তার আগেই চলে গেলাম তো ইংল্যান্ডে৷ ফের গেলাম শ্বশুরমশাই যখন মারা গেলেন৷ সে তো আর আমের সিজন না৷ ভালো হিসমাগর হত, খুশি বলেছিল৷
– তোমরা আমের সিজনে একবারও যাওনি?
রোহিণী প্রায় বিশ্বাসই করতে পারছে না৷
– নাঃ, অরুণলেখা জবাব দিচ্ছেন।
– পরে মে মাসে একবার-দুবার উনি দেশে গেছেন কাজ নিয়ে৷ দিল্লিতে হাসির বাড়িতে মায়ের সঙ্গে দেখাও করে এসেছেন, কিন্তু তখন আর আমগাছ কোথায়? বাড়িই তো বিক্রি হয়ে গেল৷ হাতবদল হয়ে যারা কিনেছিল, তারা খেত হয়তো।
অরুণলেখা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন৷
– রথের মেলার কথা বলছিলে দিদান৷
রোহিণী মনে করায়৷
– হ্যাঁ রথের মেলা বসত নাগেরবাজার থেকে সাতগাছি অবধি পুরো যশোর রোড জুড়ে৷ এদিকে দমদম রোডের দিক থেকে শুরু হয়ে যেত৷
– কী বিক্রি হত ওখানে?
– ওরে বাবা! কী বিক্রি হত না? মাটির পুতুল, মাটি দিয়ে তৈরি ফল, শসা, কলা, পেয়ারা, আম, ঠিক সত্যিকারের মতো দেখতে৷ সেই দেখে বাবাইয়ের কী আনন্দ!
অরুণলেখা যেন দেখতে পাচ্ছেন ছোট্ট বাবাইয়ের হাসি৷
– বাবাইও যেত রথের মেলায়!
রোহিণী বলে৷
– ও বাবা! ও তো আগে পা বাড়িয়ে তৈরি৷ কাকা পিসিদের কোলে চড়ে মেলায় যাবার জন্য পা বাড়িয়ে থাকত৷ একরকম ছোট্ট ছোট্ট চিনে লন্ঠনও বিক্রি হত৷
রোহিণী লক্ষ করে অরুণলেখা যত না জিনিসের নাম করছেন, তার চেয়ে বেশি জোর দিচ্ছেন ‘কত কী বিক্রি হত’ শব্দগুলোর উপর৷
অরুণলেখা এখনও জীবনের যে ঘটনাগুলো মনে করতে পারেন, তার অনেকগুলো হয়তো সীমন্তিনীর জানা৷ কিন্তু অরুণলেখার জীবনের অনেক খুঁটিনাটিই তো ও জানে না৷ উনি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেসব গল্পও হারিয়ে যাবে চিরকালের মতো৷ এসব ভাবতে ভাবতে সীমন্তিনীর একটু অস্থির লাগল৷ কী ভেবে ও তাড়াতাড়ি বাড়ির চটিটা গলিয়ে অরুণলেখার ঘরে এল৷ দুপুর থেকেই রীতিমতো ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে৷ অরুণলেখা জানলার পাশে রাখা বেতের গোল চেয়ারে বসে বৃষ্টি দেখছেন৷
সীমন্তিনী কী যেন ভাবছিল দমদমের বাড়ির কথা হওয়ার পর থেকে৷ হঠাৎ ও বলে
– আচ্ছা দমদমের বাড়িটা কারা কিনেছিল?
– বিষ্টুবাবু বলে এক ভদ্রলোক৷ উল্টোদিকের পাড়া দেবীনিবাসে থাকতেন৷ ওঁর একটা দেশলাইয়ের কারখানা ছিল৷ আর হোসিয়ারি বিজনেস না কী সব ছিল৷
– দেশলাই কারখানায় কি তৈরি হত? দেশলাই কাঠি?
প্রশ্নটা করেই রোহিণী বুঝতে পারে প্রশ্নটা খুব বোকা বোকা হয়ে গেল৷ দেশলাই ছাড়া আর কীই বা তৈরি হতে পারে দেশলাই কারখানায়? অরুণলেখা হেসে ফেললেন।
– দেশলাইয়ের কাঠি, বাক্স৷ কাঠিগুলো বাক্সে ভরা হতে হবে তো! একবার খুশি লিখেছিল দেশলাই কারখানায় দাউ দাউ করে আগুন লেগে অনেক টাকার মাল নষ্ট হয়েছে৷
– ভদ্রলোক বাড়ি প্রোমোট করতে দিলেন কেন?
সীমন্তিনী জিজ্ঞেস করল৷
– প্রোমোটিং হয়েছিল নাকি?
অরুণলেখা এবার আর ঠিক মনে করতে পারছেন না।
– হয়তো অর্থকষ্টে পড়েছিলেন৷ ওই সময় কারখানাগুলো তো লাটে উঠে গেছিল৷ ট্রেড ইউনিয়ন, অমুক তমুক৷ ভদ্রলোকের এক ছেলে দুর্গাপুরে অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছিল ওর পরে পরেই৷ ভদ্রলোক নাকি ডুকরে ডুকরে কেঁদেছিলেন এই বাড়ি অভিশপ্ত৷ যে থাকবে, তারই পুত্রশোক হবে৷ আমার দেওরকেও তো ওর কয়েকবছর আগে পুলিশ গুলি করে মেরেছিল রাতের অন্ধকারে৷

অরুণলেখা একটানা কথা বলে হাঁফাচ্ছেন একটু৷
– একটু জল খাবে দিদান?
– নাঃ, থাক৷ বাড়ি প্রোমোটিং হয়েছে জানলে কী করে মামণি?
প্রশ্নটা সীমন্তিনীর প্রতি৷
– বাঃ, আমরা গেছিলাম না? অরুণাভ যেবার কলকাতায় গেল৷ আমার সঙ্গে আলাপের পর আমরা তো একদিন দেখতে গিয়েছিলাম তোমাদের পুরনো জায়গা৷ তখনই দেখেছিলাম বোর্ড লাগানো আছে ওখানে৷ বাড়ি ভেঙে ফ্ল্যাট উঠবে৷ তোমার ছেলে ফিরে এসে বলেওছিল তোমাকে৷ ছবি তুলেছিল তোমাদের দেখাবার জন্য৷ তোমার মনে নেই?
অরুণলেখা একটু শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন।
– বলেছিল বাবাই? কি জানি, আজকাল আর কিছু মনে পড়ে না৷ শুধু আগের বাড়ি, সেই রাস্তাগুলো, সেই মানুষগুলোই চোখের সামনে ভাসে৷
– মাম্মা, তুমিও গেছ ওই বাড়িতে?
রোহিণীর বিস্ময় আর ধরছে না৷
– না রে, ওটাকে বাড়িতে যাওয়া বলে না৷ আমি তো বাইরে থেকে দেখেছি বন্ধ বাড়ি৷ ঠিক যেন অপেক্ষা করছে লোকেরা এসে ভেঙে ফেলবে সেই জন্য৷
সীমন্তিনী বলে। তারপর হঠাৎ আরও একটা তথ্য মনে পড়ে ওর৷
– ওহোঃ! আর একটা কথা মনে পড়ল মামণি৷ এটা কি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি কখনও? আচ্ছা, ওখানে এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল৷ আমাদের ওঁর বাড়িতে ডেকে খুব আদর যত্ন করেছিলেন৷ বলেছিলেন, তোমরা দিদি বলতে ওঁকে৷ কী যেন নামটা! দাঁড়াও, এতদিন পরে মনেও করতে পারছি না৷
সীমন্তিনী ভাবতে চেষ্টা করে৷
– অপাদি, না না পপাদি মনে হয়!
একটু অনিশ্চিতভাবে বলে সীমন্তিনী৷ অরুণলেখার মুখটা হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে৷
– কে! পপাদির সঙ্গে দেখা হয়েছিল তোমাদের বলনি তো?
একটু মৃদু বকুনি দেন অরুণলেখা৷ ত্রিশ বছর আগের একটা এনকাউন্টার এতদিন বাদে বলার সময় পেল মাম্মা! আর দিদানও এমন করে বলছে যেন পরশুই কারও সঙ্গে দেখা হওয়ার বিষয় বলতে ভুলে গেছে মাম্মা৷ গোটা জিনিসটাই সাররিয়াল৷ কান খাড়া করে শুনতে শুনতে এসব চিন্তাতরঙ্গ খেলা করে যায় রোহিণীর মাথায়৷ অরুণলেখা বলছেন,
– পপাদিকে চিনব না? বিয়ে হয়ে আসার পর ওর ছিল আমার সত্যিকারের বড় ননদের মতো৷ হাসি আর খুশি তো তার আগের থেকেই বন্ধু৷ পপাদি আমাকে নতুন বউ বলে অদ্ভুত একটা স্নেহের চোখে দেখত৷
– উনি তো বিয়ে করেননি, না? ভাইদের সংসারে থাকেন বলেছিলেন৷
– না না, বিয়ে হয়েছিল পপাদির৷ সে এক দুঃখের কাহিনি৷ অনেক দিনক্ষণ ঠিকুজি-কুষ্টি মিলিয়ে নাকি বারেন্দ্র পাল্টি ঘর দেখে বিয়ে দিয়েছিলেন ওর বাবা৷ স্বামীর ঘরে গিয়ে দেখে লোকটির বহু বছর ধরে একজন অন্য মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক আছে৷ একবস্ত্রে সেই যে ঘর ছেড়ে চলে এল আর ফিরে যায়নি৷ এসব আমি আমার শাশুড়ির কাছ থেকে শুনেছিলাম৷ মা বলতেন, ‘পপাটা বড় দুঃখী৷’ আমি বিয়ের পর থেকেই দেখেছি ও বাবা ভাইদের সংসারে রয়েছে৷ দাসীর মতো খাটত৷ কিন্তু ওর প্রাপ্য সম্মানটা পায়নি কোনওদিন৷ আমাকে একবার বলেছিল পপাদি দুঃখ করে… ‘বাবা মা উঠতে বসতে বলত– চলে এলি কেন জেদ করে? মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে পারতিস্৷ স্বামীর ঘরে লাথিঝাঁটা খাওয়াও অনেক বেশি সম্মানের৷ মেয়েদের এত জেদ ভালো নয়৷ একটু মানিয়ে নিতে হয়৷ তুই বল্ দেখি যেখানে দেখি ঘরটাই গোড়া থেকে ভাঙা, সেখানে মাটি কামড়ে থাকব কোন্ ভরসায়?’
রোহিণীর মনে হল প্রায় ষাট বছর আগের একটি মেয়েকে বর্ণনা করছেন অরুণলেখা৷ অথচ মনে হচ্ছে দিদান সদ্য ওই মহিলার সঙ্গে কথা বলেছে৷ ওই মহিলা দাদাইয়ের চেয়ে বড়৷ এখন তার মানে প্রায় নব্বই বছর বয়স হবে ওঁর৷ মাম্মার সঙ্গেও তো দেখা হয়েছে ত্রিশ বছর আগে৷ এখন কি বেঁচে আছেন উনি? এবার কলকাতায় গেলে একবার মহিলার খোঁজ করে দেখবে বলে ঠিক করল রোহিণী৷ বৃষ্টির তোড় একটু কমেছে৷ আবার সেকেন্ড দফায় চা খেতে ইচ্ছে করছে সীমন্তিনীর৷ এবার সীমন্তিনী উঠল চা করতে৷ রোহিণী পা দোলাতে দোলাতে গম্ভীরভাবে বলল,
– আমার জন্য একটু এনো তো মাম্মা৷ আর হ্যাঁ, তোমার স্টোরে কি কেক ফেক আছে বের কর৷
সীমন্তিনী ওর দিকে কটমট করে তাকিয়ে চা করতে গেল৷ ফিরেছে শুধু কেক নয়, আরও বেশ কয়েক রকম স্ন্যাক্স সাজিয়ে৷ কেউ খেতে চাইলে খুব আনন্দ হয় সীমন্তিনীর৷ এখন বাড়িতে সবার মাপা খাবার৷ অরুণলেখার তো বটেই৷ অরুণাভ চিরকালই স্বাস্থ্য সচেতন৷ রণো আর রোহিণী কবজি ডুবিয়ে ভাত মাছ মাংস খাওয়ায় বিশ্বাসী নয়৷ রণো মাঝে সম্পূর্ণ ভিগান ডায়েট ফলো করছিল৷ এখন সেই ফেজ়টা ওভার হয়েছে বলে সীমন্তিনী মনে মনে একটু নিশ্চিন্ত৷ রোহিণীও পারলে নিরামিষ খেতেই প্রেফার করে৷ ওদের প্রজন্মকে খাইয়ে সুখ নেই– সীমন্তিনী তা বুঝে গেছে৷
চা আর স্ন্যাক্স সাজিয়ে সীমন্তিনী ঘরে এসে দেখল অরুণলেখা আর রোহিণীর গল্প হিমালয় ভ্রমণের দিকে ঘুরে গেছে৷ রোহিণী চোখ বড় বড় করে শুনছে৷ অরুণলেখা বলছেন।
– তারপর সুন্দরানন্দজি এক এক করে ওঁর সব সংগ্রহ আমাদের দেখালেন৷ বাবাইয়ের তখন ছ’বছর বয়েস৷ আমরা ইংল্যান্ডে যাবার আগে একবার টুক করে বেরিয়ে পড়েছিলাম৷
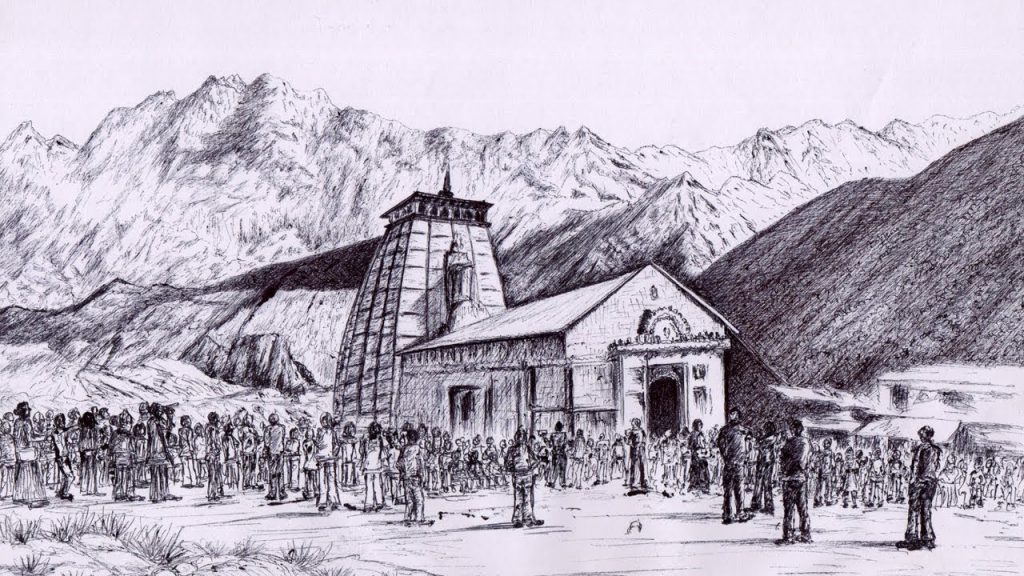
– টুক করে তোমরা কেদার বদ্রি গঙ্গোত্রী এসব চলে গেলে! যেন শপিং করতে মলে যাচ্ছ!
হাসি আর থামতে চাইছে না রোহিণীর৷ সীমন্তিনী ধমক দিচ্ছে…
– অত হাসির কী আছে? তখন ওরকম যেত৷ লোকের তখন স্ট্যামিনাও অনেক বেশি ছিল৷ আমার ঠাকুর্দা বার্মা থেকে অন্য অনেকের সঙ্গে হেঁটে হেঁটে কলকাতা ফিরেছিলেন৷ সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময়৷ জাপানিরা যখন বার্মা দখল করে নিল তারপর৷
অরুণলেখাও সায় দিলেন।
– এটা একদম ঠিক বলেছ মামণি৷ তখন লোকেরা অনেক কষ্ট করতে পারত৷ সেই আগের যুগে জলধর সেন কি দেবেন ঠাকুর ছেড়ে দাও, ওঁরা তো বিখ্যাত পরিব্রাজক। কিন্তু আমাদের বাঙালি ঘরের কত মহিলারাও মাইলের পর মাইল হাঁটতে কসুর করতেন না৷ তীর্থযাত্রা আর হিমালয়ের সৌন্দর্য দেখা– এক ঢিলে দুই পাখি মারা হয়ে যেত৷
– ঢিলটা হল হাঁটা?
রোহিণী ফোড়ন কাটে৷
– হ্যাঁ? কী বলছ দিদিভাই?
অরুণলেখা একটু থতমত খান৷ রোহিণী গল্পের দিকে ফেরে আবার৷
– না, কিছু না৷
– সবটাতে ফিচলেমি
সীমন্তিনী ঝঙ্কার দেয়৷
– আচ্ছা মামণি, তুমি ওই যে তোমার চেনা মহিলার কথা বলতে যিনি হিমালয়ে ঘুরতেন, আর বই লিখতেন সেসব নিয়ে?
– কে, রানিদি?
অরুণলেখা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন
– রানিদির মতো মানুষ দেখা যায় না চট করে৷ ওঁদের একটা দল ছিল৷ ভাসুর, জা, সবাইকার সঙ্গে একসঙ্গে মিলে ঘুরতেন৷ হিমালয়ে, এদিকে কুম্ভে, কত কত যে হাঁটতেন৷ প্রতিদিন উনিশ কুড়ি মাইল করে হেঁটে রাতে চটিতে বসে ডায়েরিতে লিখে ফেলতেন সেদিনের ভ্রমণবৃত্তান্ত৷ এনার্জি পেতেন কোথায় তাই ভাবি৷ পূর্ণকুম্ভ, হিমাদ্রি, ওসব বিখ্যাত বই ওই ডায়েরির মেটিরিয়াল থেকেই লেখা৷
– চটি কী?
– চটি হচ্ছে পান্থশালা৷ ইন্ বলতে পার৷ ভ্রমণে ক্লান্ত মানুষেরা রাতে ওই চটিতে যাহোক একটু খেয়ে মাথা গুঁজত৷ রাতটুকু কাটানো, তারপর আবার হাঁটা৷
– এখনও চটি আছে হিমালয়ে!
রোহিণীর জিজ্ঞাসার শেষ নেই৷
– এখন আছে কিনা বলতে পারব না৷ রানিদিরা যখন গেছেন পঞ্চাশের দশকে তখন হাঁটতেও হত বেশি৷ দুর্গম পাহাড়ি জায়গায় বাসের রাস্তা তৈরি হয়নি৷ থাকার জায়গাও ছিল না ওই চটিগুলো ছাড়া৷
– তোমরাও ওই চটিতে ছিলে?
– আমরা যখন গেছি তখন বিড়লাদের গেস্টহাউস তৈরি হয়ে গেছে৷ খুব একটা আরামদায়ক কিছু না, তবু চটির চেয়ে বেটার৷ পরিচ্ছন্ন মধ্যবিত্তের বেসিক থাকার জায়গা৷
– সেইবারই কি তোমার সঙ্গে তোমার দাদার দেখা হল?
সীমন্তিনীর মুখ ফসকে প্রশ্নটা বেরিয়ে গেছে৷ রোহিণী সঙ্গে সঙ্গে লুফে নিয়েছে৷
– দাদা মানে? সুমিত্র, যার নাম রবীন্দ্রনাথের দেওয়া?
অরুণলেখা একটু চুপ করে থাকলেন৷ তারপর বললেন,
– হ্যাঁ, সেই দাদাই বটে৷ যার কথা তোমাকে ইন্টারভিউতে বলেছিলাম৷
তারপর সীমন্তিনীকে বললেন,
– নাঃ, দাদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল আরও পরে৷ সে গল্প অন্য কোনওদিন বলব৷ বিলেত আসার আগে যেবার হিমালয়ে বেড়াতে গেলাম, তখন অবধি তো সব ঠিকই ছিল৷ বাবা মাও রয়েছেন তখন৷ পুরো ঘটনাটাই তো ঘটল অনেক পরে৷
কোন ঘটনার কথা বলছে দিদান! দাদার সঙ্গে দেখা হওয়ার ব্যাপারটাই বা কী? দিদানের দাদা কি তাহলে শান্তিনিকেতনে ছিলেন না? রোহিণীর মনে হঠাৎ অনেক প্রশ্ন গজগজ করছে৷ কে এই গল্পটা ঠিক বলতে পারবে? মাম্মাই বা কতটা জানে? দাদুর খাতাটায় কি দিদানের বাবা, মা, দাদার বিষয়ে কিছু লেখা আছে? আর একবার খুঁজে দেখা দরকার৷ আজ যেন হঠাৎ সুর কেটে গেছে৷ অরুণলেখা চোখ বুজে ফেলেছেন৷ দিদান কি ঘুমিয়ে পড়ল হঠাৎ? রোহিণী কী একটা বলতে গিয়েও কথা গিলে নিল৷ সীমন্তিনী ইশারায় ওকে বারণ করছে কথা বলতে৷ সত্যি আজকে অনেক কথা বলেছে দিদান৷ বাকি গল্পটা পরের জন্য থাক৷
*পরবর্তী পর্ব প্রকাশিত হবে ৭ সেপটেম্বর ২০২২
*ছবি সৌজন্য: Pinterest, Shiksha, Worthpoint
অপরাজিতা দাশগুপ্ত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক। আগে ইতিহাসের অধ্যাপনা করতেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট মেরিজ কলেজে ইতিহাস ও মানবীচর্চা বিভাগের ফুলব্রাইট ভিজিটিং অধ্যাপকও ছিলেন। প্রেসিডেন্সির ছাত্রী অপরাজিতার গবেষণা ও লেখালিখির বিষয় উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের গোড়ায় বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকের চিন্তাচেতনায় এবং বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নারী। অধ্যাপনা, গবেষণা, ও পেশা সামলে অপরাজিতা সোৎসাহে সাহিত্যচর্চাও করেন। তিনটি প্রকাশিত গ্রন্থ - সুরের স্মৃতি, স্মৃতির সুর, ইচ্ছের গাছ ও অন্যান্য, ছায়াপথ। নিয়মিত লেখালিখি করেন আনন্দবাজার-সহ নানা প্রথম সারির পত্রপত্রিকায়।


























5 Responses
বুধবারের প্রতীক্ষায় থাকি বাকি কদিন।এবারের ঘটনাগুলোর আংশিক যেন স্থান,কাল ভেদে অন্য ফ্রেমে আরো চেনা আমার কাছে তাই আরো বেশি ভালো লাগলো।
থ্যাংক ইউ!
eagerly waiting for Wednesday! each episode has been absolutely fascinating and amazing to see the 3 very different generations interacting. Aparajita ke onek onek abhinandan. And must add that the illustrations are fantastic. Love to get hold of some of the paintings …. are those paintings all by the same artist?
Thank you, thank you! This means a lot to me. I think the images are a combination of intelligently-selected stock images and art work. A lot of people seem to be liking them a lot.
Khub valo lagchhe.Anek kichhur sathe nijeke relate korte parchhi.