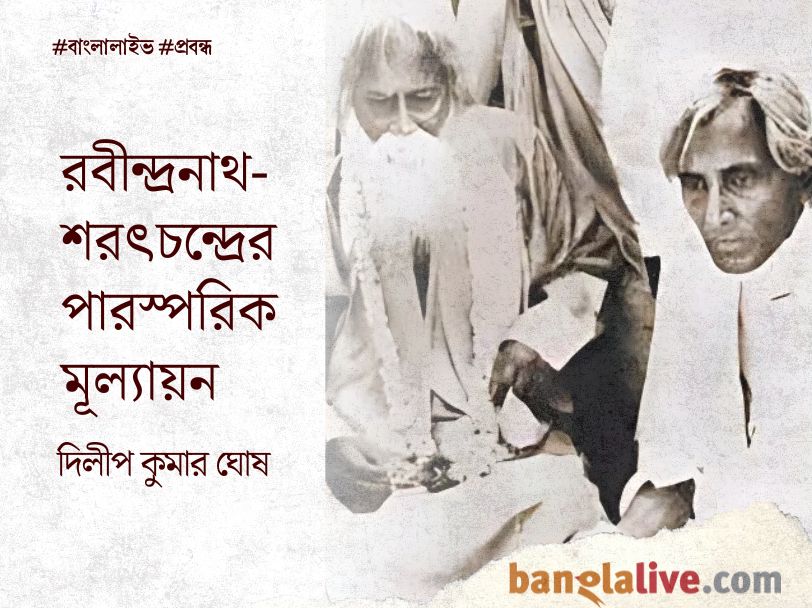(Rabindranath and Sarat Chandra)
“বস্তুত আমি আজ অতীতের প্রান্তে এসে উত্তীর্ণ— এখানকার প্রদোষান্ধাকার থেকে ক্ষীণ কর প্রসারিত করে তাঁকে আমার আশীর্ব্বাদ দিয়ে যাই, যিনি বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের উদয় শিখরে আপন প্রতিভাজ্যোতি বিকীর্ণ করচেন।” ২৯ ভাদ্র ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে লিখিত এই আশীর্বাণী— প্রমথ চৌধুরীর সভাপতিত্বে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে শরৎচন্দ্রের তিপান্নতম জন্মতিথি উপলক্ষে আয়োজিত ৩১ ভাদ্র ১৩৩৫-এর সংবর্ধনাসভায়— রবীন্দ্রনাথ প্রেরিত আশীর্বাদের শেষ বাক্য। (Rabindranath and Sarat Chandra)
বাল্যকালে ‘প্রকৃতির প্রতিশোধ’ নাট্য-কাব্যের পাঠ শুনে চোখের জলে ভেসে শরৎচন্দ্রের রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। রেঙ্গুনে থাকাকালীন ১৯০৫-এর আগে-পরে বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নতুন নতুন গানও শরৎচন্দ্র বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গাইতেন। শরৎচন্দ্রের লেখার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে ‘ভারতী’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘বড়দিদি’ গল্পের মাধ্যমে; গল্পকারের নাম ধারবাহিকের প্রথম দুটো কিস্তিতে প্রকাশিত না হওয়ায় অনেক সাহিত্যবোদ্ধা যে রচনাকে রবীন্দ্রনাথের বলে ভুল করেছিলেন। (Rabindranath and Sarat Chandra)
আরও পড়ুন: পারস্যে রবীন্দ্রনাথ, জন্মদিনে
১৩২০ সনের আষাঢ় মাসে ‘ভারতবর্ষ’-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যার কিছুটা অংশ সম্পাদনা করেই দ্বিজেন্দ্রলাল মৃত্যুমুখে পতিত হলে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি এবং হাইকোর্টের জজ সারদাচরণ মিত্রকে সম্পাদক করার ব্যাপারে আলোচনা শুরু হয়। শরৎচন্দ্র প্রমথনাথকে সপ্তাহখানেকের মধ্যে লেখা দুটো চিঠিতে পরিষ্কার জানান— “দ্বিজুবাবু আর নাই—আর আমিও অন্য সম্পাদকের কাছে নিজের লেখার যাচাই করিতে পারিব না। সেটা আমার পক্ষে অসাধ্য। অবশ্য রবিবাবু ছাড়া।” “দ্বিজুবাবুর মৃত্যুর পর রবিবাবু ছাড়া এত বড় কাগজ—এত বেশী আয়োজন, এত বেশী subscription—আর কেউ চালাতে পারবে না।” (Rabindranath and Sarat Chandra)
মাতুল ও বাল্যবন্ধু উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে সাহিত্যালোচনা প্রসঙ্গে রেঙ্গুন থেকে এই সময়েই লিখছেন, “…আমার চেয়ে ভাল সমজদার এখনকার কালে এক রবিবাবু ছাড়া আর কেউ নেই।” (Rabindranath and Sarat Chandra)
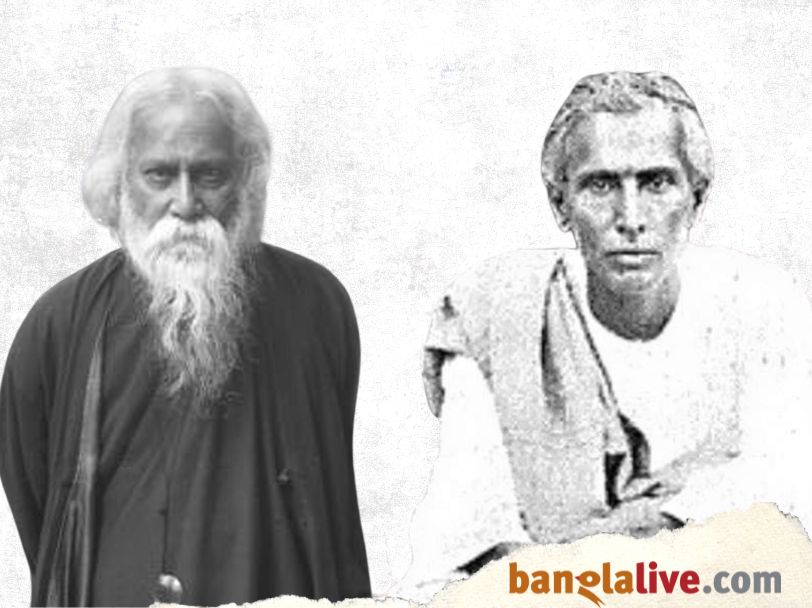
তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থের প্রকাশক ‘গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স’-এর এবং ‘ভারতবর্ষ’-এর অন্যতম স্বত্বাধিকারী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে ভারতবর্ষে ধারাবাহিকভাবে ছদ্মনামে প্রকাশিত ‘শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী’ নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে ১৯১৫ সালের শেষের দিকে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকেই চিঠিতে লিখেছেন, “রবিবাবু নিজের আত্মকাহিনী লিখিয়াছেন, কিন্তু নিজেকে কেমন করিয়াই না সকলের পিছনে ফেলিবার সফল চেষ্টা করিয়াছেন।” (Rabindranath and Sarat Chandra)
১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে কলকাতায় স্থায়ীভাবে ফিরে আসার পর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয় এবং কংগ্রেসের কাজে ও সাহিত্যসেবায় সেই অন্তরঙ্গতা বৃদ্ধি পায়। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে ‘নারায়ণ’ পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল চিত্তরঞ্জন দাশের সম্পাদনায়। ১৯১৫-য় তৎকালীন ভারতসম্রাটের জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথকে নাইট উপাধি প্রদান করা হয়। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ সেই উপাধি বর্জন করেন। ১৯-এর ১৬ অগস্ট অমল হোমকে লিখিত পত্রে শরৎচন্দ্র লিখছেন— “দেশের বেদনার মধ্যে আমরা যেন নতুন করে পেলাম রবিবাবুকে। এবার একা তিনিই আমাদের মুখ রেখেছেন। ‘নারায়ণে’র সময় সি. আর. দাশ একদিন আমাকে বলেছিলেন যে, রবিবাবু যখন নাইটহুড নেন, তখন না কি দাশ সাহেব কেঁদেছিলেন। এখন একবার তাঁর দেখা পেলে জিজ্ঞাসা করতাম, আজ আমাদের বুক দশ হাত কি না বলুন।” (Rabindranath and Sarat Chandra)
“বিশ্বভারতীর সাহায্যকল্পে ১৩৩০ সনে রবীন্দ্রনাথের ‘বিসর্জন’ নাটক কলকাতায় এম্পায়ার থিয়েটারে অভিনীত হচ্ছিল, যে অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং জয়সিংহের ভূমিকায় নেমেছিলেন।”
প্রমথ চৌধুরীর কাছে টেলিফোনে রবীন্দ্রনাথের বোলপুরে থাকার সংবাদ জেনে ২৯ পৌষ ১৩২৮ (১৯২২ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে) শরৎচন্দ্র বাজে শিবপুর থেকে চিঠিতে তাঁকে লেখেন— “আমাদের পাড়ায় একটি ছোটখাটো সাহিত্য সভা আছে। দু’একমাস অন্তর কাহারো বাটীতে তাহার অধিবেশন হয়।… কয়েকদিন হইতে আমরা ক্রমাগত তর্কাতর্কি করিয়াও মীমাংসা করিতে পারিতেছি না এ সভায় আপনার পায়ের ধুলা পড়ার কিছু মাত্র সম্ভাবনা আছে কী না। এবার যখন বাড়ি আসিবেন, যদি অনুমতি দেন, আমরা গিয়া আপনার কাছে আবেদন করি।” (Rabindranath and Sarat Chandra)
১৭ মে ১৯২৩ শ্রীমতী লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে পাঠানো চিঠির একজায়গায় শরৎচন্দ্র লিখছেন— “হুগলী জেলে আমাদের কবি কাজী নজরুল উপুস করিয়া মর-মর হইয়াছে। বেলা ১টার গাড়ীতে যাইতেছি, দেখি যদি দেখা করিতে দেয় ও দিলে আমার অনুরোধে যদি সে আবার খাইতে রাজী হয়। না হইলে আর কোন আশা দেখিনা। একজন সত্যকার কবি। রবিবাবু ছাড়া আর বোধহয় এখন কেহ আর এতবড় কবি নাই।” (Rabindranath and Sarat Chandra)
বিশ্বভারতীর সাহায্যকল্পে ১৩৩০ সনে রবীন্দ্রনাথের ‘বিসর্জন’ নাটক কলকাতায় এম্পায়ার থিয়েটারে অভিনীত হচ্ছিল, যে অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং জয়সিংহের ভূমিকায় নেমেছিলেন। ১২ ভাদ্র ‘৩০ অমল হোমকে শরৎচন্দ্র চিঠিতে লেখেন— “আমাকে বিসর্জ্জনটা দেখাও।… রবিবাবুর অভিনয় দেখিনি কখনো। সুরেশ সমাজপতির কাছে তাঁর গল্প শুনেছিলাম একবার।… একবার যদি তাঁর মুখে সঙ্গীত -সমাজে রবিবাবুর বিসর্জ্জন অভিনয়ের গল্পটা শুনতে! অতএব ও বস্তু না দেখে মরছি না। তুমি এই চিঠি পেয়েই খবর নেবে আবার কবে হচ্ছে, আর দু’খানা দশ টাকার টিকিট কিনবে।” (Rabindranath and Sarat Chandra)
৩০ বৈশাখ ১৩৩৮ দিলীপকুমার রায়কে শরৎচন্দ্র চিঠিতে লিখেছেন, “আমার বয়েস হয়ে গেছে, রবীন্দ্রনাথেরও বয়েস হোলো, এখন মাঝে মাঝে আশঙ্কা হয় এর পরে বাঙ্গলার উপন্যাস-সাহিত্যের স্থানটা হয়ত একটু নেমে আসবে।”
অমল হোমের বিয়েতে থাকতে পেরে ভারী খুশি শরৎচন্দ্র তাঁকে ৩০ ডিসেম্বর ১৯২৭ (পৌষ ১৩৩৪)-এ চিঠি লেখেন। সেই চিঠির শেষাংশে লেখেন— “অনেক দিন পর সেদিন বিবাহ-সভায় রবীন্দ্রনাথকে দেখলাম। কী আশ্চর্য্য সুন্দর,— চোখ ফেরানো যায় না। বয়স যত বাড়ছে, রূপ যেন তত ফেটে পড়ছে। না, রূপ নয়— সৌন্দর্য্য! জগতে এত বড় বিস্ময় জানি না।” (Rabindranath and Sarat Chandra)
৩০ বৈশাখ ১৩৩৮ দিলীপকুমার রায়কে শরৎচন্দ্র চিঠিতে লিখেছেন, “আমার বয়েস হয়ে গেছে, রবীন্দ্রনাথেরও বয়েস হোলো, এখন মাঝে মাঝে আশঙ্কা হয় এর পরে বাঙ্গলার উপন্যাস-সাহিত্যের স্থানটা হয়ত একটু নেমে আসবে।” (Rabindranath and Sarat Chandra)
রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে শরৎচন্দ্র ৮ অগ্রহায়ণ ‘৩৮ অভিনন্দনপত্রে লেখেন, “কবিগুরু, তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই। তোমার সপ্ততিতম বর্ষশেষে একান্তমনে প্রার্থনা করি জীবন-বিধাতা তোমাকে শতায়ু দান করুন। আজিকার এই জয়ন্তী উৎসবের স্মৃতি জাতির জীবনে অক্ষয় হৌক।” ৯ পৌষ ‘৩৮ অপরাহ্ণে টাউন হলে রবীন্দ্র-জয়ন্তী-উৎসব উপলক্ষে সাহিত্য-সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন শরৎচন্দ্র। ১১ পৌষ টাউন হলে কবিগুরুর সংবর্ধনা সভায়, রবীন্দ্র-জয়ন্তী-উৎসব-পরিষদের সভাপতি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু অসুস্থ থাকায়, পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি কবি কামিনী রায় শরৎচন্দ্র-রচিত অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন। (Rabindranath and Sarat Chandra)
২৮ পৌষ, ১৩৩৮ অমল হোমকে শরৎচন্দ্র চিঠিতে লিখেছেন— “সত্যি অমল, আমি যে কতখানি খুশি হয়ে এসেছি। সে তোমরা (না তুমি?) টাউন হলে সভাপতির আসনে আমাকে টেনে বসালে, আমার গলায় মালা দি’লে বলে নয়,— আমার লেখা মানপত্র কবির হাতে দিলে ব’লেও নয়— যেভাবে এই বিরাট ব্যাপারটি সম্পন্ন হল, এ অনুষ্ঠানটিকে যে নিষ্ঠায়, শ্রমে ও শ্রদ্ধায় সার্থক ক’রে তুললে, তাতেই আমার আনন্দ, অকপট আনন্দ। (Rabindranath and Sarat Chandra)
কবির সম্বন্ধে আমি এখানে ওখানে কখনো কখনো মন্দ কথা বলেছি রাগের মাথায়, এ যেমন সত্যি— এও তেমনি সত্যি যে, আমার চাইতে তাঁর বড় ভক্ত কেউ নেই,— আমার চাইতে কেউ বেশী মানে নি গুরু ব’লে,— আমার চাইতে কেউ বেশি মকসো করে নি তাঁর লেখা। তাঁর কবিতার কথা বলতে পারবো না, কিন্তু আমার চাইতে বেশীবার কেউ পড়েনি তাঁর উপন্যাস,— তাঁর চোখের বালি, তাঁর গোরা, তাঁর গল্পগুচ্ছ। আজকের দিনে যে এত লোক আমার লেখা প’ড়ে ভাল বলে, সে তাঁরি জন্য। এ সত্য, পরম সত্য আমি জানি। আর কেউ বললে কি না-বললে, মানলে কি না-মানলে তাতে কিছু এসে যায় না। তাই আমি আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে যোগ দিয়েছি এই জয়ন্তীতে, না দিয়ে পারি নি।” (Rabindranath and Sarat Chandra)
১০ মাঘ ‘৩৮ তাঁকেই কৌতূহলী হয়ে আবার লেখেন, “আচ্ছা, শান্তিনিকেতনে কবির আড্ডাটা কেমনতরো হয় বলো দিকি। কিন্তু সে আড্ডায় হয়তো তিনিই শুধু কইবেন কথা— অন্যে রবে নিরুত্তর। মনোপলিতে আড্ডা জমে না–শুধু সলিলোকিতে যেমন জমে না নাটক।” (Rabindranath and Sarat Chandra)
২৯ আশ্বিন ১৩৩৯ রবীন্দ্রনাথের ‘পুনশ্চ’ কাব্যগ্রন্থের অন্তঃপুরের ‘সাধারণ মেয়ে’, ‘সাহিত্যসম্রাট’ শরৎবাবুর ‘বাসি ফুলের মালা’ গল্পের বই পড়ে তাঁকেই অনুরোধ করেছেন ‘নিতান্তই সাধারণ মেয়ের গল্প’ লেখার জন্য। (Rabindranath and Sarat Chandra)
১৩৪২ বঙ্গাব্দে দিলীপকুমারকে শরৎচন্দ্র লিখছেন, “বুদ্ধদেব বসু যদি ব’লে থাকেন আমার চেয়ে রবীন্দ্রনাথ ঢের বড় ঔপন্যাসিক সে তো সত্যি কথাই বলেছে মন্টু। নিজের মন তো জানে এ সত্য,—পরম সত্য।”
৩১ ভাদ্র ‘৩৯ শরৎচন্দ্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে কলকাতার টাউন হলে সংবর্ধনা সভা আয়োজিত হবে বলে স্থির হয়। শরৎচন্দ্রের এই ৫৭তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নামে চিঠি এবং আশীর্বাণী একটা খামে জয়ন্তী-উৎসবের অন্যতম উদ্যোক্তা নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের ঠিকানায় রেজিস্ট্রি করে পাঠান। চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানান, “সম্প্রতি সাংসারিক বিশেষ দুর্য্যোগ না থাকলে আমি নিশ্চয়ই তোমার অভিনন্দন সভায় যোগ দিতুম, এমন কি শারীরিক অস্বাস্থ্য ও দুর্ব্বলতাও বাধা ঘটাত না।” আশীর্বাণীতে লেখেন, “তোমার জন্মদিন উপলক্ষ্যে “কালের যাত্রা” নামক একটি নাটিকা তোমার নামে উৎসর্গ করেছি। আশা করি আমার এ দান তোমার অযোগ্য হয় নি।… কালের রথযাত্রায় বাধা দূর করবার মহামন্ত্র তোমার প্রবল লেখনীর মুখে সার্থক হোক এই আশীর্ব্বাদ সহ তোমার দীর্ঘজীবন কামনা করি।” (Rabindranath and Sarat Chandra)
শরৎচন্দ্রের এই সংবর্ধনা সভা অবশ্য টাউন হলে অনুষ্ঠিত হতে পারেনি রাজনৈতিক দলাদলি এবং কয়েকজন সাহিত্যিকের উপদ্রবের ফলে। শরৎচন্দ্র টাউন হলের প্রবেশ পথ থেকে ফিরে যেতে বাধ্য হন। শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে ২৯ আশ্বিন ‘৩৯ চিঠিতে লেখেন, “আমার ভাগ্য ভালো যে ৩১শে ভাদ্র আপনার কলিকাতায় আসা সম্ভবপর হয় নাই—আসিলে সেদিনের অনাচার দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইতেন। আর সবচেয়ে পরিতাপ এই যে আমার প্রায় সমবয়সী সাহিত্যিকেরাই এই উপদ্রবের সূত্রপাত করিয়াছিল।” চিঠিতে অবশ্য তিনি এ কথা লিখতে ভোলেননি, “কালের যাত্রার সঙ্গে যে আশীর্ব্বাদ আপনার পাইলাম সে আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। আপনার তুচ্ছতম দানও যে-কোন সাহিত্যিকের সম্পদ, আমি এ দান মাথায় করিয়া লইলাম।’ (Rabindranath and Sarat Chandra)
১৩৪২ বঙ্গাব্দে দিলীপকুমারকে শরৎচন্দ্র লিখছেন, “বুদ্ধদেব বসু যদি ব’লে থাকেন আমার চেয়ে রবীন্দ্রনাথ ঢের বড় ঔপন্যাসিক সে তো সত্যি কথাই বলেছে মন্টু। নিজের মন তো জানে এ সত্য,—পরম সত্য।… রবীন্দ্রনাথ যদি বলতেন আমার কোন বই-ই উপন্যাস-পদ-বাচ্য নয়, তাতেও বোধ করি একটা সাময়িক বেদনা ছাড়া আর কিছুই মনে হতো না।” (Rabindranath and Sarat Chandra)
“১২ মাঘ ১৩৪৪ শরৎচন্দ্রের শ্রাদ্ধবাসরে শান্তিনিকেতন থেকে প্রেরিত ‘শরৎচন্দ্র’ শিরোনামাঙ্কিত লিপিতে কবি বিবৃত করলেন— যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে,/ ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।/ দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি’/ দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে ধরি’।”
৭ অক্টোবর ১৯৩৬ রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে শরৎচন্দ্রকে চিঠিতে জানালেন, “আগামী রবিবারে তোমার প্রৌঢ়বয়সের প্রারম্ভকে অভিনন্দিত করব বলে সঙ্কল্প করেছি।… আমি কাল অপরাহ্ণে কলকাতায় পৌঁছব। সেখানে যদি তোমার কাছ থেকে সম্মতি পাই তাহলে কথাটা পাকা হতে পারবে।” (Rabindranath and Sarat Chandra)
বেলেঘাটার ‘প্রফুল্ল-কানন’-এ রবিবাসরের বার্ষিক উদ্যান-সম্মিলনে শরৎচন্দ্রের ৬০ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় রবিবাসরের অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ তাঁর পঠিত আশীর্বাণীতে বলেন, “তুমি জীবনের নির্দিষ্ট পথের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ উত্তীর্ণ হয়েছ। এই উপলক্ষ্যে তোমাকে অভিনন্দিত করবার জন্যে তোমার বন্ধুবর্গের এই আমন্ত্রণসভা।… আজ শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনে বিশেষ গর্ব্ব অনুভব করতে পারতুম যদি তাঁকে বলতে পারতুম তিনি একান্ত আমারি আবিষ্কার। কিন্তু তিনি কারো স্বাক্ষরিত অভিজ্ঞানপত্রের জন্যে অপেক্ষা করেন নি।… তিনি বাঙালির বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিয়েছেন। (Rabindranath and Sarat Chandra)
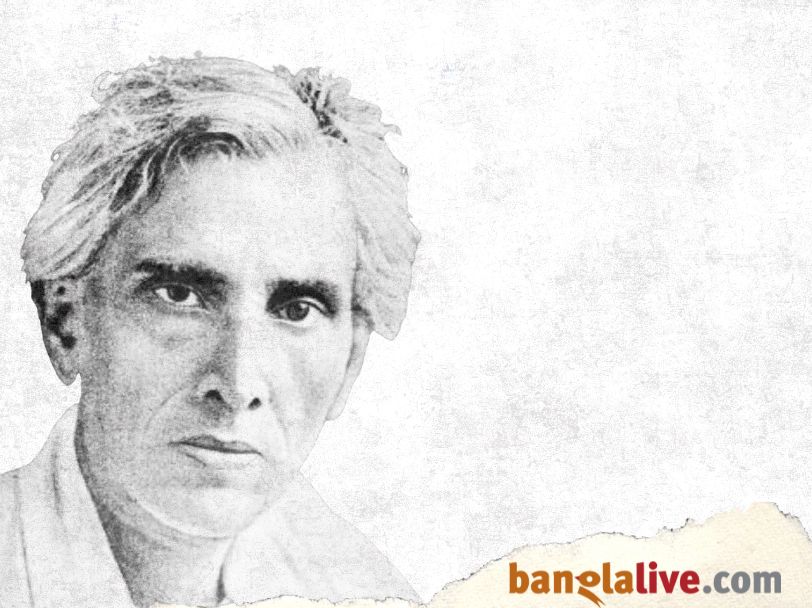
সাহিত্যে উপদেষ্টার চেয়ে স্রষ্টার আসন অনেক উঁচুতে, চিন্তাশক্তির বিতর্ক নয় কল্পনাশক্তির পূর্ণ দৃষ্টিই সাহিত্যে শাশ্বত মর্যাদা পেয়ে থাকে। কবির আসন থেকে আমি বিশেষভাবে সেই স্রষ্টা সেই দ্রষ্টা শরৎচন্দ্রকে মাল্যদান করি। তিনি শতায়ু হয়ে বাংলাসাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করুন,…” (Rabindranath and Sarat Chandra)
শরৎচন্দ্র ১২ কার্তিক ‘৪৩ উমাপ্রসাদকে চিঠিতে জানিয়েছেন, “আমার একষট্টি বছরের প্রারম্ভকে কবি আশীর্ব্বাদ করেছেন। অকৃপণ ভাষায়, মন খুলে মঙ্গল কামনা করেছেন।” (Rabindranath and Sarat Chandra)
আরও পড়ুন: বর্ষামঙ্গল ও রবীন্দ্রনাথ
১৯৩৮-এর জানুয়ারিতে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সময় শরৎচন্দ্রকে চিঠি লিখে উদ্বিগ্ন রবীন্দ্রনাথ জানালেন, “তোমার আরোগ্য লাভের প্রত্যাশায় বাংলাদেশ উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকবে।” ১৬ জানুয়ারি কথাশিল্পীর জীবনাবসানে সেই প্রত্যাশার করুণ পরিণতি লক্ষ করে ব্যথিত শোকাভিভূত কবি ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধিকে বললেন, “যিনি বাঙ্গালীর জীবনের আনন্দ ও বেদনাকে একান্ত সহানুভূতির দ্বারা চিত্রিত করেছেন, আধুনিক কালের সেই প্রিয়তম লেখকের মহাপ্রয়াণে দেশবাসীর সঙ্গে আমি গভীর মর্মবেদনা অনুভব করছি।” (Rabindranath and Sarat Chandra)
১২ মাঘ ১৩৪৪ শরৎচন্দ্রের শ্রাদ্ধবাসরে শান্তিনিকেতন থেকে প্রেরিত ‘শরৎচন্দ্র’ শিরোনামাঙ্কিত লিপিতে কবি বিবৃত করলেন— যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে,/ ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।/ দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি’/ দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে ধরি’। (Rabindranath and Sarat Chandra)
মুদ্রিত ও ডিজিটাল মাধ্যমে সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
পেশায় শিক্ষক দিলীপকুমার ঘোষের জন্ম হাওড়ার ডোমজুড় ব্লকের দফরপুর গ্রামে। নরসিংহ দত্ত কলেজের স্নাতক, রবীন্দ্রভারতী থেকে বাংলা সাহিত্যে স্নাতকোত্তর। নেশা ক্রিকেট, সিনেমা, ক্যুইজ, রাজনীতি। নিমগ্ন পাঠক, সাহিত্যচর্চায় নিয়োজিত সৈনিক। কয়েকটি ছোটবড় পত্রিকা এবং ওয়েবজিনে অণুগল্প, ছোটগল্প এবং রম্যরচনা প্রকাশিত হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে 'সুখপাঠ' এবং 'উদ্ভাস' পত্রিকায় রম্যরচনা এবং দ্বিভাষীয় আন্তর্জালিক 'থার্ড লেন'-এ ছোটগল্প প্রকাশ পেয়েছে।