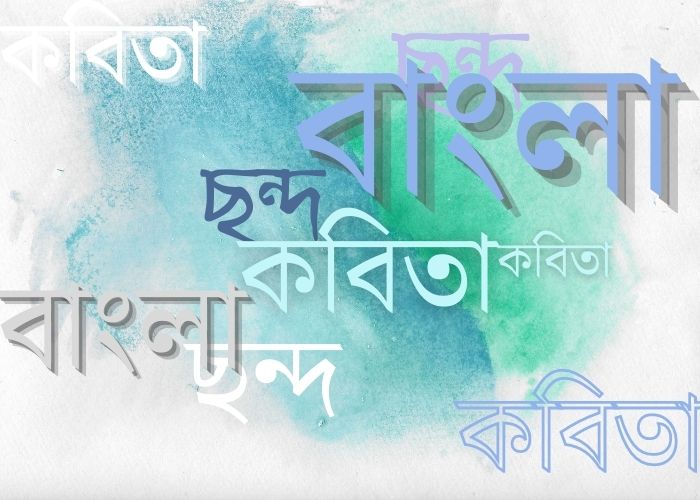অতিছন্দ : পিঙ্গলের ছন্দসূত্র–অনুযায়ী অক্ষর ধরে–ধরে ছন্দের প্রকারভেদ করা হয়েছে। সে–হিসাবে ছন্দ, অতিছন্দ, বিচ্ছন্দ‒ তিনটি শ্রেণি। প্রতি শ্রেণিতেই সাতটি করে মোট ২১টি ছন্দ। ‘ছন্দ’ শ্রেণিতে ২৪ থেকে ৪৮ অক্ষরের ছন্দ স্থান পেয়েছে। অতিছন্দে ৫২ থেকে ৭৬ অক্ষর। বিচ্ছন্দে ৮০ থেকে ১০৪ অক্ষর। তালিকা (পাশে অক্ষরসংখ্যা):
ছন্দ
১। গায়ত্রী–২৪
২। উষ্ণিক–২৮
৩। অনুষ্টুপ–৩২
৪। বৃহতী–৩৬
৫। পঙ্ক্তি–৪০
৬। ত্রিষ্টুপ–৪৪
৭। জগতী–৪৮
অতিছন্দ
অতিজগতী–৫২
শক্করী–৫৬
অতিশকূরী–৬০
অষ্টি–৬৪
অত্যষ্টি–৬৮
ধৃতি–৭২
অতিধৃতি–৭৬
বিচ্ছন্দ
কৃতি–৮০
প্রকৃতি–৮৪
আকৃতি–৮৮
বিকৃতি–৯২
সঙ্কৃতি–৯৬
অভিকৃতি–১০০
উৎকৃতি–১০৪
[গায়ত্রী, অনুষ্টুপ‒ এধরনের প্রধান কিছু ছন্দ ছাড়া পৃথক করে অন্যগুলির আলোচনা থাকবে না। ‘ছন্দ’ শ্রেণিভুক্ত সাতটি ছন্দের আবার অক্ষরসংখ্যা হিসাবে আট ভেদ এবং অবশেষে ওই সাত ছন্দের একটি করে অক্ষর ক্রমশ বাড়ার ক্রম–অনুযায়ী আরও পাঁচ ভেদ। ‘বৈদিক ছন্দ’ দেখুন।]
অতিজগতী: অতিছন্দের অন্যতম ছন্দ। ছন্দ ও বিচ্ছন্দের মতোই অতিছন্দ সাত প্রকার। পিঙ্গলের তালিকা অনুযায়ী এই ছন্দে থাকে ৫২টি অক্ষর। অর্থাৎ, প্রতি চরণ এতে ১৩–অক্ষরের (যেহেতু, ‘ছন্দোমঞ্জরী’ অনুযায়ী, চারটি পদ বা চরণ মিলে পদ্য হয়)
অতিপর্ব: ইংরেজিতে anacrusis; ছন্দে–লেখা কোনো পঙ্ক্তির প্রথমেই দু–মাত্রার একটি শব্দ যোগ করে কবিতাটিকে অনেকসময় চিত্তাকর্ষক করে তোলা হয়, অর্থবহ করে তোলা হয়। এই দু–মাত্রা সাধারণত একটু ফাঁকা জায়গা রেখে লেখা হয়, মূল পঙ্ক্তির ছন্দবিন্যাসে এটির কোনো প্রভাব থাকে না। আর, এই দু–মাত্রায় প্রস্বরও থাকে না। মূল পঙ্ক্তির গোড়ায় প্রস্বর থাকে। ধ্বনিতরঙ্গ এতে করে নিম্নগামী থেকে ঊর্ধগামী হয়। উদাহরণ:
ঘোর ঈশানে সঘনে গরজায়
ওই প্রলয়পাগল অশনি;
ভাঙা কুঞ্জবনের দরজায়
নাচে রুদ্রাণী দিগ্বসনী; (আরও দেখুন: ‘আভ্যন্তর অতিপর্ব’)
অতিশক্করী: অতিছন্দের অন্যতম। ৬০টি অক্ষর। অর্থাৎ, অপভ্রংশের এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৫–অক্ষর। অষ্টম ও পঞ্চদশ মাত্রার পর যতিপাত হয়। বাংলা–কবিতার বহু ছন্দ অপভ্রংশের ছন্দ থেকেই গড়ে উঠেছে। এই ছন্দটিও বাংলায় ‘মালতি’ নামে পরিচিত। বিদ্যাপতির কাব্যে অতিশক্করীর উদাহরণ:
হাথক দরপন মাথক ফুল
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল।
বাংলায় ‘মালতি’:
প্রখর রবির তাপ শিরে সহ্য হয় হে।
তার তাপে বালি তাপে পদে সহ্য নয় হে।।
অতিশয়োক্তি: সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকার। ইংরেজিতে ‘হাইপারবোল’(hyperbole) বা এগজ্যাজারেশন (exaggeration)। এতে উপমানই প্রবল, উপমেয়কে তা আত্মসাৎ করে নিজেই হয়ে ওঠে উপমেয়। এবং তা এত অধিক পরিমাণে ঘটে যে উপমেয় অদরকারি হয়ে পড়ে। উপমেয়ের বিধেয় অংশ থেকে উপমার ব্যাপারটি বুঝে নিতে হয়। এতে উপমেয় ও উপমানের মধ্যে সাদৃশ্যের বেলায় দেখা যায়, কবির কল্পনা একটা অন্য ব্যঞ্জনা ধারণ করছে:
বক্ষের নিচোল বাস যায় গড়াগড়ি
ত্যজিয়া যুগল স্বর্গ কঠিন পাষাণে।
‘যুগল স্বর্গ’ উপমান। উপমেয় ‘স্তনযুগল’ উল্লিখিতই হল না।
অতিশয়োক্তির পাঁচটি রূপ: ১। ভেদে অভেদ ২। অভেদে ভেদ ৩। সম্বন্ধে অসম্বন্ধ ৪। অসম্বন্ধে সম্বন্ধ ৫। কার্যকারণের ক্রমনাশ। শেষেরটিকে পৌর্বাপর্বনাশও বলা হয়। শেষেরটিতে, এবং সম্বন্ধে অসম্বন্ধ ও অসম্বন্ধে সম্বন্ধ‒ এই তিনটিতে উক্তির বেশ বাড়াবাড়ি লক্ষ করা যায়:
আমি নইলে মিথ্যা হত সন্ধ্যা তারা ওঠা
মিথ্যা হত কাননে ফুল ফোটা।।
আচার্য্য দণ্ডী, আনন্দবর্ধন, অভিনবগুপ্ত প্রমুখ পণ্ডিত অতিশয়োক্তিকেই শ্রেষ্ঠ অলংকার হিসাবে গণ্য করেছেন।
অতিসজ্জিত: অতিকল্পিতও বলা হয়। ইংরেজি ‘ব্যারোক’ শব্দের বাংলা পরিভাষা। Baroque শব্দটি পর্তুগিজে barroco স্প্যানিশে barrueco‒ আভিধানিক অর্থ, খসখসে অমসৃণ মুক্তো। কলা–সমালোচক ও ঐতিহাসিকেরা শব্দটি গোড়ার দিকে ব্যবহার করতেন স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলার বিশেষ একটি রীতি বা শৈলীর ক্ষেত্রে। ওই রীতি ষোলো শতকের শেষদিক থেকে সতেরো শতক জুড়ে ইতালিতে প্রচলিত হয়, পরে জার্মানি ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে। শব্দটি প্রথমদিকে নিন্দাসূচক ছিল, পরে বর্ণনাত্মক বিশেষণ হিসাবে অন্যান্য শিল্পমাধ্যম যেমন সংগীত, সাহিত্য ইত্যাদির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে থাকে।
সাধারণভাবে এ–রীতিতে রেনেসাঁর ধ্রুপদি আঙ্গিককে কাজে লাগিয়ে সেটিকে ভেঙে অতিনাটকীয়, জমকালো, সাড়ম্বর, অদ্ভুত ও আতিশয্য়পূর্ণ একধরনের শৈলী তৈরি করা হয়। কাব্যের ক্ষেত্রে বাগাড়ম্বরপূর্ণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আঙ্গিক সচেতনতাকে এই বিশেষণে অভিহিত করা হয়। মিলটনের ‘প্যারাডাইস লস্ট’-এর বেশ কিছু অংশ এই পর্যায়ে পড়ে। তবে, সবচেয়ে ভাল উদাহরণ জামবাতিস্তা মারিনো (Giambattista Marino: 1569-1625) রচিত কাব্য ‘অ্যাদ্যোন’ (Adone: 1623)। ভিনাস ও অ্যাডোনিসের প্রেম নিয়ে লেখা এই ইতালীয় কবির এ–কাব্যের শৈলী থেকে একটা শব্দই তৈরি হয়ে গেছে ‘মারিনিজ্ম’ (marinismo); তাঁর অতি অলংকৃত শৈলীটি সে সময় এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে তাঁর বহু অনুকরণকারী তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তাঁদের বলা হত marinist। স্পেনীয় কবি লুইস দে গংগোরা (Luis de Gongora:1561-1627) আর–এক সার্থক উদাহরণ, এঁরও নাম থেকে একই কারণে ‘গংগোরিজম’ শব্দের উদ্ভব। ইতালির ‘মারিনিজম’-এর সমার্থক শব্দ ইংল্যান্ডে ছিল ‘ইউফুইজ্ম’ (Euphuism)। এই নামটি তৈরি হয়েছে ইংরেজ নাট্যকার–ঔপন্যাসিক জন লিলি–র (John LyLy: 1554–1606) গদ্য–রোমান্স ‘Euphues:The Anatomy of Wit’ (1578) থেকে। ওতেও বাক্যালংকার, অনুপ্রাস ইত্যাদির অতিরিক্ত আড়ম্বর। ইংরেজি কাব্যে জন ডানের অধিবিদ্যক কবিতাগুলি ছাড়াও রিচার্ড ক্র্যাশর কবিতা (Richard Crashaw: 1612–1649) ব্যারোক–কাব্যের উজ্জ্বল উদাহরণ।
বাংলায় মধুসূদন দত্তের ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ ব্যারোক অর্থে অতিসজ্জিত শৈলীর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।
অতীন্দ্রিয়বাদ: ইংরেজিতে mysticism; এ–ধারার কবিদের বলা হয় mystic poet, বাংলায় বলা যায় মরমিয়া কবি। যে কাব্য নিগূঢ় অর্থবহ, আধ্যাত্মিক সংকেতবহ, দ্যোতনাময়, প্রতীকী বা রূপকাত্মক, গুহ্য, রহস্যময় তাই অতীন্দ্রিয় কাব্য।
এটি কোনো কাব্য আন্দোলন বা মতবাদ নয়, এ–হল একটা বোধ। কবি যখন বাস্তব জগতের অন্তরালে যে শাশ্বত সত্য, তা উপলব্ধি করেন এবং সেই ধারণাটি তাঁর কাব্যে ফুটে ওঠে অস্পষ্ট ও রহস্যময় ভাষায়, তখনই সে–কাব্য হয়ে ওঠে মিস্টিক। যা–কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে যার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয় না, একধরণের অজ্ঞাত কারণ কবিকে যখন এই মহাবিশ্ব, এই জীবনচক্র ইত্যাদি সম্পর্কে রহস্যময়তায় আচ্ছন্ন করে, কবি তা থেকে অর্জন করেন গভীর এক চেতনা। সেটিই অতীন্দ্রিয় চেতনা।
রোমান্টিসিজ্ম থেকেই মিস্টিসিজ্ম–এর উৎপত্তি। ড: শশীভূষণ দাশগুপ্তের মতে, “কাব্যের রোমান্টিক ধর্ম এবং মিস্টিক ধর্ম কিন্তু কোথাও পস্পরবিরোধী নহে।… রোমান্টিক মনই রহস্যের অতলে আরও একটু ডুবিয়া মিস্টিক হইয়া ওঠে”। অতীন্দ্রিয়বাদী চেতনার সার্থক উদাহরণ মেলে বাউল গানে, সহজিয়া গানে, সুফিদের গানে, পদাবলিতে।
বাংলা কাব্যে বিশুদ্ধ গীতিকাব্যের নব্যধারার পথকৃৎ বিহারীলাল ছিলেন প্রকৃতই অতীন্দ্রিয়বোধের সমৃদ্ধ কবি:
উদার অনন্ত নীল হে ধাবন্ত অম্বুরাশি!
আনন্দে উন্মত্ত হ’য়ে কোথায় ধেয়েছ ভাই!
মহান তরঙ্গ রঙ্গে কি মহান্ শুভ্র হাসি!
বল কারে দেখিয়াছ? কোথা গেলে দেখা পাই!
বিহারীলালের মিস্টিকচেতনা আরও কাব্যময় ও শিল্পিত হয়ে লিপিবদ্ধ হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে। আধুনিক কবিদের মধ্যেও অনেকেরই বহু কবিতায় অতীন্দ্রিয়বোধ ফুটে উঠেছে। অজিত দত্তের ‘মাছেরা’, ‘শরৎ’; সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের ‘জন্মাষ্টমী’; অরুণ মিত্রের ‘ভরসন্ধ্যায় সে ফিরে আসে’; এরকম বহু কবিতা।
কাব্যের অতীন্দ্রিয়বাদ এবং দর্শনের আধ্যাত্মিক–অতীন্দ্রিয়বাদে আকাশ–পাতাল ফারাক। ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির অতীন্দ্রিয়বাদে ঈশ্বরের বিষয়টিই মুখ্য। কাব্যে সরাসরি তা নয়।
ইংরেজি–কাব্যে মিস্টিক–কবি হিসাবে শ্রেষ্ঠ উদাহরণ উইলিয়ম ব্লেক (1757–1827)।
অত্যুক্তি: একটি গৌণ অর্থালংকার, যেখানে সৌন্দর্য, লালিত্য়, বীরত্ব ইত্যাদি গুণ অতিরিক্ত বাড়িয়ে বলা হয়, এবং এর মাধ্যমে যোগ্য ব্যক্তির যোগ্যতাকে অতিরঞ্জিত করা হয়।
অদ্ভুত: অন্যতম কাব্যরস। ভরতের রসপ্রস্থানে যে–আটটি স্থায়ীভাবের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে ‘বিস্ময়’ স্থায়ীভাবটি থেকে ‘অদ্ভুত’ রস তৈরি হয়।
অধিক: অর্থালংকারের নানাপ্রকার শ্রেণিবিভাগ। তার মধ্য়ে একটি গৌণ শ্রেণিও রয়েছে। ‘অধিক’ সেই শ্রেণিভুক্ত। গৌণ শ্রেণির অলংকারগুলি বাংলায় ব্য়বহৃত হয় না, আগেও হয়নি সেরকম।
অধিকারূঢ় বৈশিষ্ট্য: এটি একটি রূপক। উপমান যখন অসম্ভব বলে মনে হয় (অধিক–আরূঢ়), সেটি যদি উপমেয়ে আরোপিত হয়, তখন এই রূপক হয়।“অগ্নি–আখরে আকাশে যাহারা লিখেছে আপন নাম”‒আগুন দিয়ে তো আর কোনো অক্ষর লেখা যায় না, তাই এখানে এই রূপক প্রযোজ্য হয়েছে।
ছবি সৌজন্যে বংলালাইভ
জন্ম গড়শিমুলা গ্রামে (অধুনা জামতাড়া জেলা)। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের চাকরি থেকে স্বেচ্ছাবসর নিয়ে ২০০১ সাল থেকে লেখালেখির কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। কবি, প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক। ২০০৯ সালে অনুবাদের জন্য পেয়েছেন সাহিত্য একাডেমি পুরষ্কার। এ ছাড়াও পেয়েছেন অন্যান্য সম্মান ও পুরষ্কার। রয়েছে বারোটির বেশি প্রকাশিত গ্রন্থ।