১৯৩২ সালের ১৯ ডিসেম্বর। কলকাতার হাতিবাগানের মোড়ে সেদিন একটি নতুন সিনেমা হলের উদ্বোধন ঘিরে সাজো সাজো রব। নামটি যার বেশ কাব্যময় ও অর্থবহ― ‘রূপবাণী’ (Rupbani)। হবারই কথা। কারণ, নামকরণ করেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (Rabindranath Tagore)। এমনকি আজ এর উদ্বোধকও তিনি। ফলে, সাড়া তো পড়বেই। রবীন্দ্রনাথ তো বরাবরই সিনেমার ব্যাপারে আগ্রহী। কয়েকমাস আগেই, ১৯৩২-এর ২২ মার্চ তাঁর পরিচালনায় মুক্তি পেয়েছে নিউ থিয়েটার্স-এর ছবি ‘নটীর পূজা’। রীতিমতো স্টুডিওতে গিয়ে ছবিটির তত্ত্বাবধান করেছিলেন কবি। এর বছর দুয়েক আগে, ১৯৩০ সালে জার্মানিতে গিয়ে প্রথমবার সবাক চলচ্চিত্র ‘Pation Play’ দেখেছিলেন তিনি। গিয়েছিলেন বার্লিনের ‘ইউফা’ স্টুডিওতে। সেখানকার কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেন কিছু লিখে দেবার জন্যে, যার চিত্ররূপ দিতে চান তাঁরা। কবি লেখেন ‘The Child’ কবিতাটি। এটি রবীন্দ্রনাথের একমাত্র কবিতা, যেটি প্রথমে ইংরেজিতে লেখা হয়েছিল। পরে যা বাংলায় ‘শিশুতীর্থ’ নামে লেখেন তিনি। যাই হোক, সেইসময় যে কোনও কারণে, ছবিটি হয়নি। তবে, ঐ ইউফা স্টুডিওতে সেবার কবিকণ্ঠে গান ও আবৃত্তির সবাক চিত্র তোলা হয়, ১৯৩১ সালে যা দেখানো হয়েছিল কলকাতায়। সুতরাং, বোঝাই যাচ্ছে, সিনেমার ব্যাপারে কতটা আগ্রহ ছিল রবীন্দ্রনাথের। তাই, এদেশীয়দের হাতে তৈরি হওয়া একটি নতুন চলচ্চিত্র প্রেক্ষাগৃহের নামকরণ ও উদ্বোধনের জন্যে কবি তো এগিয়ে আসবেনই।

১৯৩১ সালের ২৫ এপ্রিল অমর চৌধুরীর পরিচালনায় প্রথম বাংলা সবাক ছবি ‘জামাইষষ্ঠী’ মুক্তি পায়। ফলে, ‘রূপবাণী’ (Rupbani) চালু হওয়ার আগেই সবাক বাংলা ছবি তথা তখনকার লব্জ অনুযায়ী ‘টকি’-র সঙ্গে বছরখানেক ধরে পরিচয় ঘটে গেছে চলচ্চিত্রপ্রেমীদের। এর মধ্যে ১২/১৩টি বাংলা টকি মুক্তিও পেয়ে গেছে। তখন থেকেই আবার সিনেমাকে ‘বই’ বলারও শুরু। যা আজও অনেকের মুখে শোনা যায়। তখন সাধারণ মানুষের মনে আলোড়ন ফেলেছে সদ্য আসা কথা বলা সিনেমা, যা দেখার জন্যে হলগুলোই ভরসা। ফলে, তিনটে শো-টাইম অনুযায়ী মানুষের ঢল নামত বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে। সেইসময় পরাধীন ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তাপ সর্বত্র। নানারকম সমস্যায় জর্জরিত সাধারণ মানুষের জীবন। তারই মধ্যে রেকর্ড-রেডিও-র পরে পরেই আসা বাংলা টকি দেখে একটু শান্তি ও বিনোদন পেতে চাইতেন তাঁরা। যা খুবই স্বাভাবিক।
আরও পড়ুন- ‘সীতা’র কপিরাইট কেড়েও রোখা যায়নি তাঁর উত্থান, শতবর্ষে বাংলা নাটকের ‘শিশির যুগ’
‘রূপবাণী’ নির্মাণের জন্যে তিনজন ব্যক্তি মিলে ‘স্ক্রীন কর্পোরেশন লিমিটেড’ নামে একটি কোম্পানি খোলেন। এঁরা হলেন বি.সি.নান ব্রাদার্স-এর সুধীরচন্দ্র নান, প্যারিস কোলাপসিবল্ গেট কোম্পানির স্বত্বাধিকারী রবীন্দ্রনাথ দত্ত এবং ন্যাশনাল ডাই অ্যান্ড ওয়াটার প্রুফ ওয়ার্কস-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও আইনজীবী মনোরঞ্জন সরকার। এছাড়া পরিচালক-গোষ্ঠীর মধ্যে আরও ছিলেন প্রভাসচন্দ্র নান ও প্রকাশচন্দ্র নান। সবাই মিলে ঠিক করলেন প্রেক্ষাগৃহটিকে নান্দনিক, আধুনিক প্রযুক্তিগত ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা ইত্যাদি সব দিক থেকে অভিনব করে গড়ে তুলতে হবে। সেইমতো, একেকটি বিভাগের জন্যে বেছে নেওয়া হল দক্ষ শিল্পী, ইঞ্জিনিয়ার ও সংস্থাকে। শুরু হল নির্মাণ। শেষ হতে সময় লাগল না বেশি। এক অপূর্ব চেহারায় প্রতীয়মান হল ‘রূপবাণী’। সত্যিই রূপে একেবারে অনন্যা!

প্রেক্ষাগৃহের দুটি অংশ। বাইরে তোরণদ্বার। তার পর কিছুটা প্রশস্ত প্রাঙ্গণ পেরিয়ে মূল প্রেক্ষাগৃহ। আভিজাত্যে ভরা নির্মাণশৈলী। প্রাঙ্গণটি যেন অনেকটা অভিজাত বাড়ির ঠাকুরদালানের মতো। তোরণদ্বারের দুদিকে দুটো বড় দরজা। একটা দিয়ে গাড়ি ঢোকা, অন্যটি বেরোনোর। মহিলাদের ব্যবহারের জন্যে আলাদা সিঁড়ি এবং দোতলায় উঠে তাঁদের বিশ্রামঘর। ছবি দেখানোর পর্দার সামনে অনেকখানি প্রশস্ত মঞ্চ। যেখানে প্রয়োজন হলে গানবাজনা বা নাটক করা যেতে পারে। মঞ্চের দুপাশে আলোক-বৃক্ষের মতো দুটি তালগাছের মডেল, যা অবশ্য কিছুদিন পরে বিলুপ্ত হয়। সিনেমা শুরুর সময়, আলো ঝপ করে না নিভে, ধীরে ধীরে কমে, ক্রমে অন্ধকার হয় (পরে অনেক প্রেক্ষাগৃহেই এই প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয়েছিল)। এছাড়া, প্রতি তিন মিনিট অন্তর হলের ভেতরের গরম দূষিত বাতাসকে বাইরে বের করে দিয়ে, বাইরের ঠান্ডা টাটকা বাতাস ঢোকানোর ব্যবস্থা রাখা ছিল। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক সোপান একে বলা যেতে পারে। রূপবাণীকে সাজিয়ে তোলা হয়েছিল সুন্দরভাবে। দেওয়াল-চিত্র এঁকেছিলেন শান্তিনিকেতন কলাভবনের প্রথম চারজন ছাত্রের অন্যতম অর্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। হলের অসামান্য সৌধটি নির্মাণ করেন চারজন বিলেতফেরত ইঞ্জিনিয়ার এবং গোটা প্রেক্ষাগৃহের ভেতর-বাইরে যে রং ছিল তার সামগ্রিক combination-টির পরিকল্পনা করেছিলেন ডি. ডি. রবিনসন।
অনেক দিক থেকেই রূপবাণী স্বকীয়তা দেখিয়েছিল। তখন যেসব শব্দযন্ত্র সিনেমা হলে ব্যবহার হত, সবই ছিল বিদেশি কোম্পানির। কিন্তু রূপবাণী বসালো ‘সিস্টোফোন’ নামে একটি মেশিন, যেটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে বসে তৈরি করেছিলেন Applied Physics-এর এম.এস.সি-র ছাত্র বামাদাস চট্টোপাধ্যায়। সেইসময় এ ছিল এক যুগান্তকারী উদ্ভাবন। অনেকেই এর প্রশংসা করেছিলেন এক জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। যেমন, প্রখ্যাত চলচ্চিত্র-ব্যক্তিত্ব নিরঞ্জন পাল ‘বাতায়ন’ পত্রিকায় এ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেছিলেন, ‘… বামাদাস চট্টোপাধ্যায় এম. এসসি, শব্দমুখর যন্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া যে যন্ত্রটি আবিষ্কার করিয়াছেন ইহাকেই আমি মনে করি বৈদেশিক শোষণ দণ্ডের বিরুদ্ধে উত্তোলিত ভারতের একমাত্র ক্ষুদ্র তর্জনী।… এই সিস্টোফোন অদূর ভবিষ্যতে যে বৈদেশিক শোষিত অর্থের পরিমাণ অধিকাংশ কমাইয়া দিবে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দিগ্ধ।’ সত্যিই দেখা গেল, সিস্টোফোন জনপ্রিয় হবার পর, বিদেশি কোম্পানিগুলোর এই ধরনের শব্দযন্ত্রের দাম প্রায় অর্ধেক হয়ে গিয়েছিল।
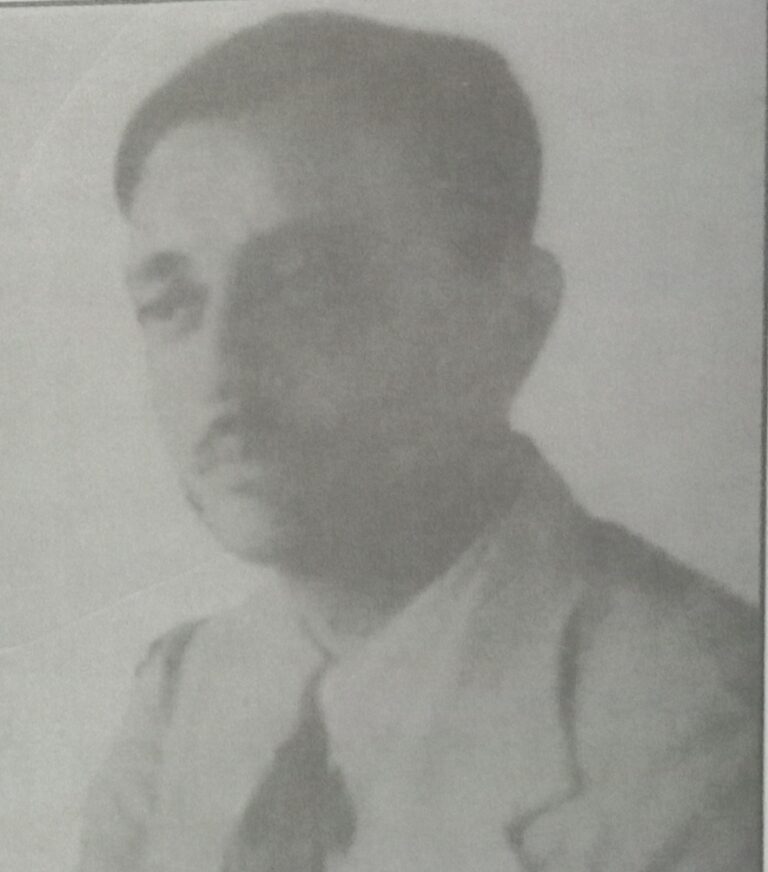
আগেই বলা হয়েছে, রূপবাণীর দ্বারোদ্ঘাটনের দিনটি ছিল ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৩২। নির্দিষ্ট দিনে এসে দেখা গেল, প্রেক্ষাগৃহে ছবি দেখানোর প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা তখনও পুরোপুরি কার্যক্ষম হয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে ঐ দিনেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। প্রসঙ্গত, ঐ বছরই (১৯৩২) রবীন্দ্রনাথ ‘চিররূপের বাণী’ নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন। যার মধ্যে সবাক চলচ্চিত্র ও ‘রূপবাণী’ নামকরণের সঙ্গে একটা সম্পর্ক যেন স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। কিন্তু এই উপলক্ষেই কবিতাটি লেখা হয়েছিল বা ঐ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তা পড়া হয়েছিল কিনা, এসব নিয়ে কোনও নির্দিষ্ট তথ্য চোখে পড়ে না। কবিতাটি শুরু হয় এইভাবে― ‘প্রাঙ্গণে নামল অকালসন্ধ্যার ছায়া/ সূর্যগ্রহণের কালিমার মতো।/ উঠল ধ্বনি : খোলো দ্বার!’ কবিতাটি দীর্ঘ। শেষের দুটি লাইনে কবি যা লিখলেন, তা যেন সবাক চিত্ররূপের প্রতি ইঙ্গিতবাহী― ‘দেহমুক্ত রূপের সঙ্গে যুগলমিলন হল দেহমুক্ত বাণীর/ প্রাণতরঙ্গিনীর তীরে, দেহনিকেতনের প্রাঙ্গণে।’
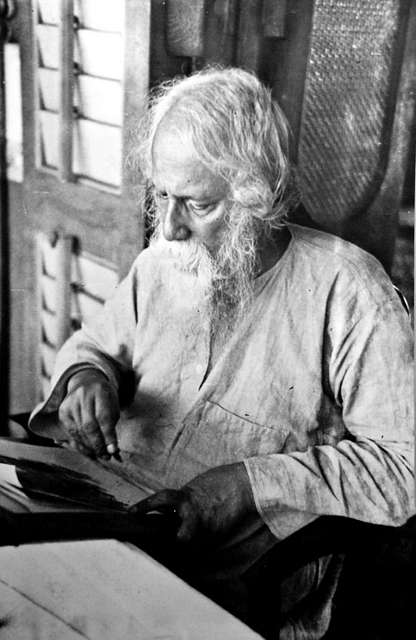
উদ্বোধনের ঠিক এক সপ্তাহ পরে, অর্থাৎ ১৯৩২ সালের ২৬ ডিসেম্বর, যে ছবি দিয়ে রূপবাণীর জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল, এক দিক থেকে সেটিও ছিল গুরুত্বপূর্ণ― ‘বেঙ্গল ১৯৮৩’। কারণ, এটিই ছিল প্রমথেশ বড়ুয়া নির্দেশিত ও অভিনীত প্রথম সবাক বাংলা ছবি। তখন থেকে ৫০ বছর পরের (১৯৮৩) বাংলার একটি কাল্পনিক অবস্থা ছবিতে দেখাতে চেয়েছিলেন বড়ুয়াসাহেব। এর বছর দুয়েক আগে কলকাতায় এসেছিল Frederic Lonsdale-এর লেখা ও Norma Shearer অভিনীত ‘The Last of Mrs. Cheyney’ ছবিটি। অনেকেই তখন তা দেখেছিলেন। সম্ভবত এই ছবি দেখেই প্রমথেশ বড়ুয়ার মাথায় ‘বেঙ্গল ১৯৮৩’-র আইডিয়াটা আসে। এর পর, যখন তিনি ফ্রান্সের কক্স স্টুডিওতে মি. রোজার্সের কাছে ফিল্মের পাঠ নিচ্ছেন, সেইসময় চিত্রনাট্য লেখা অভ্যেস করার সময় ‘বেঙ্গল ১৯৮৩’-র খসড়া করেছিলেন। ছবিটিতে অভিনয়ে ছিলেন প্রমথেশ বড়ুয়া, প্রভাবতী বড়ুয়া, ফণী বর্মা, সুশীল মজুমদার, সমর ঘোষ, রেণুকা ঘোষ প্রমুখ। ক্যামেরা ও শব্দগ্রহণের দায়িত্বে ছিলেন যথাক্রমে বিভূতি দাশ ও তাপস চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক, ছবিটি একেবারেই সাড়া জাগাতে পারেনি। কয়েকজন চিত্রসমালোচক তো বেশ বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন ছবিটির। ফলে, এক সপ্তাহ বাদেই উঠে যায় ‘বেঙ্গল ১৯৮৩’।
এর পর, দ্বিতীয় ছবি হিসেবে ১৯৩৩ সালের ১ এপ্রিল রূপবাণীতে মুক্তি পায় প্রিয়নাথ গাঙ্গুলি পরিচালিত ‘যমুনা পুলিনে’। মাঝখানে কয়েকমাস ছবি দেখানো হয়নি এই সদ্যজাত প্রেক্ষাগৃহটিতে। যাই হোক, এভাবেই শুরু হল রূপবাণীর চিত্র-অভিযান। এর পর থেকে প্রায় ৭-৮ দশক ধরে অজস্র ছবি, চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব, অগনিত দর্শক ইত্যাদি ধারণ করে এক বিরাট সময়ের সাক্ষী থেকেছে এই চিত্রগৃহটি। কয়েক বছর আগে অবধিও মূলত বাংলা ছবি রিলিজের অন্যতম জনপ্রিয় chain ছিল রূপবাণী, অরুণা, ভারতী। কলকাতার তিনদিকে থাকা এই তিনটি প্রেক্ষাগৃহই আজ কালের গর্ভে বিলুপ্ত।

রূপবাণী যেখানে ছিল, আজ সেখানে বেচাকেনা ও বাসস্থানের ‘আধুনিক’ উপস্থিতির নিদর্শন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এরকম অনেক ঐতিহ্যমণ্ডিত চিত্র ও মঞ্চগৃহই বর্তমানে স্মৃতিতে পর্যবসিত। গত কয়েক দশকে মানুষের জীবনযাত্রায় যে আকস্মিক পরিবর্তন এসেছে, তার কারণ অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা বিশেষজ্ঞদের বিষয়। সময়ের দাবি অনুযায়ীই হয়তো সবকিছু হচ্ছে। যাকে অবশ্যই এককথায় ভালো বা খারাপ বলা শক্ত। তবুও এসব দেখে, মধ্যবয়স অতিক্রান্ত অধিকাংশ মানুষের মনে বোধহয় একটু খোঁচা লাগে। জীবনের চলাফেরার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা অনেককিছুর হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া মানতে কোথাও যেন কষ্ট হয়। একটা কথা বলতেই হয়, এর ফলে, আমরা আপন জাতিবৈশিষ্ট্যের অনেককিছুরই বিনাশ ঘটিয়ে ফেলে, এক ধরনের সর্বজনীন মিশ্র সংস্কৃতিকে বোধহয় আঁকড়ে ধরছি— যা আমাদের নিজস্বতার হানি ঘটাচ্ছে অনেকটাই। এসব সত্ত্বেও, এ কথাও সত্যি, যতই এক ধরনের বৈভবী হিসেবি আচরণের হাত ধরে তথাকথিত ‘আধুনিকতা’ আসুক না কেন সমাজে, সেইসব বেহিসেবি স্বতস্ফূর্ত মুহূর্তগুলো, যা জড়িয়েছিল রূপবাণীর মতো বাংলার আরও অনেক নিজস্ব নিদর্শন, সংস্কৃতি ও চলাচলের সঙ্গে, সেগুলি চিরকাল জীবন্ত হয়ে থাকে যায় মানুষের মনে। এর সত্যতা অমর।
তথ্যঋণ :
১) সোনার দাগ― গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ (যোগমায়া প্রকাশনী, ডিসেম্বর ১৯৮২)
২) বাংলা চলচ্চিত্রের বিকাশে প্রমথেশ বড়ুয়া― সংকলন/সম্পাদনা/মূল্যায়ণ : নন্দন মিত্র (চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি কেন্দ্র, এপ্রিল ২০০৬)
৩) রবীন্দ্র রচনাবলী : জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ (পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮)
৪) বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের ইতিহাস― কালীশ মুখোপাধ্যায় (পত্রভারতী, এপ্রিল ২০১২)
৫) বাতায়ন (আর্টিস্ট ফোরাম, ৪র্থ বর্ষ প্রথম সংখ্যা, চৈত্র ১৪২৩)
৬) রাজার কুমার― রবি বসু (দেশ, বিনোদন সংখ্যা ১৩৮৩)
জন্ম ১৯৬৫-তে কলকাতায়। বেড়ে ওঠা চন্দননগরে। স্কুল জীবন সেখানেই। কলকাতার সিটি কলেজ থেকে স্নাতক। ছোটো থেকেই খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ। গান শেখাও খুব ছোটো থেকেই। তালিম নিয়েছেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও। দীর্ঘদিন মার্কেটিং পেশায় যুক্ত থাকার পর, গত বারো বছর ধরে পুরোপুরি লেখালেখি, সম্পাদনার কাজে যুক্ত। পুরনো বাংলা গান, সিনেমা, খেলা ইত্যাদি বিষয়ে অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকা, এই সময়-সহ বহু পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। সম্পাদিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তমকুমারের "হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি মোর", হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের "আনন্দধারা", রবি ঘোষের "আপনমনে", মতি নন্দীর "খেলা সংগ্রহ"। লিখেছেন "সংগীতময় সুভাষচন্দ্র" বইটি। সাত বছর কাজ করেছেন "মাতৃশক্তি" ও "জাগ্রত বিবেক" পত্রিকায়। বর্তমানে নিজস্ব লেখালিখি ও সম্পাদনা নিয়ে ব্যস্ত।

























