বাংলা ১৩২৮ সালের ৮ পৌষ ‘বিশ্বভারতী’কে ‘সর্বসাধারণের হাতে সমর্পণ’ করে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই অর্থেই ১৪২৮ সালের ৮ পৌষ (২৪ ডিসেম্বর ২০২১) তারিখটিকে বিশ্বভারতীর শতবর্ষপূর্তি হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে এ বছর। বিশ্বভারতীর ইতিহাস সম্পর্কে যাঁরা অল্পবিস্তর ওয়াকিবহাল তাঁরা জানেন, বিশ্বভারতীর কাজকর্ম শুরু হয়ে গিয়েছিল তার বছর তিনেক আগে থেকেই। ঠিক তিনবছর আগে ১৩২৫ সালের ৮ পৌষ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়েছিল বিশ্বভারতীর। এই ‘ভিত্তিপ্রস্তর’ বিষয়টিকে কিঞ্চিৎ প্রতীকী মূল্যেই ধরে নিতে হবে। বিশ্বভারতী তো একটা বিল্ডিংয়ের নাম নয়, যে তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হবে। আশ্রম চত্বরের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায় একটু গর্ত খুঁড়ে কিছু মাঙ্গলিক দ্রব্য সংস্থাপন করে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই প্রতীকী ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।
ভারতীয় সংস্কৃতির অনুসারী এই মঙ্গলাচরণের সঙ্গে আরও একটা ব্যাপার জুড়ে ছিল সেদিন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিভিন্ন দেশের পুরুষ ও মহিলাদের অনুরোধ করা হয়েছিল, যেন তাঁরাও ‘বিশ্বমানবের প্রতিনিধি স্বরূপ’ ওই গর্তের মৃত্তিকাপূর্তিতে হাত লাগান। সেদিনের অনুষ্ঠানের এই বিবরণ পড়বার সময় এখন মনে হয়, যেন অনেক আদর-যত্নে ‘বিশ্বভারতী’ নামক একটা চারাগাছই রোপণ করা হয়েছিল সেইদিন সেই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠানে; যেখানে প্রতীকী অর্থেই ‘বিশ্ব’ ও ‘ভারতবর্ষ’ একযোগে মিলেমিশে গিয়েছিল। বিশ্বভারতীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে অবশ্য বোঝা যায়, ‘চারাগাছ’টির একটা বীজতলা প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল তারও আগে। প্রশ্ন হল কত আগে? কিন্তু তার চেয়েও জটিল প্রশ্ন, বিশ্ব আর ভারতের সম্মিলনের তাত্ত্বিক ভিত্তিটার প্রকৃত স্বরূপ কী? প্রথমে প্রথম প্রশ্নটার দিকে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা যাক।
১৩০৮ সালের ৭ পৌষ যখন কবির ‘ব্রহ্মবিদ্যালয়’ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন বিশ্বকে একনীড়ে মিলিত করার আকাঙ্ক্ষার উল্লেখ অন্তত কোথাও পাওয়া যায় না। ব্রহ্মবিদ্যালয় বা ব্রহ্মচর্যাশ্রমের নিজস্ব একটা বিবর্তন-ইতিহাস আছে। চিন্তক রবীন্দ্রনাথের চিন্তাচেতনার ইতিহাসের সমান্তরালে সেই বিবর্তন-ইতিহাস বা জেনেসিসের সুস্পষ্ট পরিচয় মেলে। ১৯০১ সালের শান্তিনিকেতনের ‘ব্রহ্মবিদ্যালয়’ ভাবনা আর ১৯১০ সালের আশ্রমের ভাবকল্পনা যে অনেকটাই আলাদা তা ‘ব্রহ্মবিদ্যালয়’ প্রতিষ্ঠাপর্বে বন্ধু জগদীশ চন্দ্র বসু-সহ আরও অনেককে লেখা কবির চিঠিপত্রের সঙ্গে ১৯১০ সালে লেখা ‘তপোবন’ বা ‘সামঞ্জস্য’ প্রবন্ধ মিলিয়ে পড়লেই অনেকটা স্পষ্ট বোঝা যায়।
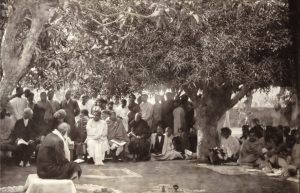
খুব সংক্ষেপে বললে, ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সূচনাপর্বে কবির আশ্রমচিন্তার প্রস্থানভূমিতে ছিল ‘প্রাচীন ভারতবর্ষ’ নামের একটা গম্ভীর অনুশাসিত তপোবনের ভাবকল্প, আর ১৯১০ সালের আশ্রম বিদ্যালয় ভাবনার মধ্যে ছিল ‘বাঘে গরুতে একঘাটে জল খাওয়া’ সম্মিলনী প্রসাদপুষ্ট অন্য এক তপোবন। তপোবন ভাবনার এই রকমফের বোঝবার সময় মনে রাখতে হয়, এই সময়ই স্বয়ং আশ্রমগুরু ‘গোরা’ লিখছেন, ‘গীতাঞ্জলি’ লিখছেন। সেই তপোবনেরই বটুবালকদের জন্য উন্মুক্ত পরিসরে উৎসবের নাটক ‘শারদোৎসব’ লিখেছেন তারও দু’বছর আগে ১৯০৮ সালে। কিন্তু বিদ্যাসূত্রে বিশ্বকে মেলাবার আকাঙ্ক্ষার কথা তখনও শোনা যায়নি কবির মুখে।
তবে ব্রহ্মবিদ্যালয় যে একদিন তার বিশ্বরূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে তা ১৯১১ সালেই আন্দাজ করেছিলেন দূরদর্শী আশ্রম-শিক্ষক অজিতকুমার চক্রবর্তী। অজিতকুমার তাঁর ‘ব্রহ্মবিদ্যালয়’ বইতে লিখেছেন, ‘আশ্রমের মধ্যে আমরা যেন কোনোদিনই সাম্প্রদায়িক কোনো কথাই না তুলি, ইহার বিশ্বরূপটিই যেন দেখি।’ আরও তাৎপর্যপূর্ণভাবে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ‘ক্রমে— এটি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আকার ধারণ করিবে, এখানে নব নব জ্ঞানের বিকাশ দেখা দিবে।’ ব্রহ্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই এখানে গড়ে উঠবে অসাম্প্রদায়িক উদার একটি বিদ্যাসমবায়ের ক্ষেত্র, এমনই মনে হয়েছিল অজিতকুমারের। ফলতঃ, ব্রহ্মবিদ্যালয় পর্বের আদর্শ থেকে স্বাভাবিক বিবর্তনের ধারাতেই এখানে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠবে, এমনই মনে হয়েছিল তাঁর। বাস্তবে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বিশ শতকের প্রথম পর্বের অস্থির বিশ্বরাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত।
ব্রহ্মবিদ্যালয়ের একেবারে সূচনাপর্বে (১৯০২) শিতোকু হোরি জাপান থেকে পড়তে এসে কার্যত বিশ্বভারতীর বিশ্বজনীনতার সূচনা করেছিলেন বটে, কিন্তু যে-সময়ের কথা বলা হচ্ছে তখন পর্যন্ত ব্রহ্মবিদ্যালয় ঠিক ‘বিশ্বগত’ হয়ে ওঠেনি। বিশ্বগত না হলেও এইসময়ের একদশকের মধ্যেই বৃহত্তর ভারতের ব্রহ্মদেশ, বোম্বাই প্রদেশ, আসাম,উড়িষ্যা, পাঞ্জাব ইত্যাদি প্রদেশের ছাত্রেরা তখন শান্তিনিকেতনে পাঠগ্রহণ করতে আসছেন যা সেকালের নিরিখে খুব কম কথা নয়। কিন্তু বিশ্বগত একটি প্রতিষ্ঠানের ভাবনা যে রবীন্দ্রনাথ এরই কাছাকাছি সময় থেকে ভাবতে থাকবেন, তার আভাস রয়েছে তাঁরই চিঠিতে। ১৯১৩ সালের ৩ মার্চ ‘সিকাগো’ থেকে একটি চিঠিতে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংকটের উপলব্ধি কবি প্রকাশ করেছেন এইভাবে:
‘—এখানে [আমেরিকায়] মানুষের শক্তির মূর্তি যে পরিমাণে দেখি পূর্ণতার মূর্তি সে পরিমাণে দেখতে পাই নে।—মানুষের যতদূর বাড় হবার তা হয়েছে, এখন সময় হয়েছে যখন যোগের জন্য সাধনা করতে হবে। আমাদের বিদ্যালয়ে আমরা কি সেই যুগসাধনার প্রবর্তন করতে পারব না? মনুষ্যত্বকে বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত করে তার আদর্শ কি আমরা পৃথিবীর সামনে ধরব না?’

এ হল সেইসময়ের কথা যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাসন্ন। যুদ্ধ শুরু হয়নি বটে, কিন্তু পশ্চিমা বাতাসে তখনই ভেসে বেড়াচ্ছে বারুদের গন্ধ। আমাদের মনে হয়, বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে এবং বিশ্বযুদ্ধকালীন পর্বে মনুষ্যত্বের নিদারুণ পরাভবের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলে হয়তো ‘বিশ্বভারতী’র ভাবনা ঠিক ওইসময়েই বাস্তবায়িত হত না! রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন, যুদ্ধোন্মাদ রাষ্ট্রগুলি তার নাগরিকদের ওই যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করার জন্য হাতের যে-তাসটা খেলে চলেছে তার নাম ‘ন্যাশানালিজম্’। এই ‘ন্যাশানালিজম্’ পদার্থটার মধ্যে একরকম সংকীর্ণতা আছে। আপন দেশকে শ্রদ্ধা করার মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ নয়; অন্য দেশ বা জাতিকে খাটো না করে সংকীর্ণ ন্যাশানালিজম্ যেন চলতেই পারে না।
১১ অক্টোবর ১৯১৬ তারিখে লস এঞ্জেলেস থেকে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লেখা কবির একটি চিঠির মধ্যে এই ‘সংকীর্ণ স্বাজাতাতিকতা’র বিপ্রতীপে গঠনমূলক প্রতিবিধানের একরকম অঙ্গীকার স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারিত হল। তিনি সেখানে লিখছেন:
‘শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগের সূত্র করে গড়ে তুল্তে হবে— ঐখানে সার্ব্বজাতিক মনুষ্যত্বচর্চ্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে— স্বাজাতিক সঙ্কীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসচে— ভবিষ্যতের জন্য যে বিশ্বজাগতিক মহামিলনযজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্চে তার প্রথম আয়োজন ঐ বোলপুরের প্রান্তরেই হবে। ঐ জায়গাটিকে সমস্ত জাতিগত ভূগোলবৃত্তান্তের অতীত করে তুলব এই আমার মনে আছে— সর্ব্বমানবের প্রথম জয়ধ্বজা ঐখানে রোপণ হবে। পৃথিবী থেকে স্বাদেশিক অভিমানের নাগপাশবন্ধন ছিন্ন করাই আমাদের শেষ বয়সের কাজ। এই জন্যেই বিধাতা কোনো খবর না দিয়ে হঠাৎ এই পশ্চিমের ঘাটে আমার নৌকো এনে ভিড়িয়েচেন—।’
মনে রাখতে হবে, এই কথাগুলো যখন লিখছেন রবীন্দ্রনাথ, তার অল্প কয়েকমাস আগেই জাপানে ‘ন্যাশানালিজম্’-কে ধিক্কার জানিয়ে সেই অগ্নিক্ষরা বক্তৃতা দিয়ে এসেছেন। বুদ্ধের দেশ জাপান কেন পশ্চিমের অনুকরণ করে নিজেদের হাজার বছরের সংস্কৃতি বিকিয়ে ফেলবে— এই ছিল সেই ১১ জুন টোকিয়ো ইম্পিরিয়াল ইউনিভার্সিটিতে প্রদত্ত বক্তৃতায় উৎক্ষিপ্ত ক্ষুব্ধ আক্ষেপ। ২৮ অক্টোবর শিকাগো থেকে থেকে লেখা আর একটি চিঠিতে রথীন্দ্রনাথকে আগের চিঠির রেশ ধরে আরও লিখছেন কবি, ‘একদিন রামমোহন রায় আমাদের ব্রহ্মলোকে উদ্বোধিত করেচেন। সেই ব্রহ্মলোকেও জাত নেই দেশ নেই।— বাংলা দেশের চিত্ত সর্ব্বকালে সর্ব্ব দেশে প্রসারিত হোক্, বাংলা দেশের বাণী সর্ব্বজাতি মানবের বাণী হোক্। আমাদের বন্দেমাতরম্ বাংলাদেশের বন্দনার মন্ত্র নয়— এ হচ্চে বিশ্বমাতার বন্দনা।’
যে-সময়ের কথা বলা হচ্ছে তখন পর্যন্ত ব্রহ্মবিদ্যালয় ঠিক ‘বিশ্বগত’ হয়ে ওঠেনি। বিশ্বগত না হলেও এইসময়ের একদশকের মধ্যেই বৃহত্তর ভারতের ব্রহ্মদেশ, বোম্বাই প্রদেশ, আসাম,উড়িষ্যা, পাঞ্জাব ইত্যাদি প্রদেশের ছাত্রেরা তখন শান্তিনিকেতনে পাঠগ্রহণ করতে আসছেন যা সেকালের নিরিখে খুব কম কথা নয়। কিন্তু বিশ্বগত একটি প্রতিষ্ঠানের ভাবনা যে রবীন্দ্রনাথ এরই কাছাকাছি সময় থেকে ভাবতে থাকবেন, তার আভাস রয়েছে তাঁরই চিঠিতে।
এই উদ্ধৃতাংশটির মধ্যে দুটি বিষয় খেয়াল করা দরকার। যে- ‘বন্দেমাতরম্’ গানকে তখন জাতীয়তাবাদের মূলমন্ত্র হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা হচ্ছিল, রবীন্দ্রনাথ সেই গানটির মধ্যেই কিনা দেখতে পাচ্ছেন ‘বিশ্বমাতার বন্দনা’! দ্বিতীয়ত, ঔপনিষদিক ব্রহ্মলোকের ধারণাটিকে আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনার পরিবর্তে দেশ ও জাতিগর্বের ঊর্ধ্বে সর্বমানবের আদর্শ আশ্রয়স্থল হিসেবে এখানে প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে। ‘বন্দেমাতরম্’ গানটিকে ‘বিশ্বমাতার বন্দনা’ বলবার ক্ষেত্রে হয়তো ওই গানের শেষ স্তবকে ‘ধরণীং ভরণীম্’ কথাগুলো স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু এই ভাবটি তাঁর নিজের গানে এর এগারো বছর আগেই আরও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছিল। ‘ও আমার দেশের মাটি’ গানে কবি লিখেছিলেন, ‘তোমাতে বিশ্বময়ীর বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।’ ফলে, বলাই যায়, দেশমাতৃকার বন্দনার সঙ্গে বিশ্বমাতৃকাকে জড়িয়ে নেওয়ার রবীন্দ্র-প্রকরণটি ঠিক বিশ্বযুদ্ধপর্বের আকস্মিক অর্জন নয়। বিশ্বযুদ্ধকালীন প্রেক্ষাপটের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও আন্তরিক উপলব্ধি তাঁর প্রতিষ্ঠানটির ইতিহাসে অনুঘটকের মতো কাজ করে তাকে বিশ্বগত করে তুলতে গভীরভাবে প্রণোদিত করেছিল, এইটুকুই হয়তো বলা যায়।
বিশ্বের সঙ্গে ভারতকে ঠিক কীভাবে অন্বিত করা যায়, বা করার চেষ্টা হয়েছিল সে সময়, সে অবশ্য দীর্ঘ আলোচনার বিষয়। আমাদের দ্বিতীয় জিজ্ঞাস্য এই বিষয়টি খানিকটা তত্ত্বগতও বটে। ‘বিশ্বভারতী’ ভাবনার বনেদে যে-তত্ত্বটি অতি স্পষ্ট, তা নিয়ে আমরা সবাই কমবেশি ওয়াকিবহাল। কিন্তু বিষয়টি আলাদা করেও মনোযোগ দাবি করে।
বিশ্ব ও ভারতকে সম্মিলিত রূপে বোঝানো যাবে এমন একটা কার্যকর শব্দ বা শব্দবন্ধ তখন খুঁজে চলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। খুব সম্ভব পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীই ‘শুক্ল যজুর্বেদ’-এর বাজসনেয়ী সংহিতার মধ্যে খুঁজে পান একটি বৈদিক মেটাফর: ‘বেনস্তৎপশ্যন্নিহিতং গুহা সদত্র্য বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্’। এই মন্ত্রের শেষাংশ ‘যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্’— যেখানে বিশ্ব এসে একনীড়ে সম্মিলিত হয়েছে;— এটিই হয়ে উঠল বিশ্বভারতীর মোটো (motto)। ‘বিশ্ব’-এর সঙ্গে ‘ভারতী’ শব্দটি একাধারে যেমন ভারতবর্ষকে নির্দেশ করে তেমনি তাতে সারস্বত সাধনার অন্যতর ব্যঞ্জনাও আভাসিত হয়। ঠাকুরবাড়ির সংস্কৃতির নিরিখে এই ‘ভারতী’ শব্দটার বিশেষ গুরুত্ব ছিল ওই সারস্বত সাধনার অর্থে। ‘ভারতী’ (১৮৭৭) পত্রিকার সূচনাকালের প্রস্তাবনা অংশটিতে তার সাক্ষ্য মেলে।

হয়তো এই দ্বিতীয় সম্ভাব্য অর্থটির ঈষৎ ব্যঞ্জনা বজায় রেখে মূলত বিশ্ব আর ভারতকে সম্মিলিত আধারে দেখার আকুলতাই প্রাধান্য পেয়েছিল রবীন্দ্রনাথের ‘বিশ্বভারতী’ ভাবনায়। ১৩২৬ সালের বৈশাখে ‘শান্তিনিকেতন পত্রিকা’য় ‘বিশ্বভারতী’ নামের একটি রচনায় অবশ্য রবীন্দ্রনাথ গুরুত্ব দিয়েছিলেন ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিকল্পে একটি সমন্বিত ও কার্যকর দেশীয়রকম আদর্শ বিদ্যাউৎপাদনের কেন্দ্র হিসেবে তাকে গড়ে তোলার দিকেই। ওই প্রবন্ধের শেষ বাক্যটি ছিল, “এইরূপ আদর্শ বিদ্যালয়কে আমি ‘বিশ্বভারতী’ নাম দিবার প্রস্তাব করিয়াছি।” এই লেখা যখন প্রকাশিত হচ্ছে, তার চারমাস আগে বিশ্বভারতীর সেই ‘ভিত্তিপ্রস্তর’ স্থাপন অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়ে গেছে, এবং দু’মাস পরে ১৮ আষাঢ় ১৩২৬ বিশ্বভারতীর কার্যারম্ভ শুরু হয়ে যাবে। সেই কার্যারম্ভের দিনের ভাষণে আবারও বোঝা যাবে, বিশ্ব ও ভারতকে ঠিক কীভাবে মিলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছিল তাঁর চেতনায়?
বিধুশেখর শাস্ত্রী-ক্ষিতিমোহন সেনের মতো পণ্ডিতেরা তখন প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞানের নিত্যনতুন অনুসন্ধানে ব্যাপৃত। তাঁদেরই পাশাপাশি আসন পেতেছেন সিংহলের মহাস্থবির। আর একদিকে অ্যান্ড্রুজ সাহেবকে ঘিরে বসেছেন ইংরেজি সাহিত্য-পিপাসুজনেরা। নিঃসন্দেহে এও একরকম বিশ্বজনীনতার ছবি। তবে এ ছবি ঠিক তপোবনের মতো নয়, বরং নালন্দা-তক্ষশীলার মতো। ভারতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকাশ বৌদ্ধযুগেই ঘটেছিল, তপোবনের যুগে নয়। এ হল একরকম আন্তর্জাতিক সম্মিলনের ছবি। অন্যদিকে তপোবনের ঋষিদের বিশ্ববোধ ছিল জগতের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে পরিব্যাপ্ত।

সে যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের এইসময়ের মনোভঙ্গির আরও পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর মাদ্রাজে প্রদত্ত ‘The Centre of Indian Culture’ (১৯১৯) শীর্ষক বক্তৃতায়, যার মোদ্দা কথাটা হল, পৃথিবীকে আলোকিত করার মতো কিছু অতীত সঞ্চয় ভারতবর্ষের আছে। ‘আত্মবৎ সর্বভূতেষু’ দেখাই হল ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তঃসার। ভারতবর্ষ তার বিদ্যাসামর্থ্যে আপন অক্ষে স্বয়ম্প্রভ হয়ে দাঁড়িয়ে পৃথিবীকে তার গূঢ় বাণী শোনাবে, এই ছিল কবির সে সময়ের অভীপ্সা। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয়টি হল, ভারতবর্ষের বিকল্পে প্রাচ্য বা এশিয়াকেও সম্প্রসারিত ভূগোলে রবীন্দ্রনাথ কখনও কখনও উল্লেখ করেছেন তাঁর এই ভাষণে; এবং তা করেছেন প্রতীচ্যের ‘অপর’ হিসেবে প্রাচ্যের একটি আদর্শায়িত ভাবকল্প প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। মার্কিন মুলুকে প্রদত্ত ‘An Eastern University’ বক্তৃতায় যেমন তিনি বলছেন,
‘In The Midst of much that is discouraging in the present state of the world, there is one symptom of vital promise. Asia is awakening. This great event, if it be directed along the right lines, is full of hope, not only for herself, but for the whole world.’
বিশ্ব ও ভারতকে সম্মিলিত রূপে বোঝানো যাবে এমন একটা কার্যকর শব্দ বা শব্দবন্ধ তখন খুঁজে চলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। খুব সম্ভব পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীই ‘শুক্ল যজুর্বেদ’-এর বাজসনেয়ী সংহিতার মধ্যে খুঁজে পান একটি বৈদিক মেটাফর: ‘বেনস্তৎপশ্যন্নিহিতং গুহা সদত্র্য বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্’। এই মন্ত্রের শেষাংশ ‘যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্’— যেখানে বিশ্ব এসে একনীড়ে সম্মিলিত হয়েছে;— এটিই হয়ে উঠল বিশ্বভারতীর মোটো (motto)। ‘বিশ্ব’-এর সঙ্গে ‘ভারতী’ শব্দটি একাধারে যেমন ভারতবর্ষকে নির্দেশ করে তেমনি তাতে সারস্বত সাধনার অন্যতর ব্যঞ্জনাও আভাসিত হয়।
এশিয়া জাগছে শুধু তার নিজের জন্য নয়, সারাবিশ্বের জন্য। ভারত, প্রাচ্য, তথা এশিয়াকে এইভাবে আদর্শায়িত করে দেখার একটা দৃষ্টিভঙ্গি তখন পাশ্চাত্যের শান্তিবাদীদের মধ্যেও তৈরি হয়েছিল। রম্যাঁ রলাঁ, অ্যান্ড্রুজ প্রমুখ ছিলেন সেইধারার প্রতিভূ ব্যক্তিত্ব। রবীন্দ্রনাথের ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁদেরই মধ্যে কেউ কেউ এসে পৌঁছেছিলেন কবির ‘বিশ্বভারতী’র কাজে আত্মনিয়োগ করতে। কবি ইয়েটস্ যখন রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি ‘গীতাঞ্জলি’র ভূমিকা লিখছেন, তখন তার মধ্যেও সেই দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রকাশ ঘটেছে। আর এইখানেই, বস্তুত প্রাচ্যের আদর্শায়িত এই মডেলের সঙ্গে ‘আধুনিক’ জাপান, পাশ্চাত্য ছাঁচে-বন্দি জাপানের কোনও মিল খুঁজে পাননি রবীন্দ্রনাথ।
এরমধ্যে তাত্ত্বিক বিসংবাদটি হল: এই যে, এশীয়বাদ, এই যে প্রাচ্যনির্মাণ— তা যদি পাশ্চাত্যের ‘অপর’ হিসেবে গড়ে উঠে থাকে, তাহলে তাতেও প্রশ্রয় পায় একরকমের কাঠামোতন্ত্র; যা প্রকারান্তরে একরকম ক্ষমতাতন্ত্রেরই পোষকতা করবে। কেননা কাঠামোতন্ত্র মানেই তা কোনও না কোনওভাবে ক্ষমতাতন্ত্রেরই পরিপোষক। অন্তত আজকের উত্তর-অবয়ববাদী চিন্তকেরা এ প্রশ্ন তুলতেই পারেন। সে কথা যদি ছেড়েও দিই তাহলেও প্রশ্ন উঠতে পারে, এশীয়বাদের মহিমাখ্যাপনের সঙ্গে কি ‘জাতিগত ভূগোলবৃত্তান্তের’-ই নতুন একটা উপক্রমণিকার সূচনা হয় না? যতই আদর্শায়িত করে উত্থাপন করা হোক, এশীয়বাদ কি আসলে আর একরকম ‘সংকীর্ণ মহাদেশিকতা’কেই প্রশ্রয় দেবে না? অন্তত ‘সর্বমানবের’ কথাটির মধ্যে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের যে বিপুল ‘মানব’কে বুঝেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, আদর্শায়িত এশীয়বাদ কি তার সঙ্গে আদৌ তুলনীয়?

বিশ্বভারতীর বাস্তবায়নের ইতিহাসে কিন্তু আলাদা করে এই এশীয়বাদের ছায়াসম্পাত ঘটেনি। প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যবিদ্যার সমান গুরুত্ব সেখানে লক্ষ করা গেছে। শুধু তাত্ত্বিক বিদ্যাচর্চায় নয়, বিশ্বভারতী তার প্রায় সূচনার দিনগুলোতেই (১৯২২) শুরু করেছিল শ্রীনিকেতনের পল্লিপুনর্গঠনের মতো কর্মকাণ্ড। বাস্তবে যা করছেন আর বক্তৃতায়; বিশেষ করে ইংরেজি বক্তৃতায়, যথাক্রমে অবাঙালি এবং অভারতীয় টার্গেট অডিয়েন্সের সামনে যা বলছেন কবি— তাতে কোথায় যেন একটা তাত্ত্বিক অবস্থানগত অস্পষ্টতা থেকে যাচ্ছে বলেই মনে হয়। অথচ ১৩২৮ সালের ৮ পৌষ বিশ্বভারতীর লোকার্পণের দিনে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে খুব স্পষ্ট করেই বলেছিলেন, ‘এই বিশ্বভারতী ভারতবর্ষের জিনিষ একে সমস্ত মানুষের তপস্যার ক্ষেত্র করতে হবে।’
এই বলার মধ্যে কিন্তু বাস্তব আর তত্ত্বমূর্তির তেমন কোনও বিরোধ নেই। ভারতবর্ষের মাটিতে শিকড় বিস্তার করে বিশ্বের আকাশে তার ফল-ফুল ও শুশ্রূষাময় ছায়া মেলে ধরাই ছিল বিশ্বভারতীর লক্ষ্য। তাতে দেশের মাটির সঙ্গে বিশ্বময়ী বিশ্বমায়ের আঁচল সহজেই মিলে যেতে পারে এক সঘন আশ্লেষে।
*ছবি সৌজন্য: Twitter, Facebook, Wikimedia
মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিশ্বভারতীতে বাংলার অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ ভবনের মুখ্য সমন্বয়ক। বেজিং ফরেন স্টাডিস ইউনিভার্সিটির আমন্ত্রিত ভিজিটিং ফেলো হিসেবে ২০১৯ সালে তিনি চিন যান। বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি, চিন্তাজগৎ এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর চর্চার বিশেষ ক্ষেত্র। 'বাকিরাত্রির ঘুম' (কাব্যগ্রন্থ), 'কোথায় আমার শেষ' (উপন্যাস), 'গোষ্ঠীজীবনের উপন্যাস' (আলোচনাগ্রন্থ ), 'উপন্যাসের যৎকিঞ্চিৎ' (প্রবন্ধ সংকলন), 'রবীন্দ্রনাথ: আশ্রয় ও আশ্রম' (প্রবন্ধ সংকলন) ইত্যাদি তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ। বেশ কয়েকটি বইয়ের সম্পাদনাও করেছেন। বিচিত্র বিষয় নিয়ে পড়াশোনা তাঁর একমাত্র প্যাশন।

























