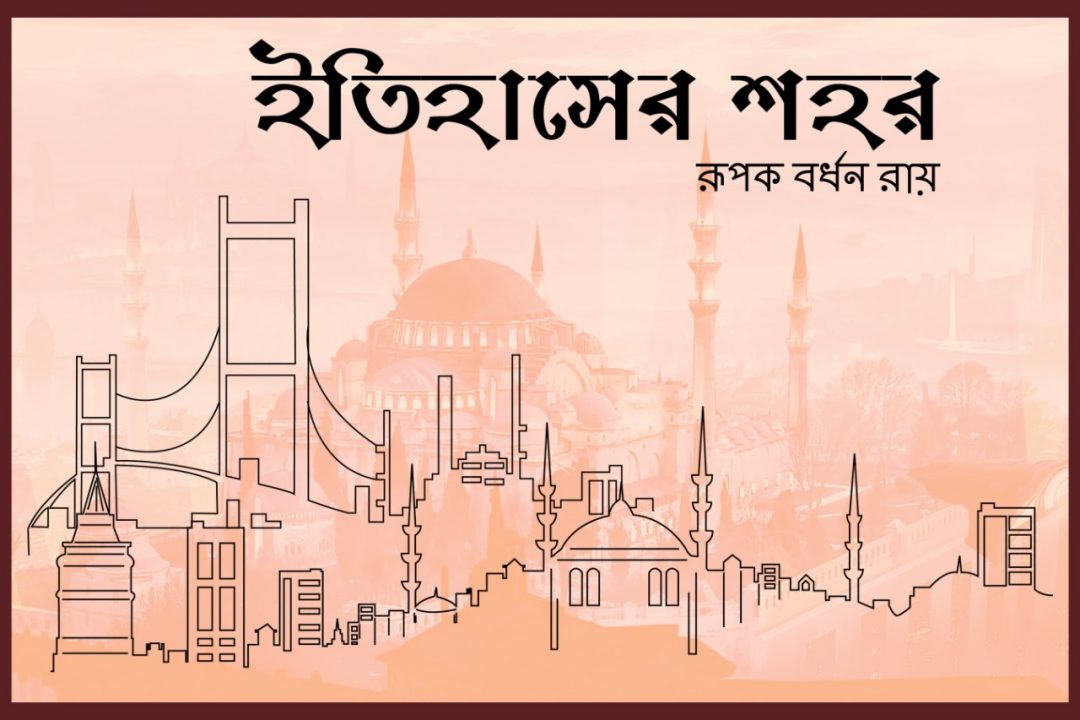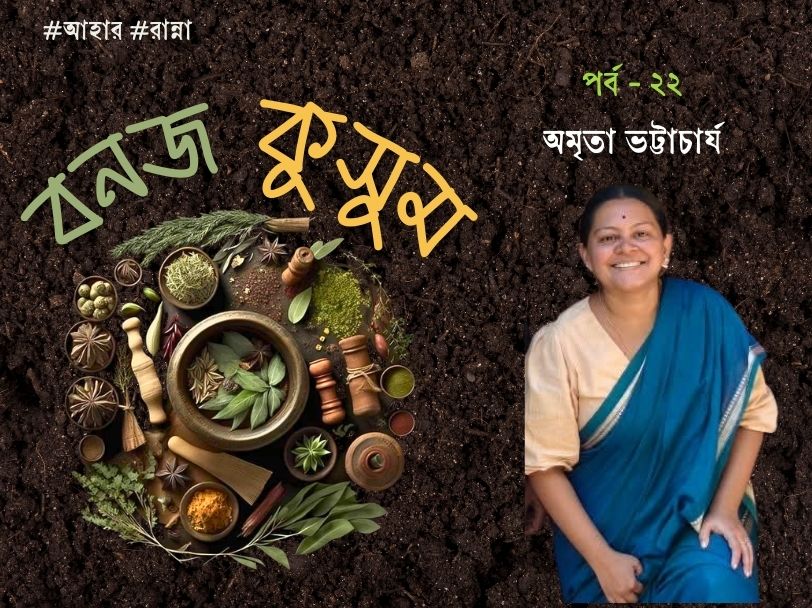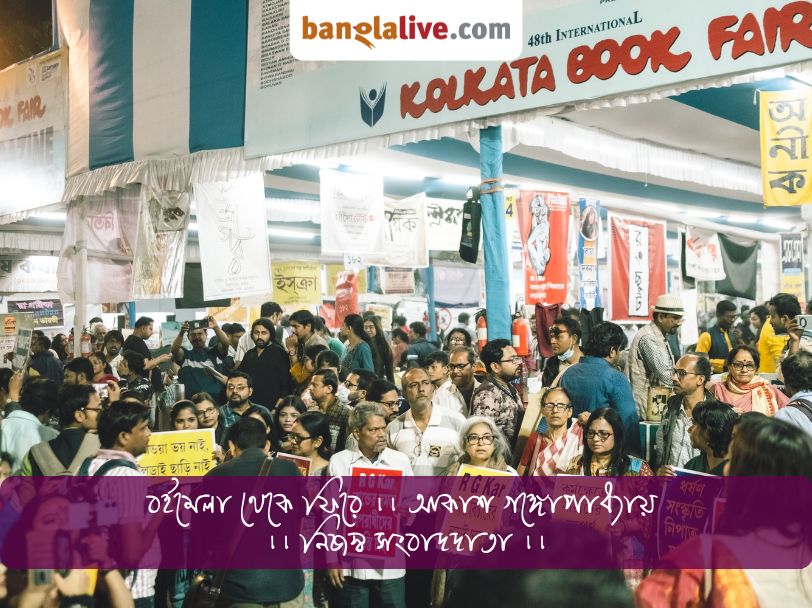এখনকার তালিন এক পেল্লায় আধুনিক শহর। চারিদিকে ঝাঁ চকচকে বাড়িঘর। রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দক্ষিণ ইউরোপের, এমনকী উত্তরের জার্মানি বা অন্যান্য দেশের প্রধান শহরগুলোর বেশিরভাগেরই রাস্তাঘাট দেখলে দিব্যি স্বদেশের কথাই মনে পড়ে। তার মূল কারণ, পৃথিবীর নানান দেশ থেকে এসে জড়ো হওয়া লোকসংখ্যা। একই দেশে তুলনামূলকভাবে কম বিত্তশালী শহরের ছবিটাই একেবারে আলাদা। তালিন সেই দিক থেকে বিত্তশালী হলেও তার নাগরিক সংখ্যা এতই কম যে রাস্তা ঘাট দেখলে, সেখানে যে মানুষ বসবাস করে তা বোঝারই উপায় নেই। বন্দর থেকে নাক বরাবর চওড়া রাস্তা পার করে আমরা এগিয়ে চলেছি পুরনো মধ্যযুগীয় সিটি-সেন্টারের দিকে।

রাস্তার দু’ধারে অত্যাধুনিক কোম্পানির অফিস, বাড়িঘর ছাড়াও যেটা চোখে পড়ে তা হল কার্পেটের মতো বিছানো এক একটা লন। সেই সব লনে কখনও কোনও পদচিহ্ন পড়েছে বলে তো মনে হল না। মিনিট দশেক হাঁটার পর রাস্তা সরু হয়ে আসে। পায়ের তলার পিচ বদলে যায় পাথর বাঁধানো পথে আর চোখের সামনে ধরা পড়ে বিরাট উঁচু এক পাথুরে দেওয়াল। আর একটু এগিয়ে গেলেই দেওয়ালটা দু’ভাগ হয়ে যায় আর সেই ভাগ হয়ে যাওয়া পথ আগলে দাঁড়ায় উঁচু মিনারের মতো মোটা থাম দেওয়া দরজা। এখন সে দরজার পাল্লা না থাকলেও এটাই পুরনো তালিনের প্রবেশপথ। এই সেই ইরুর সমাধিক্ষেত্র যার উপর দাঁড়িয়েই ড্যানিশদের হাত ধরে, ভাইকিং, রুশ, হিটলার হয়ে এ শহর তার বর্তমান কাঠামোয় বিবর্তিত হয়েছে। ধন্য মানবসভ্যতা, ধন্য মানবের স্থিতিস্থাপকতা।
প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে তা হল, এই সিটি-সেন্টার অন্যান্য মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় শহরের মতো আয়তনে তেমন সংকীর্ণ নয়। বেশ প্রশস্ত রাস্তাঘাট। দু’দিকে পুরনো দোতলা-তিনতলা বাড়িগুলির একতলায় এখন জমজমাট রেস্তোরাঁ, ক্যাফে ও দোকানপাট। অগস্ট মাস বলেই বোধহয় এখন সে সব আরও জমজমাট। রাস্তা বরাবর সোজাসুজি তাকালে আকাশের কাছাকাছি একটা লম্বা মিনারের মত দেখা যায়। ওটিই পুরনো তালিন ক্যাথেড্রালের টুম্ব। ওই চত্বরটাই আমাদের গন্তব্য।

আরও বেশ খানিকটা এগিয়ে গেলে রাস্তাটা দু’ভাগ হয়ে যায়। আমরা বাঁদিক নিয়েছি, কাজেই সেই চূড়া খানিকক্ষণের জন্য অদৃশ্য হয়েছে। এর মানে যে আমরা পুরনো শহর থেকে দূরে সরে যাচ্ছি তা নয়, এই রাস্তাও ঘুরে একই চত্বরে গিয়ে ওঠে। গোটা ইউরোপ জুড়েই মধ্যযুগীয় সমস্ত শহরের একই নকশা; “অল রোডস লিড টু রোম!” তাই আঁকা-বাঁকা পথে নানান দোকানপাট ও ওপেন এয়ার রেস্তোরাঁ পেরিয়ে আমরা অবশেষে একটা খোলা চত্বরে এসে পড়েছি। এটাই পুরনো তালিন শহরের সিটি সেন্টার।
অন্যান্য মধ্যযুগীয় টাউন সেন্টার, যেমন প্রাগ, ফ্র্যাঙ্কফুর্ট, টুর্স ইত্যাদির সঙ্গে তালিনের একটা বিশেষ পার্থক্য চোখে পড়ে। চৌকোনো চত্বরটা জুড়ে বাড়িঘর দেখে বোঝার উপায় নেই তাদের পিছনের রাস্তায় কীভাবে যেতে হবে। এক আধটা রাস্তা যে নেই তা নয়, তবে হাতে গোনা। আর একটু খুঁজলেই চোখে পড়বে যে প্রত্যেকটা বাড়ির একতলায় একটা করে গাড়িবারান্দার মতো সুড়ঙ্গ করা রয়েছে। পর্যটক মনকে ব্রাত্য রেখে শহরের অন্দরমহলে ঢোকার এই এক দারুণ ব্যবস্থা। যেন নগরবাসী জানান দিচ্ছেন, “আপাত নয়, সত্য তালিনকে চিনে নিতে হলে আপনার খোঁজার চোখের প্রয়োজন, সে দিব্যদৃষ্টি খুঁজে পেলে তবেই অন্দরমহলে প্রবেশাধিকার। নচেৎ নয়।”
বেচারা গুলগুলি এতক্ষণ ধরে হাঁটাহাঁটির পর একটুকুও রাগেনি দেখে আমি বেশ অবাকই হয়েছি। ওর কতটুকু বয়স, তাও সারাক্ষণ প্যারাম্বুলেটারে চড়ে চুপচাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে। এইবার বেচারার একটু খাওয়াদাওয়ার প্রয়োজন। আর আমাদেরও পেটে কিছু দেওয়ার পালা। আর সেখানেই আমার পড়াশোনাটা কাজে লাগবে, সে কথায় পরে আসছি। ছায়ায় ঘেরা ছোট একফালি জায়গায় সবাইকে বসিয়ে আমি ক্যামেরা হাতে বেরিয়ে পড়লাম। গুলগুলির খাওয়াদাওয়া শেষ হতে যতটুকু সময় পাওয়া যায় আরকী। সেই আমার সাধের নগর অভিসার।

সুড়ঙ্গ দিয়ে ঢুকতেই শান্ত নিরিবিলি পাড়া চোখে পড়ে। লাল, হলুদ, গোলাপি বাড়ি। তিন চারটে বাড়ি মিলিয়ে একটা করে সর্বজনীন গৃহস্থ দালান। বেশিরভাগ বাড়ির দোতলার বারান্দা বা জানলা থেকে গুলঞ্চলতার মত লতা ঝুলে রয়েছে। কয়েকটায় নানা রঙের ফুল। একটা মিষ্টি গন্ধ আসছে। হয়তো কোনও এস্তোনীয় প্রণয়িনী স্নান সেরে আতরের ভাঁড়ার উপুর করেছেন…! এক্ষুণি বারান্দায় এসে নীচে অপেক্ষমান প্রেমিকের দিকে চেয়ে স্মিত হাসবেন। এইসব আকাশ বাতাস কাল্পনিক গল্পগাছার কথা ভাবতে ভাবতেই চোখে পড়ে একটুকরো ক্যাফে আর তার সঙ্গে বাড়িতে বানানো চকোলেটের দোকান।
আরও খানিকটা এগিয়ে গেলাম। আসলে পর্যটন চত্বর ছেড়ে যতটা ভিতরে ঢোকা যায় ততই নগর-হৃদয়ের কাছাকাছি চলে যেতে পারি, এ আমার চিরন্তন ধারণা। যত দিন গেছে, যত নতুন নতুন শহরের বুকে কান পেতেছি, সে ধারণা আরও দৃঢ় হয়েছে। চকোলেটের দোকান পেরিয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে যেতেই রাস্তাটা দু’ভাগ হয়ে গেছে। এই জায়গাটা খানিকটা আমাদের চণ্ডীমণ্ডপের মতো। একটা কুয়ো, তার পিছনে চণ্ডীমন্দিরের মতো ছোট একটা প্রার্থনা করবার জায়গা। দু’ধারের রাস্তাই সবুজে ঢাকা। বড় গাছের ছায়ায় বসে আড্ডা মারার জন্য গোটাকয়েক বেঞ্চি। পৃথিবীর সর্বত্রই বুঝি শান্ত নাগরিক যাপনের রূপ এমনই। এবার ফেরার পালা। আমি সাধারণত লেসার টাউনের দিকটায় যেতে পছন্দ করি বেশি। প্রাগের লেসার টাউনের বইয়ের দোকানে খুঁজে পাওয়া রত্নের কথা তো আপনাদের আগেই বলেছি। তবে এ যাত্রায় তা হওয়ার নয়। বাকিরা সবাই অপেক্ষায় রয়েছে। এবার কিছু পেটে দেওয়ার পালা। সে কথায় আসা যাক।
উত্তর ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশের আবহাওয়াতেই শরীর গরম রাখার জন্য যা প্রয়োজন পড়ে, তার মধ্যে প্রথমটি হল মদ বা সুরা আর দ্বিতীয়টি মাংস। মাংস বলতে মুরগি বা টার্কি নয়, এক্কেবারে রেড মিট। ইউরোপের এই দিকটায় সেই মাংস আসে ষাঁড় আর এল্ক চাষের মাধ্যমে। মধ্যযুগ এই ট্রেড রুটের মধ্যবর্তী নানা শহরে বহু ব্যবসায়ী ও সদাগর এসে দিনকয়েকের জন্য বাসা বাঁধতেন। তাদের বসবাস ও মনোরঞ্জনের জন্য প্রাগ শহরের মতোই নানা ছোটখাটো মোটেল যেমন তৈরি হয়েছিল, তেমনি গড়ে উঠেছিল কিছু খানাপিনার আখড়া। সেগুলির নাম টেভার্ন।

এই টেভার্নগুলি সাধারণত মহিলারা দেখাশোনা করতেন। ইতিহাসে তাঁদের নাম টেভার্ন ফ্রাম্প। একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে জার্মান ভাষায় ‘ফ্রাউ’ মানে মহিলা, আর নর্ডিক ভাষার প্রতিপত্তির ফলে ‘ফ্রাম্প’ মানেও তাই। মধ্যযুগীয় পুরুষতান্ত্রিক বর্বরতার হাত থেকে নিজের সুরক্ষা ও দোকানের সুরক্ষা নিশ্চিত করার তাগিদে টেভার্ন ফ্রাম্পদের বেশ খিটখটে মেজাজ রাখতে হত। টেভার্নের নিয়মনীতিও তিনিই ঠিক করতেন। শুধু তাই নয়, অতিথিরা কোনও কারণে বিরক্ত হলে বা তাদের একঘেয়ে লাগলে ফ্রাম্প তাদের নানা গল্প শুনিয়ে মনোরঞ্জন করতেন। এই টেভার্নেই ছিল তাঁদের রাজত্ব, আর আগত অতিথিরা তাঁদের প্রজা, যাদের তিনি খাওয়াবেন, দাওয়াবেন, বকবেন, গল্প শোনাবেন আবার ভালও বাসবেন!

তালিনের পরিকল্পনা হওয়ার পর থেকেই মনে মনে ইচ্ছা ছিল এমন একটা টেভার্নে যদি লাঞ্চ সারা যায়? বিশেষ আশার আ্লো দেখা না গেলেও আসার আগেরদিন রাতে খেয়াল হল, এখানে ১৪৭৫ সালে তৈরি এক টেভার্ন এখনও রীতিমত রমরম করে চলছে। খাবারের খোঁজ চলছে। এমন সময় হঠাৎই আমাদের চোখে পড়ল একটা নাম; ইংরেজিতে যার অর্থ “থার্ড ড্রাগন”। পর্যটকদের টুপি পরিয়ে টাকা আদায় করার জন্য এই ধরনের নানা নামের বুজরুকি পৃথিবীর সমস্ত দেশেই দেখেছি। কাজেই আর একটু খোঁজ নেওয়া প্রয়োজন।

কপাল ভাল, এক এস্তোনিয়ান পথিক জুটে গেল। আর তাঁর কাছ থেকে শুনলাম যে দোকানটা পর্যটন চত্বরের কোণার দিকে হলেও তালিনের বহু মানুষ এখানে খাওয়াদাওয়া করতে আসেন, এবং তার বয়স নয় নয় করে প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছরের কাছাকাছি। একথা শুনে সবাই উত্তেজিত, আর আমি? নেহাত আশেপাশে অত লোক বলে, নাহলে আমায় লোকে সেদিনই একবিংশ শতাব্দীর আর্কিমিডিস ভেবে বসত! আছে! আছে! আমার টেলিপ্যাথির জোর আছে!
দোকানের মধ্যযুগীয় কাঠামো এখনও একইরকম রাখা। বসার জায়গা, খাবার পরিবেশন করবার বাসন পত্র সবই সেই বহু ব্যবহারে ভাঙাচোরা, চটা ওঠা। ভিতরে দু’ তিনজন টেভার্ন ফ্রাম্প। সেই সময়কার আবহাওয়া ধরে রাখতে কটমটে চাহনি আর খটমটে মেজাজ উভয়েই জিইয়ে রেখেছেন দেখলাম। এছাড়াও টেভার্নের ভিতরে বড় করে একটা বোর্ড টাঙানো আছে। তাতে যা লেখা তার বাংলা মানে দাঁড়ায়
“টেভার্ন ফ্রাম্প হইতে সাবধান! তীক্ষ্ণ জিহবা, তবে উষ্ণ হৃদয়!”

কিন্তু খাব কী? এক ফ্রাম্প বেশ বাজখাই গলায় বললেন, “এল্ক সুপ, অক্স মিট সসেজ আর ওই যে ব্যারেল দেখছ, ওর থেকে ওই তিন হাত লম্বা কাঁটাটা দিয়ে যত পার পিকল্ড শশা তুলে নাও।”
আমিও ঘাবড়ে টাবড়ে গিয়ে সুড়সুড় করে সেই খাবারই অর্ডার করে দোকানের বাইরে রাখা বেঞ্চে এসে সবার সঙ্গে বসে পড়লাম। খাবারটা মুখে তোলার পর তার মহিমা টের পাওয়া গেল। আহা! সে কি কথায় বোঝানো যায়? তেল চুপচুপে টাটকা সসেজ আর গরম গরম এল্কের মাংসের টুকরোয় ভরা স্টুর স্বাদ বুঝতে হলে মশাই একবার ফ্রাম্পধামে আপনাকে ঢুঁ মারতেই হবে।
ড. রূপক বর্ধন রায় GE Healthcare-এ বিজ্ঞানী হিসেবে কর্মরত। ফ্রান্সের নিস শহরে থাকেন। তুরস্কের সাবাঞ্চি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করেছেন। বৈজ্ঞানিক হিসেবে কর্মসূত্রে যাতায়াত বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে। লেখালিখির স্বভাব বহুদিনের। মূলত লেখেন বিজ্ঞান, ইতিহাস, ঘোরাঘুরি নিয়েই। এ ছাড়াও গানবাজনা, নোটাফিলি, নিউমিসম্যাটিক্সের মত একাধিক বিষয়ে আগ্রহ অসীম।