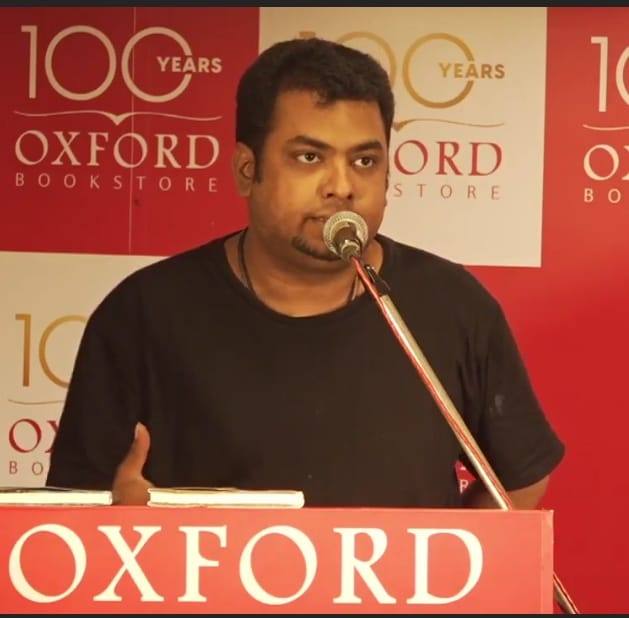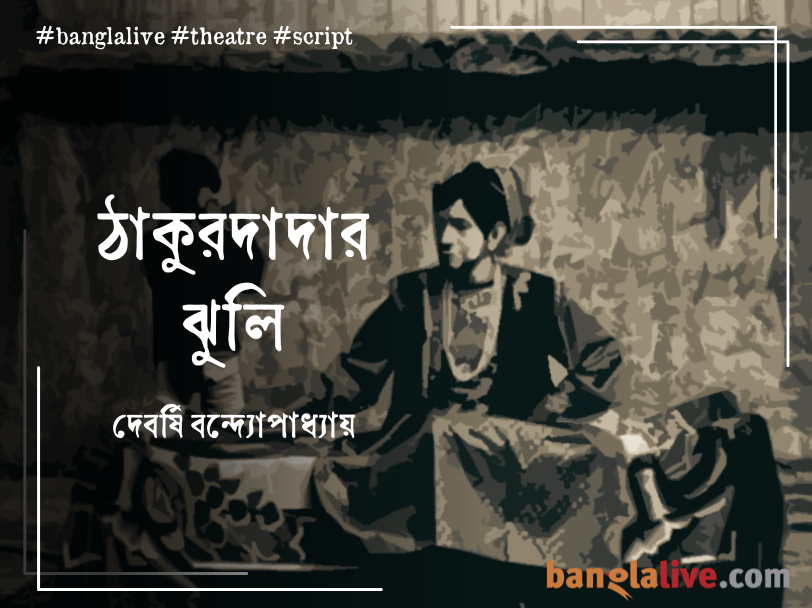সাম্প্রতিক কালের জনপ্রিয় সিনেমা(Cinema) বা থিয়েটারের(Theatre) বেশিরভাগই সেকেলে সম্পত্তি। দাদুর জুতো জামা বা জহরকোট। তা সে উৎপল দত্তই হোক বা মৃণাল সেন বা উত্তম কুমার, সত্যজিৎ রায় বা ঋত্বিক ঘটক অথবা সুকুমার রায়। মৌলিক সিনেমা, থিয়েটার, গান থেকে ক্রমশই আমাদের সরে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান বিরোধী দু’দলই নিজে কিছু লিখে প্রযোজনা করার প্রবণতাকে এড়িয়ে যেতে চাইছেন। এমনকি, ক্লাসিককে আজকের দিনে ফেলেও অসাধারণ নতুন চেহারা দেওয়া যায়, তা থেকেও খুব জরুরি কোনও কাজ চোখে পড়ছে না। তর্ক করতেও ঠাকুরদাদার থলি। বেশিরভাগই, পুরোনো বোতলে নতুন মদ। প্রতিবাদ বলতে সেই নবারুণ, আর প্রেম বলতে এখনও জীবনানন্দ! আর বেস্টসেলার বলতে এখনও থ্রিলার…
কেন ঘটছে এমন? আত্মবিশ্বাসের অভাব? নাকি, বাজার ধরার সুলভ ছক? তুলনায় কম বিখ্যাত শিল্পীরা কিন্তু নিজেদের লেখা থেকেই সিনেমা বা থিয়েটার করছেন অনেকেই। তাঁদের আত্মবিশ্বাসের অভাব ঘটছে না। আর যদি ধরেই নেওয়া যায়, সেকেলে কাজ করে বাজার ধরার ছক, তাহলে আপামর ৮ থেকে ৮০-র দর্শক হঠাৎ এত নস্টালজিয়াপ্রেমী হয়ে গেলেন কেন?
সাম্প্রতিক গাজা বা সন্দেশখালি বা রামমন্দির, কিছুই কি দাগ কাটতে পারছে না আর?
লেখার শুরুতেই যে পূর্বতন খ্যাতনামা ব্যক্তিদের নাম লিখলাম, তাঁরা প্রায় সকলেই নিত্য সিনেমা বা থিয়েটারের কাজ করলেও লেখার সাথে সরাসরি তাঁদের যোগাযোগ ছিল। কেউ লেখা থেকে সিনেমা বা থিয়েটারের দিকে চলে গেছেন তো কেউ পাশাপাশি লিখে গেছেন অসংখ্য প্রবন্ধ বা কবিতা। স্বাধীনতা পরবর্তী একাধিক পত্র-পত্রিকা বেরোচ্ছে নানা খ্যাতনামা পরিবার থেকে। ঠাকুরবাড়ি, রায়বাড়ি বা কবিতা ভবন প্রমুখ অজস্র বাড়ির নাম করা যায় এ-প্রসঙ্গে। অর্থাৎ লেখা, মৌলিক লেখাই ছিল, খ্যাতনামাদের শিল্পযাপনের মৌলিক প্রণোদনা। লেখা এমন এক বিষয় যার সঙ্গে সরাসরি রাজনীতি ও সংস্কৃতি এইভাবে নিত্য জারি রাখত তার সংলাপ।
বিগত দশ বারো বছরের রাজনীতি থেকে মানুষ মুখ ফিরিয়েছে নানা কারণে। বুদ্ধিজীবী শব্দটাও কার্যত গালাগাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। নাটকের কথা বললে এখনও উইঙ্কল টুইঙ্কল বা তিস্তাপারই প্রবাদের মতো চলে আসে। তারপর কি নতুন কাজ হচ্ছে না? অজস্র হচ্ছে। কিন্তু সামগ্রিক পরিস্থিতির কারণেই হয়তো মানুষের নতুন কিছুর প্রতি আস্থা হারিয়েছে এবং যা কিছু পুরোনো তা নস্টালজিয়ার সঙ্গেই গ্রহণ করতে এক ধরণের কমফোর্ট পাচ্ছে মানুষ।
বিগত দশ বারো বছরের রাজনীতি থেকে মানুষ মুখ ফিরিয়েছে নানা কারণে। বুদ্ধিজীবী শব্দটাও কার্যত গালাগাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। নাটকের কথা বললে এখনও উইঙ্কল টুইঙ্কল বা তিস্তাপারই প্রবাদের মতো চলে আসে। তারপর কি নতুন কাজ হচ্ছে না? অজস্র হচ্ছে। কিন্তু সামগ্রিক পরিস্থিতির কারণেই হয়তো মানুষের নতুন কিছুর প্রতি আস্থা হারিয়েছে এবং যা কিছু পুরোনো তা নস্টালজিয়ার সঙ্গেই গ্রহণ করতে এক ধরণের কমফোর্ট পাচ্ছে মানুষ। এর অবশ্য আরেকটা কারণ, প্রযুক্তিগত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের হাতে এত অপশন, নিবিড় অভিনিবেশের অভ্যাসও তাই বদলে গিয়েছে।
কিন্তু ফেসবুকে বা ইউটিউবে তরুণ প্রজন্ম বারবার সমকাল নিয়ে কথা বলছে। তাতে মতামতও দিচ্ছেন নানা বয়সী মানুষ। রিয়্যাক্ট করছেন। এই প্রতিক্রিয়া তাহলে অন্যান্য মাধ্যমের ক্ষেত্রে শিথিল হয়ে যাচ্ছে কেন! কেন অনুরাগ কাশ্যপ এসে খিস্তি মেরে যাচ্ছেন বাংলা ছবিকে! কেনই বা বাংলা ছবির পাশে দাঁড়ানোর কথা মন্ত্রের মতো বলে যেতে হচ্ছে! আমাদের মৌলিক চিন্তার কি এতই আকাল দেখা দিল! এত এত সাহিত্য ও সিনেমার ঐতিহ্য কি আমাদের কিছুই বলছে না!

বলছে। তাই তো ফেলুদা আর ব্যোমকেশ নিয়ে এই বিক্রিবাটার চৈত্রসেল। বছরে তিরিশবার চিত্রাঙ্গদা আর শ্যামা-শাপমোচনের অশ্রুমোচনের কথা কত আগে সুমন বলেছিলেন। দেখুন, এখনও আমাকে সেই সুমনের কথাই বলতে হচ্ছে, কারণ নতুন গান শুনে যে স্মৃতি তৈরি হবে, তা ঘটেনি। কারণ যাঁরা নতুন উপন্যাস বা গান লিখছেন, তাঁদের কাজ আমাকে ভরসা দিচ্ছে না। কেন দিচ্ছে না? কারণ আমার প্রজন্মের যে সব সংকট, যেখানে শহর ছেড়ে যাওয়া আমার বন্ধুরা আছে, কর্পোরেট রাজনীতি আছে, রাজনীতির দুর্নীতি আছে, সমলিঙ্গের প্রেমের কোণঠাসা হওয়া আছে, বিয়ের ধারণা অচল হয়ে গেছে, প্রযুক্তির অসুস্থ আস্ফালন আছে সময়ের এই টক্সিক চেহারা, এই সাইকোটিক চেহারা যা ধর্মের মোড়কে লুম্পেনাইজেশানের হাত ধরে ব্যাপক অংশের মানুষের মান্যতা চোরাগোপ্তা পথে আদায় করছে, তাকে খামচে ধরতে পারছে না কেউ। অবশ্যই এইসব নিয়ে নিয়মিত খিস্তি করছে ফেসবুকে অনেকেই। খাপ পঞ্চায়েত বসছে। কিন্তু সাহিত্য বা শিল্পের বিস্তারে সেই আধার খুলে যাচ্ছে না। কারণ তার জন্য পড়াশোনা লাগে। সাহিত্যের হাজার বছরের ইতিহাসটা জানতে হয়। একটু ধৈর্য্য, সময়, নিষ্ঠা, মনোনিবেশ লাগে। তবে না ধরা দেবে রূপ। তবে না দেখা পাব নিজের ভাষার! একা থাকতে হবে তার জন্য কিছুক্ষণ। সারাক্ষণ নিজের মুখের ছবি ফেসবুকে পোস্ট করে গেলে কীভাবে হবে!
আরও পড়ুন : কবেকার কলকাতা শহরের পথে
বাংলার নতুন বছর আরেকবার চলে এল। বাংলা ভাষাটাকে সবদিক থেকে শেষ করে দেওয়া গেছে। বাঙালি মধ্যবিত্তের ছেলেমেয়েরা আর বাংলা মাধ্যমে পড়ে না। শ্রেণিগত ভাবে ইংরেজি মাধ্যম তাঁদের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য বহু বছর ধরেই। এই পয়লা বৈশাখেও তাদের অনেকেই আবার শহরজুড়ে সেমিনারে ‘বাঙলা ভাষার এ কী হল!’ বলে ফাটিয়ে দেবেন। কিন্তু তাতে লীলা মজুমদারের চেয়ে মারবেল কমিক্সের গুরুত্ব এক চুলও বাড়বে না। বাংলায় চাকরির অভাবে যারা বাইরে থাকতে বাধ্য হচ্ছে, তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়বে না। শুধু বক্তৃতা দেব আমরা। যেমন শুধু নাটক আর সিনেমা করে যাব আর ফেসবুক পোস্টে বলে যাব, নিজেরা কত মহান। বন্ধুরা লাইক দেবে। পনেরো সেকেন্ডের জন্য আমরা নিজেদের এ যুগের উৎপল বা উত্তম কুমার ভাবব। ঘোর কেটে গেলে, আত্মবিশ্বাসের অভাব হবে। কারণ আমরা জানি, আমরা গভীর বা নতুন কথা বলতে পারছি না। তাই দাদামশাই বা ঠাকুরদার আকাচা জহর কোটের খোঁজে ঠাকুরদালানের নীচের গুপ্তধন খুঁড়ব। নাহলে টিকিট বিক্রি হবে না।
কৃতজ্ঞতা স্বীকার: সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়
পেশা মূলত, লেখা-সাংবাদিকতা। তা ছাড়াও, গান লেখেন-ছবি বানান। শখ, মানুষ দেখা। শেল্ফ থেকে পুরনো বই খুঁজে বের করা। কলকাতার রাস্তা ধরে বিকেলে ঘুরে বেড়ানো।