দুটো বেড়ালনী এসেছে রমাকান্তদের পাশের পাড়ায়। কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসল, কেউ জানে না। শুধু আসল কথাটা এই, যে দু’জনেই পরমাসুন্দরী| রমাকান্তর তাই সম্প্রতি কিঞ্চিৎ চিত্তচাঞ্চল্য ঘটেছে। সে অভিজাত সুদর্শন যুবক। তাবড় তাবড় বুড়োহাবড়া, দড়িপাকানো চেহারার মুনিঋষিরাই উর্বশী-মেনকা-রম্ভাকে দেখে আদেখলেপনা করেন; সেখানে রমাকান্ত তো লোভনীয় সুপাত্র!
রূপের বিচারে এই দুটি মার্জারনীর মধ্যে যেটি উনিশ, তার নাম লাবণ্যপ্রভা আর যেটি বিশ, বিধুমুখী। লাবণ্যপ্রভার তো যা রূপ, এক দেখাতেই পাত্রপক্ষ বিয়েতে রাজি হয়ে যাবে আনন্দে থাবা ঘষতে ঘষতে। আর বিধুমুখীর জন্য নাকি স্বয়ম্বরসভার আয়োজন করা হচ্ছে খুব শিগগিরই। তবে দু’জনেরই বেজায় ডাঁট। ওই তো একফুটিয়া শরীর, তাতেই সারাক্ষণ রূপের গুমোরে মটমট করছে! এ তল্লাটের লোকজন বেড়াল-কুকুরের সঙ্গে সেলফি তুলতে খুব ভালোবাসে। কেন, ভাবছেন তো? আরে বাবা, এটা হল দক্ষিণ কলকাতার বনেদি অঞ্চল। বেশিরভাগ বাড়িতেই কুকুর-বেড়াল-পাখি-বিলিতি মাছের কাচঘর। এখানে আয়েসি কুকুর, সুখী বেড়াল, তিরিক্ষি টিয়াপাখি… এদের সব আলাদা আলাদা নাম আছে। এই যেমন রমাকান্ত সরকার হল সরকারবাড়ির হুলো, ক্যামেলিয়া বোনার্জি হল বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের মাদী ল্যাব্রাডর, গোঁসাইবাড়ির বুড়ো খিটখিটে ময়নাটার নাম হরেকৃষ্ণ। এখানে যে কোনও বাড়ি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে বলা হয় রমাকান্ত নিবাস, ক্যামেলিয়া ভিলা, হরেকৃষ্ণ কুটির।
শুধু কি এটুকুই নাকি? রমাকান্তর নামে ফি বছর তার জন্মদিনে বিলিতি খেলনা আর গ্রিটিংস কার্ড পাঠায় সরকার বাড়ির নাতজামাই, সেই খাস বিলেত থেকে পার্সেল করে। সেখানে পেটমোটা খামে পষ্ট করে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা থাকে, ‘মিস্টার রমাকান্ত সরকার, কেয়ার অফ শ্রীমতী তারাসুন্দরী সরকার’ ইত্যাদি ইত্যাদি। পার্সেল দিতে এসে বুড়ো ডাকপিওন হরেন তার ইয়া বড়ো বড়ো তরমুজের বিচির মতো দোক্তা খাওয়া দাঁতে ‘হেঁ হেঁ’ করতে করতে প্রতিবারই এক কথা বলে, ‘রমাবাবুর নামে পার্সেল এয়েচে। তেনাকে ডাকুন, সই করে তবে নিতে হবে!’একবার তো ভোট চাইতে এসে আনকোরা নতুন এবং ভোটে জিতে গেলে হলেও-হতে-পারেন মন্ত্রীমশাইয়ের হাতজোড় করে সে কী অনুনয়-বিনয় ! ‘অনুগ্রহ করে রমাকান্তবাবুকে একটিবার ডেকে দিন; আমি নিজে ওঁকে অনুরোধ করব, যাতে আমাকে ভোট দেন!’ আসলে নেতাটির দোষও ছিল না তেমন। সকলের মুখেই তো শুনছিলেন, ‘এটা রমাকান্ত সরকারের বাড়ি!’
তা হ্যাঁ, যে কথা হচ্ছিল। এই বেড়ালনী দুটো কিন্তু কাউকে মোবাইল ফোনের ক্যামেরা বাগিয়ে ধরতে দেখলেই রাগে গরগর করে। কেউ আহ্লাদ করে চুকচুক শব্দ করে ডাকলে ঠ্যাকার দেখিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। এখন কথা হল, বিধুমুখীর স্বয়ম্বরসভায় কোন্ কোন্ বেড়াল আসবে! পাড়ার আর বেপাড়ার যত খেঁকুটে, রোঁয়া ওঠা, ছোঁচা, পালোয়ান, জন্মপ্রেমিক, আলসে, হুঁকোমুখো হুলোর দল? বিধুমুখীর হাবভাবে যা বোঝা যায়, তার একটু দেখতে ভালো আর দেমাকি হুলো পছন্দ; লেজ উঁচিয়ে, নিজের উপর আস্থা অটুট রেখে সরু কার্নিশ বেয়ে তরতর করে এগিয়ে যাওয়া হুলো। সারা বেড়ালকুল যাকে সমীহ করবে। পুরোপুরি আত্মনির্ভর হুলো! গায়ের চিকন লোমে অক্সিঅ্যাসেটিলিন ফ্লেমের মতো রোদ্দুর পড়লে চিড়িকচিড়িক ঝিলিক মারবে।

হুলোর পরিচয় কীসে? মেজাজে আর লেজে। লেজটি যেন বাহার দেওয়া হয়। মুখশ্রী? সে একটু এদিক ওদিক হলে মানিয়ে নেবে বিধুমুখী। পুরুষমানুষের, থুড়ি হুলোবেড়ালের ব্যক্তিত্বই আসল! মোদ্দা কথাটি হল, রোয়াব থাকা চাই! রাজাবাদশার মতো কেতা; ওই মানুষদের পাড়ার মস্তানরা যেমন, মানে হাতকাটা নেলো, ল্যাংড়া শিবু, ক্ষুর পাঁচু ওইরকম নয়! এই ধরো মহারাজা বিক্রমাদিত্য, সম্রাট অশোক, টিপু সুলতান … এমন। লাবণ্যপ্রভা একটু মনমরা। তার বেলায় সাধারণ দেখাশুনো করে বিয়ে, আর যমজ বোনটার জন্য স্বয়ম্বরসভা ! তবে কিনা যে যেমন কপাল করে আসে!
ছাদের আলসেতে সার সার হুলো বসে। এক একজন এক এক পদের! বিধুমুখীর নরম ঠোঁটে ধরা ‘বরমাল্য’, অর্থাৎ কোন গেরস্ত বাড়ি থেকে চুরি করে আনা একটুকরো তেলাপিয়া মাছ। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, বরফচাপা মাল। যে হুলোর সামনের থাবাজোড়ার কাছে বিধুমুখী লজ্জা লজ্জা মুখ করে মাছের টুকরোটি রাখবে, সেই বেড়ালের ভাগ্যেই শিকে ছিঁড়বে। তা ছিঁড়ল ! পাশের পাড়ার হুলো রমাকান্ত । খুবই বনেদি আর বড়লোক বাড়ির পেয়ারের পুষ্যি। যেমন ব্যক্তিত্ব, তেমনই রূপ! দেখলে মনে ভয়, ভক্তি, প্রেম সবই জাগে। বিধুমুখী লাজুক লাজুক মুখে তার হবু ইহকাল-পরকালের থাবার সামনে নৈবেদ্যের মতো মাছের টুকরোটি রাখলে সারা মহল্লা কাঁপিয়ে ‘ম্যাও ম্যাও’ করে সমবেত বেড়ালের দল অভিনন্দন জানাল।
এটা হল দক্ষিণ কলকাতার বনেদি অঞ্চল। বেশিরভাগ বাড়িতেই কুকুর-বেড়াল-পাখি-বিলিতি মাছের কাচঘর। এখানে আয়েসি কুকুর, সুখী বেড়াল, তিরিক্ষি টিয়াপাখি… এদের সব আলাদা আলাদা নাম আছে। এই যেমন রমাকান্ত সরকার হল সরকারবাড়ির হুলো, ক্যামেলিয়া বোনার্জি হল বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের মাদী ল্যাব্রাডর, গোঁসাইবাড়ির বুড়ো খিটখিটে ময়নাটার নাম হরেকৃষ্ণ। এখানে যে কোনও বাড়ি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে বলা হয় রমাকান্ত নিবাস, ক্যামেলিয়া ভিলা, হরেকৃষ্ণ কুটির।
নতুন বরমশাই একটু শুঁকে মাছের টুকরো থেকে সামান্য একটু কোণ ভেঙে নিয়ে মুখে তুলল। বাকিটা প্রসাদ। বিধুমুখীর জন্য। লাবণ্যপ্রভা মলিন মুখে এক কোণে দাঁড়িয়ে। তার দিকে তাকিয়ে বরমশাই গম্ভীর গলায় বলল, ‘হিঁয়াও।’ অর্থাৎ ‘ইধর আও।’ ক্যাটওয়াক করতে করতে লাবণ্যপ্রভা এসে দাঁড়াল সামনে। রমাকান্ত থাবা দিয়ে নিজের গোঁফ আঁচড়ে ঘোষণা করল, ‘ঘরওয়ালি তো হল, কিন্তু পুরোর সঙ্গে যৌতুক হিসেবে আধা … মানে সেটাও কি মুখ ফুটে চেয়ে নিতে হবে?’ বিধুমুখী বেজার হল, লাবণ্যপ্রভা লজ্জায় আরও ফিকে ফিকে গোলাপিরঙা হল। বরমশাই উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল। তার মোসাহেব যত ছোঁড়া, বুড়ো আর আধদামড়া বেড়ালের দল ‘ম্যাও ম্যাও’ শব্দে জয়ধ্বনি দিতে লাগল। কান পেতে শুনলে যার মানে দাঁড়ায়, ‘জয় মহারাজ রমাকান্তর জয় ! জয় মহারাজ শালীবাহনের জয়!’
যতক্ষণ এইসব কাণ্ডকারখানা চলছিল, সব বেড়ালদের মধ্যমণি হয়ে মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হতে বেশ ভালোই লাগছিল রমাকান্তর। কিন্তু এবার যেন একটু একটু অস্বস্তি হচ্ছে! বিয়ে তো হয়ে গেল; এখন দু-দুটো বৌকে নিয়ে সে যাবে কোথায়? সরকারবাড়িতে বিশাল হাঙ্গামা লেগে যেতে পারে জোড়া বৌ দেখলে। আর বিধু আর লাবণ্যর পক্ষেও একই বাড়িতে বাস করা নেহাত সহজ হবে না। এ তো আর বাংলা সিরিয়াল নয়, যে যখন যে পারছে আসলের সঙ্গে সুদ আদায় করে ছাড়ছে! ওসব বিজ্ঞাপনে হয় ; ‘বাই ওয়ান, গেট ওয়ান ফ্রি!’ সব কথাই তো কান পেতে শোনে রমাকান্ত! এই তো সেদিন বড়োজেঠু ছোটকাকে বলছিল,‘বিশু, একটা কথা জেনে রাখিস। এই বাজারে কোনও কিছুই মুফতে মেলে না। জানবি, কোথাও না কোথাও একটা গ্যাঁড়াকল ঠিক লুকিয়ে আছে!’ ইস, অতটা লোভ করা উচিত হয়নি ! লাবণ্যপ্রভা কী কী ঝামেলায় ফেলবে, কে জানে!
আর সত্যি বলতে কী, এটা বনেদি বাড়ি। এ বাড়ির ছেলেপুলেরা ‘লবে’ পড়ে বিয়ে-থা করে না। তাদের রীতিমতো দেখেশুনে সম্বন্ধ করে তবেই বিয়ে হয়। কানাঘুষোয় রমাকান্ত শুনেছে, এ বাড়িতে চার পুরুষ আগে নাকি ‘হাপ-লব’ গোছের কিছু একটা ঘটেছিল। মানে কর্তা-মা তারাসুন্দরীর শ্বশুরমশাই। তবে সবটাই ঠারেঠোরে বলে বৌ-মেয়েরা। বলে, আর মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসে। তাঁর নাম ছিল বাবু শ্রী ব্রজদুলাল সরকার। বৈঠকখানা ঘরে একটা পেল্লায় রঙিন ছবিও টাঙানো আছে। পালাপার্বণে ছবিতে মালা পরানো হয়। সা-জোয়ান চেহারা, জম্পেশ পাকানো গোঁফ, বাবরি চুল, হাতে রুপোর মুণ্ডি দেওয়া ছড়ি। পরনে হিরে-বসানো সোনার বোতাম আঁটা শৌখিন পাঞ্জাবি আর ফরাসডাঙার মিহি জমিনের ধাক্কাপাড় ধুতি। পায়ে শুঁড়তোলা বাহারি চটি। ওই ছবির দিকে চোখ পড়লেই রমাকান্ত মনে মনে নমো করে মাথা নিচু করে মানে মানে কেটে পড়ে!

কিন্তু এখন সে কী করবে? যা বোঝা যাচ্ছে, দুই বোনে আদায়-কাঁচকলায়। এক কাজ করলে হয়। জমাদারের যাতায়াতের জন্য বাড়ির পেছনদিকে বাগানের ভেতর দিয়ে যে লোহার ঘোরানো সিঁড়িটা আছে, তার পাশে একটা ছোট্ট খুপরি আছে ; গাছের সার, খুরপি, জলের পাইপ, ঝারি এসব ডাঁই করা থাকে। লাবণ্য ওখানেই থাকবে। সে তো আর পাটরানী নয়! আর বিধুমুখীকে সঙ্গে নিয়ে রমাকান্ত সোজা গিয়ে কর্তা-মার পায়ে হত্যে দেবে। বিধু তার রানি হতে পারে, কিন্তু কর্তা-মার তো ছিচরণের দাসী ! হ্যাঁ, দোষ অবিশ্যি রমাকান্ত করেছে! রূপ দেখে মাথার ঠিক রাখতে পারেনি; কিন্তু এই তো সেদিন বুল্টি মাস্টারের কাছে বসে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইছিল না… ‘প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, কে কোথা ধরা পড়ে, কে জানে?’ রমাকান্তরও তো সাধ হয় যে নিজের একটা ভরভরন্ত ঘর-সংসার হোক!
যেমনটি ভাবা, তেমনই কাজ। খুপরি ঘরে লাবণ্যকে গ্যারেজ করে সে গুটিগুটি তারাসুন্দরীর ঘরে এল ; পিছু পিছু বিধুমুখী। লাবণ্য গাঁইগুঁই করছিল বটে; কিন্তু তুতিয়েপাতিয়ে রমাকান্ত তাকে সামলে এসেছে। কটা দিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকুক, খাবারদাবারের অসুবিধে হবে না; তারপর কর্তা-মার মনমর্জি বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।
সত্যি রূপের জোর আছে বটে বিধুমুখীর। কর্তা-মা একটিবার দেখেই গলে জল! ‘রমাকান্ত, বে’ করে বৌ নিয়ে এলি ? আহা, দেখি দেখি! কী চাঁদপানা মুখ! দাঁড়া, সকলকে ডাকি।’ আশি শতাংশ লজ্জার সঙ্গে বিশ শতাংশ অহংকার মেশানো মুখ নিয়ে তারাসুন্দরীর পায়ে লুটোপুটি খাচ্ছিল রমাকান্ত। কিন্তু ওই যে! রবি ঠাকুর তো লিখেই গেছেন, ‘আমি সকল দাগে হব দাগী, কলঙ্কভাগী।’ তা কলঙ্কের আর বাকি রইল না কিচ্ছুটি। রমাকান্তকে দিনের মধ্যে দশবার করে খুপরি ঘরে ঢুকতে বেরতে দেখেই মালী ব্যাটাচ্ছেলের মনে সন্দেহ জেগেছিল। তিনদিনের মাথায় হাতেনাতে ধরা পড়ে গেল রমাকান্ত। সে তখন লাবণ্যপ্রভার গোসা ভাঙাতে ব্যস্ত ছিল। চেঁচামেচি শুনে তারাসুন্দরী হাঁকপাঁক করতে করতে হাজির হলেন; তাঁর কোলে বিধুমুখী। ঝটকা দিয়ে কোল থেকে লাফ মেরে নেমে গেল বিধু।
চোরের মতো মুখ করে ঘাপটি মেরে বসে আছে রমাকান্ত। কী দৃশ্য! বিধুমুখী আর লাবণ্যপ্রভা মুখোমুখি, তাদের লেজ শক্ত, পিঠ বেঁকানো, ঘাড়ের রোঁয়া ফুলে উঠেছে, দুই সতীনে চুলোচুলি লাগল বলে! তারাসুন্দরী অতি বিচক্ষণ মহিলা। বুঝতেই পারলেন রমাকান্তর টাল খাওয়া অবস্থাটা! আহা, বেচারি নিজেকে সামলাতে পারেনি! কাছাখোলা পুরুষ! ঘরে-বাইরে দু-জনকে সামলেসুমলে রাখা কি সোজা নাকি? মেলা হ্যাপার কাজ! তিনি উবু হয়ে বসে আদুরে শব্দ করে ডাকতে লাগলেন দুই সুন্দরী মেনিবেড়ালকে। খানিক পরে দেখা গেল, তিনজনেই তারাসুন্দরীর পায়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে আহ্লাদে আটখানা হয়ে।
ক্যাটওয়াক করতে করতে লাবণ্যপ্রভা এসে দাঁড়াল সামনে। রমাকান্ত থাবা দিয়ে নিজের গোঁফ আঁচড়ে ঘোষণা করল, ‘ঘরওয়ালি তো হল, কিন্তু পুরোর সঙ্গে যৌতুক হিসেবে আধা … মানে সেটাও কি মুখ ফুটে চেয়ে নিতে হবে?’ বিধুমুখী বেজার হল, লাবণ্যপ্রভা লজ্জায় আরও ফিকে ফিকে গোলাপিরঙা হল। বরমশাই উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল। তার মোসাহেব যত ছোঁড়া, বুড়ো আর আধদামড়া বেড়ালের দল ‘ম্যাও ম্যাও’ শব্দে জয়ধ্বনি দিতে লাগল।
তারাসুন্দরী বৈঠকখানায় লাল ভেলভেটের সোফায় বসে। নীচের কাশ্মীরি গালচেতে আরামে ঘুমোচ্ছে রমাকান্ত, দু-পাশে দুই বৌ নিয়ে। তারাসুন্দরী সটান তাকিয়ে রইলেন তাঁর শ্বশুরমশাইয়ের ছবিখানার দিকে। তারাসুন্দরীর শাশুড়ি চন্দ্রাননা দেবী তিন বছরের খোকা আর ছ’মাসের খুকিটিকে রেখে অকালে গত হলে ব্রজদুলাল সরকার নিজের শ্যালিকাকে বিয়ে করে ঘরে তোলেন। তাঁর নাম ছিল শোভারানি দেবী। দ্বিতীয় পক্ষেরও দুটি কন্যাসন্তান ছিল। ব্রজদুলাল যদিও নাকি ঘোষণা করেছিলেন, মা-মরা ছেলেপুলের যত্নআত্তি আপন মাসি ছাড়া কে-ই বা করবে ; কিন্তু কানাঘুষো চলেছিল, ব্রজ সরকার নাকি শ্যালিকার রূপে মোহাবিষ্ট হয়ে নিজেই তড়িঘড়ি আগ বাড়িয়ে বিয়ের প্রস্তাব দেন। শোভারানির মা-বাবা বিত্তবান বিপত্নীক জামাইয়ের বিরাগভাজন হতে চাননি।
আচমকা বিদ্যুচ্চমকের মতো কী যেন ঝিলিক দিয়ে গেল তারাসুন্দরীর মনে। নামের মিল, কাজেরও মিল ! দুহাত জড়ো করে কপালে ঠেকালেন তারাসুন্দরী দেবী। সবই তাঁর গৃহদেবতা গোবিন্দজিউর কৃপা! জয়গুরু!
*ভেতরের ছবি: Pixels, Saatchiart
ইলেকট্রনিক্সের ছাত্রী ঈশানী রায়চৌধুরী তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে ভাষান্তরের কাজে যুক্ত। নিজস্ব লেখালেখির মাধ্যম হিসেবে সবচেয়ে পছন্দ রম্য গদ্য আর ছোট গল্প | আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, ফ্রিডা কাহলো, খলিল জিব্রান, আর কে নারায়ণ প্রমুখ লেখকদের কাজ ভাষান্তর করেছেন। 'কৃষ্ণচূড়া আর পুটুস ফুল', 'আবছা অ্য়ালবাম', 'বাবু-টাবুর মা', ওঁর কয়েকটি প্রকাশিত বই।




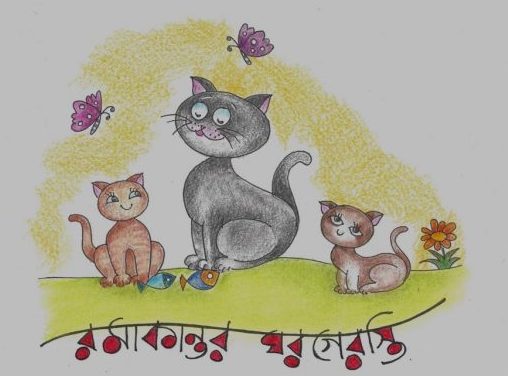





















One Response
খুব ভাল হয়েছে ।