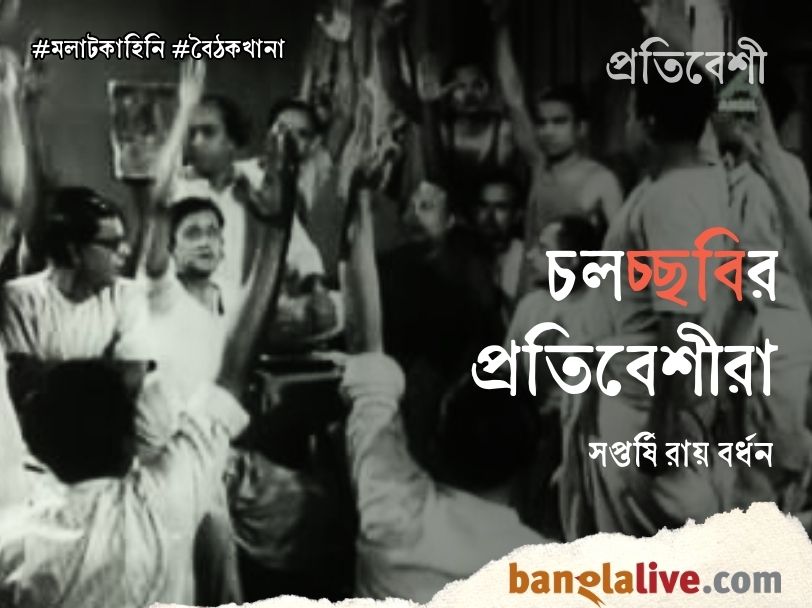বহুদিন আগে পড়েছিলাম গপ্পোটা – হালকা মনে পড়ছে, বোধহয় তারাপদ রায়ের লেখা।
পুববঙ্গের কোনও এক গ্রামে পশ্চিম বাড়ি আর দক্ষিণ বাড়ি ছিল একে অন্যের প্রতিবেশী। দুই পাশাপাশি বাসাবাড়ির মধ্যে নড়বড়ে এক টিনের বেড়া। বেড়ার শেষ মাথায় সীমান্তে একটা বিশাল আম গাছ। খুব পুরনো আর বুড়ো সে গাছ। আর এই গাছটা নিয়েই যত বিপত্তি। গাছটার দুটো নাম, দক্ষিণ বাড়িতে লালবাগের আমগাছ আর ওধারে, অর্থাৎ পশ্চিম বাড়িতে, কলমি আমগাছ। এ বাড়ির দাবী– রাজা পঞ্চম জর্জের কালে ঠাকুরদা লালবাগে বেড়াতে গিয়ে যে এক ঝুড়ি খুব মিষ্টি আম নিয়ে এসেছিলেন তার ফেলে দেওয়া আঁটি থেকে এই গাছ হয়েছিল। ও বাড়ির দাবী, ঠাকুমা নাকি অনন্তকাল আগে ধামরাইয়ের রথের মেলা থেকে স্বহস্তে কিনেছিলেন এই কলমের চারা। দুটি পুরনো সংসার, একই চৌহুদ্দির মধ্যে, দুই পড়শির বাস নয় নয় করে একশ বছরের কাছাকাছি, ভারি মধুর সে সম্পর্ক। কিন্তু একটা টোকো আম গাছকে ঘিরে, সম্বৎসর এক বিবাদ লেগেই থাকত দুই পড়শির মধ্যে। এই সব মধুর সম্পর্ক, পাতানো আত্মীয়তা নষ্ট হয়ে যেত কালবোশেখির ঝড়ে। ঝড়ের বাতাসে যখন টুপ টুপ করে আম ঝরে পড়ত দু’বাড়ির উঠোনে, তুমুল হুলুস্থুল পড়ে যেত। দুপক্ষই দাবী করত সব আম তাদেরই প্রাপ্য কারণ গাছটা তাদের। একবার আমিন ডেকে জরিপ করে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হয়েছিল। তখন নাকি দেখা যায় দু’বাড়ির সীমানা চলে গেছে সরাসরি আমগাছের বিশাল গুঁড়ির মধ্য দিয়ে। অতএব সমাধান হয়নি। যতদিন গাছে আম থাকত, অর্থাৎ ঐ জ্যৈষ্ঠের শেষাশেষি অবধি, আম নিয়ে, আম পাড়া নিয়ে তুমুল বচসা চলত দুই বাড়ির মধ্যে। দু’বাড়ির মধ্যে মুখ দেখাদেখি, কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যেত। বেড়ার অন্য প্রান্তে অন্দরমহলে যাতায়াতের একটা গেট ছিল। ঝগড়া চরমে উঠলে পেরেক মেরে বন্ধ করে দেওয়া হত সেই গেট। বেশ কয়েক দশক ধরে এই গোলমাল চলেছিল যা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল দুই বাড়ির বংশধরেরা! (Cinema)

শেষ অবধি এই ঘটনা কতদূর গড়িয়েছিল জানা না গেলেও গ্রাম বাঙলার সমাজজীবনের এক বাস্তব ছবি ধরা পড়েছে তারাপদবাবুর লেখনীর প্রকাশে।
মানব সভ্যতার ঊষাকালে জোট বা যূথবদ্ধভাবে বসবাস শুরু হয়। খাদ্য অন্বেষণ করে জীবনযাপন এবং প্রাকৃতিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই– এই ছিল সেই মানব গোষ্ঠীর প্রাথমিক কাজ। আর পাশাপাশি বসবাসের ফলেই তারা হয়ে উঠেছে একে অপরের পড়শি বা প্রতিবেশী। ইতিহাসের গতিপথের দিকে ফিরে তাকালে দেখা যায় এক পারস্পরিক সম্পর্কের অদৃশ্য বন্ধনে বাঁধা পড়েছে গোষ্ঠী প্রবণতা।
প্রতিবেশীর বন্ধন ও সম্পর্ক কখনও পড়েছে ঘাত-প্রতিঘাতের পাকচক্রে, কখনও বা তা বর্ণিল হয়ে উঠেছে সখ্য, সহযোগিতা, সহমর্মীতার মোহময় রঙে। বাংলা গল্প উপন্যাসের পাতায় পাতায় জন্ম নিয়েছে এমনই কত কাহিনি আর বাঙময় হয়েছে কত না অসংখ্য চরিত্র। সে সব সাহিত্যকীর্তি থেকে বাংলা সিনেমা সিঞ্চন করেছে তার রসদটুকু দশকের পর দশক। কখনও এক উঠোনের পড়শি তারা, কখনও পাঁচিলের ওধারের, অথবা সীমানার আগল ভেঙে– ভিনদেশের।
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা উপন্যাসের নিশ্চিন্দিপুর সেলুলয়েডের ফ্রেমে উঠে আসে ১৯৫৫ সালে। অজপাড়াগেঁয়ে অপু, দুর্গা, সর্বজয়া, হরিহর আর ইন্দির ঠাকরুন– এই পাঁচজন মানুষের এক পরিবারের গল্প “পথের পাঁচালি” আসলে পল্লীসমাজের এক টুকরো ছবি। শ্যামালিমা প্রকৃতির মাঝে প্রতিবেশীদের ভিড়। পাঁচিল পেরিয়ে এক প্রতিবেশী যেমন অভিযোগ নিয়ে আসে টুনির গলার মালা চুরির তেমনই অপর প্রতিবেশী দুর্দিনে সর্বজয়ার পাশে দাঁড়ায় খানিক সাহায্যের আশ্বাস নিয়ে, ছোট মেয়েটির হাতে পাঠিয়ে দেয় খানিক কাঁচা সবজি। নেড়াদের বাড়ি, রাণুদিদিদের বাড়ি, পটলিদের বাগান– এটাই ছিল অপু দুর্গার জগতের সীমা যার মধ্যে মিশে থাকে ফল কুড়নো আর চড়ুইভাতির আনন্দ, প্রথম রেল গাড়ি আর যাত্রা দেখার বিস্ময় কিম্বা গোড়া ব্যান্ডের সুর মূর্ছনা। যেদিন হরিহর কাশী যাওয়া মনস্থ করেন তাঁর তিন পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে– সেদিনও এই পড়শিরাই, গাঁয়ের পাঁচজন হিসেবে এসে দাঁড়ান তাঁর সামনে। হতাশার সুর নামে হরিহরের গলা বেয়ে। বলেন– “মাঝে মাঝে ভিটে মাটির মায়াও ছাড়তে হয়”।
আসলে ভিটে মাটির মায়া বড় মায়া। তার সঙ্গে মিশে থাকে প্রতিবেশী সম্পর্কিত কিছু মানুষের টান যা রক্তের সম্পর্কের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। দিন গুজরানের ছন্দে পা মেলায় সেই সব মানুষেরা– দুঃখসুখের ভাগিদার হয়ে। সময়ের দাবী মেনে অলক্ষে তারা হয়ে ওঠে ঘরের মানুষ। ১৯৪৭ এর দেশভাগ আসলে এরকমই এক স্বজন হারানোর ঘটনা যখন আমরা হারিয়েছিলাম আমাদের সেই ঘরের মানুষদের। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন “বিষণ্ণ আলোয় এই বাংলাদেশ, এ আমারই সাড়ে তিন হাত ভূমি” – যার মধ্যে ভেসে ওঠে এক অলিখিত অধিকারবোধের ছবি। মানচিত্রের ওপর ঢ্যাঁড়া কেটে, এক রাতের নোটিশে “দ্যাশ” ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছিল অগণিত নিরপরাধ মানুষকে যাদের কথা উঠে এসেছে ঋত্বিক ঘটকের তিনটি ছবি – “মেঘে ঢাকা তারা”, “কোমল গান্ধার” ও “সুবর্ণরেখা”–র কাহিনি বিন্যাসে। কিন্তু মানুষ তো সামাজিক জীব। আশাভঙ্গই হয়তো বা দিশা দেখায় নতুন পথের। “সুবর্ণরেখা” ছবিতে যেমন শহরের প্রান্তিক পতিত জমিতে গড়ে ওঠে “নবজীবন কলোনি”। ছিন্নমূল হয়েও বাঁচার তাগিদে শরণার্থীরা খুঁজে নেয় তাদের “নতুন বাড়ি”। পড়শিরা হাতে হাত বেঁধে দাঁড়ায় রাতবিরেতে ধেয়ে আসা পুলিশ আর লেঠেলবাহিনীর বিরুদ্ধে। তৈরি হয় স্কুল। হরপ্রসাদ দাদা বলেন “জীবনটা স্বার্থে নয়, পরার্থে আসে গৃহিণী। নিজের পুত্র কলত্রে আবদ্ধ যে জনা, সে তো বাঁইচাই নাই”!

গ্রাম, শহরতলির সীমানা পেরিয়ে বাংলা ছবির ক্যামেরা এবার ঢুকে পড়ে মহানগরের এক মেস বা বোর্ডিং বাড়িতে। শহরের বাইরে থেকে এসেছে মানুষজন– কেউ বিদ্যার্জন কেউ বা জীবিকার তাগিদে। একের সঙ্গে আরেকের পরিচিতি নেই। তারা নিজ নিজ অভ্যাসের দাস। কিন্তু এই মহানগরে সবারই চাই মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই। বাঙালি জীবনে এই মেস বা বোর্ডিং কেন্দ্রিক যৌথজীবনে রুমমেটরা প্রতিবেশীর ভূমিকায়।
“সাড়ে চুয়াত্তর” ছবিতে “অন্নপূর্ণা বোর্ডিং” জুড়ে এরকম নানা চরিত্রের ভিড় জমেছে। রামপ্রীতি, শিববাবু, অখিলবাবু, কামাখ্যা, কেদার প্রভৃতি বোর্ডাররা একদিকে, আর অপরদিকে মালিক রজনীবাবুর ভাইজির পরিবার- মেয়ে রমলা ও স্বামী অঘোর। কয়েকদিনের জন্য তাঁরা আশ্রয় নেন বোর্ডিং এর ঘরে। যে বাস ছিল স্বল্পকালের, তা ক্রমশ প্রলম্বিত হয়। অন্নপূর্ণা বোর্ডিং বাড়ির তলায় তলায় বাসরত বাসিন্দারা প্রতিবেশী হয়ে ওঠে। কেদার পৌঁছে যায় রমলাদের ঘরে “মাসিমা মালপো খামু” অনুরোধ নিয়ে।
এরকম আরেকটি বোর্ডিং “বসন্ত বিলাপ”। এই মহিলা বোর্ডিং এর বাসিন্দাদের মধ্যে চারজন- অনুরাধা, নবনীতা, পার্বতী এবং নীতা। পাড়ার প্রতিবেশী চার যুবক শ্যাম, লালু, সিধু আর গুপ্ত- তাদের টার্গেট বসন্ত বিলাপের ঐ “সিংহবাহিনী”। দুই যুযুধান পক্ষের পারস্পরিক দেয়া নেয়া চলে দীর্ঘদিন যার রঙ ক্রমশ বদলে যায়। বিমল করের গল্প নিয়ে দীনেন গুপ্তর এই ছবি ১৯৭৩ সালে প্রকাশ পেয়েছিল। ঠিক এর আগের বছরগুলো নকশাল আন্দোলন আর রাজনৈতিক অস্থিরতা পাড়ায় পাড়ায় প্রতিবেশীদের মধ্যে তৈরি করেছিল এক অবিশ্বাসের আবহ। সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে ‘বসন্ত বিলাপ’ আসলে প্রতিবেশী আটজন যুদ্ধরত যুবক-যুবতীর দলকে নিয়ে একটি রোমান্টিক কমেডি যারা শেষ পর্যন্ত সুন্দরভাবে জুটিবদ্ধ। কোনও ক্রমবর্ধমান নাটকীয় মুহূর্ত নেই, কোনও আকর্ষক দ্বন্দ্ব নেই, দুঃখের নেই কোনও গভীরতা।
“পাড়া” ব্যপারটা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কেমন হারিয়ে গেছে। একটা সময়ে পাড়ায় বাড়িগুলোর স্থানিক এবং ভৌগলিক অবস্থান কখনই সেখানে থাকা মানুষের মধ্যে আলাপ পরিচয়ের পক্ষে অন্তরায় হয়ে ওঠেনি। খেলার মাঠ, আড্ডার ঠেক, ক্লাবের লাইব্রেরি, পূজা পার্বণ এবং আরও পাঁচটা সামাজিক অনুষ্ঠানকে ঘিরে প্রতিবেশীরা নিজেদের মধ্যে বেঁধে রাখতেন সহমর্মিতার সাঁকো। পাশাপাশি ছাদ, মুখোমুখি বারান্দা আর জানালার পাটায় বসে চলত বাক্য বিনিময়। কখনও সে সখ্যর, কখনও পরনিন্দার আবার কখনও রীতিমত রনং দেহি আবহে- সংঘাতের। কখনও বা “এ বাড়ির খেঁদি চায় ভুরু কুঁচকে, ও বাড়ির খেঁদা হাসে মুখ মুচকে” পেরিয়ে হত মধুরেন সমাপয়েত!
“ওরা থাকে ওধারে” ছবি এরকম দুটি বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের সহবস্থানের গল্প, যার একটি ঘটি এবং অপরটি বাঙাল পরিবার। প্রতিবেশী হিসেবে তাদের মধ্যে যেমন ভাব ভালোবাসা তেমনই থেকে থেকে বিরোধ, বিশেষত মোহনবাগান– ইস্টবেঙ্গলের খেলা নিয়ে। ঘটি বাড়ির ছেলে চঞ্চল আর বাঙাল বাড়ির মেয়ে প্রমীলা। চঞ্চল প্রমীলাকে পড়ায়। আসে নানা ধরণের বিপদ, দুর্বিপাক। কিন্তু অন্তঃসলিলা হয়ে বয়ে চলা তাদের প্রেমের ধারা অবশেষে দুই পরিবারকে বাঁধে প্রজাপতির নির্বন্ধে। ওদিকে বাগবাজার অঞ্চলের গয়লানি মাসী লেনের “পাশের বাড়ি”-র খোলা জানালাও এক সময় হয়ে ওঠে দুই প্রতিবেশীর মন দেওয়া নেওয়ার অলিন্দ। এদিকে ক্যাবলরাম আর ওদিকে লিলি। হয়তো বা আজকের দিনে এ ঘটনা ব্যক্তিগত স্থানের গোপনীয়তা ভঙ্গের জালে জড়িয়ে একটা হুলুস্থুল বাঁধবার অবকাশ থাকলেও, সে সময়ে কেউই বোধহয় এ নিয়ে মাথা ঘামায়নি! গান, খুনসুটি সবই চলেছিল দুই প্রতিবেশীর মধ্যে।

মফঃস্বল শহরের চেহারাটা ছিল খানিক স্বতন্ত্র। কলকাতা থেকে আগত অতিথি, অভ্যাগত, আগন্তুকদের ব্যাপারে প্রতিবেশীদের উৎসাহ কিঞ্চিৎ বেশি। খানিক বিস্ময়, খানিক মুগ্ধতা সব মিলিয়ে শহুরে ছাপ লাগানো মানুষের সাহচর্য লাভের বাসনা। ১৯৭৪-এ মুক্তিপ্রাপ্ত ছায়াছবি “মৌচাক” মনে পড়ে? কলকাতা থেকে মাইল ৭০ দূরে জুট মিলে ওভারশিয়ারের চাকরি করতে যায় উচ্চশিক্ষিত তরুণ শীতেশ রায়। সেখানেও প্রেম আসে পশ্চিমের খোলা এক জানালা বেয়ে। সুন্দরী প্রতিবেশী নিপা অক্লেশে গেয়ে ওঠে “যদি বন্ধ ঘরের জানালাটা খুলেইছো, তখন আকাশ হয়ে আমি ধরা পড়বই তো”।
প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে প্রতিবেশী সচেতনতা খানিক বেশি। সেটা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাদের অবস্থা “ঘরেও নহে, পারেও নহে, যে জন আছে মাঝখানে”– অর্থাৎ মনে প্রাণে তারা ধারণ করেন তাদের সংস্কৃতিকে, ভাষাকে, খাদ্যাভ্যাসকে, সামাজিক আচার আচরণকে, কিন্তু যে দেশে প্রদেশে তাদের বসত, সেখানকার রীতিনীতির কাছে থাকে একধরণের দায়বদ্ধতা। ধরা যাক বাঙালির “পশ্চিম”-এর কথা। পালামু, হাজারিবাগ, দেওঘর, মধুপুর, রাচিঁ, নেতারহাট, শিমুলতলা, ম্যাক্লাস্কিগঞ্জ, গিরিডি– যেখানে কেউ যেতেন হাওয়াবদলে, কেউ বা জীবিকার দায়ে, কেউ বা অবসর জীবনের শান্তি যাপনে। যাই হোক কারণ, তাঁদের সঙ্গে যেত এক টুকরো বাংলা যা সযত্নে লালন করে তাঁরা ভাগ করে নিতেন প্রতিবেশীদের সঙ্গে। লেখক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা দীর্ঘ সময় কেটেছিল বাংলার বাইরে এবং সে সময়ের দেখা কিছু চরিত্র, ঘটনা মিলিয়ে মিশিয়ে লিখেছিলেন “দাদার কীর্তি”। সেই গল্প নিয়ে তরুণ মজুমদারের ছবি মুক্তি পেয়েছিল আশির দশকের গোড়ায়। পশ্চিমের এক ছোট্ট শহরের কয়েক ঘর বাঙালি প্রতিবেশীর জীবন কাটে নিজ ছন্দে, লয়ে। স্কুল, কলেজ, আদালত, আমবাগান, ছন্দবাণী ক্লাব, পুজো পার্বণ ঘিরে লেখা হয় তাদের দিন যাপনের রোজনামচা। কলকাতা থেকে আগত নিতান্তই ভোলাভালা ছেলে কেদার খানিক তরঙ্গ তোলে সেই জীবনে। ভিন্ন চরিত্রের মানুষগুলো একটা পরিবারবদ্ধ হয়ে সেই তরঙ্গে ভেসে যায়। তাদের কোঁচড় ভরে শুক্তির ভিড়ে যার মধ্যে সুপ্ত থাকে আনন্দ আর সুখ।
কবি শঙ্খ ঘোষ লিখেছিলেন “আমাদের পথ নেই আর/ আয়, আরও বেঁধে বেঁধে থাকি… কিছুই কোথাও যদি নেই/ তবু তো কজন আছি বাকি,/ আয় আরো হাতে হাত রেখে/ আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি”। এই হাতে হাত বেঁধে রাখবার মন্ত্রই হল আসলে ভাল থাকার দ্বিজমন্ত্র, যা বাংলা চলচ্ছবির ফ্রেম জুড়ে উঠে এসেছে দশকের পর দশক, নিরন্তর উন্মাদনার বার্তা বয়ে।
সপ্তর্ষি রায় বর্ধনের জন্ম, কর্ম এবং বর্তমান ঠাঁই তার প্রাণের শহর কলকাতায়। প্রথাগত ছাত্রজীবন কেটেছে কলকাতার পাঠভবন স্কুল, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ এবং যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে। লেখাজোকা, ছবি তোলা, নাট্যাভিনয় আর হেরিটেজের সুলুক সন্ধানের নেশায় মশগুল। সঙ্গে বই পড়া, গান বাজনা শোনা আর আকাশ পাতাল ভাবনার অদম্য বাসনা। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা তিন- "রূপকথার মতো- স্মৃতিকথায় প্রণতি রায়", "খেয়ালের খেরোখাতা" এবং "চব্য চোষ্য লেহ্য পেয়"।