মূল গল্পটির লেখক শ্রী তরুণ কান্তি মিশ্র আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্যের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কথাকার। ওড়িয়া ভাষার জনপ্রিয় এই কথাসাহিত্যিকের জন্ম ১৯৫০ সালে। পেয়েছেন ভারত সরকারের সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার, ওড়িআ সাহিত্যের সর্বোচ্চ পুরস্কার শারলা পুরস্কার সহ বহু সম্মাননা।
গল্পটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন প্রদীপ কুমার রায়। অনুবাদ পত্রিকা ও ভাষা সংসদের যৌথ ব্যবস্থাপনায় ‘সোনালী ঘোষাল সারস্বত সম্মান’ (২০২৩)-এ ভূষিত করা হচ্ছে শ্রী প্রদীপ কুমার রায়কে। প্রবাসে অনুবাদ চর্চার জন্য বিশেষ সাহিত্য সম্মান তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে এবছর।
পেটের ভেতরটা কেমন তোলপাড় করছে, বমি বমি লাগছে…
উঠোনের এক পাশে বসে পড়ে সাবিত্রী, মুখ নিচু করে, কিন্তু বমি হয় না। পেটের ভেতরের তোলপাড়টাও আস্তে আস্তে কমে যায়। সেইখানেই সে বসে থাকে দু’মিনিট ।
ঘরের ভেতর থেকে ডাক শোনা যায়– মম্মি…মম্মি… খিদে পেয়েছে…
মম্মি ডাকটা সাবিত্রীর পছন্দ নয়। কিন্তু বাইধর বলেছিল, মা ডাকটা ভারি সেকেলে। মম্মি ডাকটাই সুন্দর।
ছেলের নাম অভিমন্যু রাখতে চেয়েছিল সাবিত্রী, কিন্তু বাইধর বলেছিল -স্ফুটনিক।
আদরের ডাক ‘পিন্টু’
পিন্টু আবার ডাকে — মম্মি…
উঠানের পাশের নর্দমায় কতগুলো পোকা সলসল করছে আমের খোসার নৌকায় বসে। কোনখান থেকে পচা গন্ধ আসছে, কিছু হয়ত মরেছে, জানা যাচ্ছে না।
সাবিত্রী হাঁটুতে ভর দিয়ে ওঠে। পেটের ভেতরের অদৃশ্য সত্তা একটু চমকে পড়ার মতো নড়চড় হয়, তারপর ঘুমিয়ে পড়ে।
— না বার্লি নয়, আমি দুধ খাব…
পিন্টু পাশ ফিরে শোয়, দেওয়ালের দিকে মুখ করে।
রাতের জন্য অল্প কিছু সাগু ছিল, সেইটুকুই সম্বল। সাবিত্রী জিগ্যেস করে– সাগু খাবি!
অনিচ্ছা সত্ত্বেও পিন্টু হ্যাঁ বলে, দেওয়ালের দিকে মুখ করে।
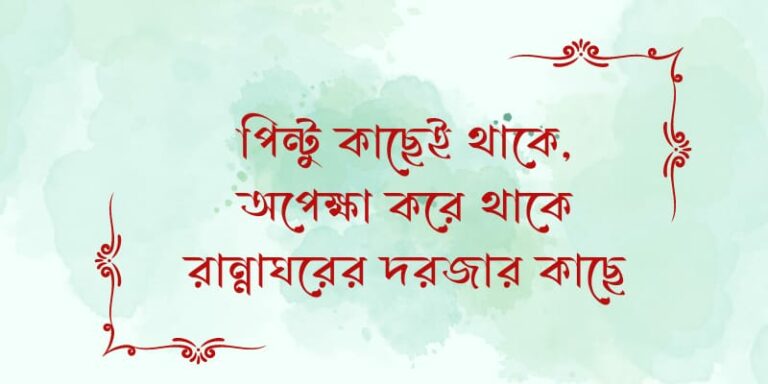
আজকে তেরো দিন হল, গুনে গুনে তেরো দিন… ডাক্তার, কবিরাজ বলতে পারছেন না পিন্টুর কী রোগ হয়েছে। ক্লিনিকের ডাক্তার কতগুলো পরীক্ষা করাতে বলেছিলেন, হাতে পয়সা নেই বলে করাতে পারেনি। কবিরাজ তিন প্রকার ওষুধ দিয়েছিলেন, ডাক্তার পাঁচ প্রকারের, কিন্তু জ্বর কমছে না। ছেলেটা সেইদিন থেকে খাটে, আর ওঠেনি।
কখনও কখনও জ্বরটা এত বেড়ে যায় যে গায়ে হাত দেওয়া যায় না, ছেলেটা আবোলতাবোল বকতে থাকে, হয়ত কাঁদে, একবার তো কাঁদতে কাঁদতে এমনি হাসতে লাগল যে সাবিত্রী ভয় পেয়ে গেছিল।
বাইধর তিনদিন পর বাড়ি ফিরে শুনেছিল, বলেছিল, হয়তো কেউ তন্ত্রমন্ত্র করেছে, গুণ্ডুচি নায়ক ওঝার কাছে নিতে হবে। সাবিত্রীর ইচ্ছা ছিল না; পরেরদিন বাইধর ট্রাক নিয়ে আবার চলে গেল টেনসা, ছেলেকে আর ওঝার কাছে নেওয়ার কথা ওঠেনি।
ফিরে আসল দুদিন পরে, সেই মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে।
এখন এই মেয়েটাকে নিয়ে বাইধর মেতেছে, আগে ছিল এক বাঙালি মেয়ে, তার আগে এক ছত্তিসগড়ি মেয়ে, এখন এই দক্ষিণী মেয়ে কাবেরী।
মেয়েটাও আসল একটা…! ট্রাক থেকে নেমে দুম দুম করে চলে আসবে ঘরের ভেতরে, সত্যি যেন তার নিজের জমিদারি, সাবিত্রী তার ঝি, বাইধর তার চাকর।
ঘরে এসে চিৎকার করে ডাকবে পিন্টুকে, এই ছোকরা, আয় তো আমার কোমরটা টিপে দিবি, সালুর ঘাটি থেকে ট্রাকে বসে বসে আমার কোমর পাছায় ভীষণ ব্যথা।
রান্নাঘরে বসে তখন বাইধর বাসি রুটি কামড়াতে থাকবে, সাবিত্রী বাসন মাজতে থাকবে কি আর কিছু করতে থাকবে, সে মেয়েটির কথা শুনে বাইধরকে বলবে, খবরদার, ওই মাগি যদি আমার ছেলেকে কিছু বলে তাহলে আমি ওর গায়ের খাল ছিঁড়ে নেব।
বাইধর চুপচাপ রুটি গিলতে থাকবে, যেন তার সংসারে কেউই নেই, না সাবিত্রী না ওই মেয়েটি। একটু পরে বাইধর ডাকবে, এই পিন্টু, আয় দেখবি আয়, আমি তোর জন্য কী এনেছি…!
পিন্টু কাছেই থাকে, অপেক্ষা করে থাকে রান্নাঘরের দরজার কাছে। সে দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে বাবার পিঠে।
বাইধর তার পকেট থেকে বের করবে ভালো একটা খেলনা কি প্যাকেটভর্তি লেবেনচুস। গতবারে সে এনেছিল একটা ভীষণ ভালো খেলনা, চক্চকে কালো রঙের এক পিস্তল। প্রথম গুলিটা এমন শব্দ করে ফাটল যে সাবিত্রী চমকে উঠেছিল।
— বাবা আমাকে দাও, আমাকে দাও…
পর পর তিনটি গুলি ফোটে, জবরদস্ত গুলি। শোওয়ার ঘর থেকে উঠে এসেছিল কাবেরী, চিৎকার করে বলেছিল, বন্ধ কর, কান ফেটে যাচ্ছে, তোর গাড়িতে বসে বসে আমার হাড় মাংস এক হয়ে গেছে। আমাকে একটু শান্তিতে ঘুমোতে দে…
হাই তুলে কাবেরী ফিরে গেছিল শোওয়ার ঘরে।
রাতে দুজন বাইরে খায়, কোনও হোটেলে কি কোনও বন্ধুর বাড়িতে। যাওয়ার সময় বাইধর বলে যায়, তাদের ফিরে আসতে অনেক রাত হবে, তাই তারা বন্ধুর বাড়িতে রাতটা থেকে যাবে।
সাবিত্রী কিছু উত্তর না দিয়ে ধড়াম করে দরজা বন্ধ করে বিছানায় আছড়ে পড়ে।
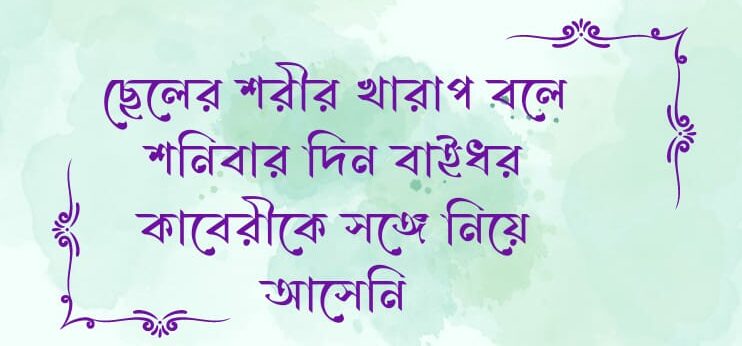
আগে ও খুব কাঁদত, ছোট্ট বাচ্চাদের মতো। এমনকি বাইধরের পায়ের উপরে মাথা রেখে বলত, চোখের জলে, চুমুতে ভিজিয়ে দিত তার দুটো পা– আমাকে ছেড়ে কোথাও যেও না, তোমাকে আমার দিব্যি। বাইধর তখন চুপ থাকত, একদম নীরব। কাঁদতে কাঁদতে সাবিত্রী অসাড় হওয়ার পড়লে ও ঘর থেকে বেরিয়ে যেত, চুপচাপ।
এখন সাবিত্রী একদম চুপ। সে কথা বলে না, যা বলে সেই ভাষায় সে কখনও থাকে না।
ছেলের শরীর খারাপ বলে শনিবার দিন বাইধর কাবেরীকে সঙ্গে নিয়ে আসেনি। এসেছিল সন্ধ্যায়, বলেছিল ভোর ভোর চলে যাবে সুনাবেড়া, আসবে পাঁচ দিন পরে।
ছেলে ঘুমিয়ে ছিল ঘরের ভেতরে, আলাদা আলাদা বিছানা করে তারা শুয়েছিল বারন্দায়। কিছুক্ষণ পরে বাইধর সরে এসেছিল কাছে, সাবিত্রীর কাপড় ধরে টেনেছিল। বিছানা থেকে উঠে সাবিত্রী হিস হিস করে বলেছিল, তোমার একটুও লজ্জা নেই! পেটে সাত মাসের বাচ্চা, আর একটা রোগী, আধমরা, আর তোমার সোহাগ ঝরে পড়ছে! ছিঃ!
বাইধরের মুখে দেশি মদের বিচ্ছিরি গন্ধ। সে কোনও কথা না বলে পাশবালিশটা দুই ঠ্যাঙের মাঝে চেপে ধরে ঘুমাতে চেষ্টা করে বাকিটা রাত।
পিন্টুর শরীর খারাপ সত্ত্বেও বাইধর ঘরে থাকে না, বলে মালিক ছুটি দিচ্ছে না, বলছে ছুটি দরকার যদি পুরা ছুটি দিলাম, যা ঘরে যা, আর বাচ্চার কথা বুঝ, বউয়ের কথা বুঝ…!
টাকার কথা বললে বলে– মাইনে বাকি রেখেছে মালিক, দিচ্ছে না, বলছে বিল্ পাশ হয়নি। নতুন অফিসারটা ভীষণ বদমাশ, আমার বিলটা করছে না, খেলছে….!
সাবিত্রী জানে না কতটা সত্য কতটা মিথ্যা, তাকে ও বিশ্বাস-ই করতে পারে না। ভালবাসা তো নেই, অনেকদিন আগেই মুছে ফেলেছে মন থেকে।
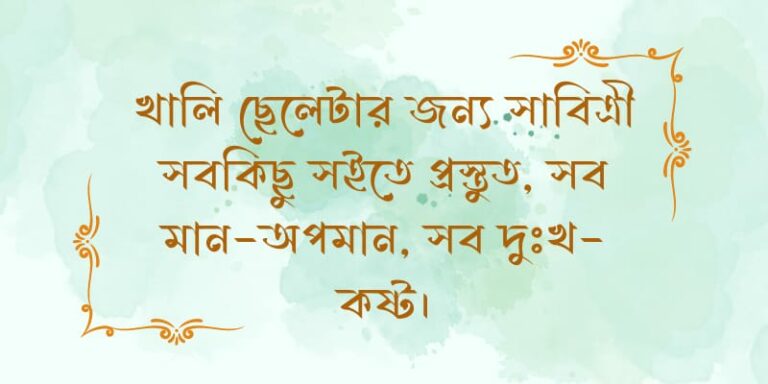
টুনির মা বলে সব মরদ এক ধরণের গো, সব-ই সেই এক লাউয়ের বিচি, এই টুনির বাবাকে দেখছিস না!
সলতে পাকাতে পাকাতে তারা দুজন এই মীমাংসায় একমত যে, ভগবান মেয়েদের জন্ম দিয়েছেন তার মনের জোর কত দেখার জন্য, তার শরীরের শক্তি কত মেপে দেখার জন্য।
খালি ছেলেটার জন্য সাবিত্রী সবকিছু সইতে প্রস্তুত, সব মান-অপমান, সব দুঃখ-কষ্ট।
পেটের ভেতরে কে পাশ ফিরে বলল, একজন নয়, দুজন।
‘মম্মি আমি বড় হলে কী হবো বল তো!’
কোলে গড়িয়ে পড়ে জিগ্যেস করে পিন্টু। সাবিত্রী বলে ‘কী হবি?’
প্রত্যেকবার আলাদা আলাদা উত্তর থাকে; বাবার মতো ট্রাক ড্রাইভার, কিংবা এরোপ্লেন ড্রাইভার, নাহলে বন্দুক হাতে পুলিশ।
একবার বলেছিল ম্যাজিসিয়ান হবে, মস্ত বড় ম্যাজিসিয়ান।
— ম্যাজিসিয়ান!
— গত পুজোর সময় পিন্টু মেলার মাঠে ম্যাজিক শো দেখেছিল। ম্যাজিকওয়ালা কেমন দেখতে দেখতে শূন্য থেকে ফুলের বৃষ্টি করেছিল, একটি মেয়েকে আলমারির ভেতরে ভর্তি করে অন্তর্ধান করে দিল, আর এক মেয়েকে দুখণ্ড করে কেটে আবার বাঁচিয়ে দিয়েছিল, এইরকম কত কী!
পিন্টু বলেছিল, হ্যাঁ, আমি ম্যাজিসিয়ান হব। তোকে ভালো ভাবে রাখব, ভালো ভালো খাওয়ার জিনিস, ভালো ভালো শাড়ি, ভালো ভালো খেলনা, আর তোর জন্য একটা ভালো টি ভি, তোর জন্য সব এনে দেব।
সাবিত্রী ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, আমার কিছু দরকার নেই রে সোনা! তোকে ছাড়া আমার আর কিছু দরকার নেই।
তারপর সাবিত্রী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। কোন দুঃখে পিন্টু কিছু বুঝতে পারেনি।
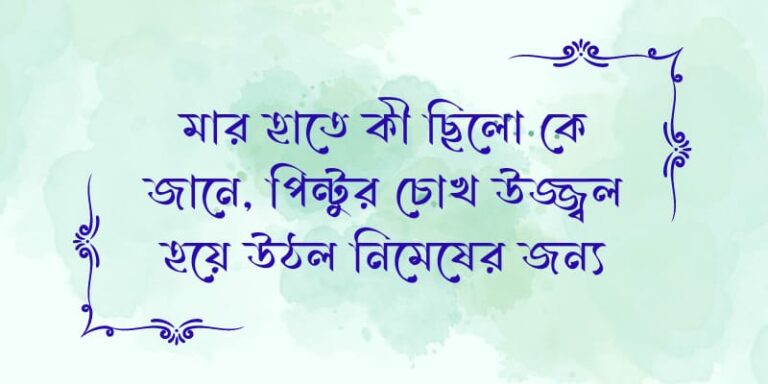
ঘরের ভেতর থেকে ডাক শোনা গেল — মম্মি মম্মি…
অতি আতুর স্বর, খুবই আলাদা।
সাবিত্রী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে, শোওয়ার ঘরে যায়।
খাটের উপর অস্থির হয়ে ছটফট করছে পিন্টু, মাথায় হাত রেখে…
— মা…মা….!
পিন্টু সচরাচর মা ডাকে না। কিন্তু ডাকে কখনও কখনও অতি আদরে, কিংবা খুব ভয় পেয়ে।
পিন্টু, কী সোনা!
আমার মাথার ভেতরটা কেমন লাগছে ।
সাবিত্রী ছেলেকে বুকে চেপে ধরে, গায় ভীষণ জ্বর।
মার হাতে কী ছিলো কে জানে, পিন্টুর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল নিমেষের জন্য। সে জোর করে জড়িয়ে ধরল মাকে তার দুর্বল হাতে।
তুই অনেক ভালো মা। আমি তোকে অনেক ভালবাসি।
যেন সেই শান্তিতেই ছেলেটি চোখ বন্ধ করে, দুটি নরম চোখের পাতা বন্ধ হয়ে যায়; জানালা দিয়ে বয়ে যায় এক দমকা বাতাস।
— পায়েস খাবি বাবা, পালোর পায়েস!
পিন্টু পায়েস খুব ভালবাসে, চালের কি সুজির কি সিমুইর।
পিন্টু কোনও উত্তর দেয় না।
— পিন্টু!
পিন্টু এমন চুপ যেন তার আর কিছু বলার নেই।
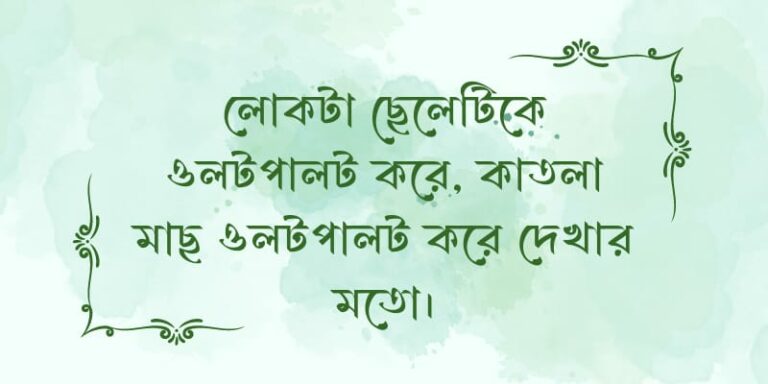
সরকারি ডাক্তরখানা বাড়ি থেকে আড়াই কিলোমিটার দূরে। অটো রিক্সার দেখা নেই, থাকলেও ভাড়ার জন্য টাকা তো নেই কাছে। দুপুরে ছেলেকে কাঁধে চাপিয়ে আসা কিছু সহজ ছিল না।
ডাক্তার ছিল না। বারন্দায় বসা সুইপার একা একা লুডো খেলছিল, মনপ্রাণ ঢেলে। লুডোর পট্টি থেকে মাথা উঠিয়ে সে দেখল মায়ের বুকে লেপ্টে থাকা ছেলেটাকে, নিস্পৃহ দৃষ্টিতে।
মায়ের কাঁধে পিন্টু ঘুমিয়ে, এমনি গভীর ঘুমে যে এতক্ষণ পরেও তার ঘুম ভাঙেনি। শান্তির ঘুম, ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নেওয়ার ঘুম।
ডাক্তারবাবু কখন আসবেন? সাবিত্রী জিজ্ঞেস করে।
আসবেন না। ঢেঙ্কানাল গেছেন। মিটিং-এ। কলেক্টর সাহেবের ফারুয়েল মিটিং। অনাসক্ত গলায় বলে লোকটা।
কোনও দিদি নেই?
আছেন। বাড়িতে।
সাবিত্রী ছেলেকে বারন্দায় শুইয়ে দেয়। সেই অবসরে খসে পড়া আঁচলের নীচের বুক দেখার সুযোগ হাতছাড়া করে না লোকটা।
সে কাছে আসে। ছেলেকে একবার দেখে, জিগ্যেস করে: কী হয়েছে?
সাবিত্রীর নীরবতাই সূচিত করে, সে কিছু জানে না।
লোকটা ছেলেটিকে ওলটপালট করে, কাতলা মাছ ওলটপালট করে দেখার মতো।
তারপর সাবিত্রীকে দেখে বলে: দেরি করে ফেলেছ, অনেক দেরি করে ফেলেছ, এখন আর এখানে কিছু করার নেই।
সাবিত্রী শুনতে পাচ্ছিল না লোকটা কী বলছে, সে চেষ্টা করছিল ছেলের হাত থেকে পুরনো আধুলিটা কেড়ে নেওয়ার জন্য।
কাল রাতে পিন্টু বলেছিল, মা আমি বড় হলে ফরেন যাব। এরোপ্লেনে বসে।
সে জিগ্যেস করেছিল, ফরেনটা কত দূর মা?
কতটা দূর সাবিত্রী কিছু বলতে পারেনি। খালি বলেছিল, ফরেন যেতে অনেক টাকা লাগে।
আজ সকালে পকেটের কোন অতল গহ্বরের থেকে পুরনো আধুলিটা বের করে দেখছিল, ভাবছিল, অনেক টাকা মানে কত পয়সা।
লোকটা সতর্ক করিয়ে দেয়, জলদি ঘাটে চলে যাও, সন্ধ্যার পর স্টাফ চলে যাবে, কাঠও যোগাড় করা সম্ভব হবে না।
পেটের ভেতরে এ যাবৎ চুপচাপ ঘুমিয়ে থাকা মাংসের পুতুলটা এখন নড়াচড়া আরম্ভ করেছে, বুকের ভেতরে কী একটা ঝম ঝম করে ভেঙে পড়ার মতো লাগছে, বাতাসে যেন বিষ বয়ে গেল, সাবিত্রীর অজ্ঞান হওয়ার অবস্থা।
কিন্তু অজ্ঞান হল না, হারিয়ে যাওয়ার বিলাস তার ভাগ্যে নেই, সে ঝুঁকে ছেলের মুখ, সারা শরীর দেখে। ছেলেকে ছোঁয় আঙুলে, দুই হাতের মুঠোয়, তারপর আছড়ে পড়ে ছেলের উপরে।
লোকটা বুদ্ধিমান, সংসার ভালোভাবে চেনে, সে কাছে এসে বলল: তুমি এখান থেকে জলদি চলে না গেলে বিপদ, তোমার বিপদ। এখন মিডিয়ার লোকজন আসবে, তোমার ছেলের ফটো তুলবে, তোমাকে নানান কথা জিজ্ঞেস করবে, ডাক্তারবাবুর খালি চেয়ারের ফটো তুলে বলবে, ডাক্তারবাবু ফিষ্টি খেতে গেছেন আর চিকিৎসা না পেয়ে বাচ্চার মৃত্যু হয়েছে। তারপর পুলিশ এনকোয়্যারি, ম্যাজিষ্ট্রেট, না বাবা… না!
সাবিত্রী কিছু বুঝতে পারছে না, চারপাশে তাকিয়ে দেখছে, এত শূন্যতা তার চারপাশের সংসারে, এত অসহায় এই সমগ্র পৃথিবী!
সে ভাবতে পারছে না কী বলবে, কী করবে।
লোকটা বলল– ট্রলিওয়ালা তো সহজে রাজি হবে না, তবে আমার একজন জানাশোনা আছে, বায়না পেয়ে ঠিক চলে আসবে। চল্লিশ টাকা নিবে। ডাকব?
আজ সকালে পিন্টু বলেছিল, সে বড় হয়ে ফরেন যাবে, মাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাবে, যত টাকা লাগে লাগুক।
টাকা আছে তো? লোকটা জিজ্ঞেস করে, বলে– আটশো টাকা তো লাগবে, কর্পোরেশনের কাঠ তো পাওয়া মুশকিল। শ্মশানওয়ালাদের আর কী দোষ! শালা সরকার ত বসে বসে…!
পেটের ভেতরে কষ্টটা ছটফট করছে, খিদের, শোকের, বিভ্রান্তির। বমি পাচ্ছে, কিন্তু বমি হল না, পেটের ভেতরের অদৃশ্য সত্তাটি শান্ত হয়ে গেল।
— শুনবে যদি একটা কথা বলি…
আরও কাছে সরে এসে লোকটা বলল: ফরেনে মানে বিদেশে অনেক গবেষণা চলছে, মানুষ কে বাঁচানোর গবেষণা। আমাকে একজন বলেছিলেন আজকে সকালে। ফরেনে থাকেন, ছুটিতে বাড়ি এসেছেন, উনি বলছিলেন মরা বাচ্চা যদি পাওয়া যেত, দেশে নিয়ে যেতাম, কে জানে, বেঁচে যেতে পারে, কত উপকার হবে।
তুমি যদি রাজি হও, এই সঙ্গে সঙ্গে খবর নিতাম…
সাবিত্রী নীচে বসে পড়ে, এমনি সে ভীষণ ক্লান্ত , কত হাঁপিয়ে ছুটেছে রোদে, উত্তপ্ত মাটির উপরে, প্রাণহারা তৃষ্ণা নিয়ে। পেটের ভেতরে অভুক্ত বাচ্চাটা এখন আবার ছটফটানি আরম্ভ করেছে, ধাক্কা মারছে অন্তঃনলিকে।
লোকটা বলল: তুমি ভীষণ ক্লান্ত, এপাশে এস।
অপরিষ্কার ডাক্তারখানার ভেতরে এমন একটা পরিষ্কার ঘর যে আছে, না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। ডাক্তারবাবুর বিশ্রামের ঘর। সেই ঘরে এসে বসার সঙ্গে সঙ্গে দুজন লোক এসে হাজির, শূন্য থেকে কী! একজন দেখতে লম্বা, কালো, নাকের তলায় মোটা গোঁফ। অন্য লোকটা মোটা, বেঁটে, কথা বলে মাথাটা নাড়িয়ে নাড়িয়ে। সেই জিজ্ঞেস করে– ‘এই !’
মনে তেমন ধরেনি সেইভাবে অন্য জন বলে– খুবই ছোট্ট পেট। দু’ কেজি হবে কি না, আচ্ছা , ঠিক আছে, কত!
সাবিত্রী শুনতে না পায় সেইভাবে সুইপার বলে — পঁচিশ ।
— দুর্, পঁচিশ না কচু! পনেরো…
মোটা লোকটা কথার মাঝে বলে, এই কাজে কত রিস্ক আছে। নার্কোটিক্ওয়ালারা যমের মতো লুকিয়ে থাকে, গন্ধ পেয়ে ঠিক চলে আসবে। ধরা পড়লে মরণ নিশ্চিত। এরোপ্লেন থেকে টেনে বের করে সোজা ফাঁসি লাগিয়ে ঝুলিয়ে দেবে। পনেরো মিলছে যদি মনে রাখ অনেক ।
চোখে চোখে বাকি কথা শেষ করে সুইপার লোকটা সাবিত্রীর কাছে আসে, বলে, ওঁরা দশ হাজার দিতে চাইছেন, গবেষণার অনুদান। অনুদান মানে কী জানো তো? মানে সাবসিডি।
বিদেশের সরকার আমাদের সরকারের মতো হারামি নয়, ওঁরা ঠিক কথা বলেন, ঠিক কাজ করেন।
খুবই সুন্দর পোশাক তারা এনেছিল সঙ্গে, যত্ন করে পিন্টুকে পরায়, গায়ে আতর লাগায়, তারপর আদর করে পিন্টুকে কাঁধে ফেলে গোঁফওয়ালা লোকটা বেরিয়ে যায়।
পেটের ভেতরের বাচ্চাটা এবার কথা বলতে পারে যেন! বলে– মা খিদে পেয়েছে… ভীষণ খিদে মা!
ছবি সৌজন্য: Picryl
প্রদীপ কুমার রায় (১৯৫৬) অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, বর্তমানে ওড়িশার ভুবনেশ্বর শহরের বাসিন্দা। পারিবারিক সূত্রে বাঙালি হলেও জন্ম, শিক্ষা, চাকরি সবকিছু ওড়িশায়। ওড়িশা ভাষা সাহিত্যে এম এ পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর লাভ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদক পেয়েছেন। দীর্ঘ ৩৭ বছর ওড়িশার বিভিন্ন কলেজে ওড়িয়া ভাষা সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপনা করেন এবং ২০১৬ সালে অধ্যক্ষ পদে অবসর গ্রহণ করেন।
কর্মজীবনের পাশাপাশি তিনি বাংলা সাহিত্যের ১৪টি উপন্যাস, ৮টি গল্প সংকলন, ৪টি জীবনী, ৫টি প্রবন্ধ সংকলন, ১২টি কবিতা সংকলন ওড়িয়া ভাষায় অনুবাদ করেছেন।
সম্প্রতি ওড়িয়া ভাষার কিছু অনবদ্য সাহিত্যের বাংলা অনুবাদের প্রয়াস শুরু করছেন তিনি। ওড়িয়া ভাষার বিখ্যাত কবি প্রদীপ কুমার পণ্ডার কবিতা সংকলন 'নির্বাচিত ৫০' এবং একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত কবি মমতা দাশের 'মায়ান্ধকার' কোলকাতার 'ভাষা সংসদ' থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

























