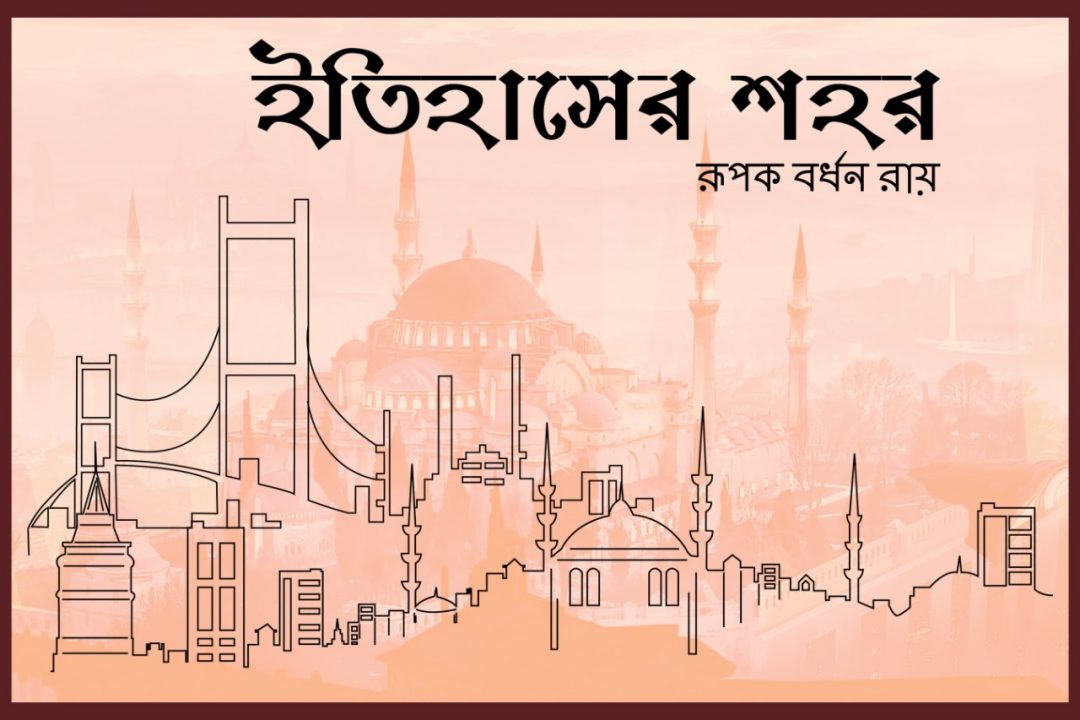টিন চত্বরের আরও একটা নাম ছিল উঙ্গেল্ট বা “Ungelt” অর্থাৎ যেখানে বিদেশিমুদ্রার আদানপ্রদান হয়। বাজারের এমন নাম কেন, সহজেই অনুমেয়। রাজা দ্বিতীয় রুডলফের রাজত্বকালে ‘উঙ্গেল্ট’ সম্পর্কে অনেক কিংবদন্তি শুনতে পাওয়া যায়।
টিন চত্বরে বেশ কিছু ইন বা মোটেল থাকলেও আগত সদাগরের তুলনায় সংখ্যাটা ছিল বেশ কমই। কাজেই মাঝেসাঝে সুহৃদয় উঙ্গেল্টবাসীরা নিজেদের বাড়িতে ব্যবসায়ীদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এমনি একবার, সুদূর পাডুয়া থেকে আগত এক ব্যবসায়ীকে নিজের ঘরে থাকতে দেন বহু পুরনো আবাসিক এক জনৈক উইল-রাইট (গাড়ির চাকা প্রস্তুতকারক) পরিবার। প্রথম কিছুদিন খানাপিনা, আমোদপ্রমোদ করে গোটা পরিবারের মনজয় করে নেন সদাগর।
কিন্তু সুখের দিন দীর্ঘস্থায়ী হল না। পরিবারের গিন্নি ঘোরতর অসুস্থ হলেন। দিন গেল, সপ্তাহ গেল, মাসও গেল। দেশের প্রায় সমস্ত ডাক্তারের সবরকম ওষুধ একটিও কাজ করল না, অবস্থা খারাপ হতে থাকল। এমনই এক সন্ধ্যায়, যখন সমগ্র পরিবার খাবার টেবিলে মুহ্যমান, অতিথি জানতে চাইলেন, “আমায় একবার চেষ্টা করতে দেবেন?”

এত চেষ্টাই যখন হল, আর একবারে আপত্তি কী? এমন ভেবে উইল-রাইট রাজি হলেন। ব্যবসায়ী বাজার থেকে কিছু জড়িবুটি কিনে এনে গিন্নির শোবার ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দিলেন। বললেন, কেউ যেন বিরক্ত না করে। একদিন যায়, দু’দিন যায়, দরজা খোলে না। পরিবারের দুশ্চিন্তা আরও বাড়ল। অবশেষে তিন দিনের দিন সদাগর দরজা খুললেন, এবং তাঁর সঙ্গে বাইরে এলেন সুস্থ স্বাভাবিক গিন্নি মা, যেন একেবারে নতুন মানুষ! সবাই হতবাক!
দিন যায়। অতিথির ফেরার দিন ঘনিয়ে এল। শেষদিনে অতিথি ঘরভাড়া বাবদ বেশ কিছু টাকা বাড়ির মালিকের হাতে তুলে দিতে চাইলেন। কিন্তু উইল-রাইট অনিচ্ছুক। যে মানুষের হাতে মৃত্যুপথযাত্রী স্ত্রী আবার স্বমহিমায় সংসারে ফিরেছেন তার কাছ থেকে হাত পেতে টাকা নেওয়ায় তিনি অপারগ। উপরন্তু বললেন, “আপনি যখনই প্রাগে আসবেন, আমার দরজা আপনার জন্য অবারিত থাকবে। এ আপনারই বাড়ি।”
ব্যব্যসায়ী সম্মত হলেন, কিন্তু যাওয়ার আগে ধন্যবাদস্বরূপ গিন্নির হাতে তিনটি মোমবাতি দিয়ে বলে গেলেন, “এই তিনটি আপনার তিন পুত্রের জন্য। যদি কখনও এই মোমবাতি জ্বালানোর দরকার পড়ে, আর যদি তার শিখার ঔজ্জ্বল্য অমলিন, অবিচলিত থাকে, জানবেন আপনার পুত্রেরা সুস্থ এবং নিরাপদ রয়েছে।”
এই ঘটনার পর কেটে গেল বেশ কিছু বছর। শুরু হল হুসাইট আন্দোলন। উইল-রাইট দম্পতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যুদ্ধে গেলেন, এবং তাঁর সুস্থতা ও নিরাপত্তা কামনায় প্রথম মোমবাতি জ্বালালেন মা। প্রতিটি রাত শিখার দিকে চেয়ে চেয়েই নিদ্রাহীন কেটে যায়। কয়েকদিন পরে মোমবাতি দপ করে নিভে গেল এবং পরদিনই ছেলের মৃত্যুসংবাদ পেলেন দম্পতি।
পুত্রশোক বুকে নিয়ে আরও কিছু বছর অতিক্রান্ত করলেন দু’জনে। দ্বিতীয় পুত্র যুবক হয়ে বাবা-মায়ের সাথে ঝগড়া করেই ভাগ্যান্বষণে বেরিয়ে গেলেন। দ্বিতীয় মোম জ্বালালেন মা। সাতদিন পর্যন্ত শিখা রইল অবিচলিত। তারপর তিনদিন তিনরাত দপদপ করে অবশেষে অস্তমিত হল। সঙ্গে সঙ্গে খবর এল অজানা জ্বরে তিনদিন অসহ্য যন্ত্রণায় কষ্ট পেয়ে মারা গেছে তাঁদের দ্বিতীয় পুত্র।

তৃতীয় পুত্রের বেলায় আর ঝুঁকি নিলেন না বৃদ্ধ দম্পতি। তবে পারিবারিক ব্যবসার কাজে খুব শিগগিরি ভিয়েনা যাওয়ার দরকার পড়ল। নিদারুণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হয়েই কনিষ্ঠ পুত্রকে যেত দিলেন বাবা। জ্বলল তিন নম্বর মোম। হপ্তাখানেক স্থিতিশীল শিখা। কিন্তু অষ্টম দিন থেকেই কম্পমান। এবার আর সময় নষ্ট না করে বাবা পৌঁছে গেলেন ভিয়েনায়, খুঁজে পেলেন একমাত্র জীবীত পুত্রকে। তবে ঘোড়ার পায়ের আঘাতে তখন তার মৃতপ্রায় অবস্থায়। ভয়ে-আশঙ্কায় আত্মহারা বাপের মনে পড়ল পাডুয়ার সেই সদাগরের কথা, যার চিকিৎসায় মৃত্যুপথযাত্রী স্ত্রীকে ফিরে পেয়েছিলেন তিনি।
ডাক পড়লো সদাগরের। আগের মতোই তিন দিনের জড়িবুটি চিকিৎসায় জ্ঞান ফিরল কনিষ্ঠ পুত্রের। পিতাপুত্র একসঙ্গে ফিরে এলেন। শোনা যায়, বৃদ্ধ উইল-রাইট তাঁর শেষ বয়স অবধি নাতি-নাতনিদের নিয়ে সুখেই ঘর করেছিলেন। শুধু একটাই শেষ ইচ্ছা তাঁর মেটেনি। সাধ ছিল সেই ধন্বন্তরী ব্যব্যসায়ীকে ফের একবার বাড়িতে ডেকে ধন্যবাদ দেবার। কিন্তু তাঁকে উঙ্গেলটে আর কখনও দেখাই যায়নি।
পাঠক, এখন আমরা যে জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছি, সেটা টাউন হলের দক্ষিণ দিক। দেওয়ালে ওই নীলচে গোল ঘড়ির মত জিনিসটা দেখছেন? ঠিকই ধরেছেন। ওটা ঘড়িই বটে, প্রাগের বিখ্যাত অ্যাস্ট্রোনমিকাল ক্লক, যার নাম ওরলজ়।
১২০০ শতাব্দীর গোড়া থেকেই প্রাগ শহরের রাজনৈতিক ও সামাজিক যাপনের মধ্যমণি এই টাউন হল। একে ঘিরেই ধীরে ধীরে পুরনো প্রাগ চত্বরের সাময়িক বিবর্তন। এই ঘড়ি তৈরি হওয়ার পর টাউন হলের মহিমা আরও বেশি করে গোটা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। ঐতিহাসিকরা প্রথমে একটু ভুল করেছিলেন।

গবেষণায় বলা হয়েছিল, এই ঘড়ির আদি স্রষ্টা মাস্টার হানুস, যার আসল নাম জান রুজ়ে। রুজ়ে সত্যিই দক্ষ ঘড়ি নির্মাতা ছিলেন। পাশাপাশি প্রাগের সুপ্রাচীন চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কের অধ্যাপকও। তবে এই নির্দিষ্ট ঘড়িটির আদি নির্মাতা হলেন “মিকালুস অফ কাদান”, ১৪১০ খ্রিষ্টাব্দে। বছর ত্রিশেক পরে ঘড়িটি এতবার খারাপ হওয়ায় খুব জটিল মেরামতির কাজ করতে ডাক পড়েছিল হানুসের। তবে তিনিই আসল নির্মাতা নন।
ওরলজ়ের মূলত তিনিটি ভাগ। প্রথমত; অ্যাস্ট্রোনমিকাল ডায়াল, যা মহাকাশে সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদির গতি প্রকৃতি নির্ধারণ করত। দ্বিতীয়ত, ঘড়ির ডায়ালের দু’পাশে বিভিন্ন ক্যাথলিক সন্তদের মূর্তি এবং “দা ওয়াক অফ দা অ্যাপস্টলস” অর্থাৎ খ্রিষ্ট-ধর্মপ্রচারকদলের মিছিল যা প্রতি ঘণ্টায় একবার করে চলনশীল হয়। মূর্তিদের এই মিছিলে রয়েছে একটি কংকাল যা মৃত্যুর প্রতীক। মিছিলের শেষে যিশু বেরিয়ে এসে ডান হাতে দর্শনার্থীকে স্নেহাশিস প্রদান করেন। তৃতীয় ভাগটি হল, ক্যালেন্ডার ডায়াল (পদক খচিত) যা মাসের হিসেব রাখে।
হানুস মারা যান ১৪৯৭-তে। তারপরে বেশ কিছু বছর ঘড়িটা বন্ধই ছিল। এ ঘটনা নিয়ে অবশ্য বেশ আকর্ষণীয় একটা গল্প প্রচলিত আছে।
ঘড়ি বিকল হয়ে যাওয়া একেবারেই আকস্মিক ঘটনা নয়। প্রাগের এই ঘড়ির এতই বিখ্যাত ছিল যে সারা বিশ্ব থেকে কাতারে কাতারে মানুষ তার টানে ছুটে আসতেন। স্বাভাবিকভাবেই এতে শহরের বেশ খানিকটা আর্থিক লাভ তো হতই, সঙ্গে সঙ্গে এ নিয়ে অহংকারেরও অন্ত ছিল না মেয়রের। সমস্যা হল, এই অহংকারের পাশাপাশি মেয়র ও তাঁর পারিষদবর্গের মনে ভীতিও তৈরি হয় এই ভেবে যে, হানুস যদি একই রকমের আর একটি ঘড়ি অন্যত্র তৈরি করেন! তাহলে তো প্রাগের একচ্ছত্র অধিকারে ভাঙন ধরবে! হানুস অবশ্য সে কথা আগে থেকেই ভেবেছিলেন এবং সরকারকে তেমন কথাও দিয়ে রেখেছিলেন যে, কোনও মূল্যেই এমন জিনিস তিনি আর কোথাও কখনও তৈরি করবেন না। তাসত্ত্বেও ভয় গেল না মেয়রের। এক রাতে, সরকারি অধিকর্তাদের নির্দেশে আততায়ীর দল হানুসের বাড়ি চড়াও হয়।
প্রাণে না মারলেও বৃদ্ধ গণিতবিদের দুই চোখ অন্ধ করে দেওয়া হয়। অসহ্য যন্ত্রণায়, দারুণ জ্বরে অসুস্থ হানুস বুঝতেই পারলেন না, যে তাঁর মতো সাতে-পাঁচে না-থাকা এক অধ্যাপকের এত বড় ক্ষতি করার প্রয়োজন কার হতে পারে।

কিন্তু সময় সমস্ত সত্যই ফাঁস করে। হানুস জানতে পারলেন এই কাজের পেছনে কাদের হাত। ফন্দি আঁটলেন প্রতিশোধের। একদিন আপন মনেই হাতড়ে হাতড়ে ঘড়ির কাছে পৌঁছলেন প্রৌঢ় গণিতজ্ঞ। তারপর সকলের চোখের আড়ালে একটা লিভারে মৃদু চাপ দিতেই ঘড়ি ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল। এর কিছুদিন পরে মাস্টার হানুস মারা গেলেন, সঙ্গে নিয়ে গেলেন ঘড়ি সারাইয়ের গোপন কথাটি। বহু বছর বন্ধ রইল ঘড়ি। মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করে, যে যতদিন পর্যন্ত মেয়র ও তাঁর পারিষদদের অন্যায় কালের আবর্তে হারিয়ে না-যাচ্ছে, ততদিন তাদের সাধের ওরলজ় আর কাজ করবে না।
চলুন এবার একবার নদীর দিকটায় যাওয়া যাক। চার্লস ব্রিজ সেরে প্রাগ কাসল পৌঁছতে অন্তত আরও মিনিট চল্লিশেক লাগবে। যে জায়গাটায় এখন চার্লস সেতুর অবস্থান, খুব সম্ভবত সেখানে একটা ফিয়র্ড (নদীর অগভীর অংশ যা হেঁটে পার হওয়া যায়) ছিল।

কথিত আছে, ৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ডিউক ওয়েন্সেসলাস আততায়ীদের হাতে স্টারা বোলেসলাভে নিহত হবার পর তাঁর মৃতদেহ পুরনো প্রাগে ফেরত নিয়ে আসার জন্য একটা কাঠের পুল তৈরি করা হয়। পাথুরে সাঁকোর উল্লেখ মেলে আরও বহু পরে, ১১৭০ খৃষ্টাব্দে। সাঁকোটি রাজা ভ্লাদিসলাভের প্রণয়িনী জুডিথের জন্য তৈরি হওয়ায় নাম হয় “জুডিথ ব্রিজ”। বর্তমান ব্রিজের যে গঠন, তার উল্লেখ ইতিহাসে বিশেষ পাওয়া যায় না। শোনা যায় সাঁকোটা বানাতে হলুদ বেলেপাথর ব্যবহৃত হয়েছিল যা সেই সময়ের তুলনায় বেশ উচ্চমানের যন্ত্রকৌশলের নিদর্শন।
পুরনো প্রাগের সঙ্গে ভ্লাটভার যে দিকটা চার্লস সেতু দিয়ে জোড়া রয়েছে, সে দিকটার নাম মালা স্ট্রানা, অর্থাৎ “লেসার টাউন”। মধ্যযুগ থেকেই মালা স্ট্রানার বেশ ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। বিশেষত এথনিক জার্মান প্রজাতি, বুর্জোয়া এবং মধ্যযুগীয় বোহেমিয়ানদের আখড়া এই বনেদি পাড়া। ১৬০০ শতাব্দী থেকে ইতালীয়রাও বসতি স্থাপন করেন এখানে।

১২৫৭ সালে ভ্লাটভার পশ্চিম পাড়ে গড়ে উঠতে শুরু করে নতুন প্রাগের এই অঞ্চল। সে কারনেই মালা স্ট্রানা আকারে খানিকটা ছোটই। নামের সঙ্গে জায়গাটার গুরুত্বের কোনও সম্পর্ক নেই। প্রথমে নাম দেওয়া হয়েছিল “Nové Město pod Pražským hradem” অর্থাৎ “প্রাগ ক্যাসেলের পাদদেশে নতুন শহর”। ১৩৪৮ সালে রাজা চতুর্থ চার্লস “নতুন প্রাগ”-এ্রর পত্তন করেন, তার সঙ্গেই নাম পালটে এ জায়গার নাম হয় “Lesser Town of Prague” এবং অবশেষে ১৭০০ শতাব্দীতে “মালা স্ট্রানা” নামটি প্রথম ব্যবহৃত হয়।
*ছবি সৌজন্য: লেখক ও pragitecture.eu
আগের পর্বের লিংক: পর্ব ১
ড. রূপক বর্ধন রায় GE Healthcare-এ বিজ্ঞানী হিসেবে কর্মরত। ফ্রান্সের নিস শহরে থাকেন। তুরস্কের সাবাঞ্চি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করেছেন। বৈজ্ঞানিক হিসেবে কর্মসূত্রে যাতায়াত বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে। লেখালিখির স্বভাব বহুদিনের। মূলত লেখেন বিজ্ঞান, ইতিহাস, ঘোরাঘুরি নিয়েই। এ ছাড়াও গানবাজনা, নোটাফিলি, নিউমিসম্যাটিক্সের মত একাধিক বিষয়ে আগ্রহ অসীম।