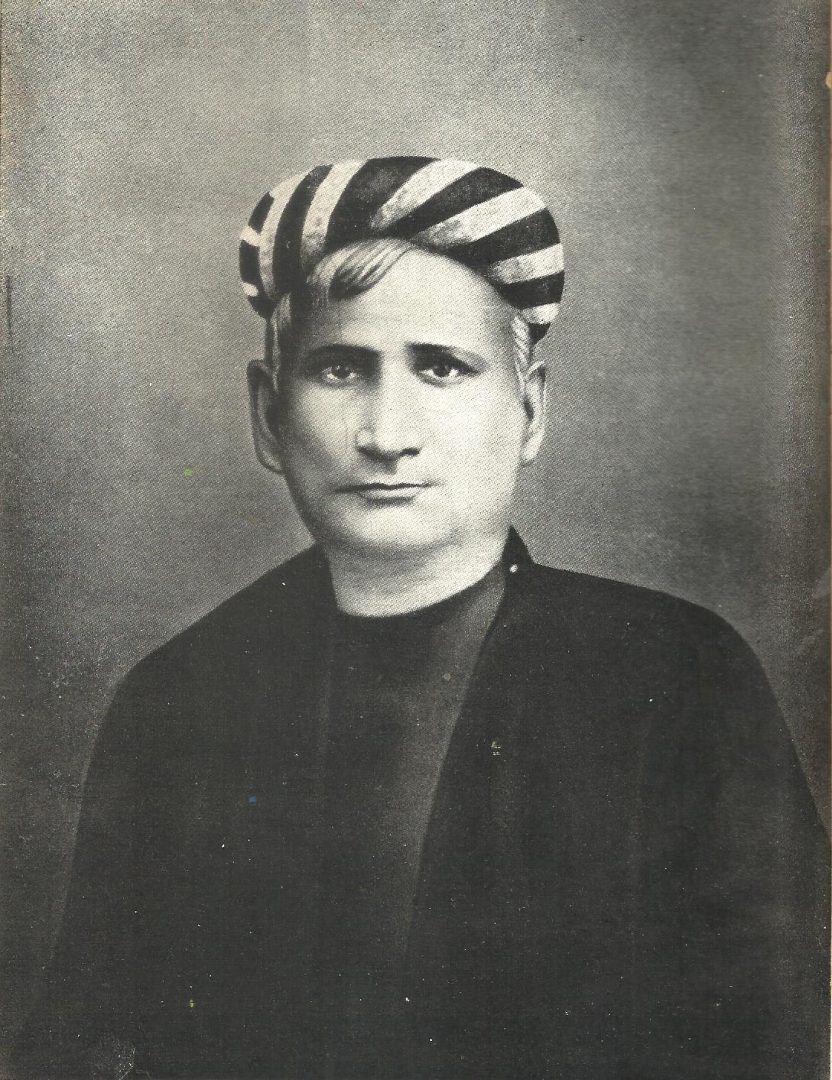‘বন্দেমাতরম্’ গানটা কি পুরোটা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা নয়? হঠাৎ এমন একটা প্রশ্ন শুনলে আপনাকেও হয়তো কিঞ্চিৎ থমকে দাঁড়াতে হবে। কোনও রাজনৈতিক মতলব থেকে এমন প্রশ্ন তোলা হচ্ছে কি না তাও মনে হতে পারে আপনার। প্রশ্নটা কিন্তু উঠেছিল অ্যাকাডেমিক চত্বর থেকেই, রাজনীতির উঠোন থেকে নয়।
শান্তিনিকেতনের ‘কালোর দোকান’-এর উলটোদিকের দোতলায় এখন যেখানে ‘বইওয়ালা বুকক্যাফে’, কয়েকবছর আগে সেখানেই ছিল ‘দে’জ পাবলশিং’-এর একটা আউটলেট। স্বত্বাধিকারী অধ্যাপক শুচিব্রত সেন নিজেই একজন ইতিহাসবিদ্। সেখানে আমার নিত্য সান্ধ্যসান্নিধ্য জমত অরুণদা (অধ্যাপক অরুণ নাগ) এবং শুচিব্রতদার সঙ্গে। শান্তিনিকেতনে এলে মাঝে-মাঝে দেখা দিতেন পুলক চন্দ। সালটা বোধহয় ২০১২। একদিন পুলকদা এসেছেন। আলোচনার মাঝপথে ঢুকেছি আমি। ঢোকামাত্র সহাস্য শুচিব্রতদা আমাকে ফস্ করে বলে বসলেন, ‘‘এই যে বাংলার অধ্যাপক, বলো তো বন্দেমাতরম্’ গানটা কি পুরোটা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা নয়?” বুঝলাম কোনও একটা তর্কের টর্নেডোর মধ্যিখানে ঢুকে পড়েছি। মনে পড়ে গেল ‘বন্দেমাতরম্’ নিয়ে ২০০৬ সালের তর্ক-তরঙ্গের দিনগুলো।
‘জাতীয় সঙ্গীত’ হিসেবে কংগ্রেসের অধিবেশনে ‘বন্দেমাতরম্’ গীত হওয়ার শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের একটি নির্দেশনামাকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী বেশ আলোড়ন উঠেছিল ২০০৬ সালে। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছিলেন, কোন হিসাবে এই বর্ষপূর্তির ফরমান? সেই আলোড়নে ‘বন্দেমাতরম্’ নিয়ে অনেক নতুন-পুরনো তর্ক আবার ঘাই মেরে ভেসে উঠেছিল। যেমন আমাদের শিক্ষক, বিশিষ্ট বঙ্কিম-গবেষক ও বঙ্কিমচন্দ্র-জীবনীকার অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’য় একটি নিবন্ধে প্রশ্ন তুলেছিলেন “‘বন্দেমাতরম্’ কি বঙ্কিমচন্দ্রেরই লেখা”। এই নিয়েও বিদ্বজ্জন মহলে তখন একটা মৃদু আলোড়ন উঠেছিল। যে গানের সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের ভারতজোড়া পরিচিতি, উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে স্বাদেশিকতার বীজমন্ত্র হিসেবে যে গান ভারতের রাজনীতি-সংস্কৃতির অনেকটা পরিসরজুড়ে ছড়িয়ে আছে, জড়িয়ে আছে— সেই গানের ‘পূর্ণ পিতৃত্ব’ নিয়েই প্রশ্ন! আনন্দবাজারের ‘সম্পাদক সমীপেষু’ বিভাগে সেসময় কথাটা গড়িয়েছিল নানাদিকে। তবে কে কী বলেছিলেন তার সবকথা স্পষ্ট মনে ছিল না তা স্বীকার করতেই হবে।
সেদিন বাড়ি ফেরার মুখে দে’জ থেকে সদ্যপ্রকাশিত পুলকদার ‘ভিন্নপাঠে বন্দে মাতরম্ ও একটি দুষ্প্রাপ্য কাব্যগ্রন্থ’ বইটি শুচিব্রতদা হাতে ধরিয়ে দিলেন। কয়েকদিন পর বাড়িতে বইটা নিয়ে বসেছি। ২০০৬ সালের নভেম্বর মাসের আনন্দবাজারের তর্ক-বিতর্কগুলোও স্মৃতিপটে তৎক্ষণাৎ ফুটে উঠতে থাকল।

পুলক চন্দের বইটা অবশ্য ঠিক ‘বন্দেমাতরম্’-এর রচয়িতা-বিতর্ক নিয়ে নয়। বইটি ছিল বিজয়লাল দত্ত নামের এক প্রায়-বিস্মৃত কবির ‘জাগো আমার মা’(১২৯৪ বঙ্গাব্দ) শিরোনামের ততোধিক বিস্মৃত একটি কাব্যগ্রন্থ নিয়ে আলোচনা। তাতে অনিবার্যভাবে এসেছে ‘বন্দেমাতরম্’ প্রসঙ্গ। ওই বিতর্কে বস্তুত নতুন একটা মাত্রাই যোগ করেছিলেন পুলক চন্দ। কিন্তু সেকথা থাক। অনেক কথার ভিড়ের মধ্য থেকে আপাতত ‘বন্দেমাতরম্’-এর ‘বঙ্গদর্শন’ পাঠ এবং ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে(১৮৮২)ব্যবহৃত একটি উদ্ধৃতিচিহ্ন নিয়ে ২০০৬-এর সেই হেমন্ত ঋতুকালীন আনন্দবাজারীয় তর্ক-বিতর্কের কিছু কথা বলা যাক।
উদ্ধৃতিচিহ্নের বিতর্কটা তুলেছিলেন অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য ৭ নভেম্বর ২০০৬ ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’য় লেখা তাঁর নিবন্ধটিতে। অমিত্রসূদনবাবুর বক্তব্যের নির্যাস হল: ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসের ব্যবহৃত এই গানটির শুরুর বারোটি পংক্তি (‘বন্দে মাতরম্—রিপুদলবারিণীং মাতরম্’ পর্যন্ত) ছিল উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে। নিজের রচনা হলে তা উদ্ধৃতি-চিহ্নিত করা স্বাভাবিক নয়! তাঁর প্রশ্ন, ‘তবে কি এই আঠাশ চরণের সঙ্গীতের প্রথম বারো চরণ অন্যের এবং শেষ ষোলো চরণ বঙ্কিমের নিজের রচনা?’
‘বন্দেমাতরম্’ রচনার সমকালীন সাক্ষ্য (১৮৭৫-৭৬ এবং আনুমানিক পরবর্তী একদশক) থেকে মনে হয় ঠিক এই জাতীয় তর্ক তখন ওঠেনি। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত ‘বঙ্কিমপ্রসঙ্গ’ বইতে বঙ্কিমভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন, “বন্দে মাতরম্ গীতটি উহার [অর্থাৎ ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসের] বহু দিন পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল।—বঙ্গদর্শনে মাঝে মধ্যে দুই এক পাত matter কম পড়িলে পণ্ডিত মহাশয় [অর্থাৎ ‘বঙ্গদর্শন’-এর কার্যাধ্যক্ষ রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়] আসিয়া সম্পাদককে জানাইতেন, তিনি তাহা ঐ দিনেই লিখিয়া দিতেন।—‘বন্দে মাতরম্’ গীতটি রচিত হইবার কিছু দিবস পরে পণ্ডিত মহাশয় আসিয়া জানাইলেন, প্রায় এক পাত matter কম পড়িয়াছে। সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, ‘আচ্ছা, আজই পাবে’। এক খানা কাগজ টেবিলে পড়িয়াছিল, পণ্ডিত মহাশয়ের উহার প্রতি নজর পড়িয়াছিল, বোধ হয় উহা পাঠও করিয়াছিলেন, কাগজ খানিতে ‘বন্দে মাতরম্’ গীতটি লেখা ছিল। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, ‘বিলম্বে কাজ বন্ধ থাকিবে, এই গীতটি লেখা আছে, উহা মন্দ নয় ত—ঐটা দিন না কেন?’ সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র বিরক্ত হইয়া কাগজ খানি টেবিলের দেরাজের মধ্যে রাখিয়া বলিলেন, ‘উহা ভাল কি মন্দ, এখন তুমি বুঝিতে পারিবে না, কিছুকাল পরে উহা বুঝিবে—আমি তখন জীবিত না থাকিবারই সম্ভব, তুমি থাকিতে পার।’”
অন্যদিকে ওই বইতেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন, প্রথম যখন ‘বন্দে মাতরম্’ গানটি তিনি শোনেন তখন শ্রোতাদের কেউ কেউ গানটির সংস্কৃত অংশের কিছু কিছু জায়গা সম্পর্কে অভিযোগ তুলে বলেন ওই অংশগুলি ‘অত্যন্ত শ্রুতিকটু হইয়াছে’। ‘শস্য শ্যামলাং শ্রুতিকটু নয় ত কি? দ্বিসপ্তকোটী ভুজৈর্ধৃত খরকরবালে ইহাকে কেহই শ্রুতিমধুর বলিবেন না।’ সেই আসরে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। হরপ্রসাদ লিখছেন, ‘বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া ধীর ভাবে শুনিলেন, তাহার পর বলিলেন, ‘আমার ভাল লেগেছে, তাই লিখেছি। তোমাদের ইচ্ছা হয় পড়, না হয় ফেলে দাও, না হয় প’ড় না।’
উদ্ধৃতিচিহ্নের বিতর্কটা তুলেছিলেন অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য ৭ নভেম্বর ২০০৬ ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’য় লেখা তাঁর নিবন্ধটিতে। অমিত্রসূদনবাবুর বক্তব্যের নির্যাস হল: ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসের ব্যবহৃত এই গানটির শুরুর বারোটি পংক্তি (‘বন্দে মাতরম্---রিপুদলবারিণীং মাতরম্’ পর্যন্ত) ছিল উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে। নিজের রচনা হলে তা উদ্ধৃতি-চিহ্নিত করা স্বাভাবিক নয়!
হরপ্রসাদের এই সাক্ষ্যটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি থেকে স্পষ্ট যে সংস্কৃত অংশটির রচয়িতা তিনি স্বয়ং! বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র প্রায় অনুরূপ একটা কাহিনি শুনিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বড়মেয়েরও নাকি ‘শ্রুতিকটু’ মনে হয়েছিল ‘বন্দেমাতরম্’। তা শুনে মেয়েকেও ওই একই উত্তর দিয়েছিলেন ‘সাহিত্য সম্রাট’। সে-হেন গানের নিরঙ্কুশ রচনাস্বত্ব নিয়েই প্রশ্ন?
অমিত্রসূদন ভট্টাচার্যের সেই নিবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে আনন্দবাজারের ‘সম্পাদক সমীপেষু’ বিভাগে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি ছাপা হয় ২৩ নভেম্বর ২০০৬। ভাষাতত্ত্বের একজন সুখ্যাত ব্যক্তিত্ব লেখেন, চুঁচুড়ার ‘ভূদেব ভবন’-এ গিয়ে খোদ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের বংশধরের মুখে তিনি শুনেছেন যে ভূদেববাবুর স্বহস্তে লেখা ‘বন্দে মাতরম্’ গানের একটা খসড়া পাঠ ছিল। আর তাতে ছিল ‘বন্দে মাতরম্’ গানের ওই প্রথম সংস্কৃত বারো চরণই! বঙ্কিমচন্দ্র নাকি ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকেই সেই খসড়াটির একটি প্রতিলিপি পান। পরে আরও কয়েকটি চরণ যোগ করে তা প্রকাশ করেন বঙ্কিমচন্দ্র। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সেই খসড়া আর আমাদের পরখ করে দেখার অবশ্য উপায় নেই, কেননা অন্য কোনও এক বিখ্যাত গবেষক সেটি ‘ভূদেব ভবন’ থেকে আগেই আত্মসাৎ করেছেন! তবে সেই ‘বংশধর’-এর নামে উদ্ধৃত ওই কথাটার মধ্যে একটা গূঢ় ইঙ্গিত থাকে বলেই মনে হয়। তাহলে কি ভূদেব মুখোপাধ্যায় বা অন্য কোনও সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি ওই প্রথম বারো চরণের রচয়িতা? তা নাহলে বঙ্কিমই বা উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে রাখবেন কেন ওই প্রথম বারো চরণ সংস্কৃত অংশ? এই প্রশ্নের মোকাবিলার উপায় কী?
সাহিত্যের ‘ফেলুদা’রা হয়তো বলবেন, উপায় আছে। প্রথমে দেখো উনিশ শতকে উদ্ধৃতিচিহ্নের ব্যবহারের রকমসকম কেমন ছিল? শুধু অন্যের উক্তি সরাসরি উদ্ধৃত হলেই কি উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যবহৃত হত তখন? না কি অন্যক্ষেত্রেও তার ব্যবহার হত? তাছাড়া দেখো বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যবহারের কি কোনওরকম স্বাতন্ত্র্য ছিল?
‘সম্পাদক সমীপেষু’ বিভাগে দীনেশচন্দ্র সিংহ এইরকম একটা প্রশ্ন তুলেওছিলেন। তিনি বলেছিলেন, “উদ্ধৃতি চিহ্ন যদি স্বকীয় বা পরকীয় রচনা চেনার একমাত্র মাপকাঠি হয়, তা হলে অপরের রচিত আরও অনেক গান-কবিতা বঙ্কিম নিজের নামে চালিয়ে দিয়েছেন বলা যায়। ‘দুর্গেশনন্দিনী’তে গজপতি বিদ্যাদিগগজের গান, ‘কপালকুণ্ডলায়’ শ্যামাসুন্দরীর কবিতা, ‘মৃণালিনী’তে গিরিজায়ার গান, ‘বিষবৃক্ষে’ লম্পট দেবেন্দ্রের গান সবই উদ্ধৃতি চিহ্নবদ্ধ। গ্রন্থমধ্যে গান-কবিতা-ছড়া যা-ই থাকুক তাকে উদ্ধৃতি চিহ্নে আবদ্ধ করাই বঙ্কিমী রীতি। তিনি অপরের লেখা গ্রহণ করলে যেমন উদ্ধৃতিচিহ্ন দিতেন, নিজের লেখা গ্রন্থে গদ্য রচনার মাঝে মাঝে কবিতা বা গান—নিজের রচনা হলেও উদ্ধৃতিচিহ্ন দিতেন।”
এখানে অবশ্য পালটা একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। ‘বন্দেমাতরম্’-এ ব্যবহৃত উদ্ধৃতিচিহ্ন তো ‘গদ্য রচনার মাঝে’ কবিতাংশ জুড়ে দেওয়ার ব্যাপার নয়! গোটা রচনাটাই তো একটা কবিতা বা গান। পুলক চন্দ আবিষ্কৃত বিজয়লাল দত্তের ওই ‘জাগো আমার মা’ কাব্যগ্রন্থটিও উনিশ শতকে রচিত ও প্রকাশিত (১২৯৪ বা ১৮৮৭ সাল)। ওই বইতে উদ্ধৃতিসহ ‘বন্দেমাতরম্’ গানের একটি সম্পূর্ণ সংস্কৃত পাঠ পাওয়া যায়। তার আঠাশটি চরণ পুরোটাই উদ্ধৃতিচিহ্নবদ্ধ রেখেছেন সেখানে কবি। সংস্কৃত অংশটি কার রচিত তার উল্লেখ অবশ্য বিজয়লাল করেননি, তবে তাঁর বাংলা কাব্যের মধ্যে অপরের রচিত ‘বন্দেমাতরম্’ গানটি ‘প্যারেনথিসিস’ করবার সময় তিনি প্রচলিত নিয়মেই তাকে উদ্ধৃতিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু পাশাপাশি এও লক্ষ করবার বিষয়, কাব্যটির ‘সুহৃদ সকাশে’ অধ্যায়ে চার-চার চরণের দুটি স্তবকও (‘বৃটন-গরিমা রীপণ প্রবর—রাজিবে জগতে ইতিবৃত্ত ময়!’) তিনি উদ্ধৃতিবদ্ধ করেছেন যা কোনওভাবেই ‘পরকীয়’ রচনা নয়। খুব ভাল করে খেয়াল করলে দেখা যাবে বিজয়লালের ওই উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে কাব্যটির মধ্যে ‘স্বর’-এর রকমফের বোঝাতে। শেষোক্ত উদ্ধৃত দুটি স্তবকের আগের স্তবকটি ছিল: ‘শত কণ্ঠ-হতে এই শুভ দিনে/উথলিছে কিবা সুমোহন তান,/শুন শুন হেথা সবে এক প্রাণে/গাইছে আনন্দে তব যশোগান!’ এরপর একটি ‘ড্যাশচিহ্ন’(—) ব্যবহার করে সেই ‘আনন্দ যশোগান’টিই উদ্ধৃত হয়েছে দুটি স্তবকজুড়ে। এই যে উদ্দীপনাময় বর্ণনাংশ থেকে গানে ‘স্বরান্তর’— সেটা বোঝাতেই যে বিজয়লাল উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যবহার করেছেন তা অনায়াসে বোঝা যায়! ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসের প্রথম সংস্করণ এবং ‘বঙ্গদর্শন’ পাঠে ‘বন্দেমাতরম্’-এর মধ্যেও উদ্ধৃত আর অনুদ্ধৃত যথাক্রমে বারো আর ষোলো চরণের অংশদুটির মধ্যেও একরকম ‘স্বরান্তর’ আছে। তবে সে স্বরান্তর ভাষাগত। সেই স্বরান্তরের প্রকৃতিও একটু স্বতন্ত্র, হয়তোবা একটু জটিল।
‘সম্পাদক সমীপেষু’ বিভাগে দীনেশচন্দ্র সিংহ এইরকম একটা প্রশ্ন তুলেওছিলেন। তিনি বলেছিলেন, “উদ্ধৃতি চিহ্ন যদি স্বকীয় বা পরকীয় রচনা চেনার একমাত্র মাপকাঠি হয়, তা হলে অপরের রচিত আরও অনেক গান-কবিতা বঙ্কিম নিজের নামে চালিয়ে দিয়েছেন বলা যায়।
প্রকৃতপক্ষে ‘বন্দেমাতরম্’ গানের প্রথম বারো চরণের মধ্যে এগারোটি চরণ সংস্কৃত। আর ত্রয়োদশ চরণ (‘তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম’) থেকে পাওয়া যাচ্ছে সংস্কৃত আর বাংলার একরকম মিশ্রপ্রয়োগ। উদ্ধৃত অংশের মধ্যে দশম চরণে ‘অবলা মা কেন এত বলে’(প্রথম সংস্করণে ছিল ‘কে বলে মা তুমি অবলে’)-র মতো বাংলা বাক্য ঢুকে আছে যেমন তেমনি আবার অনুদ্ধৃত ‘তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম/তুমি হৃদি তুমি মর্ম’-এর মধ্যে মিশে আছে ‘ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে’-এর মতো সংস্কৃত পদবন্ধ। বস্তুত ‘ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী’ থেকে শেষপর্যন্ত পুরোটাই সংস্কৃত রচনা। দেশীয় ভাষা আর সংস্কৃত যখন এভাবে মিলেমিশে যেতে চায় কোনও রচনায় তখন তাকে বলে ‘মণিপ্রবালম্’। অধ্যাপক শিশিরকুমার দাশ একজায়গায় লিখেছেন, “বঙ্কিমচন্দ্র ‘বন্দেমাতরম্’ লিখেছিলেন—আধুনিক মণিপ্রবালে।” মণিপ্রবালের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, এ হল ‘ভাষা-সংস্কৃত-যোগম্’। আমাদের বক্তব্য, মণিপ্রবাল ‘ভাষা-সংস্কৃতি-যোগম্’ও বটে। দুটি ভাষিক সংস্কৃতির সম্মিলনের উদ্দেশ্যকে একরকম সাংস্কৃতিক আগ্রহ বলাই যায়। বৌদ্ধসাহিত্যে এরকম প্রভূত দৃষ্টান্ত আছে। সেই আগ্রহের একরকম শিল্পপ্রকরণ বলা যেতে পারে মণিপ্রবালকে।
‘বন্দেমাতরম্’-এর প্রথমে উদ্ধৃত সংস্কৃত চরণগুলি যেন গাম্ভীর্যে গাঁথা বিশেষ একটা শিলাস্তর। তারপর যেন তা বাংলা ভাষার সঙ্গে মিতালি করতে করতে ক্রমশ গড়িয়ে এসেছে। শেষাংশে সংস্কৃত শব্দ ও পদবিন্যাস থাকলেও ওই মিতালির সৌজন্যেই আর সেখানে উদ্ধৃতিচিহ্নের দ্বারা ভাষিক স্তরভেদকে প্রকট করে তোলা হয়নি। ‘বন্দেমাতরম্’ গানটি ভাল করে লক্ষ করলে বোঝা যায়, সংস্কৃতের গঙ্গোত্রী থেকে কীভাবে গানটির মধ্যে ক্রমশ বাংলা ভাষা উন্মোচিত হতে হতে আবার তা সংস্কৃতের লহরে ভেসে তবে তা মোহনায় গিয়ে মিশছে! এই যে ভাষিক স্তর-স্তরান্তরের সংকেত তা স্বকীয়-পরকীয় রচনাভেদের প্রশ্নে উদ্ধৃতিচিহ্ন প্রয়োগের সরল সমীকরণের চেয়ে নিঃসন্দেহে জটিল, কারণ প্রশ্নটা ভাষাতত্ত্ব থেকে ক্রমশ সংস্কৃতিতত্ত্বের দিকে আমাদের টেনে নিয়ে যেতে চায়।
প্রসঙ্গত এইখানে উপন্যাসধৃত গানটির পাঠমুলক সমালোচনা (Textual criticism ) নিয়ে ঝটিতি দু’ একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। আমাদের হাতের কাছে ‘সাহিত্য সংসদ’ প্রকাশিত যে উপন্যাসখণ্ডটি আছে তাতে গৃহীত হয়েছে ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ’ সংকলনের বঙ্কিমশতবার্ষিকী সংস্করণের পাঠ; যা বস্তুত ১৮৯২ সালে বঙ্কিমের জীবদ্দশায় প্রস্তুত পঞ্চম বা শেষ সংস্করণের পাঠ। তাতে দেখা যাচ্ছে, ‘আনন্দমঠ’-এর প্রথম খণ্ডের দশম পরিচ্ছেদে মহেন্দ্রের অনুরোধে ভবানন্দ যখন পুরো গানটি গান তখন তার পুরোটাই উদ্ধৃতিবদ্ধ থাকে। উপন্যাসে অন্যত্রও গানের খণ্ডাংশ উদ্ধৃতিবদ্ধই আছে—তা স্বকীয় রচনাই হোক বা পরকীয় পদাবলিই হোক। আবার প্রথম খণ্ড দ্বাদশ পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ‘ধীর সমীরে তটিনীতীরে’ পদাবলিটিতে উদ্ধৃতিচিহ্ন অনুপস্থিত। সুতরাং বোঝাই যায়, উদ্ধৃতিচিহ্নের ব্যবহারের ক্ষেত্রে রচনার স্বকীয়ত্ব বা পরকীয়ত্ব মানদণ্ড হয় না সবসময়। বরং স্বর-স্বরান্তরের ভাষিক ও সাংস্কৃতিক প্রশ্নটিকেও তার সঙ্গে যুক্ত করে নেওয়া দরকার।
শান্তিনিকেতনের সেদিনের সেই সান্ধ্য আড্ডার সূত্র থেকেই এই একটা ভাবনার তন্তুজালে জড়িয়েছিলাম। বুঝতে পেরেছিলাম, নিরীহ একটা উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যেও থেকে যেতে পারে কালচারাল ডিসকোর্সের অনেক উপাদান।
ছবি সৌজন্য: মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং Wikimedia Commons
মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিশ্বভারতীতে বাংলার অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ ভবনের মুখ্য সমন্বয়ক। বেজিং ফরেন স্টাডিস ইউনিভার্সিটির আমন্ত্রিত ভিজিটিং ফেলো হিসেবে ২০১৯ সালে তিনি চিন যান। বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি, চিন্তাজগৎ এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর চর্চার বিশেষ ক্ষেত্র। 'বাকিরাত্রির ঘুম' (কাব্যগ্রন্থ), 'কোথায় আমার শেষ' (উপন্যাস), 'গোষ্ঠীজীবনের উপন্যাস' (আলোচনাগ্রন্থ ), 'উপন্যাসের যৎকিঞ্চিৎ' (প্রবন্ধ সংকলন), 'রবীন্দ্রনাথ: আশ্রয় ও আশ্রম' (প্রবন্ধ সংকলন) ইত্যাদি তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ। বেশ কয়েকটি বইয়ের সম্পাদনাও করেছেন। বিচিত্র বিষয় নিয়ে পড়াশোনা তাঁর একমাত্র প্যাশন।