‘বাঙালি জীবনে পরীক্ষা’ এই শীর্ষক বিষয়ে একাধিক ডক্টরাল থিসিস লেখা হতে পারত। একটা সময় ছিল যখন নিস্তরঙ্গ মধ্যবিত্ত জীবনে পরীক্ষা ছিল একমাত্র মরসুমি থ্রিল। হাপিয়ালি, অ্যানুয়ালি- দুধের শিশুরাও শিখে যেত জন্মের পরবর্তী মুহূর্তে। ভাগ্যিস তখনো ইউনিট টেস্ট আরম্ভ হয়নি, না হলে অশান্তির চক্র আরও ছোট হয়ে আসত। পরীক্ষার রেজাল্টের দিন কৌতূহলী পাড়াপড়শি বা আত্মীয়স্বজন স্কুলে হানা দিয়েছেন, গেটের বাইরে প্রগ্রেস রিপোর্ট দেখবেন বলে, এ আমার স্বচক্ষে দেখা।
আমি আর বড়দা ফার্স্ট হতাম। ছোড়দার জায়গা এক থেকে দশের মধ্যে ঘোরাঘুরি করত। ওর রেজাল্টের দিন কারা এসে কীরকম সামাজিক লাঞ্ছনা করে যাবেন, তাই নিয়ে মা আতঙ্কিত হয়ে থাকতেন।এদের পত্রপাঠ বিদায় করে দিলে কী হয়, তা জানতে চেয়েও উত্তর পেতাম না। আমার মা ছিলেন অতিমাত্রায় সমাজভীরু। অব্যবহিত নিকটবর্তী সমাজই তাঁর কাছে সব। অবশ্য এটা প্রকৃত ভয় না ভান, তা জানি না।
মা-কে ছোটবেলা থেকে সন্ত্রস্ত দেখার একটা সুফল হয়েছিল। নিজের জীবনে ছেলেমেয়ের পরীক্ষার ফল আর সমাজকে গুরুত্ব না দিয়ে বাঁচতে পেরেছি। পরীক্ষাই জীবনের একমাত্র নিষ্ক্রমণের পথ, এটা আমাদের পদে পদে মনে করানো হত, কারণ চাকরির ক্ষেত্রে পরীক্ষার নম্বর ছাড়া আর কিছুই কাজে লাগবে না। ব্যবসার মূলধন আমাদের হাতের বাইরে। তাছাড়া ব্যবসাকে মনে করা হত টাকা বানানোর অস্ত পদ্ধতি।
বোর্ডের পরীক্ষা মানে তো একটা গা ছমছমে ব্যাপার। পরীক্ষার্থীর জন্য কাঁটাওলা মাছ চলবে না, বেরোবার আগে রসগোল্লা দেখা যাবে না, পাছে সেটা গোল্লা হয়ে খাতায় দেখা দেয়, কপালে দইয়ের ফোঁটা, মুখে দই, তারপর মায়ের আঁচলে হাত মোছা। দইঘটিত ব্যাপারগুলো আমাদের বাড়িতে ছিল না। মা কাউকে আঁচলে হাত মুছতে দেবেন, তা অকল্পনীয়। টিফিনটাইমে সন্দেশ, মিষ্টি দইয়ের খুরি, এমনকী হরলিকস-এর মুখ বাঁধা বোতলে দুধ নিয়ে অভিভাবকরা যে উৎকণ্ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতেন, এবং পরীক্ষার্থী বেরলে তার কাছ থেকে প্রত্যেকটি উত্তর জেনে মুখে মুখে নম্বরটাও বার করে ফেলতেন, সেইটা প্রতিবেশী রাজ্যের বিন্দাস কালচারে একটা বিরাট হাসির খোরাক জোগাত। এটা অবশ্য জেনেছিলাম বাংলা ছাড়ার পর।
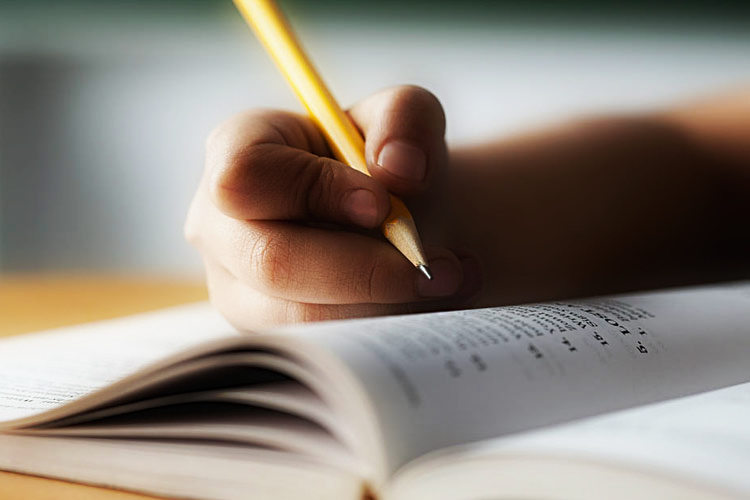
আমাকে স্কুলে ভর্তি করানোর পরই মা ফরমান জারি করলেন, ক্লাসে ফার্স্ট হোয়ো না যেন। তাহলে প্রত্যেক বছর আমি আশা করব, তুমি ফার্স্ট হও। ক্লাস টু-তে ভর্তি হয়েছিলাম সোজা। হাফ ইয়ার্লিতে বেশ কিছু ভুল করে এলাম, চেনা বানান। কিন্তু তাও ফার্স্ট হলাম। তদুপরি অঙ্কে আর ভূগোলে একশোয় একশো। অন্যরা হয়তো আরো বেশি ভুল করেছিল। ফলে, বিপদ ঘণ্টা বেজে উঠল। ক্লাস ফোরের অ্যানুয়ালে কোন কারণে সেকেন্ড। ওই একবারই।
পরের বছর প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন অনুষ্ঠানের পর স্টেজ থেকে নেমে এসে বাবা-মা কে পেলাম না। সন্ধেবেলা। স্কুলের গেটের কাছে গাছের নীচে ছোড়দা। আমাকে নিতে এসেছে। মা আসেনি? মাথা ধরেছে। শুয়ে আছে। পথে যেতে যেতে রহস্য ফাঁস করল।তুই সেকেন্ড হয়েছিস, তাই মার লজ্জা করেছে আসতে। ফার্স্ট না হলে আসবে না প্রাইজ ডে-তে। ক্লাস ইলেভেন, তারপর হায়ার সেকেন্ডারি। মা-বাবা এরপর সব প্রাইজ-ডে তে সসম্মানে এসেছেন। কিন্তু কিছু একটা কি ভেঙে গিয়েছিল বুকের ভিতর, আমার রেজাল্টই আমি, এই সত্য জেনে?
ক্লাস ইলেভেনে এই সংকট ঘনীভূত হল। নাইন, টেন, ইলেভেন, সব পরীক্ষায় ফার্স্ট, সব পেপারে সর্বোচ্চ নম্বর। তদন্ত কমিশনের ভঙ্গিতে আত্মীয়স্বজনরা এসে চা মিষ্টি খেয়ে রিপোর্ট কার্ড দেখতে চাইতেন। খুঁটিয়ে পড়ে দেখে বলতেন, তোদের বাংলা মিডিয়াম স্কুলের তো কোনও স্ট্যান্ডার্ড নেই, যা ইচ্ছে গাদাখানেক নম্বর দেয়। এরকম যদি বোর্ডে পাস তবে তো হায়ার সেকেন্ডারিতে ফার্স্ট হয়ে যাবি, হাহাহা। এঁরা কেউ ভাবতেন না, এইসব মন্তব্যের প্রভাব একটি ছোট মেয়ের মনে কী হতে পারে। নম্বর বা রেজাল্টের সঙ্গে মেধার বা মৌলিকতার কোনও সম্পর্ক নেই।
বোর্ডের পরীক্ষা মানে তো একটা গা ছমছমে ব্যাপার। পরীক্ষার্থীর জন্য কাঁটাওলা মাছ চলবে না, বেরোবার আগে রসগোল্লা দেখা যাবে না, পাছে সেটা গোল্লা হয়ে খাতায় দেখা দেয়, কপালে দইয়ের ফোঁটা, মুখে দই, তারপর মায়ের আঁচলে হাত মোছা। দইঘটিত ব্যাপারগুলো আমাদের বাড়িতে ছিল না। মা কাউকে আঁচলে হাত মুছতে দেবেন, তা অকল্পনীয়।
পরীক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে অন্তহীন অবগাহন করে আমার মনে হয়েছে, আমাদের দেশে ডিগ্রিপ্রাপ্ত অশিক্ষিতের সংখ্যা বেশি এই কারণে। ভালো নম্বর পেয়ে, না হলে কোনও মতে পরীক্ষা সাগর পার করিয়ে দেওয়াই লক্ষ্য। শিশুর কোনও গুণ, ক্ষমতা, আবিষ্কার করে তাকে বিকশিত হবার সুযোগ দেয় না মধ্যবিত্তের জন্য নির্দিষ্ট আটপৌরে স্কুলগুলি। আমার স্মৃতিশক্তি ছিল অব্যর্থ। আমি সব বিষয়ে একইরকম ছিলাম, এটাই ছিল আমার সাফল্যের উৎস। কিন্তু সেটাকে মেধা বলে মাতামাতি করার কোনও কারণ নেই। তবে এই সব সামাজিক উৎকণ্ঠা ও অত্যাচার থেকে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল গল্পের বই পড়া আর কবিতা লেখা। এই জানালা পথে আসত বাইরের সংবাদ, এক পৃথিবীর সন্ধান, যেখানে পায়ে শিকল পরে হাঁটতে হয় না। সন্দেশে লেখার স্বাধীনতা এমন এক আত্মবিশ্বাস তৈরি করে দিয়েছিল, যা আজও টাল খায়নি।
হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার তখনও মাস তিনেক বাকি। স্কুলপর্ব শেষ। শেষ পর্বে অঙ্কের টিচার ছিলেন না কয়েকমাস। কারও তত্ত্বাবধানে প্র্যাকটিস দরকার। ইংরাজিরও অবস্থা তাই। তবে ইংরাজির জন্য তো বাবাই আছেন। এই প্রথম বাড়িতে গৃহশিক্ষকের পদধূলি পড়ল। ছোড়দার স্কুলের অঙ্কের যাদুকর প্রবীণ বীরেন স্যার বাড়িতে এলেন। সব দেখে শুনে বললেন, কিন্তু ও পড়ে কোথায়? বলা হল, ও রান্নাঘরেই পড়ে, মানে আরও দুজন ছাত্র আছে তো। আপনি পড়াতে এলে ওকে জায়গা করে দেওয়া হবে। বীরেনবাবুর সেই বিস্মিত হতাশ মুখ আজও মনে পড়ে। বলছেন, ভালো ছাত্রী, একটা জায়গা তো দেবেন পড়ার?
শেষ পর্যন্ত বাড়িতে আসতে রাজি হলেন না অঙ্ক স্যার। ঠিক হল আমাকে আর এক বন্ধুকে একসঙ্গে পড়াবেন, হরিশ মুখার্জি রোডের এক গলির দোতলা ঘরে, যেখানে অন্য ছাত্ররা পড়ে। আমাদের সময় আলাদা, ছাত্রদের প্রবেশ নিষেধ।আড়াই মাসের মধ্যে দেখলাম স্যারের কলমে অঙ্কের যাদু। আমাদের কঠিন কঠিন আটকে যাওয়া অঙ্ক কেমন রুপোর কাঠি ছুঁইয়ে করে দেন। বীরেনবাবুকে নিয়ে অনেক গল্প ফিরত মুখে মুখে, কিংবদন্তীদের নিয়ে যেমন হয়।
একবার স্কুলের অঙ্ক পরীক্ষায় ইনভিজিলেশনের দায়িত্বে থাকা মাস্টারমশাই দেখলেন, এক ছাত্র পাশের জনের কাছ থেকে একটা উত্তর জানতে চাইছে। বললেন, “ওকে কি জিজ্ঞেস করছ? ওকে কি জিজ্ঞেস করছ? ও তো আছেই, হাতের পাঁচ। আমাকে জিজ্ঞেস করো। আমি যদি না পারি, তখন ওকে বোলো।” ‘ও তো আছেই হাতের পাঁচ’— এই কথাটা আমাদের পারিবারিক ভোকাবুলারিতে ঢুকে পড়েছিল।

হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার সময় আরো একটা বাড়তি আদর বরাদ্দ ছিল, ট্যাক্সিতে পরীক্ষার স্থল। যদিও তা বাড়ি থেকে খুব দূরে নয়, তবু বাস টাসে যাওয়া চলবে না। পরীক্ষার টিফিনটাইমে ওই স্কুলের ছাত্রীর দল আমাকে ঘুরে ফিরে দেখতে আসত। ফিসফিস করত নিজেদের মধ্যে— ওই দেখ বেলতলা স্কুলের ফার্স্ট গার্ল। পরীক্ষা চলাকালীন টিচাররাও এসে দেখে যেতেন, এবং নিজেদের মধ্যে আমার বিষয়ে মত বিনিময় করছেন বুঝতে পারতাম।এই অতিরিক্ত মনোযোগ ভালোই লাগত। মনে মনে জানতাম, এক থেকে দশের মধ্যে থাকাটা মোটেই অসম্ভব নয়। তবে পরীক্ষার রেজাল্টের বিষয়ে কিছুই বলা যায় না।
সেই সময় কলকাতায় একটি বড়সড় স্কুল সব শাখার মেধা তালিকায় বিরাজ করে এক দুর্ভেদ্য দেওয়ালের মতো। মফসসল বা গ্রামবাংলার দিন তখনও আসেনি। রেজাল্ট বেরিয়েছিল ১৯৭৩ সালের ৭ জুলাই। মনে আছে, রাস্তার দিকের ঘরের খাটে আমি চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছিলাম। স্কুল থেকে সহ-প্রধান শিক্ষিকা এসে ঘুম ভাঙালেন। তিনি নাকি বুঝতেই পারেননি, চাদরের মধ্যে আমি। এতটাই রোগা ছিলাম। মাকে বলছিলেন, ওকে ডাকুন। ওঠো ওঠো তুমি হিউম্যানিটিজে ফার্স্ট হয়েছ! ঘুম চোখে এই বিস্ময়কর খবর শুনলাম। স্কুলে যেতে হল তখনই। বড়দিদিমণি নাকি অধীর আগ্রহে পথ চেয়ে আছেন।
কথা ছিল আমাকে সব ক্লাসে ঘোরানো হবে। তা আর হল না। প্রবল উত্তেজনা। স্কুলের মাঠে নেমে পড়েছে হাজারখানেক ছাত্রী। তারা আমাকে যেভাবে আন্তরিক ভাবে মবিং করেছিল, ১৯৭০-এর দশকে রাজেশ খান্নাও তা কল্পনা করতে পারতেন না। সবুজ গেট একটু ফাঁক করে দারোয়ানজি আমাকে যখন বার করে আনেন, অনেকের হাতে আমার মাথা থেকে ছেঁড়া লম্বা চুলের গোছা। বাড়ি ফিরে দেখি, কালান্তর পত্রিকার এক তরুণ ফোটোগ্রাফার গলায় ক্যামেরা ঝুলিয়ে সিঁড়ির সবচেয়ে উপরের ধাপে দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞেস করছেন, এই বাড়ি থেকে একজন হায়ার সেকেন্ডারিতে ফার্স্ট হয়েছে, কোন ফ্ল্যাট জানেন?
বুঝলাম, এই বাজার বাড়ির গোলকধাঁধায় বেচারা শিখ গুজরাতি মারোয়াড়ি প্রতিবেশীদের মধ্যে দিয়ে পথ করতে করতে এতদূর এসেছে। তারা সবাই ক্লু লেস। লম্বা চুল, কিছুটা আবার ছেঁড়া, নিয়ে সামনে যেতে যেতে আমি কপালকুণ্ডলার মতো বললাম, আমার সঙ্গে আইস।
*ছবি সৌজন্য: Telegraph India, jgu.edu.com, Career India
কলকাতায় জন্ম, বড় হওয়া। অর্থনীতির পাঠ প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কবিতা দিয়ে লেখক জীবন আরম্ভ। সূচনা শৈশবেই। কবিতার পাশাপাশি গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, প্রবন্ধ, ছোটদের জন্য লেখায় অনায়াস সঞ্চরণ। ভারতীয় প্রশাসনিক সেবার সদস্য ছিলেন সাড়ে তিন দশকেরও বেশি সময়। মহুলডিহার দিন, মহানদী, কলকাতার প্রতিমা শিল্পীরা, ব্রেল, কবিতা সমগ্র , দেশের ভিতর দেশ ইত্যাদি চল্লিশটি বই। ইংরাজি সহ নানা ভারতীয় ভাষায়, জার্মান ও সুইডিশে অনূদিত হয়েছে অনিতা অগ্নিহোত্রীর লেখা। শরৎ পুরস্কার, সাহিত্য পরিষৎ সম্মান, প্রতিভা বসু স্মৃতি পুরস্কার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুবন মোহিনী দাসী স্বর্ণপদকে সম্মানিত। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমীর সোমেন চন্দ পুরস্কার ফিরিয়েছেন নন্দীগ্রামে নিরস্ত্র মানুষের হত্যার প্রতিবাদে। ভারতের নানা প্রান্তের প্রান্তিক মানুষের কন্ঠস্বর উন্মোচিত তাঁর লেখায়। ভালোবাসেন গান শুনতে, গ্রামে গঞ্জে ঘুরতে, প্রকৃতির নানা রূপ একমনে দেখতে।




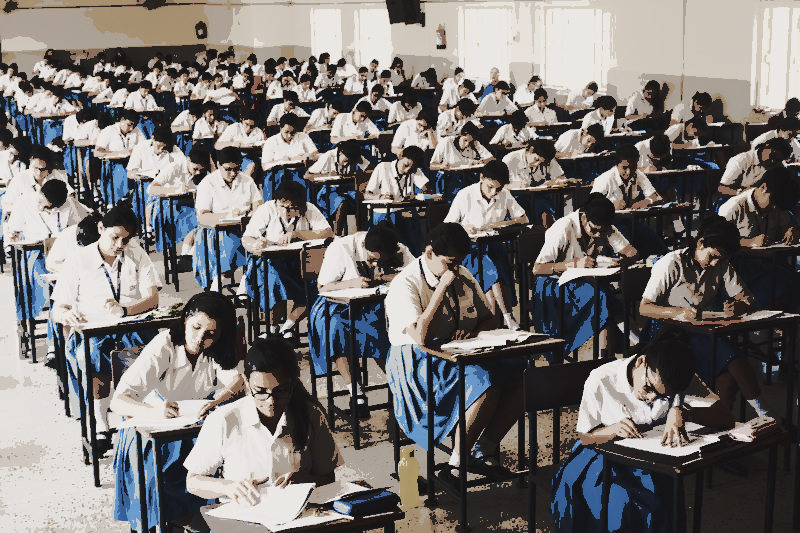





















One Response
স্বছন্দ কলম তার উদাহরণ আপনার কলম। আমরা প্রন্তিক জন, মাঝে মাঝে তব দেখা পাই। নমস্কার রইলো।