– খেরি কইরা লই৷ তুমি আর দুই পাতা পড়ো, দাদুভাই৷
– খেরি দিয়া কী হইব? যাইবেন তো কাটাবাজারে৷ কে দেখব আপনেরে? ওই বাজারে যারা আসে, তারা দশ-কুড়ি দিনেও খেরি করে না৷
– তোমার প্রত্যেক কথা এখন খোঁচামারা হইছে৷ কিরণ, আগে তো এমন ছিলা না! আমারে খোঁচাইয়া কী যে সুখ পাও!
– খোঁচা দিলাম কই? কইলাম যে খেরির কী দরকার? কাটাবাজার এমন কিছু মাইন্য সভা না যে খেরি লাগে৷ নয়টা বাইজ্যা গেছে৷ বাজার আইতে এগারোটা বাজব কম কইরা৷ কখন রান্ধন বসামু? বারোটা বাইজতে-না-বাইজতে ক্ষুধা আপনের প্যাটে পাক দিব৷ তাই কইলাম বাইরৈয়া পড়েন৷
– তুমি কেমনে জানলা যে ওই বাজারে দশ-কুড়ি দিনের অখেরি লোকজন ঘোরে?
– ক্যান? আমি কি ভুল কইছি? দোতারা বাজায় পরিতোষ৷ তারে দেখছি৷ একগাল দাড়ি৷ দারোগাবাবুর গা টিপতে আসে নয়ন৷ তার গালেও দাড়ি৷ ঘুগনি বেচে বনমালী৷ তার দাড়ি তো শ্যাখেগো মতন৷ আপনে কইছেন কাটাবাজারে অগো লগে আপনের চিনাজানা৷ ভুল কইছি?
– ঠিকই কইছ তুমি, কিরণ৷ কাটাবাজারে খেরি লাগে না৷
– এইবার মানেন৷ লাগতো কিশোরগঞ্জে৷ সেইখানে আপনের নাম ছিল৷ মান ছিল৷ পাঁচটা লোকের মইধ্যে আপনে পিরথক ছিলেন৷ কবিরাজ হিসাবে পিরথক খাতির ছিল৷ শিক্ষিত মানুষ হিসাবে কথার দাম ছিল৷ আর দেরি কইরেন না৷ বাইরৈয়া পড়েন৷
– দাদুভাই চলো৷ তোমার দিদিমায় ভুল কয় না৷ তবে প্যাঁচ মাইরা কয়৷ আসল কথাটা বুঝা যায়, ধরা যায় না৷ উকিলবাড়ির মাইয়া৷
– এখন যান৷ বাইর হয়েন৷ আমার বাপের বাড়িরে শত খোঁচাইলেও আর বাজার আইব না৷ সব ছত্রখান হইয়া গেছে৷ কে কই আছে কোনও ঠিকঠিকানা নাই৷
ষাট বছরেরও বেশি সময়ের দূরত্বে, কত নদী চলে গেছে মাঠে, কত মাঠ গেছে উন্নয়নে, উন্নয়নে হারিয়েছে বাংলা, বাতাস এখন গরমে নিজেই ছায়া খোঁজে, হারানো নদীখাতের পাতাল থেকে জল চেয়ে জিভ উঠে আসে মধ্যরাতে। সেই বালক আজও দাদু নলিনীকুমার বসু ও দিদিমা কিরণবালা বসুর সংলাপে দাঁড়াতে পারে, এখনও৷ হয়তো কিছু কথ্য শব্দ হারিয়ে গেছে অনভ্যাসে, ময়মনসিং-ফরিদপুর-পাবনার চেনা টান অচেনা হয়েছে অনাদরে, হারিয়েছে কিছু সম্ভাষণ, দুঃখ কষ্ট রাগ অভিমান অবিকল থেকে গেছে৷
কলকে থেকে তামাক ঝেড়ে থেলো হুঁকো তক্তপোষের পায়ার নীচে তিনটে ইটে কাত করে রেখে দাদু নলিনীকুমার বসু দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসা অবস্থায় বলেছিলেন দাড়িটা কামিয়ে নেবার কথা৷ কামাতে সময় লাগে তাঁর৷ কিশোরগঞ্জে একদিন অন্তর দাওয়ায় সেলুনের বাক্স নিয়ে আসতেন নিবারণ প্রামাণিক৷ মাঝরাতে লুকিয়ে চলে আসার আগের দুপুরেও এসেছিলেন৷
– তাইলে যাওনটাই চূড়ান্ত করলেন, কর্তা? গেল তো প্রায় সগগলেই৷ ভাবছিলাম কবিরাজ বইল্যা আপনেরে দুই-চাইর পাড়া থাকতে কইব৷ কলিমভাই কইল চুপেচাপে৷ সময় ফিরলে চইলা আইসেন৷ আমরা আছি৷ আপনার ঘরবাড়ি ঠিক থাকব৷
হয়তো ন’টা বাজে তখন৷ জামাইবাবা রেজ়ার দিয়েছে৷ ব্লেডও দিয়েছে৷ কিন্তু তাতে সুবিধা হয় না৷ নিজের হাতে কোনওদিন কামাননি৷ খুদে হাত-আয়নায় মুখ পুরো দেখা যায় না৷ তক্তপোশের পায়ায় আয়না রেখে ঝুঁকে পড়ে গাল দেখা বেশ কষ্টকর৷ দেরি তো হয়ই৷ রক্তপাত ঘটিয়ে ফেলেন নলিনীকুমার৷ সাবান ঘষা, দাড়ি চাঁছা এবং ফটকিরি ঘষা ইত্যাদি সারতে আধঘণ্টার বেশি সময় লাগে৷ কিরণবালা রান্না বসাবেন কখন?
আরও পড়ুন: বাংলালাইভের বিশেষ ক্রোড়পত্র: সুরের সুরধুনী
বস্তির আশপাশের ঘরে তখন উনুনে ভাত ফুটছে বা সম্বরার ঝাঁজ উঠছে৷ গুরুদাস চটি ফটফটিয়ে যেতে যেতে বলছে:
– আইজ কপালে দুঃখ আছে, নকুলের মায়ের যা চোপা, দোকানে যাইতে দশমিনিট দেরি হইলে সারাদিন গাইল্যায়৷ স্বামী জেলে৷ ঝাল মিটায় আমার উপর৷
সদ্যবিয়োনো রানিবৌদি কান্নাধরা গলায় বলছে:
– প্যাটে ভাত না পড়লে বুকে দুধ আসে ক্যামনে? তারে কত কইছি আমার মাছ মাংস লাগে না, প্যাট ভইরা ডাইল-ভাত য্যান পাই৷ সেইটাও জুটাইতে পারে না৷ পোড়াকপাল আমার৷ ভিক্ষায় বসুম আমি, কইয়া রাখলাম আপনেগো৷
কিরণবালা বসু তখন কলাই করা টিনের কাপ ধুতে ধুতে বলেছিলেন,
– এইবারে যান৷ ঘরে কিছুই নাই৷
বালক তখন পড়ছিল ‘ছিপখান তিনদাঁড় তিনজন মাল্লা বা ‘ঝড়জলের রাত্রিতে দামোদরের স্রোত সাঁতরাইয়া পার হইলেন মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগর৷’
– দাদুভাই, চল৷
বলে নলিনীকুমার তক্তপোশ আর কাঁথার মাঝখানে ভাঁজ করে রাখা একটা পাঞ্জাবি বের করেন৷ বাড়িওলা দারোগাবাবুর দেওয়া৷ দুটো পাঞ্জাবি আছে নলিনীকুমারের৷ একটা পশমের৷ দেশ ছাড়ার সময় যে দু-চারটে জিনিস আনা গিয়েছিল, তার একটি৷ গম রঙের, বড়ো শখের৷ দারোগারটা খদ্দরের৷ দেশাত্মবোধের সভার জন্য কেনা, একবারই পরেছিল দারোগা৷ পূর্ব পাকিস্তানে পাঞ্জাবি-ধুতি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ছিল৷ সেসব কবেই শত্রু-সম্পত্তি হয়ে গেছে৷ স্বাধীন ভারতে গুমোট বর্ষায় খদ্দর না শুকোলে পশম পরতে হয় নলিনীকুমারকে৷ সেটা অবশ্য বাইরে বেরলে৷ ঘরে নিমা বা ফতুয়া৷ দরজার মাথায় গুটিয়ে রাখা ধুতি নামিয়ে নেন নলিনীকুমার৷ সাদা খদ্দরের পাঞ্জাবি খুললে আট ফুট-বাই-আট ফুট ঘরে পাড়াগত পনেরোই আগস্টের গড়পরতা ভাষণ ছড়িয়ে পড়ে এবং খোলার চাল দিয়ে উড়ে যায়৷
– দাদুভাই, যাগো কাটাদেশ, কাটাবাজার আর ফাটাকপাল, তাগোরে কী কয়?
বালক চেঁচিয়ে বলে, ‘রিফুজি৷’ জবাবটা তার দাদুর কাছে শেখা এবং জোরে বলাটাও৷
কলকে থেকে তামাক ঝেড়ে থেলো হুঁকো তক্তপোষের পায়ার নীচে তিনটে ইটে কাত করে রেখে দাদু নলিনীকুমার বসু দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসা অবস্থায় বলেছিলেন দাড়িটা কামিয়ে নেবার কথা৷ কামাতে সময় লাগে তাঁর৷ কিশোরগঞ্জে একদিন অন্তর দাওয়ায় সেলুনের বাক্স নিয়ে আসতেন নিবারণ প্রামাণিক৷ মাঝরাতে লুকিয়ে চলে আসার আগের দুপুরেও এসেছিলেন৷
– কিরণ, সরিষার তেল লাগবো তো? ভাবছি বামুনপাড়ার ঘানি থেইকা আনুম বিকালে৷ শচীনের দোকানের তেলে গন্ধ ছাড়ে৷
কিরণবালা জবাব দেন,
– আনবেন তো অম্বলের শিশির মাপে৷ ওই শিশি দেইখা ঘানির লোকে আপনেরে লইয়া তামাশা করব৷ খাঁটি তেল খাওনের আউশ বাদ দেন৷
– দাদুভাই, থইলার মইধ্যে শিশি রাখো৷ সাবধানে৷ ভাইঙা না যায়৷
বালক বড়ো হয়ে পড়বে অন্নদাশঙ্করের ‘তেলের শিশি ভাঙলো বলে খুকুর পরে রাগ করো/তোমরা যে সব বুড়ো খোকা ভারত ভেঙে ভাগ করো, তার বেলা৷’
আসগর মিস্ত্রি লেনের বস্তি থেকে বেরিয়ে খানিকটা কাঁচামাটির পথ, বর্ষায় হড়কা কাদা হয়ে থাকে কিংবা পুকুর-উপচানো জলের নোংরা বিস্তার৷ এরপর পিচের পথ৷ পশ্চিমদিকে যেতে যেতে হিঙ্গন জমাদার লেন৷ উত্তরে বাঁক নিয়ে কিছুটা গেলে গোবরা রোড৷ আবার পশ্চিমমুখো চলা৷ বাঁদিকে কুষ্ঠ হাসপাতালের দশ-বারো ফুট উঁচু লাল পাঁচিল, তার ভেতরে কয়েকটা লাল বাড়ি ও খোলা মাঠ৷ লোহার গেটে ডান্ডাধারী দরোয়ান সারাদিন৷ বালক কুষ্ঠরোগী দেখেছে, তাদের আর্তনাদ শুনেছে, কোনওদিন হাসপাতালের মাঠে যাবার সাহস পায়নি৷

ডানহাতে যে বিস্তীর্ণ গোরস্থান, সেখানে সে একা একা কাটিয়েছে দিনের পর দিন সারাবেলা৷ দেখেছে কীভাবে কবর দেওয়া হয়৷ শ্রদ্ধানত মানুষেরা ঘিরে দাঁড়ায় প্রিয়জনের মৃতদেহ৷ এই শোক-আবহে বৃক্ষলতার সহৃদয় ভূমিকা থাকে৷ জামরুল-কালোজামের গাছে গাছে কেটেছে সারাদুপুর৷ মহুয়া ফুল খেয়ে ঝিমঝিম মাথায় শুয়ে থেকেছে সে বাঁধানো কবরের ওপর৷ পুকুর নির্জন হয়ে গেলে এপার ওপার করেছে দিগ্বিজয়ী একা৷ এসব অবশ্য আরো পরের ব্যাপার৷ ছোট থেকে দাদুর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতেই তার চোখে নেশা লেগেছে গোরস্থানের সবুজের৷
কুষ্ঠ হাসপাতাল আর গোরস্থানের সীমা শেষ হলে রেললাইন৷ উত্তরে শেয়ালদা স্টেশন৷ দক্ষিণে বালিগঞ্জ স্টেশন (পার্ক সার্কাস স্টেশন হয়েছে অনেক পরে) পেরিয়ে বহু দূরে দূরে ডায়মন্ডহারবার, লক্ষ্মীকান্তপুর৷ বালক তখন বালিগঞ্জটুকুই জানে৷ ভাবে কোনও একদিন সে যাবে৷ রেললাইন পেরিয়ে গোবরা রোড আরো এগিয়ে যায়৷ এটা বৈধ পথ৷ আর রেললাইন ধরে যে পথ গেছে সেটা নিষিদ্ধ৷ হয়তো সেদিন দাদুর পছন্দমতো বৈধ পথ ধরেছিল বালক৷ শুধু সেদিন কেন, বহুদিন৷ রেললাইনের গায়ে ‘গ্রেশাম অ্যান্ড ক্রাভেন৷’ কারখানা৷ ১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাসে এই কারখানায় আসবেন নকশালবাড়ি আন্দোলনের নেতা প্রমোদ সেনগুপ্ত ও অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী৷ বিপ্লব জাগ্রত দ্বারে৷ হেমাঙ্গ বিশ্বাস হাঁটতে হাঁটতে বুঝিয়ে বলবেন নকশালবাড়ি কী৷ বালকের বয়স তখন হবে ১৫ বছর৷ কারখানা পেরলে মালগাড়ি লাইন মাথার ওপর৷ তারপর উকিলবাড়ি ও আরো কিছু বাড়ি দুপাশে রেখে গোবরা রোড মিশবে ডাক্তার সুরেশ সরকার রোডে৷ এইখানে বড়ুয়ার জমজমাট চায়ের দোকান৷ বাঁদিকে গেলে চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল৷ ডানদিকে সেই কাটাবাজারের পথ৷
নলিনীকুমার তক্তপোশ আর কাঁথার মাঝখানে ভাঁজ করে রাখা একটা পাঞ্জাবি বের করেন৷ বাড়িওলা দারোগাবাবুর দেওয়া৷ দুটো পাঞ্জাবি আছে নলিনীকুমারের৷ একটা পশমের৷ দেশ ছাড়ার সময় যে দু-চারটে জিনিস আনা গিয়েছিল, তার একটি৷ গম রঙের, বড়ো শখের৷ দারোগারটা খদ্দরের৷ দেশাত্মবোধের সভার জন্য কেনা, একবারই পরেছিল দারোগা৷ পূর্ব পাকিস্তানে পাঞ্জাবি-ধুতি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ছিল৷ সেসব কবেই শত্রু-সম্পত্তি হয়ে গেছে৷
এই চারমাথায় ঝাঁপানো রাধাচূড়া গাছের গায়ে প্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাংলো বাড়ি৷ দোতলা থেকে প্রায়ই ভেসে আসে রবীন্দ্রসংগীত৷ এইখানে থাকেন পূরবী চট্টোপাধ্যায়৷ তানপুরার সঙ্গে গাইছেন৷ বালক গান শুনেছে, ফুটপাথে দাঁড়িয়ে, পূরবী চট্টোপাধ্যায়কে দেখে নাই৷ তাঁদের ফোক্সওয়াগন গলা খাঁকারি দিয়ে ছুটে গেছে৷ একটু এগোলে বাঁ হাতে নিরিবিলি গির্জা৷ নোনাফল ধরে আছে৷ ঝাউগাছ ভরে আছে৷ ব্যাপটিস্ট মিশন স্কুলের লাল ফ্রকপরা এক তরুণী কাঠের গেট আধখানা খুলে দাঁড়ায় বিকেলবেলা৷ একটু বড়ো হলে বালক এই তরুণীর বন্ধু হয়ে বড়দিনে গির্জায় আসবে বিনা পয়সায় কমলালেবু খেতে, কেক খেতে৷ এইখানে পি বড়ুয়ার কেকের ওয়ার্কশপ, হাওড়া মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, জগদ্ধাত্রী ভাণ্ডার এবং সিংহের মুখ-লাগানো পুরসভার টাইমকল৷

পশ্চিমমুখো বাঁক নিয়ে পথ হয়ে গেছে ডিহি শ্রীরামপুর রোড, পরে রামেশ্বর সাউ রোড, মিশেছে সিআইটি রোডে৷ সেটাও একদিন হবে ডাক্তার সুন্দরীমোহন অ্যাভিনিউ৷ ডাক্তার সুরেশ সরকার রোড যেখানে ডিহি শ্রীরামপুর রোডে মিশছে, সেই তেমাথায়, পুবমুখী একটা গলি, কাঁচাপথ, তালতলা নামের একচিলতে মাঠে গেছে, সেখানে বাংলার প্রথম রাজ্যপাল হরেন মুখার্জির বাড়ি। সিঁড়ি উঠেছে দশ-বারো ধাপ, তারপর চাতাল। বালক পরে জেনেছে যে এই স্থাপত্য বাংলার বিশেষ কয়েকটি বাড়িতে আছে বড়ো মাপে৷ চাতালের দু’পাশে বসবার বেদি, সেখানে বসে থাকতেন বঙ্গবালা, হরেন মুখার্জির বিধবা। কোনও আঘাতে এলোমেলো হয়ে গেছে তাঁর স্মৃতি ও জীবনযাপন, একা হাঁটতেন তালতলার ঘাসমাটিতে খালিপায়ে৷ তালতলার গলিতে কয়েক ঘর মুসলমানের বসতি৷ যা ১৯৬৪-র দাঙ্গায় আগুনে পুড়বে৷ বাসিন্দারা উৎখাত হবেন৷ অনেকটা জমি দখল করবে জনৈক বড়দা, গান্ধীবাদী সমাজকর্মী৷ তালতলার পাশে তৈরি হবে সিআইটি কোয়ার্টার৷ একদিন এই পথে হাঁটবেন বরেণ্য চিন্তাবিদ গোপাল হালদার৷
তেমাথা থেকে কাটাবাজারের দিকে হাঁটেন নলিনীকুমার৷ বালক তাঁর সঙ্গী৷ এইখানে পথের বাঁ-দিকে পুরোটাই টানা বস্তি, অসংখ্য গলির ধাঁধাপাড়া৷ মজার একটি বাড়ি, ইটের একতলার ওপর কাঠের দোতলা, কয়েকটি খ্রিস্টান পরিবারের বাস। ছোটো স্কার্ট-পরা মেয়েরা ভাঙা ইংরেজিতে কথা বলে, ফুটপাথের দোকানে নাস্তা কেনে। ‘মে গড ব্লেস ইউ” বলে কোনও খ্রিস্টীয় কল্যাণ সমিতির জিপ আসে দুপুরে খিঁচুড়ি আর ঘ্যাটের পেল্লায় হান্ডা নিয়ে, ছুটে আসে সেই মেয়েরা থালা-বাটি নিয়ে, রাত গভীর হলে তারা নেশা করে গলা ছেড়ে গান গায়, গিটার বাজে৷ এরা অনাথ সন্তান বলে জেনেছে বালক পরে, মা আছেন বাবা নেই৷
– দাদুভাই, মায়ের লগে দেখা করবা নাকি?
এইখানে থার্টিনাইন বাই ওয়ানে বালকের মা থাকেন৷ বোনও থাকে৷ বালক হয়তো বলল, ‘পরে আসুম৷’ এরপর বাঁ-দিকে মসজিদ, ফুলবাগান-তাঁতিবাগান-বেনেপুকুর থেকে নমাজ পড়তে আসে মানুষ৷ মসজিদের গায়ে আস্তাবল, সার সার ঘোড়ার গাড়ি৷ শেয়ালদা স্টেশনে ভাড়া খাটে৷ ১৯৬৪-র দাঙ্গায় এই মসজিদ-লাগোয়া গোলামের বস্তিও ছাই হয়ে যবে৷
– দাদুভাই, ডাইনদিকে ক্রিস্টোফার রোড৷ তোমার দিদিমা এইখানে অকল্যান্ডের দুধ ধরতে আসে৷ রোদ্রে পুইড়া লাইনে খাড়াইয়া কোনওদিন পায়, কোনওদিন পায় না৷ রিফুজিগো লাইন রোজ বাড়তেয়াছে৷ এইখানে কাজি নজরুল ইসলাম থাকেন৷ একবার জন্মদিনে তোমারে নিয়া আসুম৷ কাউরে চিনতে পারেন না, কথাও কইতে পারেন না৷
পরে, বালক তখন চোদ্দো কি পনেরো, দেখবে এই পথে ঝিমলাগা রাতে রিকশা থেকে নামছেন প্রমত্ত কাজী সব্যসাচী৷

গোলামের বস্তির উলটোদিকে আচার কারখানার অফিস৷ লৌহকপাটের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় কেয়ারি-করা বাগান৷ এটাকেই সাহেববাগান বলেন স্থানীয়রা৷ কয়েক পা দূরে বিরসুলহাট৷ চামড়ার গন্ধ আর হাটের কলরব৷ গা দিয়ে বেচুলাল রোড৷ এই পথ দিয়ে কি হেঁটে আসতেন আপনভোলা কবি সিদ্ধেশ্বর সেন?
– দাদুভাই, এইটা হইল দেববাবুর বাজার৷ যাগো পয়সা আছে, তারা কেনে এই বাজারে৷ আমাগো নাই, আমরা যাই কাটাবাজারে৷ পরিতোষ, কেমন আছো? দোতারা ছাড়ো নাই তো? একসের আলু দাও৷ নারুরে দেখি না কেন? বেগুন নিতাম৷ হরিশে দাম কমায় না একটুও৷
কাটাবাজার মানে ছাঁট সবজির বাজার৷ পোকায় খাওয়া, দাগধরা, কিছুটা পচে যাওয়া সবজি এখানে নষ্ট অংশ বাদ দিয়ে বিক্রি হয়৷ বাসি, শুকনো, নেতিয়ে পড়া শাক-ডাঁটাও মেলে৷
– দাদুভাই, প্যাঁড়া খাইবা? পোলের ওপর নারান বসে৷ ভালো প্যাঁড়া৷
বালক সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে জানায় সে খাবে না৷ যদিও তার খাবার ইচ্ছে আছে৷ খাবে না৷ মা বলে দিয়েছে, দাদুর কাছে কিছু চাইবি না৷ দিলেও নিবি না৷ দাদু পয়সা পাবে কোথায়?
বেলা বেড়েছে৷ রোদ চড়েছে৷ নলিনীকুমার হয়তো বললেন,
– চলো, আজ নিষিদ্ধ পথ দিয়া ফিরি৷
নিষিদ্ধ পথ মানে রেললাইন৷ দুর্ঘটনা অর্থাৎ ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু বা অঙ্গহানির আশঙ্কা আছে বলে এটা নিষিদ্ধ পথ৷ তবু লোকজন যাতায়াত করে পথসংক্ষেপ করবার জন্য৷ গরিব মানুষ কতভাবে যে বাঁচে, বালক দেখেছে বড়ো হতে হতে৷ রেললাইন নলিনীকুমারের কষ্টের পথ৷ কারণ, দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়ে তিনি ট্রেনে চেপেছিলেন৷ শেয়ালদা স্টেশনের নরকে দিন কাটিয়েছেন স্ত্রী-কন্যা-নাতিকে নিয়ে৷ আশা ছিল একদিন ফিরে যাবেন দেশে, ট্রেনে চেপেই৷
– দাদুভাই, এই লাইন আমাগো দেশে গেছে৷ কিন্তু আমাগো তো দেশ আর নাই৷ তাই আমাগো ট্রেনও নাই৷ সাবধানে চলো৷ সর্বদা নিম্নদিকে চাহিয়া চলবা৷ মাঝেমাঝে সম্মুখ দেখিয়া লইবা৷ আবার নিম্নদিকে চাহিবা৷ ঊর্ধ্বদিকে চাহিয়া পথ চলিলে উস্টা খাইয়া পড়বা৷
রেলপথে হাঁটতে বালকেরও ভালো লাগে না৷ ট্রেনের ভয় তো আছেই৷ এই পথে সেই ভয়ংকর জায়গাটা৷ মালগাড়ির ব্রিজের নীচে, যেখানে প্রায়ই কাটা মুন্ডু পড়ে থাকে আত্মঘাতী মানুষের৷ একটা লোভও আছে এই পথে৷ এই পথেই পাওয়া যায় ছবিছাপা পাতা৷
– ছবি নয়, দাদুভাই, ম্যাপ৷ এগুলি মানচিত্র৷ নানা দেশের৷ আমাদের মানচিত্র নাই৷ হারাইয়া গেছে৷
বালক কুড়িয়ে নিত ছবিছাপা কাগজ৷ নৌকো বানাবে৷ এরোপ্লেন বানাবে৷ পিস্তল বানাবে৷ কার্তিকদাকে বললে বানিয়ে দেবে৷ শিখিয়ে দেবে৷ গোরস্থানের গায়ে অ্যাটলাসের ছাপাখানা থেকে মানচিত্ররা উড়ে উড়ে আসে৷ বালক কুড়ায়৷ (চলবে)
পরবর্তী পর্ব ১৩ এপ্রিল ২০২২ প্রকাশিত হবে।
ছবি সৌজন্য: India Today, Facebook, Flickr
মধুময়ের জন্ম ১৯৫২ সালে পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহে, কিশোরগঞ্জে। লেখাপড়া কলকাতায়। শৈশব-যৌবন কেটেছে স্টেশনে, ক্যাম্পে, বস্তিতে। গল্প লিখে লেখালেখি শুরু। পরে উপন্যাস। বই আখ্যান পঞ্চাশ, আলিঙ্গন দাও রানি, রূপকাঠের নৌকা। অনুসন্ধানমূলক কাজে আগ্রহী। পঞ্চাশের মন্বন্তর, দাঙ্গা-দেশভাগ, নকশালবাড়ি আন্দোলন নিয়ে কাজ করেছেন। কেয়া চক্রবর্তী, গণেশ পাইন তাঁর প্রিয় সম্পাদনা। প্রতিমা বড়ুয়াকে নিয়ে গ্রন্থের কাজ করছেন চার বছর। মূলত পাঠক ও শ্রোতা।



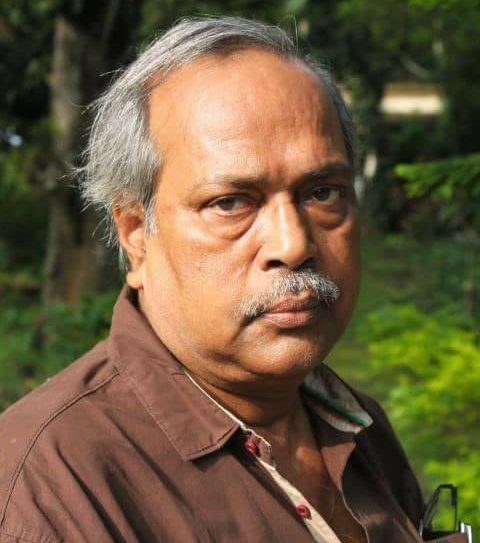






















3 Responses
বড়ো ক্যানভাসের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শুরু হল। ভালো লাগছে।
যে দেশটা আমাদের ছিল, যে দেশের কথা বাবা মা ঠাকুমার মুখে বারবার শুনতাম , সেই স্বপ্নের দেশের আরো স্বপ্নীল ইতিবৃত্ত শুনে চোখে জল তো আসেই, তার সঙ্গে একটা রাগ জন্মায় ,,,এই ভেবে যে দেশভাগের জন্য দায়ী যারা সেই ঘাতক রা আজো বহাল মসনদে। শেষ হলো আমাদের জীবন। শিকড় হীন আগাছা হলাম। এর শেষ কোথায় ??? ভালো লাগলো। অনেক ধন্যবাদ স্যার!!!
বালকের বোনের কথা বলা হয়েছিলো প্রথমে। কিন্তু পরে এই বোনকে আর দেখা যাচ্ছেনা কেন ?