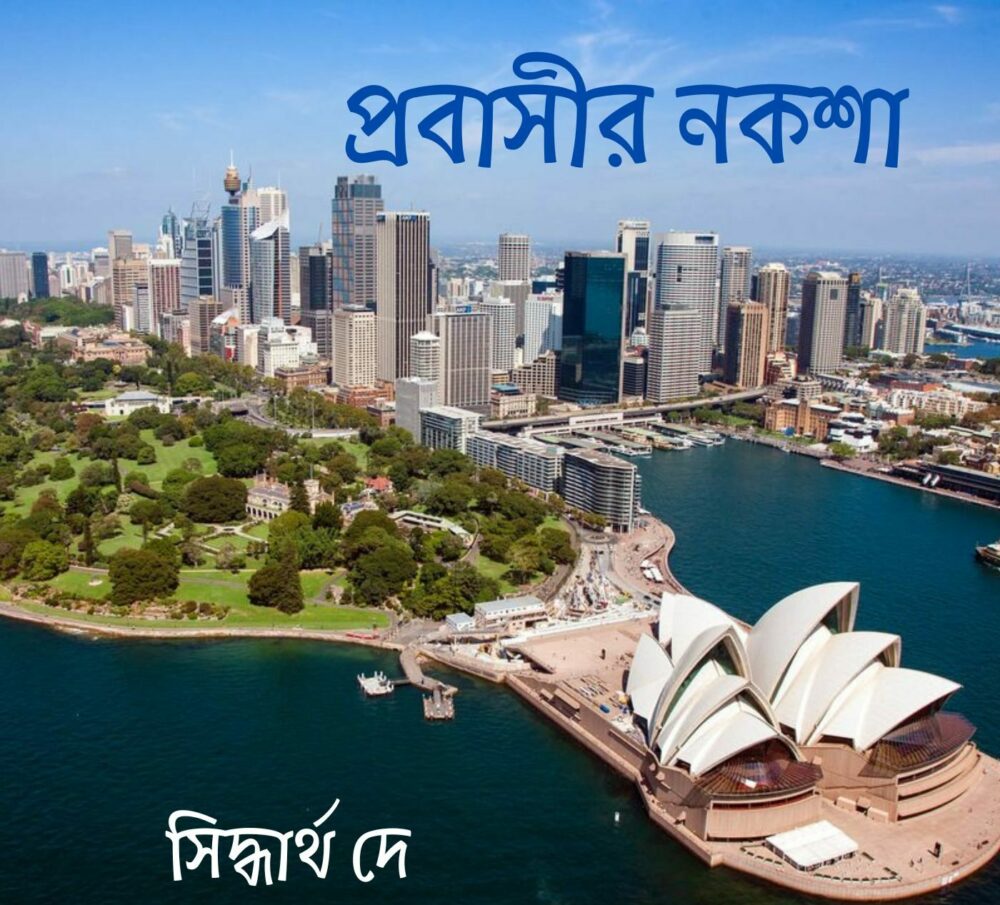পথের শেষে
গত পর্বে সিয়ারামের কথা লিখেছিলাম…
যাঁরা সে লেখা পড়েননি, তাঁদের সুবিধার্থে জানাচ্ছি সিয়ারাম আমার খড়গপুরের সহপাঠী। এক সঙ্গে পাঁচ বছর পড়েছি। কাছাকাছি রোল নম্বর হওয়ার জন্য বেশ কিছু ল্যাবেও পার্টনার ছিল। সুন্দর, নির্বিরোধী ছেলে। ওর জন্ম বিহারের প্রত্যন্ত গ্রামের এক অবস্থাপন্ন কৃষক পরিবারে। খড়গপুরে পড়ার শুরুতেই বাবাকে হঠাৎ করে হারায়। মায়ের জোরাজুরিতে ফার্স্ট ইয়ারের শেষেই বিয়ে করতে বাধ্য হয়। পাত্রীর নাম রেখা— কথাবার্তায় বুঝতে অসুবিধা হয় না, প্রায় পঞ্চাশ বছরের দাম্পত্যজীবনের পরেও রেখাজির সঙ্গে প্রেম আজও সজীব।
বছর দুয়েক আগে দেশে–বিদেশে ছড়ানোছেটানো সহপাঠীদের নিয়ে একটা ওয়াট্স্যাপ গ্রুপ বানিয়েছে আমেরিকা নিবাসী চোর। সাংঘাতিক রকমের ভালো ইঞ্জিনিয়ার চোরের পোশাকি নাম রাজশেখর, কিন্তু ঐ নামে ওকে অনেকেই চিনবে না। সেই সূত্রেই সিয়ারামের সঙ্গে পুনর্যোগাযোগ। ঘুরে–ফিরে সব বন্ধুদেরই ফোন করে এই সহজ সরল মানুষটি।
সিয়ারামের প্রবাসী হওয়ার ইতিহাস একটু অন্যরকম। দেশেই কাজ করেছে প্রায় পঁচিশ বছর। বরোদায় লারসেন টোবরোতে। কোনও কারণে বনিবনা না হওয়ায় চাকরি ছেড়ে অভিবাসী হয়ে কানাডায় পাড়ি দেয় ২০০৪ সালে, প্রায় ৫০ বছর বয়সে। সেই সময়ে দুই পুত্র প্রায় প্রাপ্তবয়স্ক। অত বেশি বয়সে বিদেশে গেলেও স্রেফ মেধা (ও বিহারের উচ্চমাধ্যমিকে একদম উপরের দিকে ছিল), দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সিয়ারাম আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। দুই পুত্রও বাবার মেধা পেয়েছে, দুজনেই ভালো কাজ করে।
কথায় কথায় একটা অদ্ভুত ব্যাপার শুনলাম। দুই পুত্র বাবা–মায়ের সঙ্গে কানাডায় আসার পর আর কোনওদিন দেশে ফিরে যায়নি। প্রায় প্রতিবছর দেশে যাওয়া বাবা–মার সঙ্গ দেওয়ার অনুরোধের বাঁধা উত্তর: তোমরাই ঘুরে এস, আমরা এখানে বেশ আছি!

ক্যানবেরা তথা অস্ট্রেলিয়ার অন্যান্য শহরের পরবর্তী প্রজন্মের কথায় আসি। এদের অনেকেরই জন্ম এদেশে, বাকি অধিকাংশই বেশ অল্প বয়সে বাবা মায়ের সঙ্গে এসেছে। সিয়ারামের পুত্রদের মতো বয়সে আসা কাউকে আমি জানি না।
আমরা দেশ ছেড়েছি নানা কারণে। অন্যতম কারণ, তথাকথিত উন্নত দেশে অনেক বেশি অর্থ উপার্জনের প্রত্যাশা। আর্থিক স্বচ্ছলতা ছাড়াও আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ার জীবনের নানা ধরণের স্বাচ্ছন্দ আর একটা বড় কারণ।
তবু দেশকে কিন্তু ভুলতে পারি না। থেকে থেকেই বুড়ি ছুঁয়ে আসি। শিশু সন্তানরাও দাদু ঠাকুমার সান্নিধ্য, আদর পায়। বাড়িতে অধিকাংশ পরিবারই ছেলেমেয়েদের বাংলা শেখানোর চেষ্টা করে। কম–বেশি সফলও হয়। কিছু শিশুর অন্য ভাষা শেখায় এক ধরনের সহজাত ক্ষমতা থাকে— তারা মোটামুটি ভদ্রস্থ বাংলা শিখে যায়। নিদেনপক্ষে অক্ষরজ্ঞান হয় অনেকেরই। কিছু বাঙালির কথা আলাদা, যাঁদের বাংলাটা ঠিক আসে না। এঁরা নিজেরাই (সোনারপুর বা দমদমে বড় হয়ে থাকলেও) যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাতৃভাষা ভুলে ময়ূরপুচ্ছধারী কাক হতে চান। সন্তানদের মানুষ করেন সাহেব বানাবার আকাঙক্ষা নিয়ে।
রবীন্দ্র–জয়ন্তী, নববর্ষের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এই বিদেশজাত বা বিদেশে বড় হওয়া শিশুরা বেসুরো গলায়, বিদঘুটে উচ্চারণে সমবেত কণ্ঠে গায়:
ডনো ডান্যে পুসপে বড়া, আমাডের এই বাসুনডারা…

আসলে গাছেরও খাওয়া, তলারও কুড়োনো দুটো এক সঙ্গে হয় না। বিলেতের মাটিতে হিমসাগর ফলানো যায় না।
পশ্চিমী সমাজে (ব্যতিক্রম অবশ্যই থাকে) ছেলেমেয়েরা ১৪–১৫ বছর বয়স থেকেই খুব স্বাধীনচেতা হয়ে যায়। তাদের ব্যক্তিগত জীবনে বাবা–মায়ের বিশেষ স্থান থাকে না। বাংলায় কথা বলা কমতে থাকে, মিশে যায় সে দেশের মূলস্রোত জীবনে। প্রায়শই (বিশেষ করে দেখেছি বাঙালিদের, দক্ষিণ ভারতীয়রা বেশ অন্যরকম) স্থানীয় ছেলেমেয়েদের সঙ্গে প্রেম হয়— হাজারবার ‘ডার্লিং’,’হানি’ বলতে শিখে যায়।
মোদ্দা কথা, এরা আর ভারতীয় থাকে না। সিয়ারামের সন্তানদের মতোই বাবা-মায়ের দেশের ভাষা, সংস্কৃতির প্রতি নিরুৎসাহী হয়ে ওঠে।
***
বাল্যবন্ধু তথাগত একবার ১৯৯৬ সালে আমার ক্যানবেরার বাড়িতে এসেছিল। ছেলে-মেয়েরা তখন খুবই ছোট। ততদিনে একটু থিতু হয়ে বসেছি— দেশ থেকে বেশ কিছু বাংলা বই নিয়ে এসেছি। প্রসঙ্গটা সেভাবে মনে নেই, তথাগত কথায় কথায় বলেছিল: “তুই কি মনে করিস তোর ছেলেমেয়ে মুজতবা আলীর রসোপলব্ধি করতে পারবে?”
আমরা, বিশেষ করে চন্দনা— খুবই চেষ্টা করেছিলাম ভারতীয় নাচ, গান, বাজনা, সাহিত্যের সঙ্গে সন্তানদের পরিচিত করাতে। বলাই বাহুল্য, খুব একটা সফল হইনি।

একটা গল্প আগেও বলেছি, আবার বলছি। কলেজের তিন বছরের সিনিয়র গৌতম বিশ্বাসও প্রায় একই সময়ে অস্ট্রেলিয়াতে আসে অভিবাসী হয়ে। সেই সময়ে বড় রকমের অর্থনৈতিক মন্দা চলছে, বেকারত্বের হার ১১ শতাংশ। দরখাস্ত করেই চলেছি, কোনও ফল হচ্ছে না।
বীতশ্রদ্ধ গৌতম এক সরকারি দপ্তরের উচ্চপদস্থ অফিসারের সঙ্গে দেখা করে। উত্তেজিতভাবে বলে: “আপনাদের দেশে চাকরি নেই, আমাদের আসতে দিয়েছেন কেন?”
ভদ্রলোক মুচকি হেসে উত্তর দেন: “আপনাদের আমরা ধরে–বেঁধে আনিনি। সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছেয় এসেছেন আপনারা। এখন মন্দা চলছে, কিন্তু লিখে রাখুন আপনার মেধা এবং অভিজ্ঞতা নিয়ে বরাবর বেকার থাকবেন না। কিছুদিন বাদে জীবনটা অন্যরকম হয়ে যাবে। তবে একটা কথা মনে রাখবেন, আপনাদের কী হল তাতে আমাদের কিস্যু যায় আসে না। আমরা চাই আপনাদের সন্তানদের, ধরে নিচ্ছি ওরা আপনাদের মেধা পাবে। দেশটার মানবসম্পদ বৃদ্ধি পাবে!”

ষাটের দশকে অস্ট্রেলিয়া থেকে ভালো জাতের ষাঁড় আনানো হত এদেশের গোরুর মান বৃদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে। বর্তমানে ভারত আমাদের মতো মনুষ্যরূপী ষাঁড়দের অস্ট্রেলিয়াতে রফতানি করছে। দেশটার মানবসম্পদ বাড়ছে।
আমরা ঠিক তাই করেছি। সন্তানদের উৎসর্গ করেছি পাতানো দেশের মূলস্রোতে।
প্রথমদিকের সংগ্রামের পর প্রত্যাশিত স্বচ্ছলতা আসে সবারই। অনেকেরই একাধিক বাড়ি, মহার্ঘ সব গাড়ি, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সঞ্চয়— সবই হয়ে যায়। সন্তানরাও বড় হয়ে যায়। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়। পশ্চিমী সমাজের আদত অনুযায়ী একদিন পারিবারিক গৃহ ছেড়ে নিজেদের জীবন শুরু করে।
শূন্য গৃহে বৃদ্ধ দম্পতি একে অপরের দেখভাল করেন। ভাগ্যবানদের সন্তানরা খোঁজখবর রাখে। অভাগাদের জোটে মাতৃদিবস, পিতৃদিবসে আদিখ্যেতা মেশানো একটা বার্তা এবং দায়সারা উপহার।
এই বৃদ্ধদের অবস্থা হয় সেই ধোপার কুকুরের মতো— না ঘর কা, না ঘাট কা। মন পড়ে থাকে এক স্বপ্নমাখা অতীতে। কিন্তু উন্নত দেশের সুযোগ–সুবিধা ছেড়ে বহুদিন আগে ফেলে আসা জন্মভূমিতে ফিরতে সাহস হয় না।
সামনে এক অন্ধকার সুড়ঙ্গ, যার শেষে একটি দরজা। ফাঁক দিয়ে একটা হালকা আলোর আভা দেখা যায়। কী আছে সেই দরজার ওপারে?
জন্ম ১৯৫৫ সালে উত্তর কলকাতার শ্যামবাজারে। জীবনের অর্ধেকটা প্রবাসে কাটালেও শিকড়ের টান রয়েই গেছে। অধিকাংশ স্বপ্নের ভাষা আজও বাংলা-- প্রেক্ষাপট কলকাতা। আই আই টি খড়গপুরের মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের স্নাতক হলেও অবসরজীবন জুড়ে আছে বাংলা সাহিত্য। আর টুকটাক কিছু লেখালেখি।