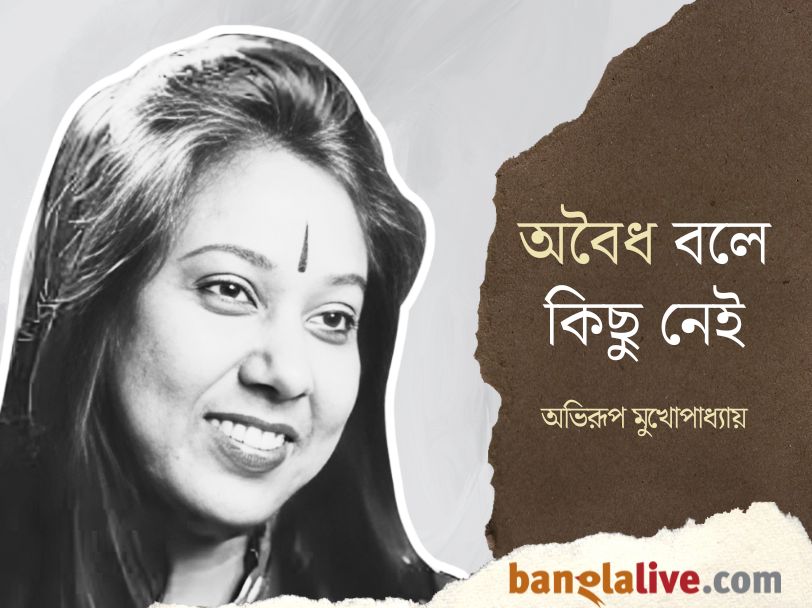(Mallika Sengupta)
আজ থেকে বেয়াল্লিশ বছর আগে, ১৯৮৩ সালে, কৃষ্ণনগরের এক ভাঙা প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছিল শীর্ণকায় এক কবিতাপুস্তিকা। যিনি লিখেছিলেন সে-পুস্তিকা, তিনি তখনও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্বের ছাত্রী। বইটির পরিচিতিসূত্রে ব্লার্বে লেখা ছিল এই কথাগুলি:
একদিকে রয়েছে প্রাক-আর্য সময়ের খরগোশ, টোটেমদেবতা, বলি, অন্যদিকে এসেছে কিশোর শ্রীরাম, অগাস্ট কোঁত, বৈবস্বত। কিন্তু এইসব ছাপিয়ে ছব্বিশ পাতার এই সামান্য বইটিতে, মূর্ত হয়ে উঠেছে এক আসন্ন ভবিষ্যতের প্রতি মায়া— যেন যাযাবর হয়ে বেরিয়ে না পড়তে হয় আমাদের। (Mallika Sengupta)
বইটি সম্পর্কে এই প্রত্যেকটি অভিধাবাক্য হয়তো সত্য। কিন্তু এর বাইরেও, আরও বিচিত্র সব চিন্তার জাদু-মুহূর্ত নিয়ে ক্ষুদ্রকার এ-পুস্তিকার মধ্য দিয়ে বাংলা কবিতায় প্রবেশ করেছিলেন এমন একজন কবি, যিনি তাঁর কবিতাজীবনে স্পষ্টত দুটি ভিন্ন স্বরে কবিতা লিখে গেছেন। প্রথম জীবনে, সংকেতধর্মের অতলে প্রতিস্থাপিত ছিল তাঁর লেখা। পরবর্তী সময়ে তিনি সজোরে, প্রত্যক্ষ আঁচড়ে, সম্পূর্ণ নতুন-পথে বলতে শুরু করেছিলেন মনের প্রতিপাদ্য অভিজ্ঞতাকে।
আরও পড়ুন: প্রত্যেক মুহূর্তে তুমি কবি
সেদিনের সেই কলেজ পড়ুয়া সমাজতত্ত্বের ছাত্রীর নাম, মল্লিকা সেনগুপ্ত। আর, তাঁর শীর্ণকায় পুস্তিকাটি হল, ‘চল্লিশ চাঁদের আয়ু’। সে-বইয়ের ‘মীনরাশি, কলিকাল’ নামের লেখাটিতে মল্লিকা লিখছেন:
করোটির চোখে দেখো দু-নলা বন্দুক, জটিল জগৎ
দুধের হাঁড়িতে ভেসে উঠে ডুবছে আবার ঘনশ্যাম পেঁচা
পূর্ণিমা সুগোল হলে মীনরাশি, কলিকাল। কাঁসর বাজল
জন্মের মুহূর্তে কার? ছেলে নয়, রৌপ্যমুদ্রা প্রসব করেছে
ঘোষাল বাড়ির বউ। কী নাম রাখবে? তবে শ্বশুরের সাথে
ওঠা-বসা মিথ্যে নয়, বাঁকানো পরিখা বেয়ে নেমেছিল স্রোত?
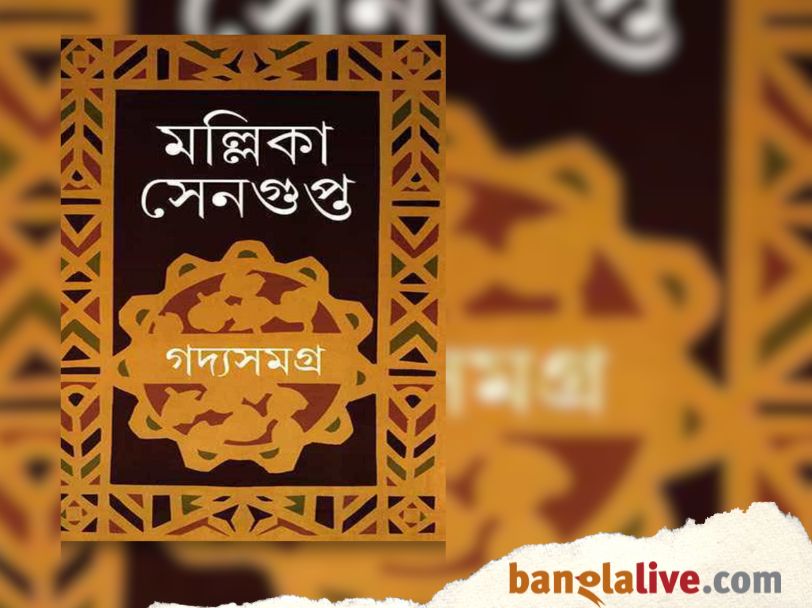
খেয়াল করতে অনুরোধ করব, কবিতা ও ছন্দ দু-জনেই যেন এখানে ঘটনা থেকে কিছু দূরত্বে দাঁড়িয়ে সব বর্ণনা করতে চাইছে। এবং পরপর কতগুলি দৃশ্যতথ্য এসে লাগছে আমাদের চোখে। আপাত বিচ্ছিন্ন মনে হলেও পরস্পর সংযোগসূত্রে এই দৃশ্যগুলি আবদ্ধ! (Mallika Sengupta)
কবিতাটির তৃতীয় লাইনের শেষ-অংশে রয়েছে: ‘কাঁসর বাজল/জন্মের মুহূর্তে কার? ছেলে নয়, রৌপ্যমুদ্রা প্রসব করেছে/ঘোষাল বাড়ির বউ। কী নাম রাখবে? তবে শ্বশুরের সাথে/ওঠা-বসা মিথ্যে নয়, বাঁকানো পরিখা বেয়ে নেমেছিল স্রোত?’ বাড়ির বউয়ের সঙ্গে তার শ্বশুরের কামসম্পর্ক, এ-ঘটনা সামাজিক বৈধতার ধারণায় ধাক্কা দেয়। বিষয়টির মধ্যে থেকে এক লঘুরঞ্জক গল্পের তাড়না খুঁজে পাওয়া যায় যেন! কিন্তু সম্পর্কটি যদি শ্বশুর-বউমার না হত? সামাজিক পরিচয় যুক্ত নয় এমন নারী-পুরুষের সম্পর্ক হত যদি? তখনও কি বলবার মতো কোনও বিষয় থাকত এ-কবিতায়? উত্তর: না। (Mallika Sengupta)
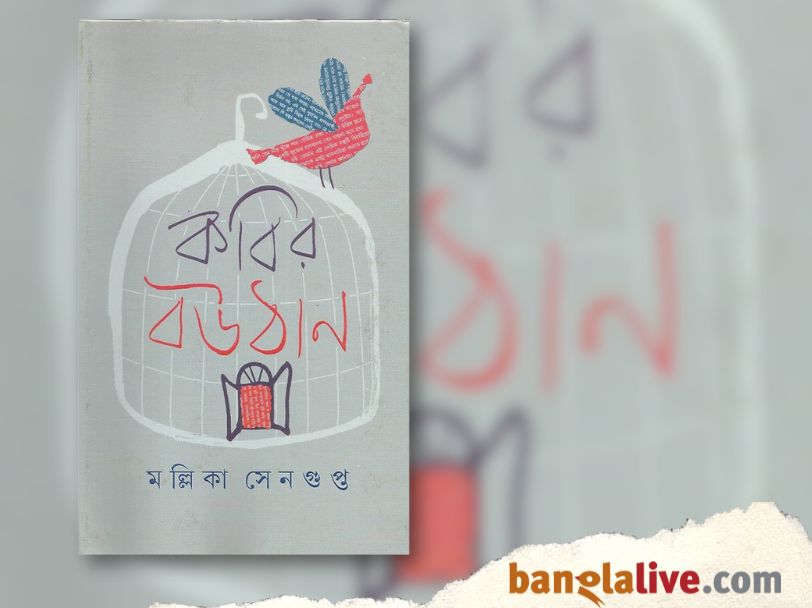
নারী-পুরুষের মধ্যেকার কামসম্পর্ক এক স্বাভাবিক বিষয়। অস্বাভাবিক এখানে সামাজিক দৃষ্টির বোধ। অর্থাৎ সমাজ-সংসারে আমি যেভাবে পরিচিত, সেই পরিচয়ের বাইরে আমি যেতে পারব না। বাইরে চলে গেলেই, প্রশ্ন তোলা হবে সংযম নিয়ে। সভ্যতার চিহ্ন নিয়েও। (Mallika Sengupta)
‘কাঁসর বাজল/জন্মের মুহূর্তে কার? ছেলে নয়, রৌপ্যমুদ্রা প্রসব করেছে/ঘোষাল বাড়ির বউ। কী নাম রাখবে? তবে শ্বশুরের সাথে/ওঠা-বসা মিথ্যে নয়, বাঁকানো পরিখা বেয়ে নেমেছিল স্রোত?’
কিন্তু মন? মনের বিচিত্র সব ইচ্ছে? সেই মনের আকাশে কিন্তু কোনও সমাজ নেই। সেই ইচ্ছের কথা শোনা, তার দায়ভারকে সাহসের সঙ্গে গ্রহণ করার কথা, আজীবন বলেছেন মল্লিকা। বলেছেন, এ-কবিতেও। তাই, লেখাটির চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ লাইনে সম্পর্কটির প্রত্যক্ষ পরিচয়চিহ্নে পৌঁছনোর আগেই, দ্বিতীয় ও তৃতীয় লাইন দুটি এক প্রবল সংকেতচিহ্নকে ফেলে রেখে যেতে চায় পাঠকের কাছে। লাইনগুলি এমন: ‘দুধের হাঁড়িতে ভেসে উঠে ডুবছে আবার ঘনশ্যাম পেঁচা/পূর্ণিমা সুগোল হলে মীনরাশি, কলিকাল।’ একটি কৃষ্ণবর্ণ পেঁচা, দুধের হাঁড়িতে ভেসে উঠে, ডুবছে। প্রশ্ন জাগে, এই দুধের হাঁড়ি কি রাতের আকাশে প্রজ্বলিত চাঁদ? এ-দৃশ্যচিন্তা হাত ধরে নিয়ে যায় পরবর্তী লাইনে, যেখানে আমাদের সমর্থনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ‘পূর্ণিমা’ শব্দটি। অর্থাৎ একটি কালো পেঁচা বারংবার চন্দ্রমন্থন করে চলেছে। (Mallika Sengupta)
মন্থন? ‘দুধের হাঁড়িতে ভেসে উঠে ডুবছে আবার ঘনশ্যাম পেঁচা’— ‘ভেসে-উঠে-ডুবছে’ এ হেন ক্রিয়ার মধ্যে হয়তো মিলনস্থ ‘মন্থন’ শব্দটির প্রচ্ছন্ন এক আভাস পাওয়া যায়। এই সূত্রে আরেকবার মনে করতে চাইব পরবর্তী লাইনটির সম্পূর্ণরূপ: ‘পূর্ণিমা সুগোল হলে মীনরাশি’। জ্যোতিষশাস্ত্রে বারোটি রাশির শেষ রাশি হল মীন। এই রাশির পরিচয়চিত্রে দেখা যায়, দুটি মাছ বিপরীত অভিমুখে একটি বৃত্তগতি স্থাপন করেছে। ভেবে দেখলে, যা অনেকটা নারীর সৃষ্টিঅঙ্গ যোনির মতনই। আশ্চর্য হই এই ভেবে যে, মল্লিকা সেনগুপ্ত এখানে একবারও ‘যোনি’ শব্দটির প্রয়োগ না-করেই, এমনকী রতিক্রিয়ার স্পষ্ট বর্ণনা না-দিয়েও এমন এক ইঙ্গিতদৃশ্যকে আমাদের সামনে রাখলেন, যা কামের সৌন্দর্যকে এক অভিনব ইশারায় বহন করে চলল! (Mallika Sengupta)
কিন্তু এই কবিতাটির প্রতি আমার বিস্ময় শুধুমাত্র এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। কীভাবে শুরু হয়েছিল কবিতাটি? ‘করোটির চোখে দেখো দু-নলা বন্দুক, জটিল জগৎ’। সম্পূর্ণ কবিতাটিতে ভ্রমণ করে আসার পর ফিরে তাকাতে ইচ্ছে করে এই প্রথম লাইনটির দিকে। কথা শুরু করেছিলাম ‘তবে শ্বশুরের সাথে/ওঠা-বসা মিথ্যে নয়, বাঁকানো পরিখা বেয়ে নেমেছিল স্রোত?’ এই লাইনটিকে ঘিরে। শ্বশুর ও বউমার যৌন-সম্পর্কের প্রসঙ্গে বলেছিলাম সমাজবোধের পরিখাচিহ্নের কথা। এবং মন যে সেই বিধিনিষেধ মানে না, সে-কথাও মনে করে নিতে চেয়েছিলাম আমরা। (Mallika Sengupta)
মন্থন? ‘দুধের হাঁড়িতে ভেসে উঠে ডুবছে আবার ঘনশ্যাম পেঁচা’— ‘ভেসে-উঠে-ডুবছে’ এ হেন ক্রিয়ার মধ্যে হয়তো মিলনস্থ ‘মন্থন’ শব্দটির প্রচ্ছন্ন এক আভাস পাওয়া যায়।
আসলে, সমাজের এই দৃষ্টিকোণ তো এক ধরণের চাপিয়ে দেওয়া অস্পৃশ্যতার নিয়মবোধ, যা আমরা কিছুটা যেন অজান্তেই অনুসরণ করি। কবিতাটি বলছে, ‘করোটির চোখে দেখো দু-নলা বন্দুক’। ‘করোটি’ শব্দটির প্রয়োগ বাংলা কবিতায় নানাভাবে হয়ে এসেছে। কিন্তু এমন ব্যবহার কি আগে আমরা সেভাবে খেয়াল করেছি? চোখের মণির শূন্যস্থানকে বলা হচ্ছে দুটি নলবিশিষ্ট একটি বন্দুক। বন্দুকের ধর্ম কী? সামনের দিকে লক্ষ্য স্থির রেখে তাকিয়ে থাকা এবং নিহত করা। মনে রাখতে হবে, দুটি পৃথক বন্দুক কিন্তু নয়, একটিই বন্দুক। সেই বন্দুক আসলে কে? আমাদের সামাজিক দৃষ্টি। বৈধ-অবৈধতার বোধ। লাইনটিতে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের শেষ ছ-মাত্রাকে অভাবনীয় সংকেতে ব্যবহার করেছিলেন মল্লিকা সেনগুপ্ত। ‘করোটির চোখে দেখো দু-নলা বন্দুক জটিল জগৎ’। এখানে ‘জটিল জগৎ’ শব্দবন্ধটিকে বিশেষভাবে খেয়াল করতে অনুরোধ করব। ‘করোটির চোখে দেখো দু-নলা বন্দুক’-এ চোদ্দ মাত্রা পার হওয়ার পর, ‘জটিল জগৎ’ শব্দ দুটিকে হয়তো পরপর দুটি নিখুঁত তিন মাত্রার ধ্বনির কারণে একটু যেন কেটে-কেটে, পৃথকভাবে আমরা পড়ি, আর সেই পড়ার মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে থাকে ‘জ’ ধ্বনির আবহ! এরফলে মনে হয়, করোটির দুটি নলযুক্ত বন্দুকের মতো সে-চোখ দুটির নাম হল— জটিল ও জগৎ। (Mallika Sengupta)
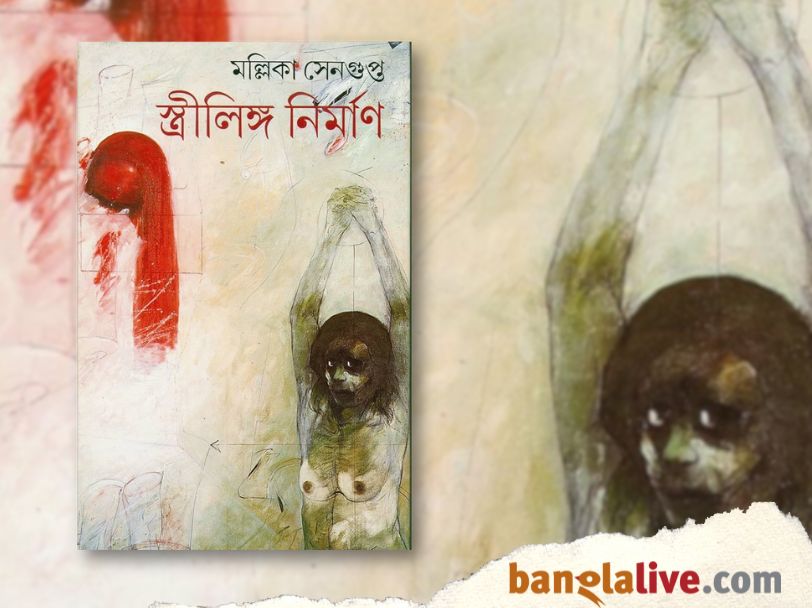
ঠিক এখানেই প্রখর হয়ে জেগে উঠতে চায় ‘করোটি’ শব্দটি। কারণ, ‘করোটি’ মানে মৃত মাথার হাড়পাত্র। অর্থাৎ যে-মন নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্ককে সমাজশৃঙ্খলা দিয়ে বিচার করে, সে-মনের দুটি চক্ষু জটিল, জগতে ভরা। সে-মন আসলে কবেই মারা গেছে, কেবল তার কাঠামোটুকু পড়ে রয়েছে। কবিতাটি শেষের দিকে পৌঁছে যে ঘটনার বিবরণ দিতে চায়, সেই ঘটনাকে দেখবার জরাগ্রস্থ দৃষ্টিকেই বলে দেয় কবিতার এই সূচনা লাইন। মাত্র ছ-মাত্রা লাইনের কবিতার এই জটিল কারুকর্ম প্রথম বই থেকেই ক্রিয়াশীল ছিল মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতায়। (Mallika Sengupta)
প্রথম বইয়ের প্রায় দু-বছর পর, ১৯৮৫ সালের ৩ সেপ্টেম্বর কবি সুবোধ সরকার ও মল্লিকা সেনগুপ্তের বিয়ের রাতে প্রকাশিত হয়েছিল ‘সোহাগ শর্বরী’।
প্রথম বইয়ের প্রায় দু-বছর পর, ১৯৮৫ সালের ৩ সেপ্টেম্বর কবি সুবোধ সরকার ও মল্লিকা সেনগুপ্তের বিয়ের রাতে প্রকাশিত হয়েছিল ‘সোহাগ শর্বরী’। বইটির কবিতা সংখ্যা ছিল তেরো। মল্লিকা সেনগুপ্তের ‘কবিতাসমগ্র’-এর গ্রন্থ-পরিচয় থেকে জানা যায় বইটি সম্পর্কে মল্লিকা বলেছিলেন: ‘বারোটা করে কবিতা দিতে পারতাম, চোদ্দটা করেও দিতে পারতাম। আর বিয়েটা সেপ্টেম্বরে নাই হতে পারত, কিন্তু কুসংস্কারকে একটু ফোঁস করতে চেয়েছিলাম।’ এই মনোভাবের সঙ্গে সমাজের অবৈধতার বোধকে অস্বীকার করবার প্রবণতা কোথাও যেন মিলে যায়। এ-বইয়ের শেষের দিকের ‘জাদুসংস্কার’ নামক একটি কবিতায় মল্লিকা লিখছেন: ‘নবদম্পতি, দেখো তোমাদের সংগমকালে/ডাকিনীরা যোনি ও লিঙ্গপথে ঢুকে যেতে পারে/রজঃসিক্ত কাঞ্জীভরম অগ্নিকে দিয়ো/আর আলো জ্বালিয়ে চুলে গিঁঠ বেঁধো পরস্পরে।’ মিলনের মুহূর্তে যৌনাঙ্গের মধ্যে দিয়ে ডাকিনীরা শরীরে ঢুকে যেতে পারে— এমন চিন্তা, শিহরন জাগায়! (Mallika Sengupta)
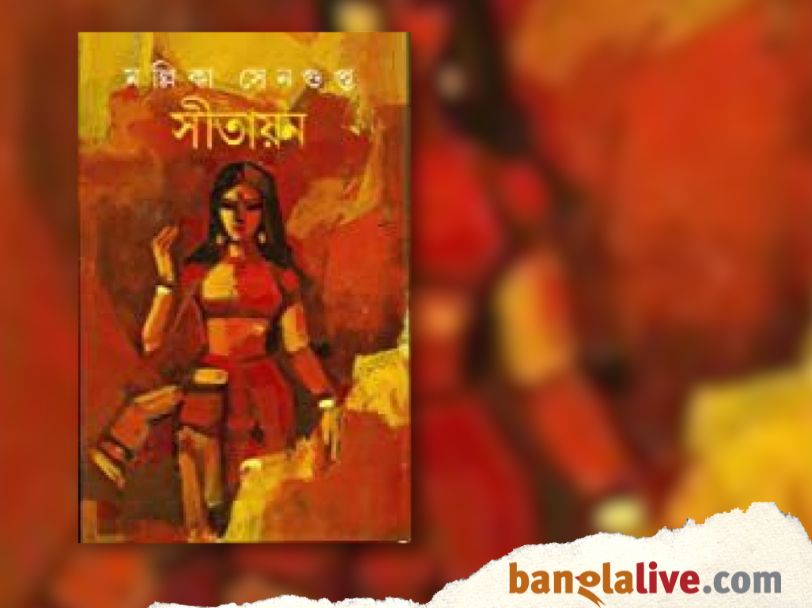
বিবাহ, রতি, সোহাগ ও স্বামীর চিহ্ন নিয়ে উন্মুখ এই বইয়ের একটি কবিতা সহজেই হয়তো চিনিয়ে দেয় মল্লিকা সেনগুপ্তের কাব্যক্ষমতার তীব্রতাকে। ‘প্রোষিতভর্তৃকা’ নামক সে-কবিতাটি এমন:
দয়িত বিরূপ হলে কালশিটে পড়ে যায় আমার জঙ্ঘায়
দধি, খই ও শর্করা মণ্ড করে ছুড়ে দিই কাকের হাঁ-মুখে
কৃষ্ণরেশমের মতো ঝকমক করে ওঠে ওদের পালক
এরপর যতবার কা কা করে ডেকে ওঠে ত্রিসীমানা জুড়ে
আরও ততদিন দেরি স্বামী ফিরবার।
‘প্রোষিতভর্তৃকা’ কথাটির অর্থ হল যে-নারীর স্বামী ঘরে নেই, প্রবাসে রয়েছে। কবিতাটির প্রথম লাইনটি থেকে এক রতি-উপোসীর চিহ্ন আমরা খুঁজে পাই। ‘দয়িত বিরূপ হলে কালশিটে পড়ে যায় আমার জঙ্ঘায়’। এর ঠিক পরপর, দধি-খই-শর্করার মণ্ড ছুঁড়ে দেওয়া কাকের হাঁ-মুখ, কৃষ্ণরেশম, ত্রিসীমানা কথাগুলি আমরা দেখতে পাই। ‘কা কা’ ধ্বনির মধ্যে স্বামীহীন একাকী স্ত্রীলোকের শরীরী হাহাকার রয়েছে। এমনকী, কাকের হাঁ-মুখটিকেও মনে হয় যেন সে-নারীর শরীরের বিশেষ কোনও অঙ্গ, স্বামীর ঘরে ফেরার জন্য যে অপেক্ষা করে আছে। (Mallika Sengupta)
‘দয়িত বিরূপ হলে কালশিটে পড়ে যায় আমার জঙ্ঘায়’। এর ঠিক পরপর, দধি-খই-শর্করার মণ্ড ছুঁড়ে দেওয়া কাকের হাঁ-মুখ, কৃষ্ণরেশম, ত্রিসীমানা কথাগুলি আমরা দেখতে পাই।
এই চিন্তাকে কুর্নিশ জানাতেই হয়। নারীর মনের আকাশের নানা বিচিত্র আবহাওয়া মল্লিকা সেনগুপ্তের সারাজীবনের কবিতায় ছড়িয়ে রয়েছে। তিনি যে কেবল নারীবাদী কবি, তা কিন্তু নয়। প্রতিবাদের আয়োজনের আড়ালে চাপা পড়ে আছে তাঁর লেখা বহু নির্জন কবিতা। সেখানেও নারী আছে। নারীর মনের বক্তব্য আছে। কিন্তু সে-বক্তব্যগুলি নিস্তব্ধতা ও সংকেতের জাদুমুহূর্তে ঢাকা। (Mallika Sengupta)
এ-বছর ২৭ মার্চ, পঁয়ষট্টি বছরে পা দিতেন মল্লিকা সেনগুপ্ত। তাঁর কবিতাকে কোনও নির্দিষ্ট মোড়কে আটকে না-রেখে, স্বাধীনভাবে যদি আমরা পড়ি তাহলে হয়তো, চারিদিকের আলো-হাওয়া-বাতাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা দেখতে পাব তাঁর অভিজ্ঞতার নানাবিধ ঋতুপরিবর্তন! (Mallika Sengupta)
অভিরূপ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৯৩ সালে, নদিয়ার কৃষ্ণনগগরে। বাংলা সাহিত্যে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বিশ্বভারতী থেকে এম.ফিল। বর্তমানে এশিয়াটিক সোসাইটি-র গবেষণা-প্রকল্পে যুক্ত। ২০২০ সালের কলকাতা বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে অভিরূপের প্রথম কবিতার বই ‘এই মন রঙের কৌতুক’, সপ্তর্ষি প্রকাশন থেকে।