(Refugee)
“আমাদের যা হল, হল। কিন্তু এরপরে ছেলের দল যত শিক্ষিত হবে, তত বোকা হবে। কেন বোকা হবে? ওই যে চাকরি পাইল নাই। আর ওরা যে রাজ হয়ে এখানে বসে গেল। বিদ্যুৎ করল। ড্যাম করল। তা এরপর কী করবে ছেলেপুলের দল? ওদের না থাকল পূর্বপুরুষের জঙ্গল। ড্যামের নিচে ওরা কুসুম লা দেখিবে না পলাশ লা দেখিবে? কোথায় থাকবে ধর্ম! জঙ্গল ডুবে গেল। ওষুধের গাছটাও ডুবে মরে গেল।”(Refugee)
বাড়েলহর গ্রামের বুক চিড়ে চলে যাওয়া সরু রাস্তাটায় বুধন মান্ডি বসে আছেন। বয়স ষাটের আশপাশে কিছু একটা হবে। সুনীল, সুনীল মান্ডি, তাঁকে ঘরে ডেকে আনে। আমাদের কাঁধে ক্যামেরা ও নানা লটবহর। ঠুড়্গা পাওয়ার প্রোজেক্ট নিয়ে ছবি করতে অযোধ্যায় গেছি শুনে বুধন চেয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। তারপর ইতিউতি বলতে থাকেন। মূলত স্মৃতিভস্ম। সান্তালি ও বাঙলা মিলেমিশে অনেক কথারই অর্থ খোঁজা দুরূহ হয়ে ওঠে। অনেক রূপকের থই পাই না। সারাদিন বিস্তর পরিশ্রম গেছে। সুনীলের উঠোনে একটু জিরিয়ে আমরা যাব জাহেরথান। বাহা পরব শুরু হবে। কিন্তু তার আগে বুধন মান্ডির কথায় তাল কাটে। মনে পড়ে, খানিক আগে, দুপুরে, টাঁড়পানিয়া গ্রামে বসে রমেনদাও বলছিলেন প্রায় একই কথা। পাহাড়ের ওপরে, নিচে সর্বত্র যে কথা টিলায়-পাহাড়ে-অবশিষ্ট বনে ধাক্কা খাচ্ছে। পরবের মধ্যেও যে দীর্ঘশ্বাস মোছে না।(Refugee)
“সরকারি বাবুরা এসে বলল, এই ড্যাম হলে বিনামূল্যে সবাই বিদ্যুৎ পাব। ঘরে-ঘর চাকরি হবে। প্রতি ঘরে একেকজন, ঘরের সবাইকে দিতে পারবে না। কাজ পাঁচ-ছয় বচ্ছর চলল। কাজ শেষ হল আর বন-জঙ্গলও শেষ হয়ে গেল। চাকরি তো পাওয়া গেল না। সাহারজুরি, বাঁধঘুঁটি আর হাতিনাদা গ্রাম থেকে মোট চার জন সিকিউরিটির চাকরি পেয়েছিল। আর দু-তিনমাসের জেসিবি পাহারা দেওয়ার কাজ পেয়েছিল অনেকে। সঙ্গে মজুরের কাজ। বাকিরা কিছুই পায়নি।”(Refugee)

ঠুড়্গা পাওয়ার প্রোজেক্ট নিয়ে কথা বলতে গিয়েও বারবার উথলে আসে ২০০২ সালের ‘পুরুলিয়া পাম্পড স্টোরেজ প্রোজেক্ট’-এর আখ্যান। আকাশচুম্বী অপ্রাপ্তি, অভিমান আর ক্ষোভ। খানিক অভ্যেসবশতই জিজ্ঞেস করে ফেলি, আপনারা জমি দিয়েছিলেন কেন? ক্ষতিপূরণ পাননি? প্রশ্নের উত্তরে শালডি গ্রামের বিশাল মুর্মু বলেছিল, “শুনলাম চাকরি হবে, বিদ্যুৎ হবে। লোভ হল। অত ভাবিওনি। বুঝিওনি। পরে বুঝলাম, লোভ হওয়া পাপ! তারপর আমাদের জঙ্গল গেল, নদী গেল, চাষের জমি গেল। এর ক্ষতিপূরণ কারা দেবে?”(Refugee)
‘লোভ’ শব্দটা কানে এসে বেঁধে। বিদ্যুৎ আর চাকরির লোভ! আজীবন এই অতি স্বাভাবিক দ্বিবিধ চাওয়ার গর্ভে বেঁচে-বর্তে-প্রতিপালিত হওয়া আমরা এহেন লোভের ক্ষত ঠাহর করতে পারি না। রাঙ্গা গ্রামের দুলাল বলছিলেন, গ্রামের কেউ কেউ ভেবেছিলেন একটা টিভি কেনা হবে। সবাই মিলে ছবি দেখা যাবে। এই লোভে কতকিছুই না গেল। লোভ আর ক্ষতি। গ্রামের মানুষজনকে জিজ্ঞেস করলেই সেই ক্ষতি বহরে বাড়তে থাকে। অথচ, সরকার নাকি ক্ষতিপূরণ দিয়েছিল। বিঘে প্রতি জমি হিসেবে তেত্রিশশো টাকা। স্থানীয় মানুষরা ভেবেছিলেন, পশুচারণভূমিটাও হিসেবের মধ্যে ঢুকবে। সেসব ঢোকেনি। অনেকের কাছেই ঠিকঠাক জমির কাগজ ছিল না। এতদিন তো কাগজের প্রয়োজনও পড়েনি। সেই কবে থেকে এই জঙ্গলে-পাহাড়ে তাঁরা আছেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা জমির দাম পাননি। বিদ্যুৎ-ও না। গ্রিডের বিদ্যুৎ চলে গেল অন্য জেলায়।(Refugee)
“হাতিরা মানুষের সঙ্গে জিততে পারেনি। তাদের যাতায়াতের করিডরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল দৈত্যাকার ড্যাম। আর সেই সুর্জন-দুর্জন নদী? আপার ড্যামের তলায় তাদেরও সলিল সমাধি ঘটেছিল।”
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে জাপানের যে দুটো কোম্পানি মিলে এই প্রকল্প সাজিয়েছিল, তাঁরা বলেছিল বছরে ৯০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে। যদিও উৎপাদন সেই লক্ষ্যসীমা অবধি পৌঁছয় না। এদিকে একটা সূত্র বলছে, জল আপার রিজার্ভারে পাম্প করে তুলে আনতেই নাকি বছরে ১৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ খরচ হয়, যা মূল উৎপাদনের চাইতেও বেশি। সরকারি হিসেবে ৪৪২ হেক্টর জমি গেছিল প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করতে। তার মধ্যে ৩৭৩ হেক্টর জমি বনভূমি। দলমা হাতির করিডরের একটা অংশও। সাঁওতাল মানুষরা বলেন, গোবরিয়া। গভীর, দুর্ভেদ্য বন। যেখানে চোখ ঢোকে না, এমন জঙ্গল। সেখানে ভাল্লুক আর চিতা, হরিণের দল, শজারু, বনরুই, হায়না, বুনো খরগোশ সহ কত বন্যপ্রাণ। সঙ্গে দলমা হাতির পাল তো আছেই। এই প্রকল্পে তাদের বাস্তু গেল, জঙ্গল গেল। রমেণদা বলছিলেন, পাহাড়ে আর ভাল্লুকের দেখাই মেলে না।(Refugee)
স্থানীয় মানুষদের হিসেব সরকারি অঙ্কের সঙ্গে মেলে না। তাঁরা বলছিলেন, কমবেশি ১৩০০ হেক্টর বনভূমি এই প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চাষজমি, পশুচারণভূমি নষ্ট হওয়ায় ক্ষতির মুখে পড়েছে অন্তত সত্তরটি গ্রাম। তারপরেও শুরুতে গ্রামবাসীরা প্রতিরোধ করেননি। কিন্তু হাতির পাল নাকি করেছিল। জাটাঝোর নদী আর সুর্জন-দুর্জন নদীর মাঝামাঝি হাতির দল নাকি রুখে দাঁড়িয়েছিল সরকারি জেসিবি ট্রাক্টরের সামনে। কিছুতেই পথ ছাড়ছিল না। তারপরে কত কাণ্ড করে হাতিদের সরানো হল। একটা দাঁতালের মাথায় নাকি জেসিবি দিয়ে আঘাতও করতে হয়েছিল। হাতিরা মানুষের সঙ্গে জিততে পারেনি। তাদের যাতায়াতের করিডরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল দৈত্যাকার ড্যাম। আর সেই সুর্জন-দুর্জন নদী? আপার ড্যামের তলায় তাদেরও সলিল সমাধি ঘটেছিল। বাঁধডি নদীর সঙ্গে ওই দুই নদীর কোনও অস্তিত্বই আর পুরুলিয়ার মানচিত্রে নেই।(Refugee)

হাতিঠাকুরের কথা উঠতে বুধন মান্ডি থম হয়ে বসে থাকেন। আমরা ধীরে ধীরে জাহেরথানের দিকে এগোই। রাঙ্গা-বাড়েলহড় পেরিয়ে যে বইহারে আমরা নামছি, তার প্রতিটা ঢাল চকচক করছে। প্রতিটা ঘাস, পথের কাঁকর। রাত পেরোলেই দোলপূর্ণিমা। জ্যোৎস্নায় চোখ পুড়ে যাচ্ছে। দেখছি, সামান্য দূরে সারি সারি আলো উঠছে আর নামছে। দূরের থান থেকে ভেসে ভেসে আসছে মাদলের আওয়াজ। আমরা জাহেরথানের মুখে আটকে যাই। সাঁওতাল না হলে এই পরবে ঢোকা নিষেধ। ঢুকতে গেলে পায়ে জুতো থাকলে চলবে না। পুরুষমানুষ হলে ধুতি পরতে হবে। ধুতি কই পাই! গায়ের গামছা পাট দিয়ে পরে নিই কোনওমতে।(Refugee)
সুনীল বাকিদের বোঝায়, আমরা ট্যুরিস্ট নই। ছবি করতে এসেছি। নানা অনুরোধের পর থানে প্রবেশের ছাড়পত্র মেলে। ভিতরে একটা শালগাছকে ঘিরে গোল করে নাচছেন সাঁওতাল মেয়েরা। সঙ্গে স্রোতের মতো ইনিয়েবিনিয়ে গান। ভিড়ের মধ্যিখানে মাদল আর কাঁসা বাজাচ্ছেন কয়েকজন। গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে গ্রামের কচিকাঁচারা। গান মাঝেমধ্যে থামছে। সামান্য বিরতি। বায়েন ফের গানের কথা উজিয়ে দিচ্ছেন। পুকুরে ঢিল পড়লে যেমন হয়, সেভাবে সুর চারিয়ে যাচ্ছে এক দেহ থেকে অন্য দেহে। আর তক্ষুনি আবার বেজে উঠছে মাদল…(Refugee)
“শেষ রাত্তিরেও টিলার ওপরে বসে ঝিমোতে-ঝিমোতে আমরা সেই মাদলের সরে সরে যাওয়া শব্দ শুনতে পাই। পাতলা থানের মতো জ্যোৎস্নায় সামনের জঙ্গলটা দেখে গা শিরশির করে ওঠে। মনে হয়, জঙ্গলের ভূত দেখছি।”
তিনদিনের বাহা পরব। উম্, সার্দি এবং সেঁদরা। থানের একপাশে ভোগ রান্না হচ্ছে। বলি দেওয়া মুরগি দিয়ে রান্না করা জাহের সড়ে বা খিচুড়ি। গ্রামের প্রত্যেকে জাহেরে এসে নায়কেবাবা তথা পুরোহিতকে প্রণাম করার পর নায়কে সবাইকে শালফুল দেবেন। আরেক পাশে শিলাপুজো হচ্ছে। নায়েকেবাবা বলছিলেন, “বাহা মানে ফুল। আমাদের শরীরেও ফুল ফোটে। ফুল ফুটলে সবাই মিলে একজোট হতে হয়। গ্রামের সবাই মুরগি দেবে। চাল দেবে। সেই চাল আর মোরগঝোল রান্না হবে আজ।” টকটকে লাল ঝোলমাংস কাঁচা শালপাতার বাটি উপচে পড়ছে। গাঁওবুঢ়ারা ভোগের তদারকিতে। (Refugee)
আজ সারারাত গ্রামের বাড়ি-বাড়ি ঘুরে ভোগ বিলোনো হবে। প্রতিবাড়ির সামনে বাজবে মাদল। পূর্ণিমা লেগে যাবে মাঝরাত্তিরে। তার আগেই ভোগ বিলোতে হবে। পূর্ণিমা ধরার আগেই খাওয়া সমাপন। শেষ রাত্তিরেও টিলার ওপরে বসে ঝিমোতে-ঝিমোতে আমরা সেই মাদলের সরে সরে যাওয়া শব্দ শুনতে পাই। পাতলা থানের মতো জ্যোৎস্নায় সামনের জঙ্গলটা দেখে গা শিরশির করে ওঠে। মনে হয়, জঙ্গলের ভূত দেখছি। বেশ খানিকটা দূরে হিল-টপে একটা লজের অশালীন আলো। (Refugee)

সন্ধেয় শুনছিলাম বাহার গান— “হেঁসাঃ মা চটেরে/জা গোঁসায় তু-দে দয় রাগে কান/ বাড়ে মা লাওয়েররে/ জা গোঁসায় গুতরুৎদয় সাঁহেদা…” অশ্বত্থগাছের ওপরে ‘গোঁসায় তুদ’ মানে ভরতপাখি গান গাইছে। বটগাছের কোটরে ‘গুতরুৎ’ অর্থাৎ সদ্য দাঁতফোঁটা বাঘের বাচ্চা দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। গুতরুৎ-এর দীর্ঘশ্বাস জানান দিচ্ছে, ‘দিশম চ বিহুরেন’ অর্থাৎ এই পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। তারই নিয়মে ঋতু বদলাচ্ছে… (Refugee)
বুধন মান্ডি বলছিলেন, ড্যামে কি কুসুম আর পলাশ ফুটবে! সামান্য ফুলই তো! কিন্তু কত মাহাত্ম্য তার। নায়কেবাবার হাতে শালফুল। গ্রামের লোকেরা পা ধুইয়ে দিলে সেই শালফুল তিনি বিলিয়ে দিচ্ছেন তাঁদের হাতে। জাহেরথানে জড়ো হওয়া সকলের হাতে শালফুল। মাথায় ফুল। শরীরে ফুল। (Refugee)
“জাহেরথান’। বাহা থেকে ফেরার পথে রণেনকে জিজ্ঞেস করি, জাহেরথান মানে কী? রণেন জানায়, এখানে দেবতার অলীক ক্ষমতা। কিন্তু ‘জাহের’ নাম কেন?”
পরেরদিন সকালে মারাংবুরু যাওয়ার পালা। পথে তিনখানা টিলা পায়ে হেঁটে পেরনো। মাঝে ঠুড়্গা নদী। নদীর বুকেই দিব্বি চাষ হচ্ছে। জুতো পরে সেই নদী পার হওয়া নিষেধ। মারাংবুরু পাহাড়েও খালিপায়ে উঠতে হবে। যাওয়ার পথে আরও একটা জাহেরথান। সিঁদুর মাখানো শিলা। রণেন বলছিল, এই শিলা বুঢাবুঢি। পাশে সরু একটা হাঁড়িকাঠ। এসবও নাকি ঠুড়্গা পাম্প স্টোরেজের জলে ডুবে যাবে। এই এত্ত উঁচুতেও জল উঠবে! শুনে রণেন বিড়বিড় করে– “বাদনায় এই পাহাড় ভরে যায়। কত কত দূর থেকে লোক আসে। বাদনাতে সোহাগ বাঁধা হয়।” (Refugee)
‘জাহেরথান’। বাহা থেকে ফেরার পথে রণেনকে জিজ্ঞেস করি, জাহেরথান মানে কী? রণেন জানায়, এখানে দেবতার অলীক ক্ষমতা। কিন্তু ‘জাহের’ নাম কেন? জাহের মানে তো প্রকাশ্য। বুঢাবুঢি দেবতা এখানে তাঁর অলৌকিক শক্তি জাহির অর্থাৎ প্রকাশ করেন, তাই ‘জাহেরথান’। কিন্তু এই শব্দ তো আরবি। সে কীভাবে সাঁওতাল দেবথানে এল! (Refugee)

ফকিররা বলেন, মারফতে দশপারা (দশ হাজার) গুপ্তজ্ঞান। এই গুপ্তজ্ঞান হল ‘বাতুন’। আর, শরিয়তিদের কারবার ‘কেতাব’ বা কোরানের যে ত্রিশপারা প্রকাশ্য জ্ঞান নিয়ে, তা হল ‘জাহের’। অর্থাৎ ‘প্রকাশ্য জ্ঞান’। বাতুন আদতে গুপ্তজ্ঞান। এই জ্ঞান দেল-কেতাব বা দেল-কোরানের ভাগে। এই দশপারা বাতুন সুফি-ফকিরদের সাধনার উপত্যকা। আর, জাহের তো লেখাই আছে কোরানে। আল্লাহর দেওয়া প্রকাশ্য জ্ঞান। এমনই ‘জাহের’ শব্দ কীভাবে যেন বয়ে-উজিয়ে এসে গেঁথে গেল আদিবাসী থানে। জঙ্গলে, পাহাড়ে দেবতার অধিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে গেল। উপচারে বলি, সিন্দুর, প্রতীকী অগ্নি-সমর্পণ। এবং ‘জাহের’। সেই থানে পরবের দিন বহিরাগত ‘দিকু’-দের প্রবেশ নিষিদ্ধ। কেউ পাছে রেগে যায়, আমাদের আগলে আগলে রাখছিলেন সুভাষদা। সুভাষ কিস্কু। তাঁর ভায়রা নায়েকেবাবা। থানের একপাশে আগুন জ্বলছে তো জ্বলছেই। (Refugee)
আমরা বেরিয়ে আসব ভাবছি। সুভাষদা বলছেন, “মেয়েরা গানের শেষে ফুল উৎসর্গ করবে আগুনে। সেইটা ক্যামেরায় তুলো।” আমি রেকর্ড অফ করি। সুভাষদা বলতে থাকেন, “ফুল আগুনে গেলে দেহ শুদ্ধশুচি। কামনা পবিত্র। এরপর ভোগে কোনও বাধ নেই। কাল পূর্ণিমা ভাঙলে ফের খাওয়া…” (Refugee)
“আমরাই হয়তো সেভাবে লড়তে পারছি না। আমরা না চাইলে দেবতা কেন রক্ষা করবেন?”
এক জাহেরথান থেকে আরেক জাহেরথান। দেবতার প্রকাশ্য অলীকশক্তির জমিন। সেখানে শালবন, মহুল, পলাশ, জল, বুনো শুয়োর, হাতি, ভাল্লুক। পাহাড়ের পর পাহাড়। ঢালের পর ঢাল। এসবও কি দেবতার প্রকাশ্য নূর নয়! জাহের নয়! কোনও বহিরাগতর এই দুনিয়ায় অধিকার নেই। ছিলও না। কিন্তু তাও যে দখল হচ্ছে সব! প্রকাশ্যেই। এইসব জমি-জঙ্গল-থানও তো প্রোজেক্টে ঢুকে যাবে। দেবতা নিজের জমি কেন ছেড়ে দিচ্ছেন! থানে পড়ে থাকা পাতা, কাঠের টুকরো এককোণে সরাতে সরাতে সুধীর বিড়বিড় করে, “আমরাই হয়তো সেভাবে লড়তে পারছি না। আমরা না চাইলে দেবতা কেন রক্ষা করবেন?” (Refugee)
প্রায় একই কথা বলতে শুনেছিলাম চরণ পাহাড়িয়াকে। “আমরাই তো গ্রাম বাঁচাতে পারলাম না।” অযোধ্যা পাহাড়ের পূর্বদিকে দুর্গম ও অরণ্যসঙ্কুল কলাবেড়া ও আমকোচায় দীর্ঘদিন যাবৎ পাহাড়িয়াদের একটা গ্রাম ছিল। পাহাড়িয়ারা জঙ্গলনিবাসী। জঙ্গলের মধ্যেই সামান্য চাষবাস, পশুচারণ, ঔষধি-ফলমূল সংগ্রহ করে জীবন কাটে। এক বন থেকে অন্য বনে অবাধে চলাফেরা। একসময় জবর পাহাড়িয়ার নেতৃত্বে তুমুল ব্রিটিশ-বিরোধী লড়াই করেছিলেন এই পাহাড়িয়ারা। কলাবেড়ার গ্রামে অবশ্য সেই ইতিহাসের সামান্য স্মৃতিও বেঁচে ছিল বলে মনে হয় না। মাঝে তাঁদের গ্রামে মাওবাদীরা এসে আশ্রয় নিতে শুরু করে। ২০০৯-১০ সালের কথা হবে। চরণ বা ভাদু পাহাড়িয়ারা মাওবাদ বুঝতেন না। তাঁরা কোনও পক্ষেও ছিলেন না। আশ্রয় দিয়েছিলেন, সে খানিক ভয়ে, খানিক সাধারণ মানবিকতায়। (Refugee)

কিন্তু এসব জানাজানি হওয়ার পরে সরকার সিদ্ধান্ত নেয়, গ্রাম উঠিয়ে দেবে। সেই মতো তাঁদের তুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয় পাহাড়ের নিচে বলরামপুর লাগোয়া মাহলিটাঁড়ে। সেখানে জঙ্গল নেই। খান তিরিশেক পরিবার, গড়ে ৬০০ স্কোয়ার ফুটের একেকটা ঘর। পশুচারণের যৎসামান্য জমি। লক্ষণ পাহাড়িয়া বলছিলেন, দীর্ঘদিন ধরে তাঁর মনে হত, এটা দুঃস্বপ্ন। কিছুদিনের মধ্যেই ফের পাহাড়ে ফিরে যাওয়া যাবে। এক দশক কাটার পরে সেই ভ্রম ঘুচে গেছে। এখনও গ্রামের বয়স্করা পাহাড়ে ওঠেন। নিজেদের ফেলে আসা গ্রাম দেখতে আসেন। জঙ্গলে ঢোকেন। গাছের তলায় ঘুমোন। তারপর সন্ধে হলে নেমে আসেন নিচে, রাস্তার পাশে, ৬০০ স্কোয়ার ফুটের ঘরে। নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা নেশায় ডুবে থাকে। কয়েকজন মোবাইল পেয়েছে। তাদের না আছে শিকড়, না আছে ভবিষ্যৎ। ছিন্নমূল হওয়ার হতাশা কেমন বীভৎস হতে পারে, তা এই গ্রামে ঢুকলে টের পাওয়া যাবে। (Refugee)
রমেন হেমব্রম বলছিলেন, ঠুড়গা পাওয়ার প্রোজেক্ট হলে পাহাড়েরও বারো-পনেরোটা গ্রামের মানুষ ছিন্নমূল হবেন। কিন্তু সরকারি প্রকল্পে তো উচ্ছেদের প্রসঙ্গ নেই। নোটিশ নেই। পুনর্বাসনের প্যাকেজ নেই। তাহলে? রমেনদা শুনে হাসেন। জঙ্গল-লাগোয়া রাঙ্গা, বাড়ুয়াজারা, বাঁধঘটু, দুলগুবেরা, বাড়েলহর, টাঁড়পানিয়া, ভূঁইঘোরা, হাতিনাদা, বিদ্যজারা, তিলিয়াভাষা, শালডির মতো গ্রামগুলোর সব বসতবাড়ি উঁচু জায়গায়। ফলে ড্যামের জলে বাড়ি ডুববে না। তাই সরকারি খাতায় উচ্ছেদ নেই। কিন্তু প্রকল্পে যে ২৯২ হেক্টর জমি জলের তলায় চলে যাবে, যার মধ্যে ২৩৪ হেক্টর বনভূমি, বাকিটা চাষের জমি, রায়তি জমি, চারণভূমি, জাহেরথান, মারাংবুরু— এসব গেলে মানুষ কী নিয়ে বসে থাকবে? কীভাবেই বা থাকবে? এসব বাদ দিয়ে গ্রামই বা কীভাবে থাকবে? ফলে উচ্ছেদ তো হতেই হবে। অন্তত হাজার দুয়েক মানুষ। সঙ্গে এত এত গাছ, হাতি, বুনো প্রাণি। সব জলের তলায়।” (Refugee)
“পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়ির সন্তানরাই সাঁওতালদের পূর্বপুরুষ।”
অযোধ্যাপাহাড়ের এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে ঘুরতে ঘুরতে আসন্ন ধ্বংসের ছবিগুলো কেমন বিকট হয়ে উঠতে থাকে। ঝাঁ চকচকে পিচের রাস্তা ধরে সারি সারি ট্যুরিস্টের গাড়ি। রাস্তার মাঝে নেমে পলাশগাছের তলায় সেলফি, জঙ্গলে নেমে হইহল্লা। আপার ড্যামের রাস্তা জুড়ে খাবারের দোকান। দূরে নিসর্গের ধ্বংসাবশেষকেও ক্যামেরায় ধরছেন কেউ-কেউ। সাজানো বিকট সৌন্দর্য প্রভূত মুনাফার জন্ম দিচ্ছে। বহুমাত্রিক মুনাফা। হিলটপে হিন্দি গান বাজছে। তিল ধারণের জায়গা নেই। আর, সামান্য দূরে বাড়ুয়াজারা, বাঁধঘুঁটু, দুলগুবেড়ায় গ্রামসভার মিটিং বসেছে। প্রকল্পের বিরোধিতা করায় সরকারি স্তরে নানা চাপ আসছে গ্রামবাসীদের ওপর। মামলাও রুজু হয়েছে কয়েকজনের বিরুদ্ধে। কিন্তু এখনও অবধি তাঁরা প্রকল্পের কাজ শুরু হতে দেননি। দুলন মাঝি বলছিলেন, পাহাড়ের চেয়ে উঁচু জলের কথা ভাবলেই আতঙ্ক হয়। এত এত জল সব খেয়ে নেবে! (Refugee)
“তারপর, ঠাকুরজিউ-র হাতে প্রাণ পেয়ে হাঁস ও হাঁসিল আকাশে উড়তে লাগল। কিন্তু তারা বসবে কোথায়? খাবে কী? জালাপুরিতে তো শুধু জল আর জল। অতঃপর ঠাকুরজিউ ভূভাগ তৈরিতে মন দিলেন। কচ্ছপ জলের ওপর ভেসে রইল। তার পিঠের ওপর নাগ সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ধরে রইল সোনার থালা। কেঁচো দিনরাত এক করে মাটি এনে সেই থালায় ভরল। এভাবেই পৃথিবী একদিন মাটিতে ভরে গেল। ঠাকুরজিউ মাটির ওপরটা মসৃণ করে দিলেন। যেগুলো উঁচু হয়ে থাকল, সেগুলো হল পাহাড়। ঠাকুরজিউ মাটির ওপর বুনে দিলেন ‘শিরম’ ঘাসের বীজ, বুনলেন দুব্বো ঘাস। তারপর একে-একে সৃষ্টি করলেন করমগাছ, শালগাছ, মহুয়া আর কেঁদুগাছ। হাঁস আর হাঁসিল ওই শিরম ঘাসের ঝোপে আশ্রয় নিল, ডিম পাড়ল দুটো। সেই ডিম ফুটে বেরোল দুটো মানবশিশু— পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়ি। ঠাকুরজিউ তাদের থাকার জন্য জায়গা ঠিক করে দিলেন—হিহিড়ি পিপিড়ি। মানবশিশুর প্রথম বাসভূমি। পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়ির সন্তানরাই সাঁওতালদের পূর্বপুরুষ।” (Refugee)
আরও পড়ুন: স্থানান্তর: তরাই, বন, পাহাড়, নিসর্গ: ‘অথবা এমনই ইতিহাস’
সাঁওতালি সৃষ্টিতত্ত্বে যে জল থেকে ডাঙা বানালেন ঠাকুরজিউ, বন তৈরি করলেন, সেই বন আর ডাঙাকে, সেই ডাঙার প্রাণ আর মানুষদের জন্যেই তো এতকিছু। এত প্রতিরোধ, এত লড়াই। মারাংবুরুর জঙ্গল থেকে নামার পথে শুকনো পাতার ওপর দিয়ে দূরে একছুটে পেরিয়ে যায় কোনও বুনোজন্তু। জঙ্গলের পথ শেষই হয় না। দম ফুরিয়ে আসে। থইথই বাতাস আর পাহাড়ের নাভিতে বসে হাঁপাতে হাঁপাতে মনে হয়, বিশ্বাস এক অলীক শব্দ। আমরা শহুরে দিকু, সেখানে উঁকি দেওয়ার যোগ্যতাও আমাদের নেই। কিন্তু এই উৎকট রোমান্টিকতা ও আদিবাসী আর্কেটাইপকে লগ্নি করেই মনে হয়, জঙ্গলের দেবতা একটিবার তাঁর শক্তি জাহির করুন। জাহেরথানে জড়ো হওয়া সক্কলে দৈবশক্তির বিশ্বাস নিয়েই নাহয় রুখে দাঁড়াক। জঙ্গল-লাগোয়া বাড়ুয়াজারা, বাঁধঘটু, দুলগুবেরা, রাঙাবাড়েলহার, টাঁড়পানিয়া, ভূঁইঘোরা, হাতিনাদা, বিদ্যজারা, তিলিয়াভাষা, শালডি, খুরপাহাড়, ভিতপানি, বোঙ্গাদা, চেতনবেড়া বা জামঘটুর সমস্ত জমিন হয়ে উঠুক জাহেরথান। এই জঙ্গল, বইহার, খেত যেন প্রোজেক্টের জলে তলিয়ে না যায়। (Refugee)
মুদ্রিত ও ডিজিটাল মাধ্যমে সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত
ছবি সৌজন্য- লেখক
তথ্যসূত্রঃ
1.Mongabay India, January 11, 2022
2.WBSEDCL
3.GroundXero, October 17, 2018
4.SANDRP, March 2, 2019
অনিতেশ চক্রবর্তী বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র। গবেষক। পড়ানো ছেড়ে বিজ্ঞাপনী সংস্থায় কাজ। অত:পর আরও কয়েকজনের সঙ্গে মিলিতভাবে নিজস্ব সংস্থা। ভালোবাসেন তথ্যচিত্র বানাতে। বনগ্রাম ও বনাধিকার নিয়ে কাজের সূত্রে উত্তরবঙ্গ তথা ভারতের নানা বনাঞ্চলের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। সম্পাদনা করেছেন একাধিক পত্রিকা ও মানসিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রিক দুটি বই। কবিতার বইও আছে একটি।




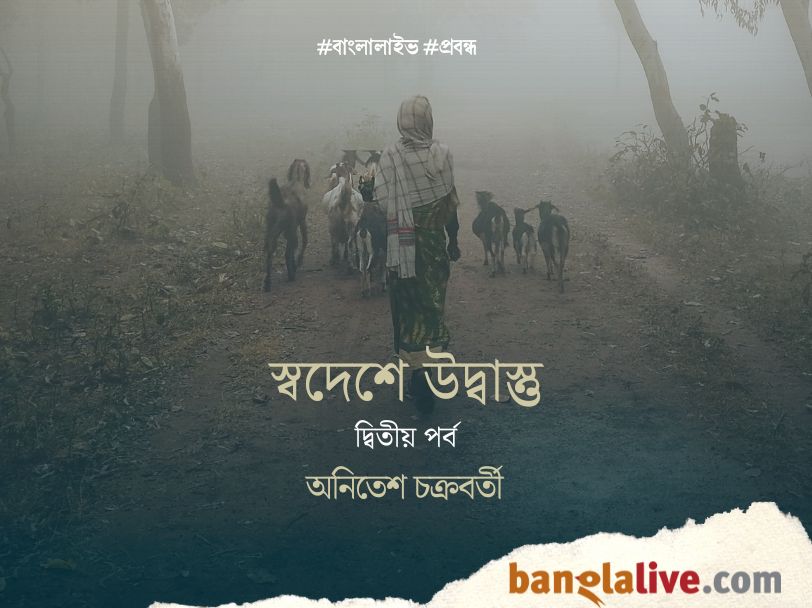





















One Response
অপূর্ব লেখা