সুরের জাদুকর হেমন্ত মুখোপাধ্যায় আজ একশো বছরে পা দিলেন। শতবর্ষের উন্মেষে তাঁকে নিয়ে চর্চা, আলোচনা, পর্যালোচনার অন্ত নেই। তাঁর প্রতিটি গান নিয়ে কথা চলছে সামাজিক মাধ্যমে, টেলিভিশনে, রেডিওতে। বাংলালাইভ শততম জন্মবর্ষে শিল্পী হেমন্তর একটি বিশেষ দিক নিয়ে কথা বলতে চেয়েছে। তাঁর একাধিক প্রবাসযাত্রা এবং প্রবাসে তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা ছিল অবিশ্বাস্য। সেই অনুষ্ঠানগুলির উপরে আলো ফেলেছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত। সুরসম্রাটের জন্মশতবর্ষে বাংলালাইভের বিশেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য:
*
‘না তুম হামে জানো না হাম তুমহে জানে…’
খুব সম্ভবত মার্চ-এপ্রিল মাস, ১৯৬৪ সাল, সুরিনাম। ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
সাতসকালেই গোটা শহর যেন উপচে পড়েছে সুরিনামের এক চিলতে ‘পারমারিব জানদেরিজ’ বিমানবন্দরে। এয়ারপোর্টের ভিতরে-বাইরে কাতারে কাতারে লোক। রয়েছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী, জনপ্রিয় নেতা জোহান এডলফ পেঙ্গেল। পরবর্তীকালে তাঁর নামেই নামকরণ হবে সুরিনামের আন্তর্জাতিক এই বিমানবন্দরের। তবে প্রধানমন্ত্রী একা নন, বিমানবন্দরে সেদিন উপস্থিত তাঁর পাত্র-মিত্র-অমাত্যরাও। রয়েছেন সুরিনামের প্রবাসী ভারতীয় প্রতিনিধিদের সদস্যরা। আসছেন এক বিশেষ অতিথি। সূদুর ভারতবর্ষ থেকে। কোনও রাষ্ট্রনেতা নন, নন কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা সেনানায়ক। তিনি একজন কিংবদন্তি বাঙালি সঙ্গীতশিল্পী। তাঁর নাম হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।
সেই প্রথমবার ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে এসেছেন হেমন্ত। ভারতীয় সংস্কৃতি জগতের তিনিই প্রথম প্রতিনিধি, যিনি আফ্রিকার এই অঞ্চলে পা রাখলেন। কয়েক শতাব্দী ধরে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জমানা থেকে সেখানে বসবাস অসংখ্য ভারতীয়দের। তাঁরা কখনও তাঁদের পিতৃপুরুষের ভূমি ভারতবর্ষ দেখেননি। কিন্তু গানের সুরেই দেশের সঙ্গে পরিচয়। আর পরিচয় এই মানুষটির সঙ্গে, যাঁর কন্ঠমাধুর্যে মাতোয়ারা শুধু ভারত নয়, গোটা বিশ্ব। এমনকি ‘অন্ধকার সেই আদিম’ আফ্রিকাও।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের জামাইকা, ত্রিনিদাদ, ব্রিটিশ গাইনা সেরে এবার সুরিনামে ‘হেমন্ত’। যেখানে গিয়েছেন, পেয়েছেন অকুণ্ঠ ভালোবাসা, সম্মান। শুধু অনাবাসী ভারতীয়রাই নন, ‘আফ্রিকান’রাও তাঁর গানের, কণ্ঠের গুণগ্রাহী ছিলেন। কিন্তু সুরিনামের অভিজ্ঞতা ছিল অনন্যসাধারণ। কোনও রাষ্ট্রনায়কও বোধহয় এমন অভ্যর্থনা পাননি। হেমন্তের বিমান তখনও বিমানবন্দরের মাটি ছোঁয়নি, ‘রেডিও সুরিনাম’-এর ভাষ্যকার ঘোষণা করছেন – “বন্ধুরা, আপনারা ধৈর্য ধরুন…আর মাত্র কিছুক্ষণ…তিনি আসছেন…ওই বিমান দেখা গিয়েছে… বিমান নামছে… লাগানো হচ্ছে সিঁড়ি… ওই দেখা যাচ্ছে তাঁকে… সেই লম্বা মানুষটি, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা… হ্যাঁ শ্রোতাবন্ধুরা, হেমন্ত কুমার সুরিনামের মাটি স্পর্শ করলেন… তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন মহামান্য প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর পারিষদরা… আজ সত্যিই এক ঐতিহাসিক দিন… আমাদের গর্বের দিন!”
এক ভারতীয় গায়কের জন্য সূদুর আফ্রিকার কোনও এক ছোট্ট দ্বীপের রেডিওতে এরকম লাইভ ধারাবিবরণী, রাজকীয় সম্বর্ধনা, জনোচ্ছ্বাস এক কথায় ছিল অপ্রত্যাশিত, নজিরবিহীন। তার সঙ্গে যুক্ত হয় সেখানকার অনাবাসী ভারতীয়দের বাঁধভাঙা উন্মাদনা। ‘বিবিধ ভারতী’র এক সাক্ষাৎকারে হেমন্ত জানিয়েছিলেন, সেখানকার বাসিন্দারা জন্মসূত্রে ভারতীয়, কিন্তু তাঁরা দেশের ভাষা জানতেন না। জামাইকা, ব্রিটিশ গাইনা, ত্রিনিদাদের ভাষা ইংরেজি। ডাচ গাইনার অধীন সুরিনামের ভাষা ডাচ ও বিহারি হিন্দি। কিন্তু সুরের তো কোনও ভাষা হয় না! তার সঙ্গে থাকে আত্মিক যোগ। তা-ই যথেষ্ট। হেমন্ত নিজেই জানিয়েছিলেন, দূর বিদেশে এমন অভ্যর্থনা, ভালোবাসা কল্পনাতীত। একজন ভারতীয় শিল্পী হিসেবে সেদিন তিনি গর্বিত, আপ্লুত বোধ করেছিলেন।

হেমন্ত দু’দিন ছিলেন সুরিনামে। অনুষ্ঠানে গানও গেয়েছিলেন। মূলতঃ হিন্দি ছায়াছবির গান-ই সেখানে প্রাধান্য পায়। গোটা সুরিনাম ভেঙে পড়েছিল সেই অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানের শেষে হাজার হাজার মানুষ তাঁঁকে একবার দেখতে চান, ছুঁতে চান। হেমন্তকে ঘিরে তাঁদের অপার বিস্ময়, মুগ্ধতা। কাউকে ফেরামনি হেমন্ত। কেউ তাঁর পোশাক (সেই বিখ্যাত হাতা গোটানো ফুল শার্ট আর ধুতি) ছুঁয়ে দেখেন আর বলেন – এমন পোশাক তাঁরা আগে কখনও দেখেননি। কেউ তাঁকে স্পর্শ করে বলেন, দেশের মাটি ছোঁয়া হল। হেমন্ত তখন প্রকৃত অর্থে – ‘আমায় করেছ একি চঞ্চল, বিহবল, দিশাহারা।’
অনুষ্ঠান শেষে জনজোয়ারে ভেসে হোটেলে ফেরার পথে এগিয়ে আসেন এক অপরিচিত, অনাবাসী ভারতীয় যুবক। প্রিয় গায়কের হাত ধরে বিনীত প্রার্থনা, একবারটি যদি হেমন্ত তাঁর বাড়ি যান। সেখানে রয়েছেন তাঁর অসুস্থ, মৃত্যুপথযাত্রী পিতা, যিনি নিজে হেমন্তের গানের ভক্ত। অসুস্থ, তাই আসতে পারেননি। কিন্তু শেষবার প্রিয় শিল্পীকে একটিবার দেখার ইচ্ছা, বলা ভালো শেষ ইচ্ছা। জানা যায়, দ্বিধা থাকলেও হেমন্ত ফেরাননি সেই অজ্ঞাতপরিচয় যুবককে। গিয়েছিলেন তাঁর বাড়ি। অসুস্থ, মৃত্যুপথযাত্রী মানুষটি ‘প্রাণের মানুষ’কে সামনে পেয়ে আনন্দে বাকরূদ্ধ, আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন। অশ্রুসিক্ত চোখে হেমন্তের দু’টি হাত বুকে চেপে ধরে বারবার জানান কৃতজ্ঞতা। হেমন্ত তাঁকে নিরাশ করেননি। মৃত্যুপথযাত্রী ভক্তের মাথার পাশে বসে গেয়েছিলেন – “না তুম হামে জানো, না হাম তুমহে জানে…”
*
‘তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ… ‘
১৯৭২ সাল, বার্লিন, জার্মানি। প্রবাসী ভারতীয়দের আমন্ত্রণে গান গাইতে গেছেন হেমন্ত। এক সপ্তাহ আগে থেকেই সারা শহরে পড়েছিল পোস্টার। সেখানেও বিপুল সম্বর্ধনা, উচ্ছ্বাস, উন্মাদনা। বার্লিন টাউন হল লোকে লোকারণ্য। এসেছেন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত, বার্লিন শহরের মেয়র, নানা মান্যিগন্যিরা। গান শুনতে শুধু বার্লিনবাসী নয়, আশপাশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকেও কাতারে কাতারে মানুষ পৌঁছে গিয়েছেন সেখানে। অনাবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়ের মানুষদের পাশাপাশি ভিড় করে এসেছেন জার্মানরাও। তাঁরা হিন্দি, বাংলা বা অন্য ভাষা তেমন কিছুই বোঝেন না। তবু তাঁরা এসেছেন…হেমন্তের কন্ঠের ‘ক্যারিশমা’ এমনই…
চার ঘন্টা বিরতিহীন গান গেয়েছিলেন হেমন্ত। আপ্লুত দর্শকরা তখন পাগলের মত চিৎকার করে বলেছেন – ‘ব্রাভো ব্রাভো! অনকোর, অনকোর!’ হেমন্তও অক্লান্ত ছুটিয়ে চলেছেন তাঁর সুরের মায়াবি ঘোড়া। একসময় অনুষ্ঠান শেষ হয়। দর্শক, শ্রোতাদের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় শেষে অনুষ্ঠানের কর্মকর্তা ও আয়োজকদের মুখোমুখি হন হেমন্ত। প্রাপ্য টাকা তিনি নিতে চাননি। বলেন, “অনুষ্ঠানের শেষ দিকে দেখলাম হলের পিছনে দু’টি রো ভরেনি। আমি চাই না আমার জন্য কারুর কোনও ক্ষতি হোক। আমায় বরং একটু কম টাকা দিন!” কিংবদন্তি গায়কের মুখে এমন প্রস্তাব শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন আয়োজকরা। এমনও হন কোনও শিল্পী?

“হ্যাঁ হন! যদি তাঁর নাম হয় হেমন্ত, তাহলে সম্ভব!” সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন অজিত চট্টোপাধ্যায়। ১৯৬০ সালে মুক্তি পেয়েছিল ‘অগ্রদূত’ পরিচালিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প অবলম্বনে ‘খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন’। জমিদার বাড়ির বিশ্বস্ত, অনুগত ভৃত্য রাইচরণের ভূমিকায় উত্তম কুমারের সেই অবিস্মরণীয় অভিনয় আজও মানুষ ভোলেননি। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন হেমন্ত। ছবিটি সেই বাজারে বিশেষ না চললেও, হেমন্তের কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত ‘তার অন্ত নাই গো নাই’ (বাউলাঙ্গ) সাধারণ মানুষের মুখে মুখে ফেরে। ছবিটি তেমন না চলায় ভেঙে পড়েছিলেন ‘অগ্রদূতে’র অন্যতম সদস্য ও ক্যামেরাম্যান বিভূতি লাহা (১৯১৫-১৯৯৭)। অজিতবাবুকে একটি চিঠি লিখে হেমন্ত বলেছিলেন, “খোকাদা (বিভূতিবাবুর ডাকনাম) কে বলিস যেন চিন্তা না করে। আমি আর ভানু (বন্দ্যোপাধ্যায়) মিলে জলসা করে ওর টাকা তুলে দেব। কোনও অসুবিধা হবে না।”
অজিতবাবু সেই সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, খুব কম শিল্পী এমন আছেন যাঁরা সতীর্থদের দুঃখ দুর্দশার ব্যাপারে এতটা ভাবেন। তাঁকে সাহায্য করতে এতটা এগিয়ে আসতে পারেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছিলেন সেই বিরলতম মানুষদের অন্যতম। তাঁর মৃত্যুর পর বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় একাধিক খাম, যাতে টাকা ভরে ইন্ডাস্ট্রির বহু মানুষ, দুস্থজনকে টাকা পাঠিয়ে ‘নিঃশব্দে’ সাহায্য করতেন হেমন্ত। কোনওদিন চাননি কোনও প্রতিদান, কোনও প্রচার। রবি ঠাকুরের গানটির সঙ্গে যেন এতটাই সম্পৃক্ত, ওতপ্রোত তিনি। হেমন্ত সেই মানুষ যিনি নিজেই হয়ে ওঠেন গান…’তার অন্ত নাই গো নাই’…
*
‘তোমার কোনো বাঁধন নাই তুমি ঘরছাড়া কি তাই’…’
সন ১৯৭১। পশ্চিমবঙ্গ তখন পুড়ছে নকশাল আন্দোলনের আগুনে। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানে (অধুনা বাংলাদেশ) জোরদার হয়ে উঠছে মুক্তিযুদ্ধের লেলিহান শিখা। স্বাধীনতা আসতে আর বেশি দেরি নেই। এসবের মধ্যেই হেমন্ত পাড়ি দিলেন ইংল্যান্ডে। একটি হলিউড প্রোডাকশনে সুরারোপের দায়িত্ব নিয়ে।

নোবেলজয়ী জার্মান সাহিত্যিক হারম্যান কার্ল হেইসের অমর সৃষ্টি ‘সিদ্ধার্থ’-কে সেলুলয়েডের পর্দায় ফেলতে তোড়জোড় শুরু করেছেন প্রথিতযশা পরিচালক কনরাড রুকস। শশি কাপুর, সিমি গ্রেওয়ালের মতো অভিনেতাদের নিয়ে সত্তরের দশকে হৃষিকেশ, ভরতপুরে তাঁর শুট্যিং সেরে নিয়েছেন রুকস। বাকি ছিল ছায়াছবির পোস্ট প্রোডাকশনের কিছু কাজ। তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সিনেমার সঙ্গীত পরিচালনার অংশটি। ‘সিদ্ধার্থ’-এর সঙ্গীত পরিচালনার ডাক পেলেন হেমন্ত। টলিউড, বলিউডের পর এবার সরাসরি হলিউডে ঢুকে পড়লেন হেমন্ত কুমার। ইন্ডাস্ট্রিতে তিনিই দ্বিতীয় যিনি হলিউড সিনেমায় সুর দিয়েছিলেন। প্রথমজন পণ্ডিত রবিশঙ্কর। কিন্তু এক অভিনব প্রস্তাব দিলেন পরিচালক রুকস। তিনি হেমন্তের অন্ধ ভক্ত। বললেন, প্রাচীন ভারতের পটভূমিতে যখন গল্প, তাতে ব্যবহৃত হোক হেমন্তের গাওয়া গান, এবং তাও কিনা বাংলায়!
স্বাভাবিক ভাবেই, হেমন্ত অবাক। ইন্দো-মার্কিন প্রডাকশন হলেও ‘সিদ্ধার্থ’ নিখাদ হলিউড মুভি। সংলাপ ইংরিজিতে। অথচ আবহে গান থাকবে কিনা বাংলায়! এতো ভারি অদ্ভুত! হেমন্ত অনেক করে বোঝান, কিন্তু কনরাড নাছোড়। হেমন্তের শোনানো অগণিত গানগুলির মধ্যে কনরাডের বিশেষ পছন্দের গান দু’টি – বিকাশ রায়ের “মরুতীর্থ হিংলাজ” (১৯৫৯) ছবি থেকে হেমন্তের সুরে, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখায় ‘পথের ক্লান্তি ভুলে’ এবং মৃণাল সেনের “নীল আকাশের নিচে” (১৯৫৮) থেকে ‘ও নদীরে।’ এখানেও গীতিকার সেই গৌরীপ্রসন্ন, সুরকার হেমন্ত।
পরিচালক রুকসের ইচ্ছায় ‘সিদ্ধার্থ’-তে সংযোজিত হল গানদু’টি। নতুন করে গাইলেন হেমন্ত। রেকর্ড হল লন্ডনের বিখ্যাত ডি লেন লি সাউন্ড স্টুডিওতে। অবশেষে ১৯৭৩ সালের ১৮ জুলাই মুক্তি পেল “সিদ্ধার্থ”। সৃষ্টি হল নয়া ইতিহাস। বিশ্ব সিনেমার দরবারে এমন দৃষ্টান্ত অভূতপূর্ব, বিরল। বিদেশি দর্শকেরা আপ্লুত হয়েছিলেন ‘সিদ্ধার্থ’ দেখে ও তার গান শুনে। এক প্রবাসী বাঙালির জবানবন্দি থেকে জানা যায়, হল থেকে সিনেমা দেখে সাহেব-মেমরা বেরিয়ে আসছেন প্রশান্ত চিত্তে, গুনগুন করে গাইছেন তাঁরা “আও নাডিরে আও নাডিরে”। সকলের মুখে মুখে ঘুরেছিল ‘সিদ্ধার্থ’ ছায়াছবি থেকে হেমন্তের গাওয়া ‘ও নদীরে’ গানটি। এরপরেই ‘৭২ সালে টরন্টো-সহ কানাডার বিভিন্ন শহরে সেই গান গেয়ে হাজার হাজার মানুষদের মুগ্ধ করবেন হেমন্ত। তার আগেই টলিউড-বলিউড ছাড়িয়ে সাত সমুদ্র, তেরো নদী পেরিয়ে হলিউডে নামিয়ে এনেছিলেন ‘হেমন্তকাল’।
*
‘ভালো করে মেলে দেখো দৃষ্টি’
আশির দশকের শেষ ভাগ। হেমন্ত তখন ঢাকায়। বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত মাইকেল মধুসূদন সম্মান গ্রহণ করতে এসেছেন। এই বাংলাদেশ জুড়ে তাঁর কত স্মৃতি, কত অবিস্মরণীয় সব অভিজ্ঞতা! আজ সেই বাংলাদেশ তাঁকে সম্মানিত করছে! হেমন্তের কাছে এ যেন ছিল পুরস্কারের মোড়কে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও দূকুল ছাপানো আবেগ। হেমন্ত আপ্লুত, কৃতজ্ঞ, আনন্দিত।
ঢাকার পাট চুকিয়ে কলকাতা ফিরবেন যে দিন, হঠাৎই হাজির এক ভদ্রলোক। সঙ্গে সকরুণ আবদার। একটা গান বেঁধে দিতে হবে। নতুন ক্যাসেট কোম্পানি খুলছেন। চান প্রথম রেকর্ডটি হেমন্তের সেই বিখ্যাত ব্যারিটোনেই ধরা থাক। তখন বেশ কিছুদিন হল শরীর ভালো যাচ্ছে না হেমন্তের। ওষুধ খেতে হচ্ছে। কয়েক বছর আগেই হয়েছে হার্ট অ্যাটাক। শরীরে জাঁকিয়ে বসেছে দুর্বলতা। তাও ভালোবাসার টানে এসেছেন বাংলাদেশ। একাধিক অনুষ্ঠানও করেছেন। তার উপর সেদিন কলকাতা ফিরবেন তিনি। ফ্লাইট ধরার তাড়া রয়েছে। কী করে এখন নতুন গান বাঁধা সম্ভব? হেমন্ত তাঁকে অনেক করে বোঝালেন। কিন্তু অজ্ঞাতপরিচয় সেই ভদ্রলোক নাছোড়। প্রায় পা ধরে লুটিয়ে পড়েন। প্রিয় শিল্পীর কণ্ঠে একটা গান তাঁর চাই, চাইইই। এবারও শেষমেশ ফিরিয়ে দিতে পারেননি হেমন্ত। টেনে নিলেন হারমোনিয়াম। ঢাকা ছাড়ার আগে আধঘণ্টার মধ্যে বেঁধে দিলেন নতুন গান, সারলেন রেকর্ডিংও। খুব সম্ভব সিরাজুল ইসলামের কথায় এ গানে সুর দিয়েছিলেন তিনি –
“ভালো করে মেলে দেখো দৃষ্টি
বুঝবে বাংলাদেশ বিধাতার কত বড় সৃষ্টি..”
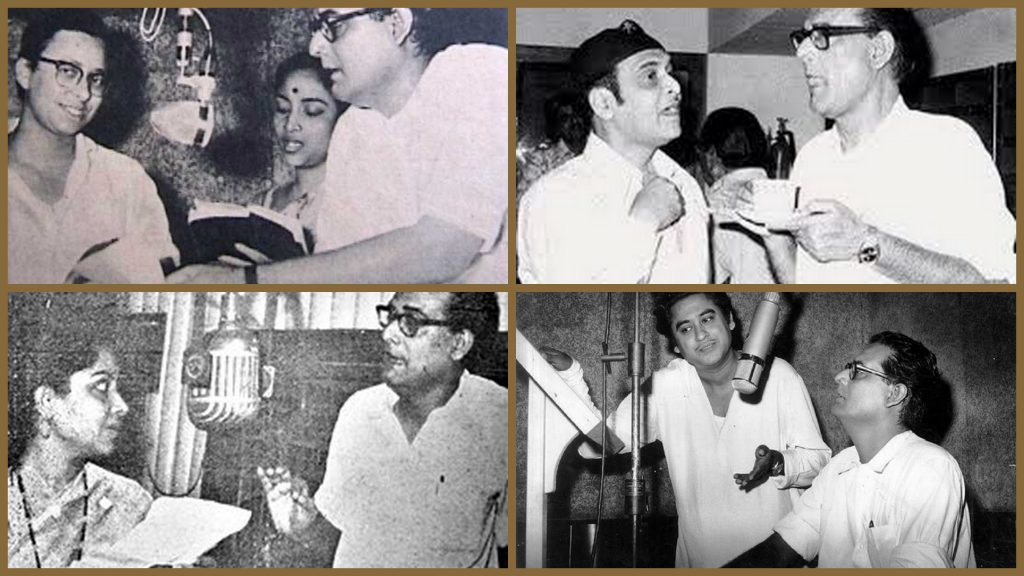
সেই তাঁর শেষ আধুনিক গানের ‘রেকর্ডিং’। ঢাকা থেকে কলকাতা ফেরার পথে ফ্লাইটেই অসুস্থ হয়ে পড়েন হেমন্ত। কলকাতা ফিরেই শয্যাশায়ী। তাঁর অসুস্থতার খবর পেয়ে সব কাজ ফেলে বম্বে থেকে ছুটে এলেন আর এক কিংবদন্তি শিল্পী, বিখ্যাত গজল গায়ক মেহেদী হাসান। কলকাতা বিমানবন্দর থেকে ট্যাক্সি নিয়ে সোজা পৌঁছলেন হেমন্তের দরবারে। এতটাই ছিল শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা তাঁর ‘দাদা’র প্রতি। তাঁর আরোগ্য কামনার প্রার্থনায় করজোড় হয়েছিল গোটা উপমহাদেশ। কিন্তু তবু সেই দিনটা এসেই গেল।
২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯।
ঊনসত্তর বছর বয়সে সুরলোকে পাড়ি জমালেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। শেষ হল ভারতীয় সঙ্গীতের এক কালজয়ী অধ্যায়। চোখের জলে তাঁকে বিদায় জানিয়েছিল গোটা বিশ্ব।
*
“আমি যদি আর নাই আসি হেথা ফিরে…”
কিন্তু আজ তাঁর প্রয়াণ নয়, আবির্ভাবের মূহুর্ত। সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, যখন সরস্বতীর এই মানসপুত্র আবির্ভূত হয়েছিলেন আজ থেকে একশো বছর আগে, বেনারসে। দেশে হোক বা প্রবাসে, তিনি আজও সমান জনপ্রিয়, সমান প্রাসঙ্গিক, সমান শ্রদ্ধেয় ও সমান বিস্ময়ের। শতবর্ষ পেরিয়ে এসে আজও হেমন্ত, হেমন্তই। তিনি অজর, অমর, অক্ষয়। বিকল্পহীন।
তথ্য ঋণ
১. আমার গানের স্বরলিপি, এস ভট্টাচার্য, এ মুখার্জি প্রেস, কলকাতা
২. আনন্দধারা, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা
২. শ্রী সুখেন্দুশেখর রায়, সাংসদ-রাজ্যসভা ও হেমন্ত গবেষক
৩. শ্রী জয়দীপ চক্রবর্তী, অধ্যাপক ও গবেষক
পেশায় সাংবাদিক প্রসেনজিতের জন্ম ১৯৮১-তে। লেখালেখির শুরু কবিতা দিয়েই। ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের ফেলো, প্রসেনজিতের গবেষণার বিষয় রাজনীতি, ধর্মতত্ত্ব ও সঙ্গীততত্ত্ব। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ছয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে লেখা। অবসরে ভালোবাসেন সরোদ বাজাতে, পুরনো চিঠি ও বই পড়তে।




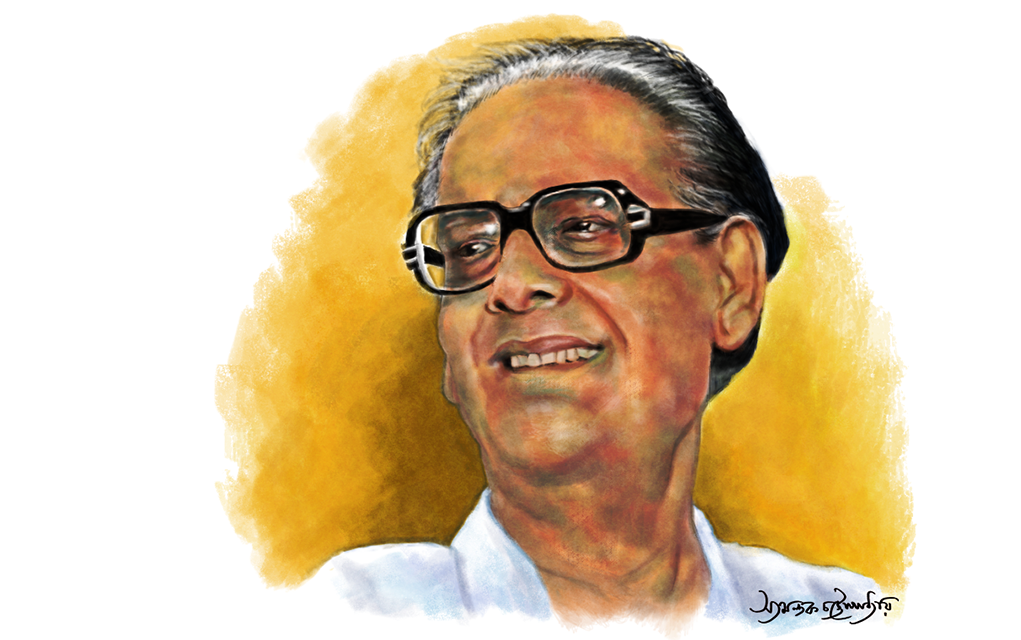





















One Response
হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এক অসাধারন সঙ্গীত প্রতিভা, তাঁর জন্ম শতবর্ষে জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রণাম।