রবীন্দ্রনাথ পড়লে মনে হয়, মানবজীবনে কবিতা ও গানের মধ্যে কোনও সংঘাত নেই। কবির সব গানকেই কবিতার মতো পাঠ করা যায়, আবার অধিকাংশ কবিতাকেই সুরারোপ করলে দিব্য গান হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই হাজার দুই গানে সুর দিয়ে স্বরলিপিও তৈরি করে রেখে গেছেন। সেই গানগুলি অবশ্যই জন্মলগ্নে কবিতা ছিল। অথচ, যথেষ্ট রবীন্দ্রমগ্নতা সত্ত্বেও, আমার শৈশবে গান ও কবিতার মধ্যে এক বিকট সংঘাত দেখা দিল।
তার দুটো মূল কারণ। এক, আমার নিজের স্বখাত সলিল। কবিতা লেখার জন্য খাতা তো যথেষ্টই কিনে দেওয়া হত। তাহলে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করে নিজের রচনা গান, সুর দিয়ে গাওয়ার কোনও দরকার ছিল কি? দ্বিতীয় কারণটা ছিল, বা ছিলেন, মায়ের স্কুলের সেই সমাজনেত্রী হেডমিসট্রেস, যিনি মাকে স্কুল-ছাড়া করেছিলেন। মায়ের অপরাধ, চোদ্দো পেরোবার আগেই নিজের বর পছন্দ করে ফেলা। আমার ধারণা, মা যদি পড়াশুনো চালিয়ে যেতে পারতেন এবং কর্মজগতে ঢুকে পড়তেন যথাসময়ে, তবে নিজের ব্যর্থতাজনিত আক্ষেপ তাঁর এত বেশি থাকত না এবং নিরীহ ছোটমেয়ের মধ্যে দিয়ে জীবনের যাবতীয় লক্ষ্যপূরণের আকাঙ্ক্ষাও এত সুতীব্র হত না।
রবীন্দ্রনাথ নিজেই হাজার দুই গানে সুর দিয়ে স্বরলিপিও তৈরি করে রেখে গেছেন। সেই গানগুলি অবশ্যই জন্মলগ্নে কবিতা ছিল। অথচ, যথেষ্ট রবীন্দ্রমগ্নতা সত্ত্বেও, আমার শৈশবে গান ও কবিতার মধ্যে এক বিকট সংঘাত দেখা দিল।
বাবা, মা, বড়দা কারও গলায় সুর নেই। ছোড়দা একটু আধটু গান করে। নিজের লেখা নয়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের। কিন্তু সে তো ছেলে, কাজেই পার পেয়ে গেল। জালে পড়লাম আমি। ওজনের অনুপাতে যে আমার গলা তেজালো এবং সুরেলা তাতে কারও সন্দেহ ছিল না।
বাড়িতে সঙ্গীতশিক্ষক কেন, কোনও গৃহশিক্ষক রাখারই সামর্থ্য ছিল না। তা ছাড়া জায়গাই বা কোথায়? এই তো দুটো ঘর। মাঝের ডাইনিং স্পেসে মাছের রক্ত মাখা আলু থেকে ছাড়ানো মোচা, সব কিছু দৃশ্যমান। তার থেকে গানের স্কুল অনেক শস্তা।
[the_ad id=”266918″]
আমাদের বাড়ির জানলা থেকে দেখা যেত গানের স্কুল। চারতলা একটা ছাইরঙা বাড়ি। তার তিনতলায় দুটো বারান্দাতেই মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে, দেখা যেত। তিনতলার সব ক’টা ঘর নিয়ে ছিল বিকেবি ইনস্টিটিউশন। আদ্যক্ষরগুলোর আড়ালে কী আছে জানা হয়নি তখন, এখন তো আর জানার প্রশ্নই নেই। আমার নিজের বিশ্বাস ছিল, গৃহশিক্ষক থাকলে আমার শেখাটা জবরদস্ত হত। কারণটা বড়দের বলার মতো নয়। জ্যাঠতুতো দাদার বিয়ের বৌভাতে গিয়ে দাদার তরুণী শ্যালিকাকে দেখলাম গানের মাস্টারের সঙ্গে সিনেমার গান গাইছে। ছাত্রীটির গান খুব যে উঁচুমানের তা নয়, কিন্তু হারমোনিয়মের সাদা-কালো রিডের উপর দু’জনের আঙুলের খেলা দারুণ চিত্তাকর্ষক মনে হয়েছিল।
যাইহোক, এসব তো বড়দের বোঝানো যায় না। তাই ‘চল তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে’-র মতো করে বাবা আমাকে একটা হলদে রসিদ কাটিয়ে বিকেবি-তে ভর্তি করে এলেন। আর আমি প্রতি শনিবার ধুলোট মেঝেতে পাতা ছেঁড়া জাজিমের উপর বসে মুখে-বলা গান লিখে নিতে থাকলাম একটা আলাদা খাতায়। মাসে পাঁচ টাকা মাইনেতে যা হয়। একজন দিদিমণি খুব কষে বিলাবল আর দেশ রাগের সরগম শেখালেন। কয়েকটা কবীরের ভজন শেখা হল। সেগুলো বাবা-মায়ের পছন্দ বলে বাড়িতে মাঝে মাঝেই গাইতে হত। আত্মীয়স্বজন এলেও। সুন্দর দেখতে এক গানের দিদি পাউডারে লিপস্টিকে সেজে আসতেন। ভারী সুরেলা গানের গলা। নির্মলা মিশ্রর গাওয়া ‘ও তোতা পাখি রে’ শিখিয়েছিলেন খুব যত্নে। গানের স্কুলে যাওয়ার পর থেকে শুনে শুনে গান তোলার ক্ষমতা বেড়ে গেল। ‘একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি‘ গাইতাম এঘর ওঘর ঘুরে। ‘সুভাষচন্দ্র’ সিনেমা দেখে দেশের জন্য ত্যাগের ইচ্ছে উথলে উঠেছিল মনে। মা-কে ছেড়ে যাওয়ার চেয়ে বড় ত্যাগ আর কী আছে?
[the_ad id=”266919″]
আত্মীয়দের ফরমায়েশে এইসব গান গেয়ে যেমন নামডাক হল, গান শেখার উপর বিরক্তিও তত শিকড় নামাল মনে। আমার স্বরচিত গানের জগতে যে মুক্তি আর আনন্দ ছিল, তা যেন হারিয়ে গেল ধীরে ধীরে। তখনও টেলিভিশন আসতে অনেক দেরি। সব বাড়িতেই ছোটখাট গানের আসরের চল। কেউ বেড়াতে এলে চা-জলখাবারের পর, ‘নাও একটা গান কর’ বলা ছিল অত্যাবশ্যক। আমার মা গাইতে পারেন না, কিন্তু গান পছন্দ করেন, এটা ছিল তাঁর মুকুটের এক পালক। প্রায় অপরিচিতদেরও পেট ভরে সুখাদ্য খাইয়ে তাঁদের কাছে গান শুনে নিতেন। ফলে আমাকে শুনতে হত, ‘দেখ, এত খরচ করে গান শেখাই, তাও তোর গলায় গান শুনতে পাই না।’

সুন্দরী মনীষা দিদিমণি একদিন কোনার একটা ঘরে হারমোনিয়ম নিয়ে বসে একটা অচেনা সুর তুলছিলেন। আমরা গিয়ে বসতে বললেন, হিন্দি গান। কাউকে বলবে না তো? আমরা মাথা নাড়লাম। সেই প্রথম শুনলাম, ‘দিল যো না কহ্ সকা।’ ‘ভিগি রাত’-এর গান। একবার লতা গেয়েছেন, একবার মহম্মদ রফি। দুটোর লিরিক আলাদা। সব পরে জেনেছি। তখন তো অর্ধেকের বেশি কথাই বুঝতে পারিনি। কিন্তু সুর আর কথার মিলন যে আবেগের এমন ঢেউ তুলতে পারে তা আগে বুঝিনি। ওই গানের অর্থ বুঝেছিলাম আরও দেড় দশক পর, মসুরি আকাদেমির লাউঞ্জে বসে শুনতে শুনতে, জ্যোৎস্নায় ঢাকা হিমালয়ের স্তব্ধতার সান্নিধ্যে। ‘কাউকে বলবে না, কেমন?’
‘চল তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে’-র মতো করে বাবা আমাকে একটা হলদে রসিদ কাটিয়ে বিকেবি-তে ভর্তি করে এলেন। আর আমি প্রতি শনিবার ধুলোট মেঝেতে পাতা ছেঁড়া জাজিমের উপর বসে মুখে-বলা গান লিখে নিতে থাকলাম একটা আলাদা খাতায়।
বলিনি আমরা কেউ-ই। নানারকম পরিবার থেকে এসেছি। কিন্তু হিন্দি সিনেমা দেখা যে খারাপ, আর হিন্দি গান কেবল পুজোর প্যান্ডেলে শোনা যায়, কিন্তু ভদ্রসমাজে গাওয়া যায় না, এটা সবাই জানতাম। তাই ক্লাসের ফাঁকে বারান্দায় দাঁড়ানো আমাদের গল্পগাছায় জড়িয়ে থাকতেন উত্তমকুমার আর তাঁকে নিয়ে আমাদের অভিযোগ, অভিমান। বম্বেতে ‘ছোটি সি মুলাকাত’ ছায়াছবির শুটিং চলছে। কী দরকার অত দূর গিয়ে, সর্বস্ব দিয়ে একটা হিন্দি বই করার, যেটা আমরা কেউই দেখতে পাব না।
যারা গান শিখতে আসত, তাদের সবার পারিবারিক অবস্থা সমান ছিল না। আলো বলে মেয়েটির মা অন্যের বাড়ি সহায়িকার কাজ করতেন। মিঠু বলে একটি ছোট মেয়ে কাকার বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছিল। তার মা-বাবা ছিলেন না। স্কুল থেকে যখন বারবার হারমোনিয়ম কেনার জন্য চাপ আসত, আলো আর মিঠু খুব বিপন্ন বোধ করছে, বুঝতে পারতাম। স্কুল নাছোড়। ভর্তির সময় বলে দেওয়া হয়েছে, হারমোনিয়ম না কিনলে চলবে না। একটি মেয়ে আসত কালীঘাটের দিক থেকে। পরিপাটি করে আঁচড়ে বেণী-বাঁধা চুল, শান্ত মুখশ্রী। সে আমাদের বারান্দার জটলা ও গল্পগুজবে থাকত না। নাম, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্কুলের মালিক মাঝেমধ্যে পয়সা উসুলের জন্য আমাদের গান শুনে যেতেন। গান কিছু বুঝতেন না, কিন্তু পায়ে তাল দিতেন। যথেষ্ট জোরে গাইছে না বলে একদিন মমতাকে বিনা কারণে বকুনি দেওয়াতে আমরা সকলেই খুব রেগে গিয়েছিলাম।
[the_ad id=”270084″]
এর মধ্যে আমার স্বল্পবাক বাবা একদিন অফিসফেরত ট্যাক্সি চাপিয়ে নিয়ে এলেন অতি সুন্দর এক হারমোনিয়ম। মেহগনি কাঠের ঝকঝকে পালিশ করা গা, সাদা রিড যেন হাতির দাঁতে তৈরি, উপরে কাচ সরালে নীল মখমলে মোড়া আর এক ঢাকা, তার ভিতর দিয়ে রিডের উপরের যন্ত্রাংশ দেখা যায়। বেলোর ভিতরেও তেমন সুন্দর নকশা। আজ থেকে বাহান্ন বছর আগে দাম ছিল একশো পঁচাশি টাকা। কাঠের একটা বাক্সের মধ্যে পাতা পুরনো চাদরের উপর বসে থাকত হারমোনিয়মটা। কিছুদিন পর বাক্সের ভিতর প্রচুর সঙ্গীতপ্রেমী আরশোলা আস্তানা বানিয়ে ফেলায় হারমোনিয়মের জায়গা হল খাটের নীচে, সেলাই মেশিনের পাশে।
স্কুল থেকে যখন বারবার হারমোনিয়ম কেনার জন্য চাপ আসত, আলো আর মিঠু খুব বিপন্ন বোধ করছে, বুঝতে পারতাম। স্কুল নাছোড়। ভর্তির সময় বলে দেওয়া হয়েছে, হারমোনিয়ম না কিনলে চলবে না।
নিজে বাজাতে না পারলেও হারমোনিয়মটা হয়ে উঠল মায়ের প্রাণ। আমাকে নিয়মিত রেওয়াজে বসানো ছাড়া হারমোনিয়মের অন্য কোনও ব্যবহার যেন না হয়, সেদিকে মায়ের সদাজাগ্রত ত্রিনয়ন। বাঙালির ঘরে হারমোনিয়ম গোপন রাখা, সেই প্রাক-টিভি যুগে, অসম্ভব ছিল। কেউ না কেউ এসে চাইবেই, কারণ সন্ধেবেলা বাড়িতে জলসা। নিয়ে যাবে মিষ্টি কথা বলে, আর ফেরত দেবে না। এই সব নানা কাল্পনিক আতঙ্কে ভুগে মা ঠিক করে ফেললেন, হারমোনিয়ম কাউকেই ধার দেওয়া হবে না। প্রতিবেশীরা ‘অবাঙালি’, হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইতে বসে না, এটা একটা সুখের ব্যাপার। সকলেই ব্যবসায়ী। বাজারের বাড়ির এক তলায় চিনির, ডালের আড়ত, বাজারের মধ্যে মুদি দোকান, তেল ও লঙ্কার গোদাম। মাছ আর ডিম বাদ দিয়ে পুরো ব্যবসার দুনিয়া তাদের করতলগত। একটু দূরে জগুবাবুর বাজারে সারি সারি মোটর পার্টস আর টায়ারের দোকান। আমাদের প্রতিবেশী শিখেরাও সেখানে বসতেন।
[the_ad id=”270085″]
শেষ পর্যন্ত, বসিরহাট থেকে আসা মায়ের এক মাসতুতো ভাই নিজের নতুন বউয়ের গানের অনুষ্ঠানের জন্য হারমোনিয়মটি চাইতে এলে মা আর মানা করতে পারলেন না। আমাদের শূন্য বুকে হাহাকার তুলে ভাই ও তার এপাড়ার বন্ধু হারমোনিয়মটি তুলে যখন বেরিয়ে যায়, মা বিপন্ন মুখে বললেন, রিকশা ডাকবি তো? পাছে রাস্তায় পড়ে টড়ে যায় হারমোনিয়ম, এই শঙ্কা। বাড়ির নীচেই রাস্তার উপর রিক্সাওলারা বসে থাকে। বামপন্থী ভাইটি বঙ্কিম হেসে বলল, ‘ মানুষে টানা রিকশায় বসব, আমি?’ বামপন্থায় আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় করে হারমোনিয়মটা সেবার অক্ষতই ফিরে এসেছিল, কয়েকদিন পর, মানুষের হাতে বওয়া হয়ে।
কলকাতায় জন্ম, বড় হওয়া। অর্থনীতির পাঠ প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কবিতা দিয়ে লেখক জীবন আরম্ভ। সূচনা শৈশবেই। কবিতার পাশাপাশি গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, প্রবন্ধ, ছোটদের জন্য লেখায় অনায়াস সঞ্চরণ। ভারতীয় প্রশাসনিক সেবার সদস্য ছিলেন সাড়ে তিন দশকেরও বেশি সময়। মহুলডিহার দিন, মহানদী, কলকাতার প্রতিমা শিল্পীরা, ব্রেল, কবিতা সমগ্র , দেশের ভিতর দেশ ইত্যাদি চল্লিশটি বই। ইংরাজি সহ নানা ভারতীয় ভাষায়, জার্মান ও সুইডিশে অনূদিত হয়েছে অনিতা অগ্নিহোত্রীর লেখা। শরৎ পুরস্কার, সাহিত্য পরিষৎ সম্মান, প্রতিভা বসু স্মৃতি পুরস্কার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুবন মোহিনী দাসী স্বর্ণপদকে সম্মানিত। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমীর সোমেন চন্দ পুরস্কার ফিরিয়েছেন নন্দীগ্রামে নিরস্ত্র মানুষের হত্যার প্রতিবাদে। ভারতের নানা প্রান্তের প্রান্তিক মানুষের কন্ঠস্বর উন্মোচিত তাঁর লেখায়। ভালোবাসেন গান শুনতে, গ্রামে গঞ্জে ঘুরতে, প্রকৃতির নানা রূপ একমনে দেখতে।




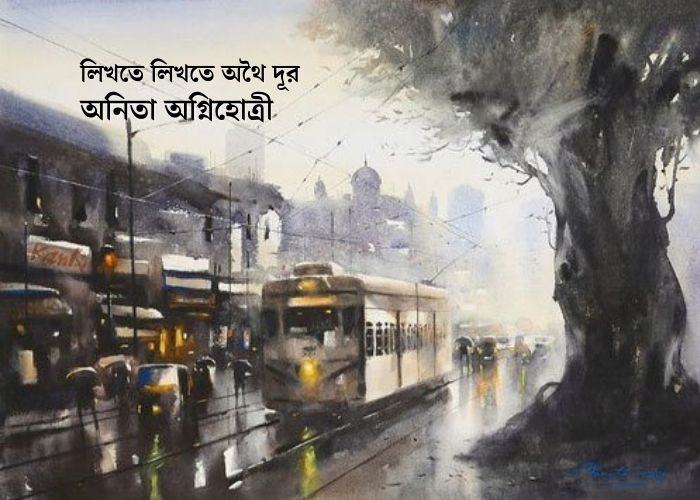





















5 Responses
One of my favourite writers.
Bhalo laglo.
কত সুন্দর ভাবে নিজের ছোটবেলা কে বর্ণনা করেছেন । পড়লে নিজেদের ছোটবেলা ও ভেসে ওঠে চোখের সামনে। খুব খুব ভালো লেখা। পরের পর্বের অপেক্ষায় রইলাম।
মন ভরে গেল।
ভালো লাগলো।আমাদের ছোটবেলায় ও হিন্দি গান গাওয়া খুব গর্হিত কাজ ছিল।
আর নিজের গানে সুর বসিয়ে না গাইতে পাওয়ার কষ্টটা অনুভব করলাম।