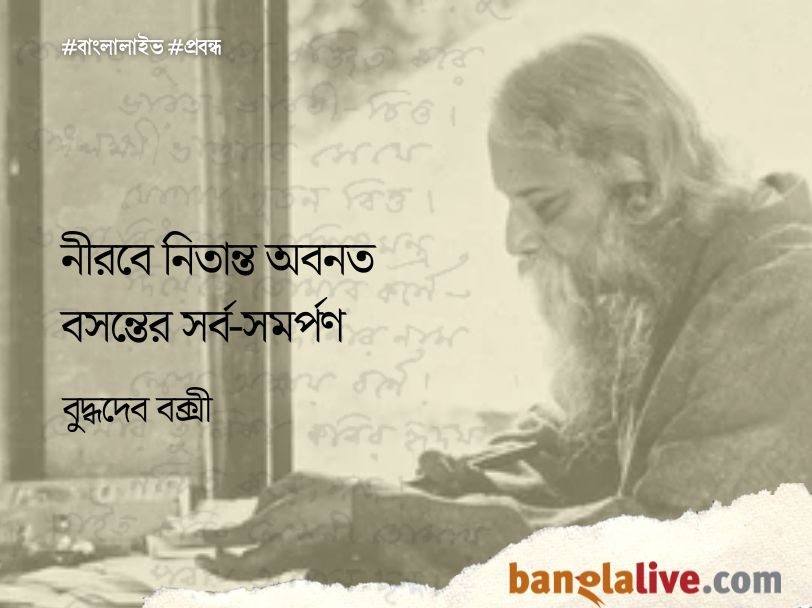(Rabindranath Tagore)
রবীন্দ্রনাথের বহুল প্রচলিত কবিতার লিস্টে (অর্থাৎ যেসব কবিতা সচরাচর পাঠ করা হয়) “উৎসর্গ” নেই। চৈতালি কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত কবিতাটি কবির শ্রেষ্ঠতম কবিতাগুলির সমতুল। হয়তো অন্তর্নিহিত ভাব, ভাষার ব্যবহার, চিত্রকল্প এবং ছন্দ খানিকটা জটিলতা সৃষ্টি করে, যা সাধারণ পাঠকের অসুবিধার কারণ হয়। কবিতা অপঠিত থেকে যায়। প্রায় নিকটতম বিষয়ের ওপর লেখা কবিতা “সোনার তরী” অত্যন্ত সহজ পাঠ্য, ছন্দময় এবং আবৃত্তি যোগ্য। হয়তো সবচেয়ে জনপ্রিয় কবিতা। (Rabindranath Tagore)
আরও পড়ুন: শাড়ির আঁচল নিয়ে অর্থহীন কথার বদলে…
(Rabindranath Tagore) রবীন্দ্রনাথের কবিতা নিয়ে লেখার আগে একটু ভূমিকা করা যেতে পারে।
আমার “রবীন্দ্রনাথ” পড়া কোনও ইস্কুলের স্ট্রাকচার্ড স্টাডি নয়। বাংলা সাহিত্যে ডিগ্রি অর্জন করা হয়নি আমার। নিতান্তই ছোটো থেকে ভাল লেগেছে বলে পড়া। বাড়িতে সঞ্চয়িতা থেকে শুরু করে গল্পগুচ্ছ হয়ে সামান্য কিছু বইপত্র, দেওয়ালে তাঁর ছবি, মায়ের গীতবিতান, স্কুলে রবীন্দ্রজয়ন্তীতে কবিতা পাঠ করা, ইত্যাদিই সেই ভাললাগার উৎস। অজান্তে তিনি কখন institutionalised হয়ে গেছেন, জানা নেই। (Rabindranath Tagore)
মধ্য আশির দশকের সময়টায় কলকাতায় কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিশেষ করে অর্থনীতির ছেলে মেয়েরা সুনীল, শক্তি ছাড়াও কল্লোল যুগের কবিদের লেখা পড়ত।
(Rabindranath Tagore) তখন ক্লাস ফোরে পড়ি। মাস্টারমশাই বললেন যে রবীন্দ্রজয়ন্তীতে “নকল বুঁদিগড়” আবৃত্তি করতে হবে। প্রথমবার স্টেজে উঠেছিলাম। ভয়ে, লজ্জায় মাথা নীচু করে অনর্গল মুখস্ত বলেছিলাম। যে ভাবে শিখিয়ে দিয়েছিলেন, ঠিক সেভাবেই, গলার কণ্ঠস্বরে ওঠানামা করিয়ে। আবৃত্তির পর প্রচণ্ড হাততালিতে প্রথম মুখ তুলি। ভীষণ ভাল লেগেছিল। সেই থেকে কবিতা মুখস্ত করা শুরু।
মধ্য আশির দশকের সময়টায় কলকাতায় কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিশেষ করে অর্থনীতির ছেলে মেয়েরা সুনীল, শক্তি ছাড়াও কল্লোল যুগের কবিদের লেখা পড়ত। বিষ্ণু দে’র কবিতার পাণ্ডিত্যের জটিলতা, সুধীন্দ্রনাথের রেফারেন্সের দুরূহতা, অমিয়বাবুর কবিতার স্পিরিচুয়াল ব্যাপার– ইত্যাদি নিয়ে, চা আর সিগারেটের সঙ্গে আড্ডা বেশ জমে যেত। অবশ্য সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন জীবনানন্দ। সেখানে আবার অনুভূতির জটিলতা। অবশ্য কনস্ট্যান্ট ভাল লাগা হিসেবে রবীন্দ্রনাথের লেখা সতত বর্তমান ছিল। (Rabindranath Tagore)
বিষ্ণু দে’র কবিতার পাণ্ডিত্যের জটিলতা, সুধীন্দ্রনাথের রেফারেন্সের দুরূহতা, অমিয়বাবুর কবিতার স্পিরিচুয়াল ব্যাপার– ইত্যাদি নিয়ে, চা আর সিগারেটের সঙ্গে আড্ডা বেশ জমে যেত।
সেযুগে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ভালবাসা ছিল, শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু মত্ততা ছিল না। মৌলবাদ ছিল না।
ক্যান্টিনে অনেকে টেবিল বাজিয়ে গানের প্যারোডি শোনাতেন। অনেকসময় অশ্লীল শব্দের ব্যবহার হত। কিন্তু হৈ হৈ করে কেউ তেড়ে আসত না। আমাদের বিশ্বাস ছিল যে রবীন্দ্রনাথ এত ঠুনকো নন যে একটা প্যারোডি করলে অপরাধ হয়ে যাবে। “সব বিদ্বেষ দূরে যায় যেন তব মঙ্গল মন্ত্রে।” (Rabindranath Tagore)
ক্যান্টিনে অনেকে টেবিল বাজিয়ে গানের প্যারোডি শোনাতেন। অনেকসময় অশ্লীল শব্দের ব্যবহার হত। কিন্তু হৈ হৈ করে কেউ তেড়ে আসত না।
(Rabindranath Tagore) ভূমিকার পর এবার প্রসঙ্গে আসি। চৈতালী কাব্যগ্রন্থের “উৎসর্গ” কবিতা নিয়ে। তেমন পরিচিত কবিতা নয়। কলেজের আড্ডায় আমি “সোনার তরী” পাঠ করি। “উৎসর্গ” পাঠ করে এক বন্ধু। তখন আমাদের নানারকম পড়াশোনা চলছে, কোনওটাই হজম হয়নি। আড্ডায় সেসব আসত। এক বন্ধু বলে, “ফ্রয়েড সাহেব দিয়ে বেশ গুছিয়ে ইন্টারপ্রিটেশন করা যেতে পারে।” আরেক বন্ধু বলে ওঠে “শুক্তিরক্ত নখরে বিক্ষত ছিন্ন করি ফেলো বৃন্তগুলি অথবা রসভরে অসহ উচ্ছ্বাসে থরে থরে ফলিয়াছে ফল, এসব লাইন তো বাৎস্যায়ন কে হার মানায় ভায়া”, ইত্যাদি, ইত্যাদি। কবিতাটি কোট-আনকোট করা যাক:
“আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে
গুচ্ছ গুচ্ছ ধরিয়াছে ফল।
পরিপূর্ণ বেদনার ভরে
মুহূর্তেই বুঝি ফেটে পড়ে,
বসন্তের দুরন্ত বাতাসে
নুয়ে বুঝি নমিবে ভূতল–
রসভরে অসহ উচ্ছ্বাসে
থরে থরে ফলিয়াছে ফল।
তুমি এসো নিকুঞ্জনিবাসে,
এসো মোর সার্থকসাধন।
লুটে লও ভরিয়া অঞ্চল
জীবনের সকল সম্বল,
নীরবে নিতান্ত অবনত
বসন্তের সর্ব-সমর্পণ–
হাসি মুখে নিয়ে যাও যত
বনের বেদননিবেদন।
শুক্তিরক্ত নখরে বিক্ষত
ছিন্ন করি ফেলো বৃন্তগুলি
সুখাবেশে বসি লতামূলে
সারাবেলা অলস অঙ্গুলে
বৃথা কাজে যেন অন্যমনে
খেলাচ্ছলে লহো তুলি তুলি–
তব ওষ্ঠে দশনদংশনে
টুটে যাক পূর্ণ ফলগুলি।
আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে
গুঞ্জরিছে ভ্রমর চঞ্চল।
সারাদিন অশান্ত বাতাস
ফেলিতেছে মর্মরনিশ্বাস,
বনের বুকের আন্দোলনে
কাঁপিতেছে পল্লব-অঞ্চল–
আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে
পুঞ্জ পুঞ্জ ধরিয়াছে ফল।”
(Rabindranath Tagore)
নীরবে নিতান্ত অবনত
বসন্তের সর্ব-সমর্পণ–
হাসি মুখে নিয়ে যাও যত
বনের বেদননিবেদন।
অনেক দশক বাদে প্রবাসে, সেদিন এক অনুষ্ঠানে কবিতাটি পাঠ করলাম। তারপর এক ভদ্রমহিলা সুন্দর করে “সোনার তরী” পাঠ করলেন। তিন দশক আগের স্মৃতি ভেসে এল। ভাবলাম কবিতা দু’টি নিয়ে কিছু লেখা যাক।
“সোনার তরী” দিয়ে শুরু করি। অনেকটা একই রকম ভাবের প্রকাশ দুটো কবিতায়। টেমপ্লেট আলাদা। গভীরতম অর্থ আলাদা। (Rabindranath Tagore)
“সোনার তরী” বহুমাত্রিক। প্রতিটি পাঠকের কাছে নিজস্ব একটা ব্যঞ্জনা নিয়ে আসে। স্টোরি লাইনের সারাংশ হল যে বর্ষার আগে ধানের স্তূপ নিয়ে “আমি” অপেক্ষা করে আছি “মাঝি”র জন্য। সে এসে নৌকায় তুলে নেবে সমস্ত কিছু। সে এল এবং নৌকা বোঝাই করে নিল। তারপর “আমাকে” ফেলে রেখে চলে গেল। “আমি” একা পড়ে রইলাম নদীতীরে।
“কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা”, লাইনে এই ভরসা না-থাকার বিবিধ সম্ভাবনা থাকতে পারে। মাঝি না-আসার, তুমুল বৃষ্টি আসা অথবা ছোট দ্বীপখানি জলে প্লাবিত হয়ে সব কিছু শেষ করে যাওয়া। জীবনের আগে সীমাহীন অন্ধকার আর মৃত্যুর পর আরেক অন্ধকার। জীবন সীমিত একটা আলো মাত্র। শঙ্করাচার্যের পদ্মপাতায় জলবিন্দুর মতো নিত্য টলটলায়মান। মানুষের প্রিমিটিভ ঈশ্বর চেতনার এখান থেকেই উৎপত্তি লাভ। (Rabindranath Tagore)
জীবনের আগে সীমাহীন অন্ধকার আর মৃত্যুর পর আরেক অন্ধকার। জীবন সীমিত একটা আলো মাত্র।
রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর কখনও জীবনদেবতা রূপে, কখনও মাঝিরূপে, কখনও নারীরূপে, কখনও বা পুরুষরূপে আসেন। দূর থেকে দেখে মনে হয় “চিনি উহারে।” সোনার তরীর এই মাঝিকে আবার দেখা যায় “দিনান্ত বেলায়।” কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে প্রত্যক্ষ করান ডিভাইন কণ্ঠে। কবিতাটির ইংরিজি অনুবাদে আবার সোনার তরীর মাঝি নারী রূপে আসেন। “From the shadows of the opposite shore the boat crosses with a woman at the helm. I cry to her, ‘Come to my island coiled round with hungry water, and take away my year’s harvest.” সোনার তরী চলে যায়– সমস্ত কর্মফল নিয়ে। আমাদের আশাহত করে। প্রত্যাশা পূরণ হয় না। আমরা আহত হই, ব্যথিত হই। শ্রীকৃষ্ণ বলেন “কর্মেই অধিকার”। “মা ফলেষু কদাচন”। অপরিমেয় আকুতি, আর প্রার্থনা ঝরে পড়ে, “এখন আমারে লহ করুণা করে।” কবিতাটি শেষ হয় এক বিষণ্ণ হাহাকারে: “শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি– যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।” (Rabindranath Tagore)
শঙ্করাচার্যের পদ্মপাতায় জলবিন্দুর মতো নিত্য টলটলায়মান। মানুষের প্রিমিটিভ ঈশ্বর চেতনার এখান থেকেই উৎপত্তি লাভ।
শতবর্ষ পরে আজও রবীন্দ্রনাথের সোনার ধান রয়ে গেছে আমাদের হৃদয়ের গভীরে।
‘উৎসর্গ’ বসন্তকালের কবিতা। ভারতীয় চেতনায় বসন্ত ঋতু মিলনের ঋতু, সম্ভোগের ঋতু। যদিও জীববিদ্যায় বা জৈবরসায়নে হোমো সাপিয়েন্স প্রজাতির মিলন অন্যান্য অনেক প্রাণীকুলের মতো প্রোগ্রামড নয়। মস্তিষ্কের গভীরে হাইপোথালামসে সম্ভাব্য সঙ্গীর বার্তা পৌঁছোয় আর ক্ষরণ হয় সেরেটোনিন, অক্সিটোসিন ইত্যাদির। সে মিলনের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। তবুও সনাতন চেতনায় মনে করা হয় বসন্ত ঋতুর ফাল্গুন, চৈত্রে মিলনেচ্ছা প্রবল হয়। রবীন্দ্রনাথ লেখেন, “প্রহর শেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্রমাস, তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ।” (Rabindranath Tagore)
ভারতীয় চেতনায় বসন্ত ঋতু মিলনের ঋতু, সম্ভোগের ঋতু। যদিও জীববিদ্যায় বা জৈবরসায়নে হোমো সাপিয়েন্স প্রজাতির মিলন অন্যান্য অনেক প্রাণীকুলের মতো প্রোগ্রামড নয়।
প্রথম স্তবকে দেখি সেই সোনার ধানের মতোই দ্রাক্ষা কুঞ্জে পরিপূর্ণ ফল। ফসলের আকাঙ্ক্ষা শেষ। পরের স্তবকে আহ্বান। তৃতীয় স্তবকে কিছু চিত্রকল্প আছে যা আপাত দৃষ্টিতে খানিকটা বাৎসায়ানের কামসূত্রের মিলনের বর্ণনায় মিলে যায়। খানিকটা ইরোটিক। বন্ধু যে ফ্রয়েড সাহেবের উল্লেখ করেছিল, সেটা বোধহয় ওই চেতন, অবচেতন ইত্যাদির কথা ভেবে। চতুর্থ স্তবকে আবার সেই কারুর জন্য প্রতীক্ষার একটা ইঙ্গিত আছে। অর্থাৎ কবিতাটিতে “সোনার তরী”র মতো সিকুয়েন্সিয়াল গল্পের গতি নেই। এখানে পুরোটাই একটা আকাঙ্ক্ষা এবং প্রতীক্ষা। চেতন অবচেতন জগতে সহাবস্থান হচ্ছে একই সময়ে। (Rabindranath Tagore)
তৃতীয় স্তবকে কিছু চিত্রকল্প আছে যা আপাত দৃষ্টিতে খানিকটা বাৎসায়ানের কামসূত্রের মিলনের বর্ণনায় মিলে যায়।
ফ্রয়েড সাহেবের তত্ত্বের বেসিক প্রিমাইসিস “পাপবোধ”। আব্রাহামিক চেতনায় আদম-ইভের আদিম পাপের থেকে মুক্তির জন্য সাধনা করতে হবে। সনাতন ধর্ম চেতনায় মানুষ অমৃতের পুত্র। ফ্রয়েডের সমসাময়িক গিরীন্দ্রশেখর বসুর মতে ভারতীয় সাইকোনালাইসিসের প্রিমাইসিস হল “ধর্মসংকট”, পাপবোধ নয়। কুন্তী, কুমুদিনী, গোরা, নিখিলেশ, মহেন্দ্র, বিপ্রদাস হয়ে রবীন্দ্রনাথের মুখ্য চরিত্রের অন্তরে বাহিরে শুধুই ধর্মসংকট। ফ্রয়েড সাহেবের সঙ্গে কবির হয়তো একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল, কিন্তু আলোচনা কি হয়েছিল সে বিশেষ কিছু জানা যায় না। মোদ্দা কথা ফ্রয়েড সাহেব দিয়ে রবীন্দ্রনাথের লেখার চরিত্র বিশ্লেষণ আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়।
ধর্মসংকট থেকে মুক্তির তত্ত্ব হয়তো সর্ব সমর্পণ। রাসতত্ত্বের সমর্থা-রতির সমর্পণ। শ্রীমদ ভাগবতে রাসলীলাই সর্ব লীলার মুকুটমনি। সেখানে রতি তিনপ্রকার। সাধারানী-রতি, সমঞ্জস-রতি, সমর্থা-রতি। মিলনের, সম্ভোগের ইচ্ছা থেকে সাধারানী রতি মোহ দ্বারা চালিত হয়। কৃষ্ণের গুণাবলীর কথা শুনে চেতনা যখন উদ্দীপিত হয়, এবং একপ্রকার অধিকার বোধ কাজ করে সমঞ্জস্য- রতিতে। সমর্থা-রতির তত্ত্ব জটিলতম। (Rabindranath Tagore)
ফ্রয়েড সাহেবের সঙ্গে কবির হয়তো একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল, কিন্তু আলোচনা কি হয়েছিল সে বিশেষ কিছু জানা যায় না।
সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় “শ্রী শ্রী গীত গোবিন্দ”র ভূমিকায় লেখেন: “শ্রী রাধাই ব্রজের মধুরা রতির মূল উৎস, শ্রীরাধিকার কৃষ্ণ-সুখৈক তাৎপর্যময়ী যে রতি, সম্ভোগ বাসনার গন্ধমাত্র যাহাতে নাই সেই রতিকে সমর্থা রতি বলে। স্বরূপ ধর্ম বশতঃ ইহা আপনা আপনি উন্মেষিত হয় — শ্রীকৃষ্ণের রূপ মাধুর্য্যাদি দর্শন বা গুণাদি সেবন ব্যতিরেকে শ্রীকৃষ্ণে এই রতি উন্মেষিত হয় এবং দ্রুত গতিতে গাঢ়তাপ্রাপ্ত হয়। সমর্থা রতি মতি ব্রজসুন্দরী দিগের কোনও সময়ই সসুখ বাসনাময়ী সম্ভোগ ইচ্ছা জন্মে না। একমাত্র কৃষ্ণকে সুখী করার বাসনা তাহাদের বলবতী। ইহাদের সম্ভোগের ইচ্ছা গৌণী। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের অঙ্গ সঙ্গের জন্য লালায়িত, তাই তাহারা নিজাঙ্গের দ্বারা তাঁহার সেবা করেন।”
“উৎসর্গ”-তে কোনও আশা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই। নিরাশা নেই, হাহাকার নেই, ক্রন্দন নেই। কেবলমাত্র সর্বস্ব নিয়ে প্রতীক্ষায় থাকা। “আমাকে” গ্রহণ করো নেই। “আমাকে” ঠাঁই দাও নেই। শুধু প্রতীক্ষা। অন্তহীন প্রতীক্ষা।
কবিতাটি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ট্র্যাডিশনের। সেখানে প্রধান গোপীনি শ্রীরাধা। শ্রীচৈতন্যদেব সেই সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথের লেখায় সেই ট্র্যাডিশন এর সর্বোচ্চ ভাব ফুটে উঠেছে।
“নীরবে নিতান্ত অবনত বসন্তের সর্ব-সমর্পণ।” (Rabindranath Tagore)
অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। কাজের ক্ষেত্র তথ্যপ্রযুক্তি। কিছুদিন স্মার্ট সিটিতে কাজ করেছেন। আড্ডাবাজ মানুষ। বইপড়া আর সিনেমা দেখা নেশা। কাজের সুত্রে সলিউশন ব্লুপ্রিন্ট, স্পেক্স, প্রপোজাল ইত্যাদি অনেক লিখেছেন। ইদানিং বাংলায় প্রবন্ধ, গল্প, ফিল্ম রিভিউ লেখার একটা চেষ্টা চলছে।