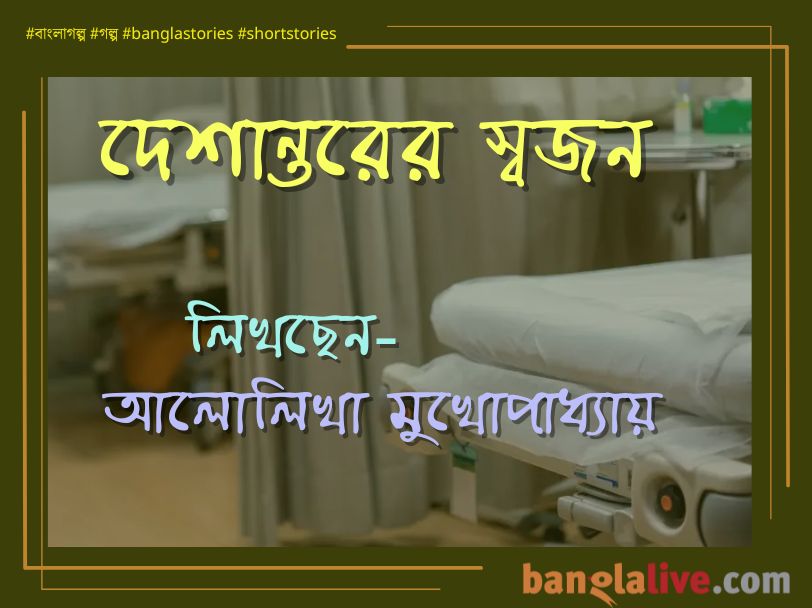সানরাইজ হেলথ কেয়ার সেন্টারের পশ্চিমের কাচে ঘেরা বারান্দা থেকে সূর্যাস্ত দেখা যায়। বিশাল দিগন্ত জুড়ে লাল আভা ম্লান হতে হতে দূরের গাছপালার আড়ালে হারিয়ে যাওয়ার আগে ‘সানরাইজ’-এর বাগানে, গাড়ির পার্কিং লটে সারি সারি আলো জ্বলে ওঠে। চারতলা বাড়িটায় শিফট বদলের সময় হঠাৎ ব্যস্ততা বেড়ে যায়। শেষ হয় অপালার একটি কর্মক্লান্ত দিন। (deshantorer swajan)
আজ নিচে নামার জন্য এলিভেটরের কাছাকাছি যেতে রাতের শিফট-এর নার্স মেলিসার ফোন এল— তুমি কি এখনও নার্সেস স্টেশনে আছো?
অপালা উত্তর দিল— না। নিচে যাচ্ছি। কেন? ইজ দেয়ার এনি প্রবলেম?
— নট অ্যাট অল। দু’শো দশের পেশেন্ট বলছে, তোমার নাকি ওকে বই দেওয়ার কথা ছিল। রাতে স্লিপ মেডিকেশন নেওয়ার আগে বই পড়বে। কিন্তু আমি তো কোনও বই দেখতে পাচ্ছি না।
এলিভেটরের ভেতর থেকে অপালা জানিয়ে দিল— বলে দাও কাল ম্যাগাজিন নিয়ে আসব। ওকে, বাই।
গাড়িতে উঠে বাড়ি ফেরার পথে অপালা ভাবছিল, অভিজিৎ হয়তো আরও দু-চারবার ওর খোঁজ করবেন। কাল সকাল থেকে আবার ডাকাডাকি শুরু হবে। কিছু অবান্তর কথা বলবেন। অথচ ডিমেনশিয়ার সূত্রপাত নয়। বয়সও তেমন বেশি হয়নি। শুধু ক্যানসার সার্জারির পর থেকে পিঠের ব্যথায় প্রায় শয্যাশায়ী হয়ে আছেন। হয়তো দীর্ঘদিন এখানেই থাকতে হবে। নার্স হিসেবে অপালার দায়িত্ব এই সব লং টার্ম কেয়ারের অসুস্থ মানুষদের দেখাশোনা করা। কিন্তু বিশেষ একজন রোগিকে যখন তখন সঙ্গ দেওয়া তো সম্ভব নয়। ভারতীয় নার্স বলে ভারতীয় রোগিকে বেশি সময় দেবে, ওয়ার্কিং আওয়ারে প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যে সে সুযোগ কোথায়? প্রফেশনাল এথিক্স অনুযায়ী সকলের প্রতিই তার সমান দায়িত্ব। অনেক বছর ধরে এই চাকরি করতে করতে অপালা বুঝেছে, ধৈর্য আর সহানুভূতির পাশাপাশি এক ধরনের ডিট্যাচমেন্টও এসে যায়। তবু, দু’শো দশ মানেই তো শুধু একটা ঘরের নম্বর নয়। সেখানে একজন চেনা মানুষ অসুস্থ অবস্থায় আছেন। অপালা যতটুকু পারে সাহায্য করে। কিন্তু অভিজিতেরও একটু বোঝা দরকার। কত লোক বছরের পর বছর লং টার্ম কেয়ারে থাকে। কখনও বার্ধক্যের জন্যে, কখনও আত্মীয়স্বজনের অভাবে চিকিৎসা আর সেবাযত্নের জন্যে এখানে চলে আসতে বাধ্য হয়। ছেলেমেয়ে থাকলেও বা কি! তাদের চাকরি, সংসার ফেলে রেখে বারোমাস অসুস্থ বাবা-মা’র পাশে থাকা সম্ভব নয়। তবু যারা এখানে পাঠায় না, তারা বাড়িতে হোম হেলথ কেয়ারের নার্স, নার্সেস এইড রেখে দেখাশোনার ব্যবস্থা করে। কিন্তু অভিজিতের দায়িত্ব কে নেবে? অপালা ভেবে পায় না, ওঁর ভবিষ্যৎ জীবনে আর কী অল্টারনেটিভ থাকতে পারে? উনি কেন বাস্তব অবস্থাটা বুঝতে চাইছেন না?
বাড়ি ফিরে স্নান সেরে বেরিয়ে অপালা শুনতে পেল মৈনাক ফোনে কথা বলছে। নিচে এসে রান্নাঘরে দুজনের চা তৈরি করতে করতে কানে এল— তোমরা কখন আসতে পারবে বলে মনে হয়? একটু ধরো, আমি অপালাকে ফোনটা দিচ্ছি। ও ঠিকমতো বলতে পারবে।
তবু, দু’শো দশ মানেই তো শুধু একটা ঘরের নম্বর নয়। সেখানে একজন চেনা মানুষ অসুস্থ অবস্থায় আছেন। অপালা যতটুকু পারে সাহায্য করে। কিন্তু অভিজিতেরও একটু বোঝা দরকার। কত লোক বছরের পর বছর লং টার্ম কেয়ারে থাকে। কখনও বার্ধক্যের জন্যে, কখনও আত্মীয়স্বজনের অভাবে চিকিৎসা আর সেবাযত্নের জন্যে এখানে চলে আসতে বাধ্য হয়। ছেলেমেয়ে থাকলেও বা কি! তাদের চাকরি, সংসার ফেলে রেখে বারোমাস অসুস্থ বাবা-মা’র পাশে থাকা সম্ভব নয়।
অপালাকে ফোনটা ধরিয়ে দেওয়ার আগে মৈনাক বলল — গ্রেট নেক থেকে রঞ্জনারা রবিবার অভিজিৎদাকে দেখতে আসতে চাইছে। আমরা কি ফ্রি আছি? তাহলে আমরাও যেতে পারি।
ফোন ধরে দু-এক কথার পর রঞ্জনাদের রবিবার সোজা ‘সানরাইজ’-এ যেতে বলল অপালা। ফেরার পথে এখানে ডিনারের নেমন্তন্নও করল। ঠিকানা, ফোন নম্বরও দিয়ে দিল ‘সানরাইজ’-এর।
চা নিয়ে বসে মৈনাককে বলল— আচ্ছা, ছুটির দিনে আবার নার্সিং হোমে যাব কেন? তোমার ইচ্ছে হলে সানডে-তে ঘুরে আসতে পারো। শনিবার হবে না। সুস্মিতার মেয়ের ব্রাইডাল শাওয়ারে যেতে হবে।
— ইচ্ছে-অনিচ্ছের কথা নয়। মানুষটাকে দেখতে যাওয়া আমাদের কর্তব্য। তুমিই বলো উনি বিকেলের দিকে একটু লোকজন আশা করেন।
— রঞ্জনারা তো যাচ্ছে। উইক ডে-তেও চেনাশোনা কয়েকজন দেখে গেছে। সেমি প্রাইভেট রুমে একজন স্ট্রোকের পেশেন্ট আছে। তার কাছে বাড়ির লোকজন আসে। সেই জন্যে বলছিলাম এক সঙ্গে ভিড় না করে অন্যদিন যেতে পারো।

আর কথা বাড়ায় না মৈনাক। যুক্তি আছে অপালার কথায় । প্রসঙ্গ বদল করে চলে যায় রাজনীতিতে। সামনে আমেরিকার প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশন। রিপাবলিক্যান আর ডেমোক্র্যাটিক দলের প্রার্থীদের প্রবল তর্কযুদ্ধ আর মিডিয়ার ঘন ঘন বিশ্লেষণ শোনার জন্য ফ্যামিলি রুমে টিভি খোলে। একসময় রান্নাঘরে ডাক পড়লে, খাবার টেবিলে দু’গেলাস জল দেয়। খেতে বসে মৈনাক জিজ্ঞেস করে— রঞ্জনাদের যে আসতে বললে, রান্না টান্না করবে কখন? শুক্রবার তোমার নাইট শিফট না? ফিরবে তো সেই শনিবার সকালে। ওদের নিয়ে বাইরে খেতে গেলে হয়।
— দরকার নেই। ওরা অত দূর থেকে আসবে। সানরাইজ থেকে এখানে এসে একটু রিল্যাক্স করতে পারবে। কাল দীপা’স কিচেনে ফোন করে রান্নার অর্ডার দিয়ে রাখব।
মৈনাক খেতে খেতে মুখ তুলল — আবার সেই বাংলাদেশি মাছ?
অপালা মাথা নাড়ল— না, না। চিংড়ি মাছ। নিজেই করে নেবো। বাকি রান্নাগুলো ওখান থেকে নিয়ে আসব। একটু ঘরোয়া আড্ডা আর খাওয়া-দাওয়া, এই তো ব্যাপার।
খাওয়ার পর ডিশ ওয়াশারে বাসন রাখতে রাখতে মৈনাকের খেয়াল হল অলির মেসেজ করেছিল। অপালাকে সে কথা বলতে ও অ্যাটলান্টায় মেয়েকে ফোন করল। দু’জনের কথাবার্তা শুনতে শুনতে মৈনাক আবার ফ্যামিলি রুমে ভোটের ডিবেটে মন দেয়।
দোতলায় যাওয়ার আগে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে অপালা বলল— অনি জুনের মিডলে নিউইয়র্কে মেডিকেল কনফারেন্সে আসবে। ফাদার্স ডে উইক এন্ডে থাকতে পারবে বোধহয়।
মৈনাক খুশি হল— ওরা সবাই আসবে নাকি? ওখানে তো সামার ভেকেশন আগে হয়।
— মনে হল চারজনই আসবে। অনি কনফার্ম করলে ওই সপ্তাহটা ছুটি নেব। রোগী সেবা বন্ধ করে ওমি, শমীদের নিয়ে সময় কাটাবো।
অপালা শুতে যাওয়ার পর মৈনাকও আর বেশিক্ষণ টিভি দেখল না। অনিরা আসবে জেনে মনটা ভাল লাগছে। ওরা অ্যাটলান্টা চলে যাওয়ার পর থেকে আগের মতো আর দেখা হয় না। অনি কলেজ পাস করে ডাক্তারি পড়ল নিউইয়র্কে। রেসিডেন্সিও করল নিউইয়র্কে মাউন্ট সাইনাই হাসপাতালে। বিয়ের পর সঞ্জয়ের সঙ্গে চলে গেল অ্যাটলান্টায়। মৈনাক আশা করেছিল, ওরা দুজন এদিকেই কোথাও প্র্যাকটিস শুরু করবে। হয়তো ওয়াশিংটন বা বস্টনে থাকবে। কিন্তু অনি মেডিকেল প্র্যাকটিসের ধারে কাছেও গেল না। ইনফেকশাস ডিজিজ-এ স্পেশালটি করে অ্যাটলান্টায় ‘সেন্টার ফর ডিসিস কন্ট্রোল’-এ রিসার্চে ভাল চাকরি পেয়ে চলে গেল। সঞ্জয় ইন্টারন্যাল মেডিসিনের ডাক্তার। ওখানেই প্র্যাকটিস শুরু করল। আর এদিকে ফেরার প্রশ্নই নেই।
ফাদার্স-ডে ভাবলে অনির ছোটবেলাটা মনে পড়ে। সাদা কাগজে ক্রেয়ন দিয়ে হিজিবিজি ছবি এঁকে কার্ড দিত। চা, কফি করতে দেওয়া হত না বলে, ওইদিন সাত সকালে উঠে ছোট একটা ট্রে নিয়ে ঘরে আসত। তার ওপর এক গ্লাস অরেঞ্জ জুস, ক’টা বিস্কুট আর কাপ কেক। মেয়েকে আদর করে ঘুমচোখে মৈনাক কনকনে ঠাণ্ডা অরেঞ্জ জুস আর বিস্কুট খেত। গোলাপি স্লিপিং পায়জামা পরা রোগা মেয়েটা কচি হাতে কাপ কেক নিয়ে বলত— প্রিটেন্ড করো তুমি কফি খাচ্ছো বাবা।আজ সেই সব পুরনো দিনের কথা ভাবতে ভাবতে মৈনাকের চোখে ঘুম এসে গেল।

সকালে সূর্য ওঠার পর, সানরাইজ’-এর হলওয়েতে ব্যস্ততার সাড়াশব্দ পাওয়া গেলেও দরকার ছাড়া রোগিদের ঘরে তখনও কেউ ঢোকে না। তন্দ্রাচ্ছন্ন অভিজিৎকে জাগিয়ে দিয়ে গত রাতের নার্স মেলিসা পেপার কাপে কফি রেখে যায়। এখানে ঘুম ভাঙলে কফি পাওয়া যায় না। আটটা সাড়েআটটা নাগাদ ঘরে ব্রেকফাস্টের ট্রে আসে। সেই সঙ্গে কফি নয়তো চা। ঘুম ভেঙে কফি পান না বলে অভিজিৎ সকালের ওই ব্যবস্থাটা করিয়েছেন অপালাকে দিয়ে। প্রথম দিকে নিজেই চেষ্টা করতেন। হলওয়ে দিয়ে হেঁটে যাওয়া ভলান্টিয়ার মেয়েগুলোকে হ্যালো হ্যালো বলে ডাকতেন। কেউ সাড়া দিত। মাইক্রোওয়েভে কফি করেও আনত। বাকিরা সেই যে গেল, আর পাত্তা নেই। অপালা বলে রাখলেও সব নার্সদের খেয়াল থাকে না। তারা তখন রোগিদের সকালের পরিচর্যায় ব্যস্ত। কেউ নার্সেস স্টেশনে ফোন কানে নিয়ে বসে আছে, কেউ এক মনে কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে, বাকি দু-চারজন কম্পিউটার বসানো ওষুধের ট্রলি ঠেলে ঠেলে একেক ঘরে ঢুকছে আর বেরনোর নাম নেই। মাঝখান থেকে জ্বালাতন করে জ্বর আর ব্লাড প্রেশার নেওয়ার মেয়েগুলো। অভিজিৎ লক্ষ্য করেছেন এদের মধ্যে হাঁদা টাইপের দু-একটা আছে। উল্টোপাল্টা প্রেশার মাপে। জ্বর নিবি তো দু-দণ্ড ধৈর্য ধর। কানে থার্মোমিটার ঢুকিয়েই বার করে নিয়ে কাগজে ছাইভস্ম কী যেন লেখে। একদিন অভিজিৎ জেরা করে জানলেন তাঁর টেম্পারেচর পঁচানব্বই। অথচ নিজের রীতিমতো জ্বর জ্বর লাগছিল। নার্সকে ডেকে নালিশ করার পরেও জ্বর ধরা পড়েনি। অপালাও যেন এসব কথার গুরুত্ব দেয় না। যা হোক, তবু ঘুম ভেঙে গরম কফিটা পাওয়া যাচ্ছে। অভিজিৎ তাই সকালের দিকে বেশি ডাকাডাকি করতে চান না কাউকে। ঘরে আর একজন রোগী আছে। সেটাও কনসিডার করা উচিৎ।
আজ রবিবার। সারাদিন ধরে ঘরে ঘরে ভিজিটর আসছে। ছুটির দিনে সব থেরাপিস্ট আসে না। দু’শো দশ নম্বরের অন্য রোগির স্ট্রোকের পরে কয়েক রকম থেরাপি চলছে। স্পিচ থেরাপি করতে করতে কথা অনেকটা স্পষ্ট হয়েছে। তার বিছানার চারপাশে আজ নাতি-নাতনি, ছেলের বউ বসে আছে। মাঝে মাঝে দুই মেয়ে আসে। অভিজিতের ধারণা এরকম রোগিকে লোকজন রেখে নিশ্চয়ই বাড়িতে রাখা যায়। আসলে বুড়োর বউ মরে গেছে বলে কেউ আর দায়িত্ব নেবে না। স্ট্রোক হওয়ার পরে হাসপাতাল থেকেই লং-টার্ম কেয়ার সেন্টারে পাঠিয়েছিল। বুড়োর যেন সে জন্যে কোনও দুঃখও নেই। অভিজিৎকে বলে— ওরা খুব কেয়ারিং। আমাকে অনেক দেখাশোনা করেছে। বাট দে হ্যাভ আদার থিংগস টু ডু। আমার এই বয়সে লং-টার্ম কেয়ারে চলে আসাই ঠিক ডিসিশন হয়েছে।

হতে পারে। মার্ক নামে আমেরিকান লোকটির বয়স বোধহয় আশির ওপরে। তাঁর পক্ষে এখানে থাকার যুক্তি আছে। কিন্তু অভিজিতের জন্যে এ ডিসিশন কে নিল? স্টম্যাক ক্যানসার চিকিৎসা শেষ হওয়ার পরে দুটো বছর তো ভালই ছিলেন। একা বাড়িতে নিজেই বাজারহাট, রান্নাবান্না করতেন। উইকএন্ডে গাড়ি চালিয়ে বাঙালির আড্ডায় নেমন্তন্ন খেতে যেতেন। সেখান থেকে কৌটো করে খাবার নিয়ে ফিরতেন। ক্লাবের ছেলেমেয়েরা দুর্গাপুজো, পিকনিক কোথাও ওঁর কাছ থেকে চাঁদা নিত না। সিনিয়র মেম্বার বলে খাতির যত্ন করত। যে মানুষ প্রায় চিরকালই একা, সত্তর বছরে পৌঁছে সে তুলনায় খারাপ তো কিছু ছিলেন না। অথচ চেনাশোনারা অভিজিৎকে প্রায় একঘরে করে দিল! তাছাড়া কী! না হলে, একটা ছুতো করে দল বেঁধে মিটিং ডেকে সানরাইজ-এ পাঠানোর ব্যবস্থা করে কেউ? তিনিও মেনে নেওয়ার লোক নন। পিঠের ব্যথাটা একটু কমলেই এখানকার কেস ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলবেন। রোগির ইচ্ছের বিরুদ্ধে কেউ জোর ফলাতে পারবে না। গাড়ি চালাতে না পারলেও ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারবেন।
দুটো বেডের মাঝখানে পর্দা টানা রয়েছে। দরজার কাছে প্রথম বেডের রোগি অবেলায় আধো ঘুমে। লো ভলিউমে দেওয়ালের টিভি চলছে। এক মহিলা চেয়ারে বসে ম্যাগাজিন পড়ছেন। রঞ্জনাদের দেখে সামান্য হেসে ‘হাই’ বলে পর্দার ওপাশের দিকে দেখালেন।
অভিজিৎ জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। রঞ্জনা চেয়ার টেনে বসা মাত্র ঘরের সব আলো জ্বালিয়ে একটি হিসপ্যানিক মেয়ে এসে ঢুকল। টেবিলে জলভর্তি প্লাস্টিকের জাগ আর ফোমের গ্লাস রেখে, পুরনো জাগ ফেরত নিয়ে গেল। ততক্ষণে অভিজিতের ঘুম ভেঙে গেছে। রঞ্জনা আর সুব্রতকে দেখে উঠে বসার চেষ্টা করতে করতে বললেন— তোমরা অত দূর থেকে এলে? হোয়াট আ প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ।
সুব্রত কাছে এসে অভিজিতের হাত ধরে। —কেমন আছেন অভিজিৎদা? এখন হাঁটাচলা করতে পারছেন? আমরা তো প্রথমে খবরই পাইনি…
বালিশে হেলান দিয়ে বসেছেন অভিজিৎ। —দ্যাটস ওকে, কে আর কাকে খবর দেবে? এখন ভালই আছি। ব্যাক পেইন থাকলেও ওষুধ আর ফিজিওথেরাপিতে কাজ হচ্ছে। তুমি কেমন আছো রঞ্জনা,? তোমার কী একটা বই সিনেমা হবে শুনেছিলাম।
রঞ্জনা হাসল— এত কিছুর মধ্যে আপনার সেটাও মনে আছে? হ্যাঁ, ছবিটা হওয়ার কথা। তবে শুটিং কবে শুরু হবে জানি না।

সুযোগ পেয়ে রসিকতা করেন অভিজিৎ —মুভিটা হলে ও যে কী দাঁড়াবে, সে তুমি জানো না। দেখলাম তো, কলকাতার ডিরেক্টররা ইমিগ্র্যান্টদের জীবন নিয়ে ছবিই করতে পারে না।
মাঝখান থেকে ফুট কাটে সুব্রত —স্টোরিগুলো আসলে আমাদের সম্পর্কে কিছু ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে লেখা। ওই যে আমরা সবাই ডিপ্রেশনে ভুগছি। ছেলেমেয়েগুলো ড্রাগ খেয়ে উচ্ছন্নে গেছে। কোন মুভিটাতে যেন দেখলাম, আমেরিকার বাঙালিদের ঘরে ঘরে বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে। শেষে, দুঃখী টাইপের একটা লোক কাঁধে ঝোলা নিয়ে দেশে ফিরে গেল।
অভিজিৎ সুব্রতর এই রসিকতাটা উপভোগ করলেন না। কেমন অন্যমনস্ক দেখায় তাঁকে। খেয়াল করে প্রসঙ্গ বদল করে রঞ্জনা, —এখানে কতদিন থাকতে হবে, ডাক্তার কিছু বলছে? এখন তো রিহ্যাবের জন্যেই আছেন?”
—এখানে কয়েকটা উইং আছে। যারা মেজর সার্জারি বা স্ট্রোকের পরে রিহ্যাবিলিটেশনের জন্যে আসে, তারা মোস্টলি অন্য ফ্লোরে থাকে। দু-এক মাসের মধ্যে চলেও যায়। আমারও সেই কেস। কিন্তু তখন রুম খালি ছিল না বলে এই ফ্লোরে লং-টার্ম কেয়ার ইউনিটে নিয়ে এল। দেখি, কবে রিলিজ করে।
কিন্তু বাড়িতে একা থাকবেন কী করে? বাথরুমে পড়ে গিয়ে পিঠে ফ্র্যাকচার হল। সারারাত উঠে বসতে পারলেন না। সময়মতো পাড়ার লোকের ফোন পেয়ে পুলিশ যদি না যেত… —সুব্রত বোঝানোর চেষ্টা করল।
—কী আবার হত? মরে পড়ে থাকতাম। যার যেমন ডেস্টিনি। তাই বলে এখানেই থেকে যাব? এখনও অতটাও অক্ষম হয়ে যাইনি সুব্রত। – সপাট উত্তর দেন অভিজিৎ।
রঞ্জনা ঈশারা করতে থেমে গেল সুব্রত। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। এটা ঠিক যে, ওঁকে কেউ জোর করে এখানে রাখতে পারবে না। আবার হেঁটে-চলে বেড়াতে পারলে হয়তো বাড়িতেই ভিজিটিং নার্স-টার্স রেখে কিছুদিন ম্যানেজ করতে পারবেন। হেলথ ইনসিওরেন্স থাকলেও খরচ অনেক বেশি হবে। দ্যাট উইল বি হিজ ডিসিশন।
সুব্রতকে নিচের ক্যাফেটেরিয়া থেকে কফি আনতে পাঠালো রঞ্জনা। এখানে এসে পৌঁছতে প্রায় দেড় ঘণ্টা লেগেছে। আবার অপালাদের বাড়ি গিয়ে তারপর লং আয়ল্যান্ডে ফেরা, অনেক রাত হয়ে যাবে। তাও আসতে পেরে ভাল লাগছে। ও জিজ্ঞেস করল— আপনাদের ডিনার দেয় কখন?
— এই তো, সাড়ে পাঁচটা নাগাদ দিয়ে যাবে। সকালে মেনু বুক থেকে অর্ডার করে দিই। খাবার ভালই। কয়েকরকম চয়েস থাকে। আমার কোনও রেসট্রিকশনও নেই। ডেসার্টে আইসক্রিম, পুডিং সব খাই। হাসতে হাসতে দরজার দিকে তাকান অভিজিৎ।
অভিজিতের ডিনার খাওয়া শেষ হওয়ার পরে আর দেরি করতে চাইছিল না রঞ্জনারা। মাঝে অপালাদের ফোন এসেছে। ওরা অপেক্ষা করে আছে। বাইরে অন্ধকার হয়ে আসছে। অভিজিৎ চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন। সাদা চাদরে ঢাকা তাঁর দুটো হাঁটুর ওপর হাত রেখে সুব্রত বলল— আজ তাহলে চলি অভিজিৎদা? আপনি এবার রেস্ট করুন। গেট ওয়েল সুন।
পর্দার ওপারে চেয়ার টানার শব্দ হল। পাশের পেশেন্টের কাছে ভিজিটর এসেছে। মৃদু স্বরে কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। ক্লান্ত অবসন্ন দৃষ্টি মেলে অভিজিৎ জিজ্ঞেস করলেন — কেন, আর কেউ এসেছে? তোমরা উঠছো কেন? এপাশে একটা চেয়ার টেনে নাও।
রঞ্জনা পেছন ফিরে কাউকে দেখতে পেল না। মনে হল অভিজিৎদা আরও কাউকে আশা করছেন। আজ রবিবার, ছুটির দিন। অথচ চেনাশোনা কেউ ওঁকে দেখতে আসেনি। হয়েতা অনেকেই এর মধ্যে ঘুরে গেছে। ওদেরই আসতে দেরি হল।
হঠাৎ অভিজিৎ বললেন— আই মাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড। লোকে আর কতবার দেখতে আসবে বলো? সবাই তো খোঁজখবর নিচ্ছে।
আরও কিছুক্ষণ বসে থেকে রঞ্জনা বলে —কাছাকাছি থাকলে আগেই আসতে পারতাম। আপনি ভাল হয়ে উঠুন। ফোনে খবর নেবো।
অভিজিৎ সামান্য হেসে হাত তুললেন —সাবধানে ড্রাইভ কোরো। থ্যাংক ইউ ফর কামিং। গুড নাইট।

সানরাইজ থেকে ওয়েল্ট মিলফোর্ডে মৈনাকদের বাড়ি যাওয়ার পথে বৃষ্টি নামল। এবছর শীত গেছে দেরি করে। বসন্ত এল দমকা হাওয়ার সঙ্গে ঝিরঝিরে বৃষ্টি নিয়ে। সকালের উজ্জ্বল আলো আড়াল করে হঠাৎ হঠাৎ মেঘ ঘনিয়ে আসে। কয়েক পশলা বৃষ্টির পর মেঘ ভাঙা ঝলমলে রোদ উঠেছে। আজ সারাদিন বসন্তের এলোমেলো হাওয়া ছিল, রোদ ছিল। সন্ধ্যের পরে বৃষ্টি শুরু হতে, অন্ধকারে অচেনা শহর থেকে মৈনাকদের বাড়ি পৌঁছতে বার দুয়েক রাস্তা হারাল সুব্রত। পথের সাথী ‘জিপিএস’-এর যান্ত্রিক মহিলা কণ্ঠ -এগিয়ে যাও, ঘুরিয়ে নাও, ডানদিকে, বাঁ-দিক, বলতে বলতে যখন ওদের অপালাদের বাড়ির সামনে নিয়ে গেল, রাত তখন প্রায় আটটা।
অসময়ের বৃষ্টি, গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে দু-এক কথার পর মৈনাক, অভিজিতের আজকের খবর নিল। কথাবার্তার মাঝে কিচেন থেকে ড্রিংক নিয়ে এল। অপালা খাবার ঘরে ডিনার সাজাচ্ছিল। রঞ্জনা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল —আপনারা তো ওঁকে অনেকদিন থেকে চেনেন। ওঁর বউকে দেখেছিলেন? সত্যিই কি ভদ্রলোক পঞ্চাশ বছর দেশে যাননি?”
অপালা হাসল —কোন উত্তরটা আগে চাও? বউ-এর খবর? সে তো বহুদিন আগে চলে গেছে। আমরা যে বছর প্রথম নিউ জার্সিতে এসেছিলাম, তখন কজনই বা বাঙালি ছিল। মৈনাক কয়েক মাস আগে এসেছিল বলে কোনও বাড়িতে অভিজিৎদা আর ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। আমি আসার পরে একদিন ওঁদের বাড়ি গেলাম। সত্যি বলতে কী আমেরিকা সম্পর্কে প্রায় মোহভঙ্গ হওয়ার যোগাড়! যেমন বাজে শহর, তেমন পুরনো অ্যাপার্টমেন্ট। অথচ অভিজিৎদা কিন্তু তার ক’বছর আগেই টরন্টো থেকে এসে সেটল করেছেন। সেদিক থেকে সদ্য আসা স্টুডেন্ট বা নতুন ইমিগ্র্যান্টদের মতো ওঁর স্ট্রাগলিং পিরিয়ড চলছিল না। চাকরিও মোটামুটি ভালই করতেন।”
ফাদার্স-ডে ভাবলে অনির ছোটবেলাটা মনে পড়ে। সাদা কাগজে ক্রেয়ন দিয়ে হিজিবিজি ছবি এঁকে কার্ড দিত। চা, কফি করতে দেওয়া হত না বলে, ওইদিন সাত সকালে উঠে ছোট একটা ট্রে নিয়ে ঘরে আসত। তার ওপর এক গ্লাস অরেঞ্জ জুস, ক’টা বিস্কুট আর কাপ কেক। মেয়েকে আদর করে ঘুমচোখে মৈনাক কনকনে ঠাণ্ডা অরেঞ্জ জুস আর বিস্কুট খেত। গোলাপি স্লিপিং পায়জামা পরা রোগা মেয়েটা কচি হাতে কাপ কেক নিয়ে বলত— প্রিটেন্ড করো তুমি কফি খাচ্ছো বাবা।
—সত্যি! এত কৃপণ ভাবা যায় না। তবে দেশে হয়তো অনেক টাকা পাঠাতে হত। কিন্তু ওঁর বউ চাকরি করত না?
— মাধবী খুব বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে কাজ করত। তবে ওর পে-চেক বোধহয় নিজের শখ-সাধ মেটাতেই খরচ হয়ে যেত। ওই ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে নিজের টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্টে কসটিউম জুয়েলারি, জামাকাপড়, ডিজাইনার ‘ব্যাগ’-ট্যাগ কিনতো। রাণাঘাটে ওর বাপের বাড়িতেও সাহায্য করত। অভিজিৎদা সে ব্যাপারে হয়তো ইন্টারফেয়ার করতেন না। কিন্তু হাই-ক্রাইম এরিয়ায় ব্ল্যাক নেবারহুডে থেকে, সাতকেলে পুরনো গাড়ি চড়ে ক’টা মেয়ে মানিয়ে নিতে রাজি হবে?”
রঞ্জনা সায় দিল —আমি তো পারতাম না। দেশেই কখনও ওভাবে থাকিনি। এখানে মোটামুটি একটা বেসিক স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করার ক্ষমতা নিশ্চয়ই ওঁদের ছিল, যদি না দেশে অনেক লায়াবিলিটি থাকে…
— সে চাপ কার ছিল না? আমাদের হাসবেন্ডরা তো সব সোনার ডিম পাড়া হাঁস। আত্মীয়-স্বজনের নীড, এক্সপেকটেশন, ডিম্যান্ড মেটাতে গিয়ে এখানে নিজেদের সংসারে এক সময় প্রায়রিটি বুঝে চলতে হয়েছে। তা বলে ভালভাবে থাকব না? এক-দু’বছর অন্তর দেশে যাব না? অপালা রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে পড়ে।
লিভিং রুম থেকে মৈনাকের গলা পাওয়া গেল— কী হল? এবার খেতে দিয়ে দাও। ওদের তো ফিরতে হবে।
ডিনার খেতে বসে মৈনাক বলল—একটু আগে অভিজিৎদার টেক্সট ম্যাসেজ এসেছে। আমার সঙ্গে ওঁর কিছু ডিসকাস করার আছে।
অপালা অবাক— এখনও জেগে আছেন? কী আবার ডিসকাস করবেন?
— সেটা গিয়ে শুনব। কাল অফিস ফেরত দেখা করে আসব।
ক্রমশ
্ছবি সৌজন্য: Forbes, shutterstock, insider
দীর্ঘকাল আমেরিকা-প্রবাসী আলোলিকা মুখোপাধ্যায়ের লেখালিখির সূচনা কলকাতার কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্বে। আমেরিকার নিউ জার্সির প্রথম বাংলা পত্রিকা "কল্লোল" সম্পাদনা করেছেন দশ বছর। গত আঠাশ বছর (১৯৯১ - ২০১৮) ধরে সাপ্তাহিক বর্তমান-এ "প্রবাসের চিঠি" কলাম লিখেছেন। প্রকাশিত গল্পসংকলনগুলির নাম 'পরবাস' এই জীবনের সত্য' ও 'মেঘবালিকার জন্য'। অন্য়ান্য় প্রকাশিত বই 'আরোহন', 'পরবাস', 'দেশান্তরের স্বজন'। বাংলা সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের জন্য নিউইয়র্কের বঙ্গ সংস্কৃতি সঙ্ঘ থেকে ডিস্টিংগুইশড সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন।