“The point is not for women simply to take power out of men’s hands, since that wouldn’t change anything about the world. It’s a question precisely of destroying that notion of power.”
[Simone de Beauvoir/ The Second Sex]
আজ ভাইদ্বিতীয়া। দুই বাংলা ও অসম-ত্রিপুরায় যা ভাইফোঁটা, বিহারে তা-ই ভরদুতিয়া, দেশের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে তা ভাইদুজ, নেপাল ও পার্বত্যে ভাইটিকা, কর্ণাটক ও দক্ষিণভাগের বিভিন্ন জেলায় ভাউবিজ, যমদ্বিতীয়া। কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে ভাইকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই যে দেশ জোড়া উদযাপন, তা কেবলমাত্র হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত। অস্বীকারের উপায় নেই যে, এটি একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান যা পুরুষজন্মকে মহিমান্বিত করে। সংজ্ঞা ও সূর্যদেবের তিন পুত্রকন্যা মনু, যম আর যমুনার গল্প প্রায় সকলেরই জানা। সর্বানন্দসুরী রচিত দীপোৎসবকল্প-এর নন্দীবর্ধন ও তাঁর বোন অনসূয়ার গল্পও বহু প্রচলিত। কিন্তু এ সকলই কাহিনি, ইতিহাস নয়। ফলে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার প্রচলন ঠিক কবে আরম্ভ হয়েছিল, তা নিয়ে বিতর্ক থেকেই যায়।
যা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই, তা হল, এই উৎসবের কারণ বা ভিত্তি। যমের ভ্রাতা মনু তাঁর সংহিতায় বলে গেছেন, মেয়েরা বিভিন্ন বয়সে যথাক্রমে পিতা, ভ্রাতা ও স্বামীর অধীন। অতএব বলা বাহুল্য, এই তিন প্রকার পুরুষের মঙ্গল কামনাও নারীর অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। তারা আলপনা এঁকে ভাইকে মাঝখানে বসিয়ে তার কপালে তিলক পরাবে, তারাই দিনভর না খেয়ে চালুনির মধ্যে দিয়ে চাঁদ দেখে স্বামীর পুজো করবে, শতাব্দীর পর শতাব্দী এসব চলে আসছে। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, যা চলছে, যেভাবে চলছে, তা চলবে কি? চলবে কেন?
কুমারী ব্রত, সধবা ব্রত: মেয়েদের আচারবিচার
পুণ্যিপুকুর পুষ্পমালা
কে পূজেরে দুপুর বেলা?
আমি সতী লীলাবতী
সাত ভা‘য়ের বোন ভাগ্যবতী।।
এ পূজলে কী হয়?
নির্ধনের ধন হয়।।
সাবিত্রী–সমান হয়।
স্বামী আদরিণী হয়।।
পুত্র দিয়ে স্বামীর কোলে।
মরণ যেন হয় গঙ্গাজলে।।
আশুতোষ মজুমদার প্রণীত ‘মেয়েদের ব্রতকথা’ বইটি ঘাঁটলে দেখা যাবে, পাঁচ বছর বয়স থেকেই মেয়েদের নানাবিধ ব্রতের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রথা বাংলার ঘরে ঘরে প্রচলিত ছিল। এই ব্রতগুলির মূল উপজীব্য চারটি: ১) ভাই (বা দাদার) দীর্ঘায়ু ও সাফল্য কামনা ২) ভাল স্বামীর জন্য প্রার্থনা ৩) সতীনের অমঙ্গল কামনা ৪) পুত্রসন্তানের জন্য প্রার্থনা। অর্থাৎ ওপরে পুণ্যিপুকুর ব্রতের যে ছড়াটি উল্লেখ করা হল, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্ন ব্রতের মাধ্যমে একটি শিশুকন্যার মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দেওয়া হত সেসবই।
দশপুতুল ব্রতের কথাতেই আসা যাক। চৈত্র সংক্রান্তি থেকে গোটা বৈশাখ মাস জুড়ে ভোরবেলা উঠে একটি বাচ্চা মেয়ে পিটুলি দিয়ে দশটি পুতুল আঁকবে। এবং পুজোর মন্ত্রে বলবে, যেন সে রামের মতো স্বামী, লক্ষ্মণের মতো দেওর, কৌশল্যার মতো শাশুড়ি ইত্যাদি পায়। শিশুকাল থেকে মেয়েদের বুঝিয়ে দেওয়া হত, এই নারীজন্ম বিবাহ ও বিবাহোত্তর জীবনের জন্য উৎসর্গীকৃত।
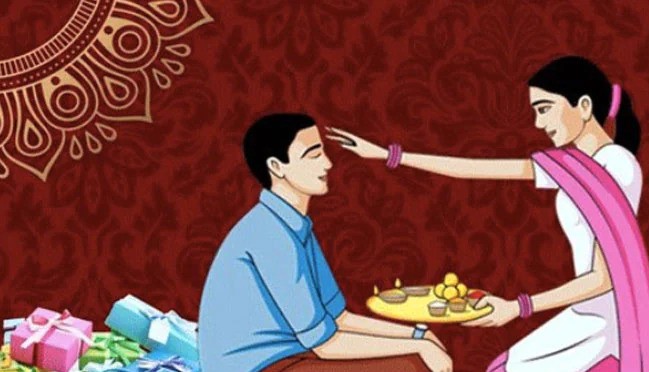
দক্ষিণারঞ্জনের ‘ঠাকুরমার ঝুলি’ থেকে সাত ভাই চম্পা ও এক পারুল বোনের গল্প জানা যায়। রাজামশাই দ্বারা প্রত্যাখ্যাত সপ্তম স্ত্রী অর্থাৎ চম্পা-পারুলদের মায়ের ও সেই সাত সন্তানদের প্রতি যে অন্যায় আচরণ হয়েছিল, এ গল্পকে তার বিরুদ্ধে এক পেলব প্রতিবাদ বলা যেতে পারে। মাটিতে পুঁতে দেওয়া বাচ্চারা একদিন ফুল হয়ে ফুটে ওঠে, বনবাসী মায়ের স্পর্শে তারা আবার মানুষের রূপ নেয়। কিন্তু ভুললে চলবে না, রাজার প্রথম ছয় রানির প্রতি অসন্তোষের মূল কারণ ছিল তাদের সন্তানহীনতা। গল্পের শেষে প্রথম ছয় রানির ষড়যন্ত্র টের পেয়ে রাজা তাদের হত্যার আদেশ দেয়। কোথাও কি এই মর্মার্থও নিহিত নেই যে, সন্তান ধারণ করতে না পারলে মেয়েরা সামাজিকভাবে ব্রাত্য, এবং উপেক্ষাই তার একমাত্র নিয়তি?
গোকুল ব্রতের মন্ত্রে লেখা আছে:
তোমাকে ঘুরায়ে পাখা
আমার হক সোনার শাঁখা
তোমাকে বাতাস করি
সতীন মেরে ঘর করি।
এই একই কথা ফিরে ফিরে আসছে কুমারী ও সধবার নানাবিধ ব্রতে। সেঁজুতি ব্রতে বলা হচ্ছে : সাত সতীনকে পুড়িয়ে মারি, কিংবা, সতীন কেটে আলতা পরি। প্রতিশোধস্পৃহা ও তজ্জনিত নৃশংসতার ইঙ্গিত ব্রতগুলির মধ্যে বিরল নয়। যতদিন বাঙালি সমাজে বৈবাহিক আইন ফলপ্রসূ হয়নি, ততদিন পর্যন্ত পুরুষদের একাধিক বিবাহ খুবই প্রচলিত ব্যাপার ছিল। অনেকে সাড়ম্বরে বিয়ে না করলেও, সঙ্গিনী রেখে দিত অন্য বাড়িতে, অন্য গ্রামে। ফলত প্রথম সঙ্গিনীর প্রতি মনোযোগ ও নির্ধারিত টাকাকড়ির উভয় ক্ষেত্রেই ঘাটতি দেখা দিত। লোকাচারের মধ্যে দিয়ে একটি মেয়েকে শৈশব থেকেই পরিচিত করা হত এ জাতীয় ‘পুরুষোচিত’ আচরণের সঙ্গে।
দশপুতুল ব্রতের কথাতেই আসা যাক। চৈত্র সংক্রান্তি থেকে গোটা বৈশাখ মাস জুড়ে ভোরবেলা উঠে একটি বাচ্চা মেয়ে পিটুলি দিয়ে দশটি পুতুল আঁকবে। এবং পুজোর মন্ত্রে বলবে, যেন সে রামের মতো স্বামী, লক্ষ্মণের মতো দেওর, কৌশল্যার মতো শাশুড়ি ইত্যাদি পায়। শিশুকাল থেকে মেয়েদের বুঝিয়ে দেওয়া হত, এই নারীজন্ম বিবাহ ও বিবাহোত্তর জীবনের জন্য উৎসর্গীকৃত।
অধিকাংশ ব্রতকথাতেই একটি বাক্যাংশ ছিল বহুব্যবহৃত: সাত ভাইয়ের বোন। পুণ্যিপুকুর থেকে শুরু করে অশ্বত্থ পাতা, যমপুকুর থেকে তুষতুলসী, সর্বত্র নিজেকে সাত ভাইয়ের বোন হিসাবে দেখার আকাঙ্ক্ষা এবং ভাইয়ের মঙ্গল কামনার কথা থাকতই। সম্ভবত, শিশুকন্যার মুখ দিয়ে প্রার্থনা করিয়ে সংসারে পুত্রসন্তানের সংখ্যা বাড়ানোর অভিপ্রায়। কেননা, পুত্রই উপার্জন করবে, সে-ই দায়িত্ব নেবে বৃদ্ধ মাতাপিতার, অবিবাহিত বোনকে রক্ষা করবে প্রতিকূলতা থেকে, তার বিয়ে দেবে, নিজে বিয়ে করে ও আরও পুত্রের জন্ম দিয়ে বংশরক্ষা করবে। এবং অনাকাঙ্ক্ষিত হলেও সত্য যে, বোনটি কোনও কারণে সংসার করতে না পারলে ‘স্বামীর ঘর’ ছেড়ে এসে ভাই বা দাদার ঘরেই উঠবে, যে ভাই বা দাদা তার আর তার সন্তানদের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করবে। গত শতকের শেষ দশকেও দেখা গেছে, বিবাহবিচ্ছিন্না মেয়ে দাদার গলগ্রহ হতে না চাওয়ায়, বিচ্ছেদের পর আত্মহত্যা করেছে।
ভাই ও বাবার সাফল্য কামনায় নির্মিত অগণিত ছড়ার ছররা দেখতে দেখতে মনে পড়ে যায় ১৯৩১-এ জন্মানো প্রথা ভাঙা এক কবির গুটিকয় পংক্তি:
“…জন্ম থেকেই যে জ্যোতিষীর ছকে বন্দী
যার লগ্ন রাশি রাহু কেতুর
দিশা খোঁজা হয়েছে, না, তার নিজের জন্য নয়
তার পিতার জন্য, তার ভাইয়ের জন্য
তার স্বামীর জন্য, তার পুত্রের জন্য
কিন্তু যার গর্ভ থেকে আমার জন্ম
সেই মায়ের কথা বলেনি কেউ।“
[কবিতা সিংহ/ আমি সেই মেয়ে]
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যমপুকুর ব্রতে একদা পড়া হত, ‘আমার বাপ-ভাই হোক লক্ষেশ্বর’। পরবর্তীতে প্রথম পংক্তির শুদ্ধিকরণ ঘটে। সেখানে লেখা হয়, ‘এই ঘটিটি জল ঢালি বাপ মার’, অর্থাৎ মায়ের নামও সংযুক্ত হয়। যদিও সে ছড়াও শেষ হয় নিজেকে সাত ভাইয়ের বোন হিসাবে দেখার আকাঙ্ক্ষায়।
জামাইষষ্ঠী ব্রতটিও পুরুষপ্রধান সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে। প্রাচীন রীতি অনুযায়ী বিয়ের পর যতক্ষণ না মেয়েটি সন্তানসম্ভবা হচ্ছে, ততক্ষণ তার মাতাপিতার অধিকার থাকত না মেয়েকে দেখার। বহুক্ষেত্রে মেয়েটি গর্ভধারণে অপারগ হলে গোটা জীবনই তার সঙ্গে তার মাতাপিতার সাক্ষাৎ হত না। সম্ভবত এর সুরাহা করতেই জ্যৈষ্ঠ মাসে পালিত হয় জামাইষষ্ঠী। মেয়েটি, স্বামী-সমেত ফি বচ্ছরে অন্তত একবার এই ব্রতের সুবাদে বাড়িতে আসার সুযোগ পেতে শুরু করে। উপরন্তু, মেয়েদের পরিবার যেহেতু বিশ্বাস করত, বিবাহিত মেয়ে মাত্রই স্বামীর অধীনস্থ, তাই ঊর্ধ্বতনকে তোয়াজ করে রাখাও ছিল আশু কর্তব্য। নইলে মেয়েটির প্রতি অন্যায় হওয়ার আশংকা প্রবল হত। তবে এতসব করেও যে মেয়েদের প্রতি অত্যাচার আটকানো যেত, যায়, এমনটা নয়। অনুষ্ঠানাদি কেবল বহিরঙ্গে বদলেছে। আর্থিকভাবে স্বচ্ছল শাশুড়িরা এখন আর নিজে হাতে রাঁধেন না, জামাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েকেও বিস্তর উপঢৌকন দেন।
অধিকাংশ ব্রতকথাতেই একটি বাক্যাংশ ছিল বহুব্যবহৃত: সাত ভাইয়ের বোন। পুণ্যিপুকুর থেকে শুরু করে অশ্বত্থ পাতা, যমপুকুর থেকে তুষতুলসী, সর্বত্র নিজেকে সাত ভাইয়ের বোন হিসাবে দেখার আকাঙ্ক্ষা এবং ভাইয়ের মঙ্গল কামনার কথা থাকতই। সম্ভবত, শিশুকন্যার মুখ দিয়ে প্রার্থনা করিয়ে সংসারে পুত্রসন্তানের সংখ্যা বাড়ানোর অভিপ্রায়।
তবু আশার কথা এই যে, গত শতাব্দীর পাঁচ-ছয়ের দশক থেকে এইসব ব্রতের জাঁকজমক ক্রমশ কমে এল। তার কারণ বোধ করি স্বাধীনতা ও দেশভাগোত্তর বাংলার অর্থনৈতিক টানাপোড়েন। ওপার থেকে আসা উদ্বাস্তু পরিবারের মেয়েরা অন্নসংস্থানের জন্য ঘরের বাইরে বেরিয়ে কাজ করতে শুরু করলেন। তার প্রভাব পড়ল এ বাংলার মেয়েদের যাপনে। অভিভাবকেরা বুঝলেন, টিকে থাকতে গেলে মেয়েদেরও দিতে হবে কর্মসংস্থানের অধিকার। তার জন্য চাই শিক্ষা। এ হেন নারীশিক্ষার সূচনা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালংকার-দের হাত ধরে ঘটলেও, বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষিত করার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তাদের ভাল বর এবং ভাল ঘরে বিয়ে হওয়া। তাকে আত্মনির্ভর করা অথবা তার আত্মপরিচয় মজবুত করে তোলা নয়। ছয়-সাতের দশক থেকে এই স্রোতের অভিমুখে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসতে লাগল।
অতএব শিশুকন্যাটিকে সাত সকালে ঘুম থেকে তুলে পিটুলি গোলার বদলে বই পড়তে বসানো হল। ভাই কিংবা দাদার সঙ্গে সঙ্গে তাকেও পাঠানো হল ভাল স্কুলে। বড় হয়ে সেও বৃদ্ধ মাতাপিতার দেখভাল করতে সক্ষম হতে পারে, এই আশায় তাকে স্নাতক, স্নাতকোত্তর পড়ানোর রেওয়াজ শুরু হল বাংলার ঘরে ঘরে। নতুন শতাব্দীর দ্বিতীয় অধ্যায়ে দাঁড়িয়ে বাংলার শহর-শহরতলিতে চাকরি করে তো বটেই, গ্রামেও মেয়েরা সেলাই শিখিয়ে, সবজি বেচে, পর্যাপ্ত রোজগার করে ছোট ভাইয়ের পড়ার খরচ জোগায়। তাহলে দ্বিতীয়ার প্রার্থনায় কেবল ভাইয়ের ক্ষেত্রেই যমদুয়ারে কাঁটা পড়বে কেন! দিদির আয়ুও কি অক্ষয় হবে না? শস্যশ্যামলা বসুন্ধরার মতো দিদিও কি সফল-সক্ষম হয়ে উঠবে না এই সুজলা-সুফলা নতুন যুগের বাংলায়?
বোন যেন হয় সোনার ভাঁটা
প্রবাসী তরুণ বাঙালি দম্পতির দুটি শিশুকন্যা। রাখির দিনে, দ্বিতীয়ার দিনে ফুটফুটে মেয়ে দুটি পরস্পরের হাতে সুদৃশ্য বন্ধন পরিয়ে দেয়, শিশির চন্দনের ফোঁটা এঁকে দেয় একে অন্যের কপালে। মুখবইয়ে ওদের ছবি দেখে প্রতীতি হয়, প্রচলিত ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার মন্ত্রকে ওই শিশু দুটি নিজেদের মতো ভেঙেগড়ে নিয়েছে। সবুজ কচিকাঁচারাই তো পারে আধমরাদের ঘা মেরে বাঁচাতে। দ্বিতীয়ার সকালে উপোস করে ওরা হয়ত পরস্পরকে বলে,
বোনের কপালে দিলাম ফোঁটা,
যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা।
যমুনা দিল বোনকে ফোঁটা
বোন যেন হয় সোনার ভাঁটা।
কিংবা ‘মেঘে ঢাকা তারা’-র নীচে অগণিত নীতাদের লড়াইয়ের সামনে নতজানু হয়ে তাদের আরোগ্য কামনায় ভাই শঙ্করেরা কখনও বলে উঠতে পারে:
যমের হাতে ফোঁটা খেয়ে যমুনা হোক অমর,
আমার হাতে ফোঁটা খেয়ে বোন হোক অমর।
সদ্য প্রচারিত একটি বিজ্ঞাপনে দেখা যায়, কিশোর ভাই মনের সুখে সিঙাড়া খাচ্ছে। হঠাৎ ক্যাশটাকা না থাকায় তার খাওয়া থমকে যায়। পাশ থেকে তার দিদি বলে, “তু মু চলা ছোটে, গুগল পে সব জগাহ চলতা হ্যায়।“ এক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যেতে পারে, গল্পে তার দিদিটি আর্থিকভাবে সক্ষম ও প্রযুক্তিগতভাবে আধুনিক। একদিকে হিরের বিজ্ঞাপনের যেমন বিবাহবার্ষিকীতে ঘরের বউকে বরটি আজও সারপ্রাইজ দিয়ে চলে কোটি টাকার হার পরিয়ে, অন্যদিকে তেমনই, এক দিদি তার ভাইয়ের খাবার বিল মেটায় অনলাইনে। মধ্য ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির মধ্যে এই লিঙ্গগত আধুনিকীকরণ অনেক বেশি স্পষ্ট। কারণ মূলত সেই, মধ্য-নিম্ন-বিত্তের সংসার প্রতিপালনের জন্য মহিলা ও পুরুষ উভয়কেই এই শতকে এসে সারভাইভালের জন্য পুরোদস্তুর কাজ করতে হয়। কিন্তু কারণ যাই হোক, মেয়েরা যে সর্বতোভাবেই সক্ষম হয়ে উঠছে, লিঙ্গসাম্যের নিরিখে এ আশাব্যঞ্জক ব্যাপার।
যে কোনও লোকাচার জন্ম নেয় সামাজিক তাগিদ থেকে। গবেষণা কিংবা আলোচনার স্বার্থে যতই বেদ-পুরাণের তথ্য উল্লিখিত হোক না কেন, তাকে দৈনন্দিন জীবনে অঙ্গীভূত করার পিছনে থেকে যায় সমকালের সুস্পষ্ট সামাজিক উদ্দেশ্য। সে সংস্কৃতজ্ঞ উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের ভক্তি আন্দোলন হোক, অথবা স্মল পক্স-এর ভয়ে শীতলা পুজোর প্রচলন। কালের নিয়মে অবশ্যই তার পরিমার্জন-ও হয়। নাহলে সভ্যতা স্থবির হয়ে পড়ে। ভ্রাতৃদ্বিতীয়াকেও আজ নয় কাল যেতে হবে এ হেন পরিমার্জনের মধ্যে দিয়ে।
একুশ শতকের বাংলায় বোন আর ভাইদের দ্বারা পরিচালিত হয়না। নিজেদের দায়িত্ব তারা নিজেরাই নিতে সক্ষম। এমনকি বিবাহবিচ্ছিন্না হলেও সে চাকরি করে, ব্যবসা চালিয়ে নিজের অন্নবস্ত্রবাসস্থানের সুরাহা নিজেই করে নিতে পারে। সুতরাং দীর্ঘদিন যাবৎ লালিত এই বিশ্বাস যে, ভাই-ই কেবল বোনকে রক্ষা করবে, প্রতিপালন করবে, তাও আজ আর প্রাসঙ্গিক নয়। মনু-র নিদানকে নস্যাৎ করে এই সমাজ বুঝতে শিখছে, একটি পরিবারে, বাবা যেমন মায়ের চেয়ে উচ্চতর আসনে আসীন নন, তেমনই দাদাও বোনের সাপেক্ষে উচ্চতর নন। দম্পতির মধ্যে দুই সঙ্গীর অবস্থান ও অধিকার সমান। একইভাবে, তাদের কন্যা ও পুত্র উভয়েই একইরকম ভরণপোষণ, অর্থ এবং মনোযোগ দাবি করে। বোনের টিউশন থেকে ফিরতে রাত হলে গলির মোড়ে দাদা দাঁড়িয়ে থাকে, তার মানে এই নয়, বোনকে প্রেমপত্র লিখতে দেখলে দাদাটির অধিকার জন্মে যায় বোনকে বেধড়ক মারধোর করার। কেননা কেউ কারও অভিভাবক নয়, উভয়েই সমকক্ষ।
একুশ শতকের বঙ্গভূমি পুত্র ও কন্যাসন্তানকে ক্রমশ সমতুল্য হিসাবে দেখতে প্রস্তুত হচ্ছে। পিতৃতান্ত্রিক এই উৎসবকে যদি যুগোপযোগী করে তুলতেই হয়, যদি তাকে হয়ে উঠতে হয় ‘সেলিব্রেশন অফ সিবলিংহুড’, তবে এ-ই সময় ভাতৃদ্বিতীয়াকে স্রেফ দ্বিতীয়া নামে ডাকার, এই তো সময়, বোনের কপালে চন্দনের তিলক পরিয়ে বলে ওঠার, ‘বোন যেন হয় সোনার ভাঁটা!’ কেননা এ প্রশ্ন শুধু নারী-পুরুষের সমানাধিকারের নয়, এক মানুষের প্রতি অন্য মানুষের সম্মান জ্ঞাপনের; সম্যক মান ও সম মান প্রদর্শনের।
জন্ম ১৭ জুন ১৯৮৬। জে.বি.রায় স্টেট আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ ও হসপিটাল থেকে আয়ুর্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্রে স্নাতক। মানসিক স্বাস্থ্যে স্নাতকোত্তর। কবিতা, সংগীত ও নাট্যচর্চার সঙ্গে নৈকট্য আশৈশব। জনস্বাস্থ্য, সমাজবিজ্ঞান, মানবাধিকার প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধচর্চা করেন নিয়মিতভাবে৷ তাঁর 'অরুণা শানবাগ নিষ্কৃতিমৃত্যু ও ভারত' (২০১৭) বইটি এদ্যবধি ইউথেনেসিয়া প্রসঙ্গে লেখা একমাত্র পূর্ণাঙ্গ বাংলা বই যা মনোজ্ঞ পাঠকমহলে প্রশংসিত। সিএএ-বিরোধী আন্দোলনের সময়ে কবি ফৈজ আহমেদ ফৈজ-এর সর্বজনবিদিত 'হম দেখেঙ্গে' (দেখে নেবো আমরাই) কবিতাটির বাংলা অনুবাদ করে অবন্তিকা জাতীয় স্তরেও জায়গা করে নিয়েছেন।


























One Response
সুন্দর লেখা।