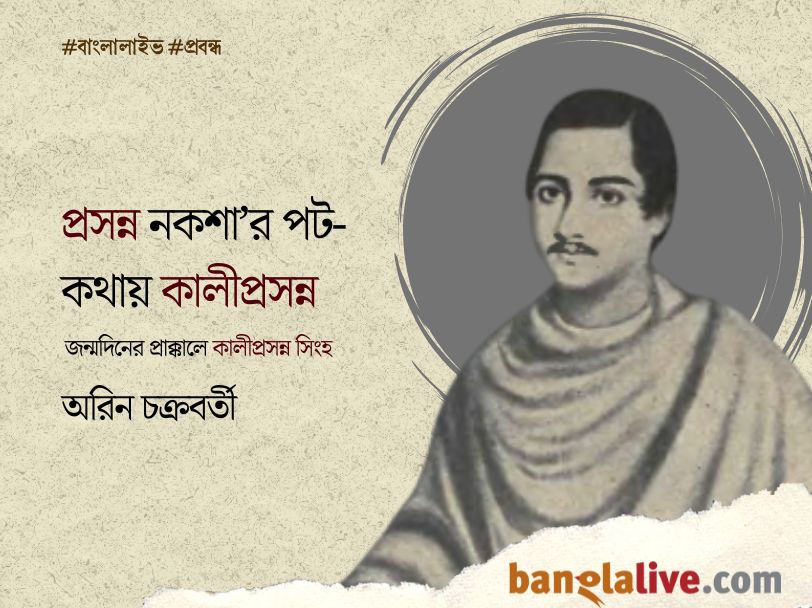প্রবাসের পটভূমিকায় লিখিত বলে উপন্যাসে ইংরিজি সংলাপ ও শব্দের বহুল ব্যবহার রয়েছে।
আগের পর্ব পড়তে: [১] [২] [৩] [৪] [৫] [৬] [৭]
১৮
এই পরিসরে আমার স্ত্রী লেখার পরিবারটি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক৷ অরুণলেখার পরিবারটির শিকড় আমাদের পরিবারের মতো পূর্ববঙ্গে প্রোথিত ছিল না৷ অরুণলেখার বাবা বাঁকুড়ার মানুষ৷ শিবপুরে এগ্রিকালচারে এমএসসি পাশ করিয়া সরকারি কৃষিবিভাগে কর্মরত ছিলেন৷ কর্মসূত্রে দু’ একবার রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং পুত্রের মুখে শুনিয়া রবীন্দ্রনাথই তাঁহাকে শান্তিনিকেতনে ডাকিয়া লন৷ ইতিমধ্যে কবি ১৯২১ সালে সুরুলে কুঠিবাড়ি ক্রয় করিয়া উহাতে শ্রীনিকেতনের কর্মকাণ্ড শুরু করিয়াছিলেন৷ চিরকালই কৃষিবিদ্যা এবং কৃষি সম্বন্ধীয় নানা পরীক্ষানিরীক্ষায় রবীন্দ্রনাথ পরম উৎসাহী ছিলেন৷ এলমহার্স্ট, কালীপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখের সহায়তায় যে কর্মকাণ্ড প্রসার লাভ করে, তাহার জন্য কবির কিছু দক্ষ সাহায্যকারীর প্রয়োঅরুণজন ছিল৷ সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে আসিয়া অরুণের বাবা শশধর মুখার্জী সীমান্তপল্লীতে সংসার পাতেন৷ সরকারি চাকুরী ছাড়িয়া তিনি যে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে শান্তিনিকেতনে পাকাপাকিভাবে রহিয়া যান, সে বিষয়ে বোধহয় তাঁহার ব্রাহ্মধর্মগ্রহণ কিছু পরিমাণে দায়ী ছিল৷ শশধরের পিতা তাঁহাকে ত্যাজ্যপুত্র করিয়াছিলেন৷ ফলে পৈত্রিক জমিজমা বিষয়-আশয়ে তিনি অধিকার হারান৷ একজন প্রকৃত সেল্ফ মেড ম্যান হিসাবে নিজ পুত্র কন্যাদের মধ্যেও তিনি মুক্তচিন্তা এবং অবাধ স্বাধীনতার সদ্গুণগুলি সঞ্চারিত করিতে সক্ষম হন৷
অরুণ এবং তাহার দাদা সুমিত্র শান্তিনিকেতনের উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে বাড়িয়া উঠিতেছিল৷ অরুণের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাতের সময় সে একুশ বৎসরের তরুণী আর সুমিত্র তখন পঁচিশ বৎসরের যুবক৷ সুমিষ্ট হাস্যময় স্বভাবের জন্য শান্তিনিকেতনের ছাত্রমহলে সে সবিশেষ জনপ্রিয় ছিল৷ অরুণলেখার মতোই সুমিত্র নামটি রবীন্দ্রনাথের দেওয়া৷ কিন্তু মোহন নামেই আমার সম্বন্ধী সমধিক পরিচিত ছিল৷ মোহন ও আমার স্ত্রী দু’জনেই অত্যন্ত গুণী ছিল৷ মোহনের বিশেষত্ব ছিল গাছপালা এবং পক্ষি বিষয়ে তাহার অদ্ভুত জ্ঞান৷ প্রকৃতির সঙ্গে সে যেন অক্লেশে একাত্ম হইয়া যাইতে পারিত৷ একটি বাঁশি ছিল তাহার সর্বক্ষণের সঙ্গী৷ আড়বাঁশিটি হাতে শান্তিনিকেতনের উন্মুক্ত প্রান্তরে যত্রতত্র সে যে শুধু ঘুরিয়া বেড়াইত, তাহাই নহে, মাঝে মধ্যে খেয়ালখুশি মতে এদিক ওদিক চলিয়াও যাইত৷ আমার নিজ ইচ্ছায় দু’ একমাস বাদে ফিরিয়া আসিত৷ শৈশব হইতেই তাহার চরিত্রে একটি পলায়নী ভাব বিদ্যমান ছিল৷ গাছ লতাপাতা উদ্ভিদ জগতের সহিত সম্পৃক্ত হওয়া যদি বা তাহার জেনেটিক প্রবণতা হয় (যেহেতু তাহার বাবা ছিলেন অ্যাগ্রোনমিস্ট), এইরূপ পালাই পালাই ভাব, এইরূপ সংসার সম্পর্কে ঔদাসীন্য, যাহা বোধ করি তাহার প্রধান চরিত্রলক্ষণ ছিল, তাহা সে কোথা হইতে পাইয়াছিল, ভাবিয়া কূলকিনারা পাওয়া যাইত না৷ সে যেন বাল্য ও কৈশোরের বয়ঃসন্ধিক্ষণ হইতে কেজো পৃথিবীর প্রতি বীতরাগ, সংসারে থাকিয়াও বৈরাগী এবং আশপাশের মানুষগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ আসক্তিহীন এক ব্যক্তি– এইরূপ যত দিন যাইতে লাগিল, ততই সকলের নিকট প্রতীয়মান হইল৷ মোহন যে মোটের উপর এইরকমই বোহেমিয়ান জীবন যাপন করিবে, তাহা একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল৷

আমার যখন বিবাহ হয়, তখন মোহন ছাব্বিশ বৎসরের যুবক৷ বস্তুত আমাদের মধ্যে মাত্র কয়েক মাসের তফাত৷ সেজন্য সম্পর্কে বড় হইলেও তাহাকে আমি কোনওদিন ‘দাদা’ সম্বোধন করি নাই৷ পরেও তাহার চরিত্র একটুও পালটায় নাই৷ পরিব্রজ্যা এবং সন্ন্যাসের যৌথ তরঙ্গ তাহাকে গৃহে সুস্থিত হইতে দেয় নাই৷ প্রায় প্রতি বৎসরই বেশ কয়েক মাসের জন্য নিয়ম করিয়া সে উধাও হইয়া যাইত৷ বাষট্টি সনের শীতে আমাদের পুত্রের অন্নপ্রাশনের সময়, জানা গেল, যথারীতি সে নিরুদ্দেশ৷ আমাদের হিন্দু সমাজের রীতি অনুযায়ী শিশুর প্রথমদিনের অন্ন তাহার মামারই মুখে তুলিয়া দেওয়া বিধেয়৷ মোহনের অভাবে তাহার পিতা, আমার শ্বশুর মহাশয়ই দৌহিত্রের মুখে প্রথম অন্ন তুলিয়া দিয়াছিলেন৷ আগেকার কালে মেয়েরা গর্ভবতী হইলে পিতৃগৃহে গমন করিত৷ সেইখানেই প্রসব হইত৷ তারপর শিশুসন্তানের অন্তত পাঁচ ছয় মাস বয়স হইলে ‘মামাবাড়ির ভাত’ অর্থাৎ প্রথম মাতৃদুগ্ধ হইতে প্রথম ‘সলিড ফুড’ খাওয়াইয়া শিশুটিকে মাতার সহিত তাহার নিজ বাটি অর্থাৎ পিতৃগৃহে প্রেরণ করা হইত৷ সেই হইতেই এইরূপ অন্নপ্রাশন বা ‘মুখেভাত’ প্রথার জন্ম৷
আমার পুত্র অরুণাভর জন্ম হয় কলিকাতার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে৷ কিন্তু দমদমের বাসায় তাহার মুখেভাতের আয়োজন হইলে শান্তিনিকেতন হইতে অরুণলেখার পিতা সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য নাতির মুখেভাত দিবার জন্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন৷ রাঁধুনিপাগল চাল আনিতেও ভোলেন নাই৷ কথিত আছে, এই চালের এত সুবাস যে রাঁধুনি পাক করিতে করিতে সুগন্ধে উন্মাদ হইয়া যায়৷ সেই চালের পরমান্ন রন্ধন করা হইলে সে যাত্রা কেউ উন্মাদ হয় নাই বটে, তবে বাবাই যে হাত পা ছুঁড়িয়া মুখ বিকৃত করিয়া বিকটভাবে দম আটকাইয়া ক্রন্দন করিতেছিল, তাহা আমার বিলক্ষণ মনে আছে৷ যাহা হউক, যে কথা বলিবার জন্য এই প্রসঙ্গের অবতারণা, তাহা হইল, আমাদের পরিবারে যখন এই আনন্দ অনুষ্ঠান হইতেছিল,তখনও মোহন নিরুদ্দেশ৷ সে যখন বাহির হইয়া যাইত, তখন ভোরবেলা অতি চুপিসাড়ে ঝোলার ভিতর কতগুলি কাপড়চোপড় লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইত৷ তারপর দীর্ঘদিন তাহার আর সন্ধান থাকিত না৷ কখনও সখনও একটি পোস্টকার্ডে মা বা বোনকে জানাইত যে সে অমুক জায়গায় আছে৷ কখনও তাও জানাইত না৷ এইভাবেই চলিবে আমরা মোটের উপর ধরিয়া লইয়াছিলাম৷
কিন্তু মানুষ ভাবে এক, আর হয় আর এক৷ ১৯৬৪ সালের মাঘীপূর্ণিমার এক রাতে মোহন আচমকা নিরুদ্দেশ হইয়া গেল৷ তাহার তিরিশ বৎসর বয়স হইতে তখন আর কয়েক মাস বাকি আছে৷ অরুণলেখার বাবা-মা পুত্রের এমত ক্রিয়াকলাপে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলেন৷ তাঁহারা প্রথমদিকে খুব যে বিচলিত হইয়াছিলেন তাহা নহে৷ ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল কখনও একটি পোস্টকার্ড আসিবে৷ সেই পত্রে বোঝা যাইবে মোহন উত্তরকাশীতে না গোমুখে, নাকি দেবপ্রয়াগে৷ কিন্তু কার্যকালে পত্র আর আসিল না৷ পাঁচ-ছ মাস কাটিয়া গেলে, অরুণের মাতাঠাকুরাণী কিছু উতলা হইলেন৷ চেনা পরিচিত যে যেখানে ছিলেন, তাঁহাদের মাধ্যমে খোঁজ খবর চলিতে লাগিল৷ আমার ভগ্নীপতি বিশ্বেশ্বর তখন হইতেই দিল্লিতে৷ বিশ্বেশ্বরও অনেক সাহায্য করিবার চেষ্টা করিয়াছিল৷ কিন্তু কোনও কিছুরই কোনও ফল হয় নাই৷ সারা ভারতবর্ষে যত সম্ভাব্য তীর্থক্ষেত্র আছে, যত সাধু-সন্ন্যাসী আছেন, সর্বত্র খোঁজ করাই ব্যর্থ হয়৷ এই সময় হইতে অরুণের বাপ-মা সম্পূর্ণ উন্মত্তের মতো হইয়া পড়েন৷ ব্রাহ্মধর্মে নিবেদিতপ্রাণ যে দম্পতি একদা হিন্দু কোনও তীর্থক্ষেত্রের ছায়া মাড়াইতেন না, আমাদের বিবাহের সময়ও যাঁহারা হিন্দুধর্মের কোনও নিয়মকানুন, যথা সপ্তপদী, কুশন্ডিকা, সম্প্রদান ইত্যাদি পালন করার বিপক্ষে মত দেন, তাঁহারা ১৯৬৫ হইতে জীবনের শেষ বৎসরগুলি প্রতি গ্রীষ্মে ও শারদাবকাশে ভারতের বিভিন্ন মন্দিরে, বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, যদি কোথাও তাঁহাদের পুত্রের সন্ধান মেলে৷ পুত্রের সন্ধান পাওয়া যায় দশ বছর বাদে, যখন একটি রেজিস্টার্ড ডাকে হিমালয়ের এক প্রান্ত হইতে একটি মোটা খাম আসে৷ তখন ঘটনাচক্রে আমরা কলকাতায়, আমার বাবার শেষশয্যার পাশে দাঁড়াইবার জন্য গিয়াছি৷
বাবার প্রয়াণে আমরা পুরো পরিবার তখন খুবই শোকগ্রস্ত৷ সেসময় অরুণলেখার বাবা-মা অকস্মাৎ শান্তিনিকেতন হইতে কলকাতায় আসেন৷ ‘পূবালী’ বাড়ির চাবি তাঁদের কন্যার হাতে গচ্ছিত রাখিয়া তাঁহারা চলিয়াছেন পুত্রের দর্শন পাইবার জন্য৷ অবশেষে ঈশ্বরের কাছে এত প্রার্থনা সফল হইয়াছে৷ একজন ভক্ত রেজিস্টার্ড ডাকযোগে তথ্য প্রমাণ দাখিল করিয়াছে– মোহন গাড়োয়ালের একটি জায়গায় সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করিতেছে৷ খবরটি যে খাঁটি, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য খামে মোহনের বর্তমান একটি ফটোগ্রাফও ছিল৷ আমরা সকলে দেখিয়া মানিতে বাধ্য হই যে ছবিটি মোহনেরই বটে৷ শ্মশ্রুগুম্ফ সমন্বিত মুখ, চেহারাতেও একটু শীর্ণ, কিন্তু দক্ষিণ ভুরুর উপর ট্রেডমার্ক সেই তিলটি রহিয়াছে৷ পরনে গেরুয়া বসন৷ কিন্তু চোখের কোণে সেই কৌতুকময় হাসিটির চিহ্ন রহিয়াছে৷ বাবার মৃত্যুর পর আমাদের মন বড় বিষণ্ণ ছিল৷ কিন্তু সন্দেহ নাই, সেই আষাঢ় সন্ধ্যায় দমদমের গৃহে, মোহনের ছবি দেখিয়া, তাহার বর্তমান বাসস্থলের সংবাদ পাইয়া, আমাদের সকলের বুক হইতে যেন পাষাণভার কিছুটা নামিয়া গেল৷ অরুণলেখার তো বটেই, মোহন হাসি ও খুশিরও বড় প্রিয় ছিল৷ দশ বৎসর পর অবশেষে যে মোহনের সন্ধান মিলিয়াছে, এবং অচিরেই অন্তত পুত্রের জন্য কাতর বৃদ্ধ দম্পতির দুঃখের অবসান হইবে, সেই সত্য আমার গভীর বিষাদের মধ্যেও রুপোলি রেখার মতো আশার সঞ্চার করিয়াছিল৷
অরুণ তাহার মাতাকে বলিয়াছিল,
– মা, একটু অপেক্ষা কর না৷ এদিকে শ্রাদ্ধশান্তি মিটলে আমিও তোমাদের সঙ্গে দাদার কাছে গিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনব৷
আমার শ্মশ্রুমাতা বলিয়াছিলেন,
– এতদিন বাদে আমার মোহনের সন্ধান পেয়েছি ঈশ্বরের অনেক করুণায়৷ আমার আর মন মানছে না৷ তুই আমার যাওয়াটা আর পিছোস্ না মা!
অরুণের পিতা বলিয়াছিলেন,
– আর সে যদি ফেরার হত, তবে এই দশ বছরে সে আপনিই ফিরত৷ সংসারধর্ম পালন তার জন্য নয়, সে তো আমরা মেনেই নিয়েছি৷ এতদিন বাদে যদি তার মুখখানি একবার দেখতে পাই, সেইতো যথেষ্ট৷
সেইমতোই স্থির হইয়াছিল, সাধকপুত্রকে তাঁহারা একবার চোখের দেখা দেখিতে যাইবেন৷ যোগাযোগ পুনস্থাপিত হইলে প্রতি বছরই তাঁহারা পুত্রের আশ্রমে গিয়া কাটাইতে পারিবেন৷
আমি দুন এক্সপ্রেসে টিকিট কাটিয়া দিয়াছিলাম৷ আমার কালাশৌচ বলিয়া আমার ভগ্নীপতি বিশ্বেশ্বর ট্যাক্সি ডাকিয়া বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে ট্রেনে চড়াইয়া দিয়াছিল৷ নতুন আশায় বুক বাঁধিয়া তাঁহারা বৃদ্ধ বয়সে অন্ধের যষ্টি, গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী পুত্রের সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছিলেন৷ তাঁহাদের কন্যার সঙ্গে তাঁহাদের সেই শেষ দেখা৷ পুত্রের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল৷ কয়েকদিন তাঁদের ওই আশ্রমে থাকিবার অনুমতি মিলিয়াছিল আশ্রম কর্তৃপক্ষের তরফে৷ আসার সময় চামৌলি হইতে কর্ণপ্রয়াগের পথে এক বাস দুর্ঘটনায় তাঁহাদের জীবনাবসান হয়৷ বাসটি গিরিখাতে পড়ায় দেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই৷ বর্ষার খরস্রোতা পাহাড়ি নদী দেহগুলি দুর্নিবার স্রোতে ভাসাইয়া নিয়া গিয়াছিল৷
***
১৯৭০-এর দশক আমার অনেক প্রাপ্তির সময়৷ আমার কন্যা জিনিয়ার জন্ম হয় ১৯৭২ সালে৷ ১৯৭৩-এর শেষে বালকপুত্র এবং শিশুকন্যাকে লইয়া আমরা আমেরিকায় পাকাপাকিভাবে চলিয়া আসি৷ আমার সামনে তখন দুটি সুযোগ ছিল৷ ইংল্যান্ডে ডিগ্রি পাইবার শেষে পুনর্বার দেশে ফিরিয়া যাওয়া, নয়তো আমেরিকায় আসিয়া নূতন ভবিষ্যতের সন্ধান করা৷ আমি ক্রমে দ্বিতীয়টির দিকেই ঝুঁকিতেছিলাম৷ জিনির জন্মের সময় হইতেই আমি মার্কিন নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকরি খুঁজিতেছিলাম৷ জিনির প্রায় এক বৎসর বয়সকালে ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার স্কুল অব ডিজাইন আমাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিল৷ অনেক নামকরা আর্কিটেক্ট এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছিলেন (বালকৃষ্ণ দোশী, ইএম পাইয়ের মতো)৷ এই প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত হইবার সুযোগ পাইয়া আমার আনন্দের সীমা রহিল না৷ কলিকাতার অবস্থা দিনের পর দিন খারাপ হইতেছিল৷ ১৯৭১-এ বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় শরণার্থী সমস্যা কিছু মারাত্মক আকার ধারণ করিয়াছিল৷ ১৯৬৭-র যুক্তফ্রন্ট সরকার অজয় মুখার্জীর দিশাহীন পরিচালনায় ভঙ্গুর আকার ধারণ করে৷ দফায় দফায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারী হইতেছিল৷ আমরা ইংল্যান্ডে আসিবার সময় সকলের আশা ছিল, বাংলার সরকার স্থায়িত্ব লাভ করিবে৷ কিন্তু বাংলার রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে তখন দুর্যোগের ঘনঘটা৷ আমরা ইংল্যান্ডে যাইবার সময় হইতেই নকশালবাড়ি আন্দোলন দানা বাধিয়া ওঠে৷ ছোটকুর মতো মেধাবী ছাত্র আন্দোলনে সামিল হইয়া বছর নষ্ট করিয়াছিল৷ তাহাকে লইয়া বাবার উদ্বেগের সীমা ছিল না৷ দেশ হইতে আসা বাবার প্রত্যেক চিঠিতেই দেশের অগ্নিগর্ভ রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ছোটকু সম্পর্কে অনিশ্চয়তা ও হতাশায় ভরা থাকিত৷ চিঠিতে পড়িতাম ছোটকু রাতের পর রাত বাড়ি ফেরে না৷ বাবা মা বিনিদ্র রজনী কাটাইতেছেন৷ আমাকে ও অন্য দুটি বোন হাসি ও খুশিকে লইয়া তাঁহাদের এ জাতীয় কোনও সমস্যায় পড়িতে হয় নাই৷ কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্রকে লইয়া তাঁহাদের শেষ জীবন বড়ই কষ্টে কাটিয়াছে৷
ছোটকু আমাদের সকলের অতি আদরের ভাই ছিল৷ তেরো বৎসরের ছোট ভাইটিকে আমি প্রায় কোলেপিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিলাম৷ আমাকে সে কিশোর বয়স পর্যন্ত দেবজ্ঞান করিত৷ দাদা অন্তপ্রাণ, সুবোধ সেই বালকের ভিতরে যে এত বিদ্রোহ প্রবণতা, সমাজ সম্পর্কে এত অসন্তোষ কবে দেখা দিল, তাহা জানিতে পারি নাই৷ সে মার্ক্স, লেনিন এবং মাও সে তুং-এর ভারী ভারী সমাজদর্শনের গ্রন্থ পড়িত৷ সমাজকে খোল নলচে শুদ্ধু পাল্টাইতে চাহিত৷ কিন্তু তাহার পদ্ধতি এবং প্রকরণ যে এত ভয়ঙ্কর এবং হিংস্র হইতে পারে, তাহা অন্য মহাদেশে বসিয়া আমি সম্যক অনুধাবন করিতে পারি নাই৷ অরুণ সদ্যোজাত কন্যাকে লইয়া ব্যস্ত৷ আমি বাবাইয়ের শিক্ষার ভিত যাতে ভালো হয়, সে চেষ্টার পাশাপাশি আমার নিজের কেরিয়ারের দিকেও মনোযোগী ছিলাম৷ মনের মধ্যে কোথাও ক্ষীণ আশা ছিল, বাংলায় রাজনৈতিক অস্থিরতার অচিরে অবসান ঘটিবে এবং ছোটকুও নিজের ভালোমন্দ বুঝিয়া উচিত সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হইবে৷ উহাকে উচ্চশিক্ষার্থে নিজের কাছে লইয়া আসিব, এইরকম চিন্তাই করিয়াছিলাম৷
কিন্তু মানুষ ভাবে এক, আর ঘটে আর এক৷ ফিলাডেলফিয়া যাইবার জন্য আমরা তখন বাক্স বাঁধাবাঁধি করিতেছি৷ বেশ কিছু জিনিস জাহাজে রওনা করানো হইয়াছে৷ অন্য দেশে যাবার বিরাট প্রস্তুতি চলিতেছে বলিয়া আমরা সেই গ্রীষ্মাবকাশে আর দেশে যাই নাই৷ আমেরিকা ব্যক্তিস্বাধীনতার দেশ৷ সেই দেশে যাত্রার সম্ভাবনায় আমি ও অরুণ দিন গুনিতেছিলাম৷ এক গ্রীষ্মের রোদালো বিকেলে অরুণ, বাবাই ও জিনিকে লইয়া সামনের পার্কে গিয়াছে, আমি বাড়িতে বসিয়া কিছু বই বাছাবাছি করিতেছিলাম, সামনে ফ্লাস্কে অরুণ চা করিয়া রাখিয়া গেছিল৷ তখন দরজায় বেল পড়িল৷ অরুণরা ফিরিয়াছে ভাবিয়া আমি দরজা খুলিতে গেলাম, যদিও অরুণ যখনই বাহির হইত, দ্বিতীয় চাবিটি লইয়া যাইত৷ ভাবিলাম কোনও কারণে চাবি নিতে ভুলিয়া গিয়াছে৷ দরজা খুলিয়া দেখি ডেলিভারি বয়ের পোশাকে পোস্টম্যান টেলিগ্রাম হাতে দাঁড়াইয়া আছে৷ টেলিগ্রাম হাতে আমি ধীরে ধীরে বসার ঘরে গেলাম৷ খুলিয়া দেখি খুশি টেলিগ্রাম করিয়াছে৷ ‘Chhotku is no more. Killed in encounter.’

১৯
গুর্মুখের চওড়া কপাল, এককালের ফর্সা রঙ এখন সূর্যের তাপে একটু তামাটে বর্ণ ধারণ করেছে৷ স্নান সেরে গুড়িয়ার হেয়ার-ড্রায়ারটা দিয়ে চুলগুলো একটু শুকিয়ে নিয়ে একটা ঝুঁটি বেঁধেছে ও৷ শিখদের তুলনায় ওর চুল এখন আর অতকিছু লম্বা নয়৷ এখানে ওসব চুল রাখা, পাগড়ি পরা এসব মহা হাঙ্গামার৷ এসব বুঝেই চুল বেশ কিছুটা কেটে ফেলেছে ও৷ দেশে থাকলে ওর বাপ-জ্যাঠারা, কখনওই অনুমতি দিত না চুল কাটার৷ শিখ ধর্মে ওসব মহাপাপ৷ কেশ, কাচ্ছা, কাঙ্গি, কড়া, কৃপাণ এসব একজন শিখের থাকতেই হয়৷ গুর্মুখ ধর্মভীরু নয়৷ ভয়ডর কাকে বলে বোঝার মতো আই কিউ ওর আছে কিনা মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় অরুণাভর৷ গুমুর্খের কোনও নিজস্ব ঈশ্বর আছে কিনা, জানে না অরুণাভ৷ গুমুর্খের কাছে অরুণাভই সাক্ষাৎ ঈশ্বর৷ ভগোয়ান য্যায়সা৷ গুর্মুখ আপাতত ওর ট্যাক্সি নিয়ে লেক্সিংটনের দিকেই যাচ্ছে৷ ট্যাক্সি চালায় গুর্মুখ৷ কবে থেকে যে গাড়ি চালাচ্ছে এখন আর ঠিক মনে করতে পারে না সে৷ ওর মনে হয় ও মায়ের পেট থেকে পড়েই ট্যাক্সি চালাচ্ছে৷ তিরিশ বছর তো হবেই৷ পাঞ্জাবে জালিয়ানওয়ালাবাগের কাছে একটা গ্রামে ওদের বাড়ি৷ জমি জিরেতও ছিল কিছু৷ ওর বাপ-জ্যাঠারা জালিয়ানওয়ালাবাগে ট্যুরিস্ট গাইডের কাজ করত৷ ট্যুরিস্টদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাত কোথায় জমায়েতটা হয়েছিল, জেনারেল ডায়ার কিভাবে ফায়ারিংয়ের কথা বলেছিল, নীরস্ত্র শান্তিপূর্ণ জনতা কীভাবে গরুছাগলের মতো পালাচ্ছিল, আশ্রয় খুঁজছিল, মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করছিল৷ ছোটোবেলায় ও বাবার সঙ্গে ঘুরত৷ বাপ যখন ট্যুরিস্টদের ওসব বলত, বাপের মুখটা কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠত৷ শিখদের গৌরবগাথা আর ব্রিটিশদের কাপুরুষোচিত আচরণ তুলনা করতে করতে ওর বাপটার চোখ চিকচিক করত৷
বাপকে অনেককাল দেখেনি ও৷ দশ বছর হয়ে গেল দেশে আর ফিরতে পারে না গুর্মুখ৷ অনেক বছর হল গুরুশরণ আর বাচ্চাটাকে দেখেনি ও৷ মাঝে মাঝে ফেলে আসা বউটার কথা ভেবে মনটা একটু খারাপ করে৷ বাচ্চাটার জন্য সত্যি কথা বলতে কি, অত টান বুঝতে পারে না গুর্মুখ৷ তারই বা কি দোষ? বাচ্চাটাকে সে তো দেখেইনি৷ অবশ্য বাচ্চাটাও আর বাচ্চা নেই৷ দশ বছরের কিশোর হয়ে গেছে৷ আগে মামাদের ফোন থেকে দেশে বাপ-মা, বউয়ের সঙ্গে কথা বলতো গুর্মুখ৷ আজকাল গুড়িয়ার ফোন থেকে মাঝে মধ্যে স্কাইপে কথা বলে।৷ ফোনের ভিডিওতে হাসি হাসি মুখ ফুঠে ওঠে বিবি আর ছেলের৷ ‘আরে তুম তো জওয়ান আদমি বন গয়া!’ কৃত্রিম বিস্ময়ে গুর্মুখ বলে ভারচুয়াল ছেলেকে৷ ওপ্রান্তে গুরুশরণ মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসে৷ মোবাইল ফোন, হোয়াটস্যাপ ইন্ডিয়ায় এসে যাবার পরে বিস্তর সুবিধে হয়েছে গুর্মুখের৷ ওর নিজস্ব ফোন নেই৷ কিন্তু গুড়িয়া ওকে ওর ফোনটা বললেই ব্যবহার করতে দেয় দেশে কল করার জন্য৷ আড়াল থেকে শোনে, কী বলছে গুর্মুখের বউ-ছেলে৷ ওদের কথাবার্তায় আমোদ পায় গুড়িয়া৷ গুর্মুখের দূর সম্পর্কের চাচাতো বোন৷ কিন্তু গুড়িয়ার সঙ্গে ইদানিং ক’বছর ধরে অন্যরকম সম্পর্ক তৈরি হয়েছে গুর্মুখের৷ ও ডাকলে গুড়িয়া না করে না৷ শরীরের সাড়া দেয় প্রয়োজন পড়লেই৷
ইদানিং ওসব পাড়ায় যাওয়া একদম ছেড়ে দিয়েছে গুর্মুখ৷ ওর শরীরে রোগটা বাসা বাধার পর থেকেই৷ ইচ্ছেটাও আজকাল কমে গেছে৷ যখন দরকার হয় গুড়িয়ার শরীরটা দিয়েই কাজ চালিয়ে নেয়৷ গুড়িয়াও সিঙ্গল এই মুহূর্তে৷ ভালো করে দেখেশুনেই বিয়ে দিয়েছিল ওর বাবা৷ কিন্তু বিয়েটা টেকেনি৷ গুড়িয়া এখন ওর বাবার দোকান সামলায়৷ ওর বাবার দোকানে আগে পাঞ্জাবি মশলা, খাবারদাবার ছাড়াও সিডিও পাওয়া যেত৷ বলিউডের ঝিনচ্যাক মসালা ফিল্ম সব নখদর্পণে ছিল গুড়িয়ার৷ ইদানিং সিডির ব্যবসাটা আর চলে না৷ বস্টনের ভারতীয়রা নেটফ্লিক্স আসার পর থেকে ফিল্ম দেখার অন্য উপায় খুঁজে নিয়েছে৷ সিডি ব্যবসাটা তাই তুলে দিয়েছে ওর বাবা৷ এখন ওদের পুরোপুরি গ্রসারি শপ৷ মশলা, পাঁপড়, ঝুরিভাজা আর সবজি৷ দেশের কিছু কিছু সবজিও মেলে ওদের দোকানে৷ সর্ষে শাক একবার নিজেই রান্না করে খাইয়েছিল গুড়িয়া৷ গুড়িয়ার সঙ্গে সম্পর্কটা বাড়ির সবাই জানে৷ খুল্লমখুল্লা না হলেও ওদের এই বিশেষ ধরনের পারস্পরিক চাহিদার জন্য মেনেও নিয়েছে ওর বাপ-মা৷ বিবাহবিচ্ছিন্না মেয়ের শরীরের খিদে মেটাবার জন্য এও একরকম ব্যবস্থা৷ গুড়িয়া ওর বিবাহিত জীবনে যে বার্থ কন্ট্রোল পিল খেত, এখনও সেই বড়ি খায় গুর্মুখের জন্য৷ এসব বিবেচনা আছে মেয়েটার মধ্যে৷ বেশ লম্বা তাগড়াই স্বাস্থ্যবতী গুড়িয়া৷ ওর কাছে এলেই শরীরে একটা উদ্দীপনা এখনও টের পায় গুর্মুখ৷
গুড়িয়ার কাছে গুর্মুখের একটা গভীর কৃতজ্ঞতাবোধ আছে৷ একধরনের মুগ্ধতাও৷ কেন, তা ঠিক জানে না গুর্মুখ৷ গুড়িয়া ওর দোকানের আমেরিকান খদ্দেরদের সঙ্গে চোস্ত ইংরেজিতে কথা বলে৷ এখানে খুব অল্পবয়স থেকে আছে বলে প্রতিদিনের জীবনে গুড়িয়ার একরকম স্বচ্ছন্দ সাবলীলতা আছে৷ তাছাড়া ওর ঘরের ঠিক পাশের ঘরেই থাকে গুড়িয়ারা৷ আপদে বিপদে গুর্মুখের জন্য ওদের টাউন হাউসের শিখদের অনেকেরই সাহায্য পায় গুর্মুখ৷ গুড়িয়া মাঝেমধ্যেই রান্না করে বাটিতে করে ওর জন্য ‘ঘর কা খানা’ তৈরি করে আনে৷ গুড়িয়ার মোবাইল থেকে দেশে কথা বলার ফলেই দেশের আত্মীয়দের সঙ্গে আবার একটা সংযোগ তৈরি হয়েছে৷ এইসব মিলিয়ে গুড়িয়ার প্রতি একধরনের নির্ভরতার বোধ আছে গুর্মুখের৷ ও যে একসময় খারাপ পাড়ায় যেত, তাও ও গুড়িয়াকে বলেছে৷ শুধু একটা কথা গুড়িয়াকে কিছুতেই বলতে পারেনি৷ সেটা বললে গুড়িয়া হয়তো আর এত সহজভাবে ওর কাছে আসতে পারবে না৷ বছর দুয়েক হলো ওর শরীরে কিছু গন্ডগোল মিলেছে৷ পরীক্ষা করাতে গিয়ে ধরা পড়েছে ও এইচআইভি পজিটিভ৷ পুরোপুরি অসুখটা বাধেনি৷ ওষুধ খেয়ে এখন নিয়ন্ত্রণে আছে৷ কিন্তু ডাক্তার ওকে বলেছে ওর অনিয়ন্ত্রিত যৌনসংসর্গ বন্ধ করতে৷ গত দু’বছর থেকে খুব সাবধানী জীবনযাপন করছে গুর্মুখ৷ ডাক্তার বলেছে ঠিকমত ওষুধ খেলে, সাবধানে জীবনযাপন করলে আরও পনেরো-কুড়ি বছর, মানে ষাট বছরে পৌঁছে যাবে ও৷ সবকিছু যদি ঠিকঠাক চলে, তাহলে ততদিনে দেশে ছেলেটা পঁচিশ বছরের হয়ে যাবে৷ দাঁড়িয়ে যাবে ততদিনে৷ মনে মনে ইদানিং খুব বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে গুর্মুখের৷ অনেক অপূর্ণ সাধ রয়ে গেছে ভিতরে৷

প্রথম যখন দেশ থেকে খালাসির কাজ নিয়ে গ্রিসে পাড়ি দিল গুর্মুখ, তখন ওর সঙ্গে কিচ্ছু ছিল না, এক ট্রাঙ্ক জামাকাপড় ছাড়া৷ আর হ্যাঁ, ড্রাইভিং লাইসেন্সটা ছিল৷ ওটার জন্যেই বেঁচে বর্তে আছে৷ গ্রামে একটা মিথ্যে ফৌজদারি মামলায় জড়িয়ে দিয়েছিল ওর চাচাতো ভাইরা৷ দেশ থেকে পালিয়ে আসার পর গ্রিসের ওই দ্বীপটায় থাকার সময় ওর মনে হত ও নির্বাসনে আছে৷ ব্রিটিশরা যেমন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে পাঠাত ইন্ডিয়ান ফ্রিডম ফাইটারদের, ঠিক তেমনি৷ তখন মনে হত সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে গ্রামের পরিচিত জীবনে ফিরে যাবে৷ যা হবার হোক৷ অন্তত দেশের মাটিতে পরিচিত লোকগুলোকে দেখে মরতে পারবে৷ তারপর কোথা থেকে কী যে হল! দু’বছর গ্রিসে থাকার পর আবার একটা জাহাজে উঠে ভাসতে ভাসতে বস্টন পৌঁছল সে৷ মাম্মির ফ্যামিলির একদল লোক কানাডা থেকে এসে একদা থিতু হয়েছিল এদেশে৷ সেই লতায়-পাতায় আত্মীয়, অচেনা, আধাচেনা মানুষগুলোর সূত্র ধরেই গুর্মুখ পাড়ি জমায় এই নতুন দেশে৷
এই আট-ন’বছরে ওর মায়ের যে আত্মীয়দের সূত্রে আসা, তাদের মাধ্যমে বেশ মন লেগে গেছে শহরটায়৷ এখানে উঁচু উঁচু বাড়ি, বড় বড় রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালাতে অন্যরম একটা মজা আছে৷ বহুদিন বাদে জীবনের মজা, বেঁচে থাকার স্বাদ আবার টের পায় গুর্মুখ৷ মাথার পিছনে ঝুঁটিতে ইদানিং একটা ছোট্ট রঙিন কাপড়ের পাড় লাগায় ও, ট্যাক্সিতে ওঠার আগে৷ ম্যাসাচুসেটসে গাড়ি চালাবার নিয়মকানুন খুব কড়া৷ তার উপর ট্যাক্সিটাও ওর নিজের না৷ ওর মামার শালার চারটে ট্যাক্সি ভাড়া খাটে৷ তারই মধ্যে একটা৷ মাস গেলে একটা মোটা অঙ্ক ট্যাক্সির মালিককে দিতে হয়৷ মহা হারামজাদা লোক সে৷ পাই পয়সা গুণে নেয়৷ তবু গ্যাসের খরচ আর মালিকের পাওনা মিটিয়েও হাতে ভালোই থাকে। ইদানিং মাসে মাসে বেশ কিছু করে জমাতেও শুরু করেছে৷ এইচআইভি-র জীবাণুগুলো শরীরে বাসা বেঁধেছিল কবে থেকে, কে জানে৷ তবে অসুখটা ধরা পড়ার পর থেকেই খুব সাবধানী হয়ে গেছে গুর্মুখ৷ তাকে অনেক হিসেব করে চলতে হবে৷ বেঁচে থাকতে হবে৷ অনেকদিনের স্বপ্ন, বেশকিছু ডলার জমে গেলে বাপ-মাকে একবার এদেশে নিয়ে আসবে সে৷ গুরুশরণ আর ছেলেটাকেও নিয়ে এসে ঘুরিয়ে দেবে সবকিছু৷ তার মতো জাহাজে করে খালাসি হয়ে আসতে হবে না বাপ-মাকে৷ জীবনে অনেক কষ্ট করেছে বাপটা৷
ছোট থেকে বাপের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ট্যুরিস্ট গাইডের কাজে অভ্যস্ত হয়ে গেছিল গুর্মুখ৷ জালিয়ানওয়ালাবাগের গল্প বলার সময় ওর বাপ সন্তর্পণে নিজের গল্প মিশিয়ে দিত জানা ইতিহাসের সঙ্গে৷ ঠাসবুনোট একটা গল্প৷ ‘আমরা এখন স্বাধীন দেশ৷ এই স্বাধীনতার মধ্যে অনেক লড়াই আছে৷ এর মধ্যে মিশে আছে দেশমুক্তির জন্য লড়ে যারা শহিদ হয়েছিলেন তাঁদের আত্মত্যাগ৷ জালিয়ানওয়ালাবাগে সেদিন যাঁদের রক্তে মাটি ভিজে গেছিল তাঁদের আত্মবলিদানের মধ্যে দিয়েই স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হয়েছে৷ স্বাধীন জীবনের আকাঙ্ক্ষা আমাদের শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিটি মানুষের রক্তে মিশে আছে৷’
বলতে বলতে ওর বাবার কথা কাঁপত, চোখে জল চিক্চিক্ করত,আবেগ আর নাটকীয়তার মিশেলে বাপ গাইডের ভাষণ শেষ করার পর সম্মিলিত জনতা, সহর্ষ হাততালিতে ফেটে পড়ত৷ গুর্মুখ তখন ঠিক বুঝতে পারত না৷ কিন্তু তিরিশ বছর পরে ইদানিং ফিকে হয়ে যাওয়া স্মৃতি থেকে বাবার ওই কথাগুলো মনের মধ্যে ঘুরেফিরে আসে৷ আত্মত্যাগ করে স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়, এই কথাটা এখন খুব ভালো বুঝতে পারে গুর্মুখ৷ সেও যদি গ্রামে খেতি জমি নিয়ে থেকে যেত, তবে ঘরপোষা আর পাঁচটা মানুষের মতোই কেটে যেত জীবন৷ কিন্তু এই যে দুটো মহাসমুদ্রের এপারে এক অন্য শহরে মানুষের ভিড়ে সে পথ হাঁটছে, বস্টন কমন্স, পন্ড পেরিয়ে বস্টন হারবারের পাশ দিয়ে চলছে তার ট্যাক্সি, এর মধ্যে একরকম স্বাধীন জীবন রয়েছে, যে জীবন কারোর কাছে দাসখৎ লিখে দেয়নি৷ এই জীবনে একরকম পূর্ণতা খুঁজে পেয়েছে ও, এখন জীবন তার সমস্ত কুহক দিয়ে ঘোর লাগায় গুর্মুখকে৷ ট্যাক্সির আধখোলা জানলা দিয়ে আসা সমুদ্রবাতাস দুলিয়ে দেয় তার মাথার পিছনের চুড়ো করে বাঁধা মোরগঝুঁটি পনিটেল৷ এক নবলব্ধ গতিময় ভারহীনতায় হাল্কা হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে যেতে থাকে গুর্মুখ সিং৷ (চলবে)
*পরবর্তী পর্ব প্রকাশিত হবে ১৯ অক্টোবর ২০২২
*ছবি সৌজন্য: Pinterest, Opindia
অপরাজিতা দাশগুপ্ত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক। আগে ইতিহাসের অধ্যাপনা করতেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট মেরিজ কলেজে ইতিহাস ও মানবীচর্চা বিভাগের ফুলব্রাইট ভিজিটিং অধ্যাপকও ছিলেন। প্রেসিডেন্সির ছাত্রী অপরাজিতার গবেষণা ও লেখালিখির বিষয় উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের গোড়ায় বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকের চিন্তাচেতনায় এবং বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নারী। অধ্যাপনা, গবেষণা, ও পেশা সামলে অপরাজিতা সোৎসাহে সাহিত্যচর্চাও করেন। তিনটি প্রকাশিত গ্রন্থ - সুরের স্মৃতি, স্মৃতির সুর, ইচ্ছের গাছ ও অন্যান্য, ছায়াপথ। নিয়মিত লেখালিখি করেন আনন্দবাজার-সহ নানা প্রথম সারির পত্রপত্রিকায়।