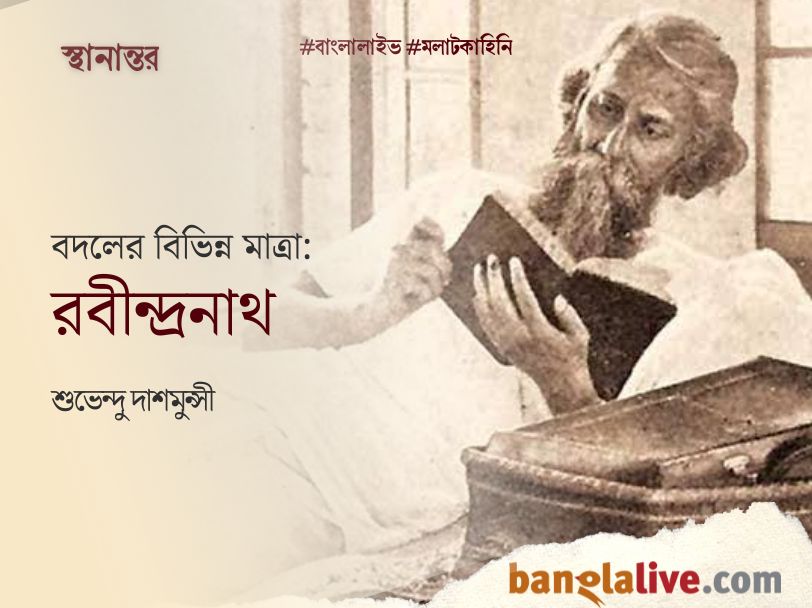(Rabindranath Tagore)
১
রবীন্দ্রনাথ বারবার বদলেছেন নিজেকে। নিজেকে বদলেছেন মানে, একদিকে জীবন যেমন তাঁর বদলেছে এক-একটি পর্যায়ে, তেমনই বদলেছে তাঁর সাহিত্যের গতিপথ। আবার একটি লেখাকে কখনও, কখনও আবার একটি বইকেও নানাভাবে বদলেছেন তিনি তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে। এই বদলের রবীন্দ্রনাথ এক আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব। তিনি এই নিত্য পরিবর্তনের মধ্যে বারবার নূতন হয়ে দেখা দেন উত্তরকালের কাছে। যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে পড়েন, যাঁরা জানতে-চিনতে চান এই আলোকসম্ভব পুরুষকে, তাঁরা বারেবারে বিস্মিত হন এই মানুষটিকে দেখে। (Rabindranath Tagore)
জীবনের প্রথম ত্রিশ বছর মূলত রবীন্দ্রনাথ থাকলেন ঠাকুরবাড়ির ঘেরাটোপে। আর উনিশ শতকের শেষ দশকে রবীন্দ্রনাথ দায়িত্ব নিলেন ঠাকুর এস্টেটের জমিদারি দেখাশোনার।
এই সন্ধানের একদিকে যদি থাকে তাঁর জীবনের কথা, আরেকদিকে আছে তাঁর রচনার বিবর্তন। লক্ষণীয়, জীবনের প্রথম ত্রিশ বছর মূলত রবীন্দ্রনাথ থাকলেন ঠাকুরবাড়ির ঘেরাটোপে। আর উনিশ শতকের শেষ দশকে রবীন্দ্রনাথ দায়িত্ব নিলেন ঠাকুর এস্টেটের জমিদারি দেখাশোনার। ততদিনে শুরু হয়েছে তাঁর লেখা, ততদিনে তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যকার। এই এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন তাঁর জীবনপর্বে। নাগরিক জীবনপ্রবাহ থেকে নিবিড়তরভাবে এই এতদিনে তিনি প্রত্যক্ষ করলেন পদ্মা-নদী-বিধৌত গ্রামজীবন। গ্রাম তো আগেও দেখেছেন, কিন্তু সে দেখা এমন ধারাবাহিক নয়, এমন সংযোগময় নয়। উনিশ শতকের এই শেষ দশকটিতে শিলাইদহ, সাজাদপুর দেখলেন রবীন্দ্রনাথ, পরিবর্তিত হল তাঁর জীবন-দেখা। (Rabindranath Tagore)

ইতিহাস পেল এক নতুন রবীন্দ্রনাথকে— তিনি জমিদার রবীন্দ্রনাথ। প্রজাকল্যাণে সতত নিয়োজিত এক ভিন্ন গোত্রের মধ্যস্বত্বভোগী। এই রবীন্দ্রনাথ কৃষিকর্ম বুঝলেন, বুঝলেন কৃষককেও। গ্রামজীবন বলতে কেবল প্রকৃতি নয়, প্রকৃতির সঙ্গে তিনি আবিষ্কার করলেন প্রাকৃতজনকেও। প্রজাহিতৈষী প্রকল্প সূচিত হচ্ছে, দূর হচ্ছে জমিদার আর প্রজার প্রতিদিনের আচারের ব্যবধান। পুণ্যাহ বা বার্ষিক করসংগ্রহের দিন রাজার আসন আর প্রজার আসনের উঁচু-নিচুর অবস্থানকে সরিয়ে দিচ্ছেন তিনি। জমিদার হিসেবে কৃষিক্ষেত্রে নতুন কারিগরি কীভাবে আরও ধনধান্যে উর্বর করতে পারে জমি, তার সন্ধান করছেন। জমিদাররূপে লক্ষ রাখছেন গ্রামোন্নয়নের দিকটিতে। (Rabindranath Tagore)
এই গ্রামোন্নয়ন চিন্তার সঙ্গে কবির শিক্ষাচিন্তা মিশ্রিত হয়ে পরবর্তী বিংশ শতকের সূচনা বর্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথ আনলেন তাঁর কর্মপ্রবাহে আরও এক নতুন বদল।
এই গ্রামোন্নয়ন চিন্তার সঙ্গে কবির শিক্ষাচিন্তা মিশ্রিত হয়ে পরবর্তী বিংশ শতকের সূচনা বর্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথ আনলেন তাঁর কর্মপ্রবাহে আরও এক নতুন বদল। সেই পর্ব অন্য-এক রবীন্দ্রনাথের যাত্রাপথের মহাসূচনা ঘটাল। ১৯০১ থেকে তিনি বোলপুর শান্তিনিকেতনে স্থাপন করলেন ব্রহ্মচর্যাশ্রম। জীবনপথ এবার পৌঁছল আর-এক নতুন মহালগ্নে।
ঔপনিবেশিক শিক্ষাচিন্তার ও শিক্ষাপদ্ধতির সমান্তরালে এক অভিনব শিক্ষাচিন্তার প্রতিষ্ঠা ও প্রসারে নেতৃত্ব দিলেন তিনি। বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে ওতপ্রোত করলেন মাটির সঙ্গে শিক্ষার্থীর সংযোগ। প্রতিষ্ঠিত হল শ্রীনিকেতন। পাঠের সঙ্গে কাজের সংযোগ ঘটালেন, কাজের সঙ্গে শিল্পোৎপাদন, পণ্যের উৎকর্ষ আর বিপণনের সংযোগ ঘটালেন। এও তো এক বদল। তবে সে বদল কেবল শান্তিনিকেতনের শিক্ষাপদ্ধতি বদলের মাত্রায় সীমাবদ্ধ নয়। এই বদল তো আসলে সমস্ত দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার এক আমূল বদলের পথ দেখায়। (Rabindranath Tagore)
আরও পড়ুন: বিয়ের গপপো: হারানো রীতির কয়-কাহন
ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার পরে ক্রমশ সেই আশ্রম-নির্মাণের মধ্য থেকেই বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত হলেন রবীন্দ্রনাথ। আর পরে সেখান থেকে সরেও এলেন রবীন্দ্রনাথ। এই জাতীয় রাজনীতির আবর্ত অতিক্রম করে তাঁকে তার পরের দশক থেকে, মানে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে নানাভাবে কবিকে যুক্ত হতে হল আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে। সেই যোগাযোগ জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে নাইটহুড ত্যাগ করে শাসক ও শাসকের দেশে বিরাগভাজন হওয়াই হোক বা মার্কিন ও জাপানের আগ্রাসন বিরোধিতার কারণেই হোক। কিংবা ধরা যাক, রবীন্দ্রনাথের বিতর্কিত ইতালি সফরের কথা। তিনি ক্রমশ বিবর্তিত হচ্ছিলেন বৃহত্তর রাজনীতির আবহ-বর্তে। রবীন্দ্রনাথের এই ক্রম-বিবর্ধমান রাজনৈতিক সামাজিক পরিসরও তো এক বদল। জীবনের বিবিধ বৃত্তে রবীন্দ্রনাথের জীবন-ভাবনা ও ঘটনাবৃত্তের এই বদল তাঁর জীবন ইতিহাসেরই ওতপ্রোত অঙ্গ। (Rabindranath Tagore)

২
এই রাজনৈতিক- সামাজিক- রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি অবশ্যই বদল ঘটছিল রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনেও। রচনারম্ভে একেবারে শুরুতে রবীন্দ্রনাথ লেখা শুরু করলেন আখ্যানকাব্য দিয়েই। কারণ, এই আখ্যানকাব্য-ই যে উনিশ শতকের বাংলা কাব্যভুবনের প্রচলিত দস্তুর। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন যে-আখ্যানকাব্য লিখছিলেন, সেই পথেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যচর্চার সূচনা। ‘কবিকাহিনী’, ‘বনফুল’ কাব্য দিয়ে শুরু করে সেখান থেকে তিনি পরে সরে এলেন বিহারীলাল চক্রবর্তীর গীতিকাব্যের ফর্মে। ‘সন্ধ্যাসংগীত’, ‘প্রভাতসংগীত’ থেকে এই আঙ্গিকে তাঁর লেখা প্রথম পর্বের রোমান্টিক কবিতার ধারাবাহিক পর্ব চলল ‘মানসী’, ‘চিত্রা’, ‘চৈতালি’-র যুগ অবধি। (Rabindranath Tagore)
এই রাজনৈতিক-সামাজিক-রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি অবশ্যই বদল ঘটছিল রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনেও।
তারপর তাঁর কবিতার বিষয়ে এল তাঁর ঔপনিষদিক পর্ব— গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, নৈবেদ্য-র যুগ আর সেখান থেকে ১৯১৪-তে বলাকা পর্ব। কি কাব্য বিষয়ে, কি কবিতার আঙ্গিকে বলাকা কাব্যগ্রন্থে ঘটে গেল পর্বান্তর। বিদেশি ব্ল্যাঙ্ক ভার্সকে বাংলায় এনেছিলেন মাইকেল মধুসূদন অমিত্রাক্ষর নামে আর সেই ছন্দমুক্তিকে রবীন্দ্রনাথ এগিয়ে দিলেন আরও এক ধাপ। তৈরি করলেন আরেক আঙ্গিকে, মুক্তক নামে। এই পথেই শেষ-জীবনে আধুনিক বাংলা কবিতা যখন গদ্যছন্দের সাধনা করছে, তখন রবীন্দ্রনাথও তাঁর মতো করে গড়ে নিলেন গদ্যছন্দ। কাব্য-সাহিত্যে প্রথম পর্বের রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ বদলে যাচ্ছেন আর হয়ে উঠছেন এক নতুনতর রবীন্দ্রনাথ। এই অভিযাত্রাতে রবীন্দ্রনাথ নিতুই নব।
আরও পড়ুন: রবিবার: কান্তাভাব থেকে ব্রহ্মভাবে উত্তরণ
এ এক দিক, যাকে বলছিলাম, কবির সৃজনলোকের বিবর্তন। এই বিবর্তন যতটা কৌতূহলপ্রদ, ততটাই গুরুত্বপূর্ণ শিল্পীরূপে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রগামী সত্তার বদলকাহিনিও। যে-রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কবি, কথাকার, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার আর গানের মানুষ, তিনিই জীবনের উপান্ত্য অধ্যায়ে তাঁর শিল্প-প্রকাশের নতুন পথ আবিষ্কার করছেন। তিনি জীবনের অন্য প্রান্তে ছবির ভাষাকে অবলম্বন করছেন নিজস্ব মনোলোকের চিত্ররূপ প্রকাশের আকাঙ্ক্ষায় আর এই শেষপর্বে তিনি তৈরি করছেন নৃত্যনাট্যের মতো এক অ-ভূতপূর্ব শিল্পরূপ। মনে পড়বে, আগে যখন নাটক লিখছিলেন, তখন প্রচলিত নাটকের ধরন দিয়ে সূচনা করেও ‘শারদোৎসব’ থেকে ইঙ্গিতধর্মী নাটকের পথ গ্রহণ করেন। সে যেমন এক বদল, সেই পথেই পরে লিখবেন ‘ডাকঘর’, ‘রক্তকরবী’, ‘মুক্তধারা’-র মতো সংকেতধর্মী নাটক। এই পথে নাট্যরচনার আরেক বদল ঘটল এক নতুন শিল্পসংরূপে— গান-নাটক-নৃত্যভাষার একত্র সংযোগে সৃষ্ট হল নৃত্যনাট্য। লিখলেন ‘শ্যামা’, ‘চিত্রাঙ্গদা’, ‘শাপমোচন’। (Rabindranath Tagore)

৩
(Rabindranath Tagore) এই জীবন- নির্মাণের সঙ্গে আছে কবির আরও এক বদলের গল্প। সেই বদলের কাহিনি লুকিয়ে আছে তাঁর গ্রন্থরচনার ধারাবাহিক। রবীন্দ্র-গবেষকরা জানেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘রক্তকরবী’ নাটকটির যে পাঠ আমরা দেখি, তার আগে তিনি নাটকটি প্রায় দশবার লিখেছিলেন। প্রথম যখন লিখেছিলেন তখন তাতে এই নাটকের প্রধান যে চরিত্র নন্দিনী, সে-ই ছিল না। ক্রমশ দ্বিতীয় পাঠ বাদ দিয়ে তৃতীয় পাঠে যুক্ত হয়েছিল এই চরিত্র। তার আগে এই নন্দিনীর নাম ছিল আবার খঞ্জিনী। রবীন্দ্রনাথের লেখা শেষ উপন্যাস ‘চার অধ্যায়’ প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ সালে। সেই উপন্যাসেরও যে রূপ আমরা এখন দেখি, তার আগে তার একটি পূর্ণাঙ্গ পাঠ তৈরি করেছিলেন তিনি। পরে তাকে পুরোটা বদলে, দেন তার নতুন রূপ। এমনকি, রবীন্দ্রনাথের লেখা বোধ করি সবচেয়ে জনপ্রিয় যে গ্রন্থ ‘গীতবিতান’, সেই বইটিকেও তো কবি প্রথম প্রকাশের পর আগাগোড়া পুরোপুরি বদলে দিয়েছিলেন। এখন যে ভাবে দেখি আমরা ‘গীতবিতান’, এই ধরনের পূজা, প্রেম, প্রকৃতি পর্যায়ে বিভক্ত ছিল না এই ‘গীতবিতান’-এর প্রথম পাঠ। তখন তা ছাপা হয়েছিল এক ধরনের রচনার কালানুক্রমে। সেই বই শুরু হয়েছিল ‘বাল্মীকি-প্রতিভা’ দিয়ে। তিনি সুধীরচন্দ্র করকে ডেকে পুরো গ্রন্থটি নতুন করে সাজালেন। বইয়ের গানগুলিকে চিহ্নিত করলেন বিভিন্ন পর্যায়ে। এমনকি পর্যায়ের মধ্যে আবার রাখলেন উপপর্যায়। যদিও এখনকার ‘গীতবিতান’-এ একমাত্র প্রকৃতি ছাড়া আর কোনও পর্যায়ের উপপর্যায়গুলি উল্লিখিত নয়। এই যে বদল, এ এক শিল্পীর সৃজনশীল সম্পাদনা-পদ্ধতি। তাকে মান্য করা দরকার ছিল বই কী! (Rabindranath Tagore)
আরও পড়ুন: যদি আমায় পড়ে তাহার মনে, বসন্তের এই মাতাল সমীরণে…
আরও কতভাবে যে বদলের মধ্য দিয়ে গ্রন্থ নির্মাণ করেন রবীন্দ্রনাথ। ধরা যাক, কাকা রবীন্দ্রনাথের কাছে ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী লিখেছিলেন যে সব চিঠিগুলি, তার পরিমার্জনা করে রবীন্দ্রনাথ তৈরি করে ফেললেন ‘ছিন্নপত্র’। সেখানেও কবির সেই পরিমার্জনাকে আমরা উত্তরকালে বুঝি যথাযথ মর্যাদা দিতে পারলাম না। উত্তরকাল ‘ছিন্নপত্র’-কে করে ফেললাম আমরা ‘ছিন্নপত্রাবলী’। রবীন্দ্রনাথ কখনও যে অংশগুলি বাদ দিয়েছিলেন, তাকে যুক্ত করা হল। কখনও যেখানে দুটি চিঠিকে একটি চিঠিতে সংহত করেছিলেন, সেগুলিকে আবার দুটি আলাদা চিঠিতে ভেঙে ফেললাম আমরা। রবীন্দ্রনাথের লেখা সব চিঠিগুলিকে একত্র করতে গিয়ে তাঁর সম্পাদনার অভিপ্রায়টি যে আমরা হারিয়ে ফেললাম! তার বেলা! এমন আরো ঘটেছে! (Rabindranath Tagore)
রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভ্রমণ-বিষয়ক একটি গ্রন্থ ‘পথের সঞ্চয়’ আর তাঁর সাহিত্যচিন্তা বিষয়ক একটি বই ‘সাহিত্যের পথে’-তে একটি নতুন ধরনে সাজিয়েছিলেন, তাঁর পূর্ব-প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ।
(Rabindranath Tagore) রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভ্রমণ-বিষয়ক একটি গ্রন্থ ‘পথের সঞ্চয়’ আর তাঁর সাহিত্যচিন্তা বিষয়ক একটি বই ‘সাহিত্যের পথে’-তে একটি নতুন ধরনে সাজিয়েছিলেন, তাঁর পূর্ব-প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ। লেখাগুলি যে ক্রমে লেখা হয়েছিল বা লেখাগুলি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যে ক্রমে প্রকাশিত হয়েছিল, তাকে বদলে লেখাগুলিকে নতুনতর এক বিন্যাসে সাজালেন। এমনকি, মনে আছে, ‘সাহিত্য’ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে পাঠক যাতে বুঝতে পারে, কোনটা আগে আর কোনটা পরে লেখা, তা বোঝাতে সূচিপত্রেই উল্লেখ করে দিয়েছিলেন লেখাগুলির প্রকাশকাল। এটা বেশ অদ্ভুত কিন্তু! সূচিপত্রে তো আর লেখার প্রথম প্রকাশকাল উল্লেখ করা হয় না সাধারণত। তবু তিনি তা করলেন, যাতে তাঁর বইয়ের পাঠক বুঝতে পারে, লেখাগুলি যে ক্রমে ছাপা হয়েছিল, সেই ক্রমে সাজানো হয়নি তাদের এই বইতে। কিন্তু পরে ঘটল কী! বইটির পরবর্তী সংস্করণ ছাপার সময়, যখন রবীন্দ্রনাথ আর নেই, তখন লেখাগুলিকে সাজানো হল রচনা প্রকাশের কালানুক্রমে। এখনও সেইভাবেই তাদের ছাপানো হয়। হারিয়ে গেল, কবির ঘটানো বদল। (Rabindranath Tagore)

(Rabindranath Tagore) বদলে দেওয়া সূচিপত্র বদলে ফেলে যে রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায়কেই আমরা অমান্য করেছিলাম, সেই পরিতাপ কী আমাদের থাকবে না? সেখানে এমনকি, ‘বাস্তব’ নামের একটি প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে অন্তর্ভুক্ত করার সময়, রবীন্দ্রনাথ পুরোটা সম্পাদনা করে সাধু থেকে চলিত বাংলা করেন। দেখা গেল, রচনার কালানুক্রমে সাজানোর জন্যে সেই প্রবন্ধটিকে আবার ফিরিয়ে দেওয়া হল তার সাধুভাষার পুরোনো চেহারায়। এই স্বাধীনতা আমাদের নেওয়া সমীচীন ছিল না। মনে রাখবেন আগ্রহী পাঠক, এই সমস্ত পরিবর্তন কিন্তু ঘটেছিল কবির গ্রন্থস্বত্বমুক্তির আগেই। সেখানে এমনও দেখা গিয়েছে যে, কবির লেখা ‘কালান্তর’ গ্রন্থটিতে বা তাঁর লেখা আরও অনেক গ্রন্থেই কবির জীবৎকালে যে প্রবন্ধগুলি ছিল, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরও বাড়তি লেখা। রবীন্দ্রনাথ যে লেখা সেখানে যুক্ত করেননি, সম্পূর্ণ রবীন্দ্রনাথকে পেতে গিয়ে, তাঁর লেখা সেই সব অগ্রন্থিত লেখাগুলিকেও যুক্ত করা হয়েছে মূল বইয়ের ভেতর! ফলে অন্যায্যভাবে বদলে গিয়েছে রবীন্দ্রনাথের বই। সে বদল কাঙ্ক্ষিত ছিল না, অসমীচীন ছিল! (Rabindranath Tagore)
আরও পড়ুন: নীরবে নিতান্ত অবনত বসন্তের সর্ব-সমর্পণ।
এখন রবীন্দ্র-রচনাবলী নিয়ে তাই নতুন করে ভাবনা শুরু হয়েছে। নতুন ভাবে সাজানো হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের বই। যথাসম্ভব সাবধানতার সঙ্গে সম্পাদনা করার বিষয়ে এক নতুন ভূমিকা নিতে হবে এই সময়ের সম্পাদককে। তাঁকে একদিকে তুলে আনতে হবে, পাণ্ডুলিপি থেকে কীভাবে চূড়ান্ত রূপ দিয়েছিলেন এক-একটি লেখা রবীন্দ্রনাথ। আর অন্যদিকে গ্রন্থ-পরিকল্পনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা কত যুক্তিযুক্ত ছিল, তার আবিষ্কারও করতে হবে এখনকার সম্পাদককে। এই নতুন যুগের সম্পাদনার কাজ ধীরে ধীরে শুরু হয়েছে। আরও বহু পথ অতিক্রম করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের জীবন আর তাঁর সৃজনে এই বিচিত্র পালা-বদলের কাহিনি সূত্র সন্ধান এক নতুন পথের দিশারি হোক। (Rabindranath Tagore)
তথ্যসূত্র
১। রবিজীবনী, ১-১০ খণ্ড, প্রশান্তকুমার পাল।
২। রবীন্দ্রজীবনী, ১-৪ খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
৩। রবীন্দ্র রচনাবলী, সার্ধশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
৪। রবীন্দ্র রচনাবলী, ১২৫ বর্ষ সংস্করণ, ষোড়শ খণ্ড, শঙ্খ ঘোষ লিখিত গ্রন্থ পরিচয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
শুভেন্দু দাশমুন্সী
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, স্যর গুরুদাস মহাবিদ্যালয়। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, গবেষক, সত্যজিৎ রায় বিশেষজ্ঞ। চিত্রনাট্যকার। গুপ্তধন সিরিজের সোনাদা চরিত্রের স্রষ্টা। গীতিকার। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত সার্ধশতবার্ষিক রবীন্দ্র রচনাবলীর সম্পাদক।