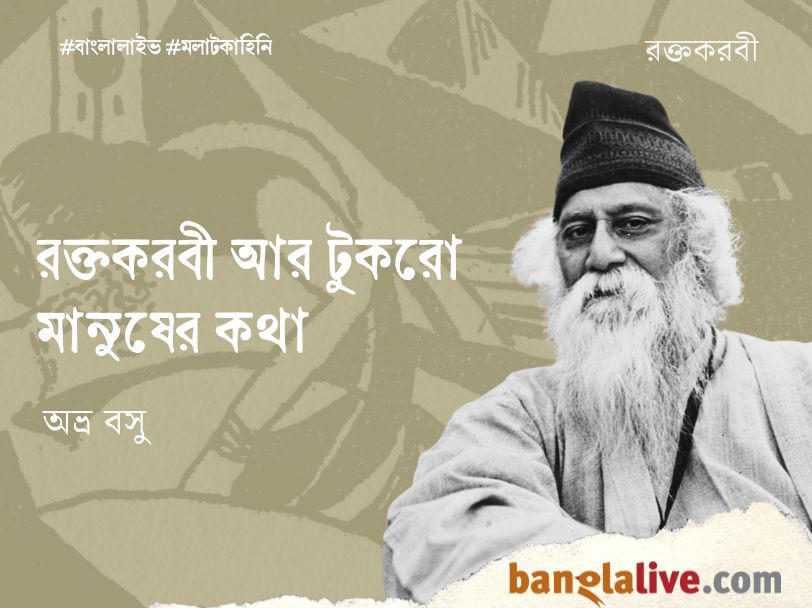(Raktakarabi)
রক্তকরবী নাটক লেখবার অনেকটা আগে, তিরিশ বছরেরও আগে, রবীন্দ্রনাথ সাধনা পত্রিকার ১২৯৮ সালের মাঘ সংখ্যায় (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৮৯২) একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, যার নাম ‘কর্মের উমেদার’। তাতে রবীন্দ্রনাথ মানুষ এবং যন্ত্র নিয়ে কিছু কথা উত্থাপন করে বলছেন: (Raktakarabi)
যন্ত্র সকল মানুষকেই ন্যূনাধিক সমান করিয়া দেয়। তাহাতে স্বাধীন নৈপুণ্য খাটাইবার স্থান নাই। জড়ের মতো কেবল কাজ করিয়া যাইতে হয়। (Raktakarabi)
আরও পড়ুন: রক্তকরবী আর শ্রীনিকেতন
এইরূপে সমাজে ধনী সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং নির্ধন একান্ত পরাধীন হইয়া পড়ে। এমনকি, সে যে-কাজ করে সে-কাজের মধ্যেও তাহার স্বাধীনতা নাই। পেটের দায়ে সে পৃথিবীর লোকসংখ্যার অন্তর্গত না হইয়া যন্ত্রসংখ্যার মধ্যে ভুক্ত হয়। পূর্বে যাহারা ওস্তাদ কারিগরের অধীনে কাজ করিত এখন তাহারা বৃহৎ যন্ত্রের অধীনে কাজ করে। (Raktakarabi)
রবীন্দ্রনাথ তার অল্প আগেই জমিদারি কাজের তদারকি করতে গিয়েছিলেন। শিলাইদহেই কাটছে বেশি সময়, মোটের উপর রোমান্টিক কবিতা, গল্পগুচ্ছ আর ছিন্নপত্রধারার চিঠিগুলি লিখেই তাঁর দিন কাটছে। কিন্তু শোষণের ছবিটা তখনই রবীন্দ্রনাথের কাছে স্পষ্ট। মানুষকে যন্ত্র সমান করে দেয়, এই কথাটা সারাজীবন ধরেই রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে বলবেন। ১৯১৬ সালে Personality গ্রন্থের ‘What is Art’ শীর্ষক ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলছেন বিজ্ঞান মানুষকে তার বিবিধতায় স্বীকার করে না। ফলে এক ধরনের সামান্যীকরণ বা generalization থাকে তার মধ্যে। তার দেখাতে সম্পূর্ণতা পাওয়া কঠিন। একটি চাকা যখন ঘোরে, তখন তার গতিটা বুঝতে গেলে তার প্রত্যেকটি দাঁড় বা spoke আর গোনবার উপায় থাকে না। কিন্তু যদি তা সজীব বস্তু হয়? (Raktakarabi)
Living things have far-reaching relationships with their surroundings, some of which are invisible and go deep down into the soil. In our zeal for definition, we may lop off branches and roots of a tree to turn it into a log, which is easier to roll about from classroom to classroom, because it allows a nakedly clear view of itself, it cannot be said that a log gives a truer view of a tree as a whole. (Raktakarabi)
“গাছকে আর গাছ বলে গণ্য করা হচ্ছে না। তাতে তার কার্যকারিতা একটা থাকছে, কিন্তু যেখানে ফুল ফোটে আর ফল ধরে, যেখানে তার সৃজনের ক্ষমতা, সেখানে তাকে পঙ্গু করে দেওয়া হয়। একই কাণ্ড তো ঘটে মানুষের ক্ষেত্রে যক্ষপুরীতে।”
সজীব মানুষের কথা রক্তকরবী-তে রবীন্দ্রনাথ কী নিবিড়ভাবে ভেবেছিলেন! যন্ত্র তাঁকে ন্যূনাধিক সমান করে তুলছে, তাঁর স্বাধীন নৈপুণ্য খাটাইবার জায়গা নেই। অর্থাৎ তাঁর ইচ্ছায় জগৎ চলছে না। ফলে সে স্বাভাবিক বিকাশে যেখানে ডাল-পালা-শিকড় মেলতে পারে, সেগুলোকে কেটেকুটে ন্যাড়া একটা অস্পষ্ট, ব্যক্তিত্ববিহীনরূপকেই হাজির করে যন্ত্র। এই যে log-এর কথা বললেন এই ভাষণে, সেই log-এর চরিত্রকে আরও তীক্ষ্ণ করে তুলে ধরেছিলেন ১৯১৭ সালের Nationalism-এর ভাষণে: (Raktakarabi)
Turn a tree into a log and it will burn for you, but it will never bear living flowers and fruits.
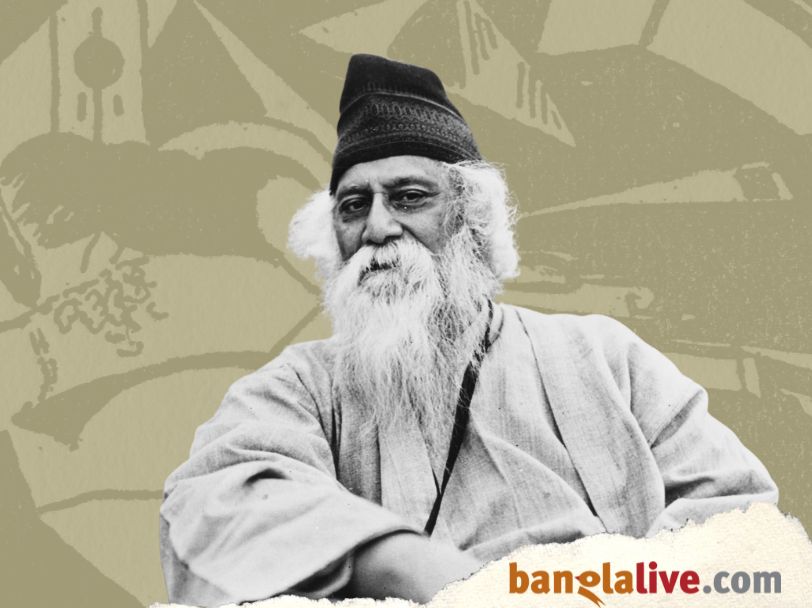
গাছকে আর গাছ বলে গণ্য করা হচ্ছে না। তাতে তার কার্যকারিতা একটা থাকছে, কিন্তু যেখানে ফুল ফোটে আর ফল ধরে, যেখানে তার সৃজনের ক্ষমতা, সেখানে তাকে পঙ্গু করে দেওয়া হয়। একই কাণ্ড তো ঘটে মানুষের ক্ষেত্রে যক্ষপুরীতে। সেখানে যাদের পিছনে পৃষ্ঠব্রণ হয়ে থাকার জন্য বিশুকে নিয়োগ করা হয়, তাকে বিশু সজীব মানুষ বলেই জানে। কিন্তু এই সজীব মানুষের সজীবতাটুকু বেঁচে থাকলে যক্ষপুরীতে চলবে কেন? সেখানে তো বেঁচে থাকার কোনও প্রয়োজনই নেই, টিঁকে থাকলেই হল। ফলে মানুষগুলো তো মানুষ নয়, সংখ্যা। রক্তকরবীর ইংরেজিতে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: (Raktakarabi)
This is a world where, with every available means in his power, the Great King exploits the resources of the underworld, of nature, of the mind, of science and of human physique and intelligence, using all the weapons of organization and the elaborate machinery of a highly centralized bureaucracy in order to add to his wealth. This wealth he measures in gold, or in souls or in facts, or in human bodies, so that men are men no longer but numbers. (Raktakarabi)
“চার্লি চ্যাপলিনের Modern Times সিনেমার প্রথম দৃশ্যটি মনে পড়াটা একেবারেই অবধারিত, যেখানে একপাল ভেড়ার পরেই সাবওয়ে দিয়ে পিলপিল করে উঠে আসে মানুষ, যন্ত্রের জাঁতাকলে আবদ্ধ মানুষ।”
পূর্ণ যৌবনে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন মানুষ ‘পৃথিবীর লোকসংখ্যার অন্তর্গত না হইয়া যন্ত্রসংখ্যার মধ্যে ভুক্ত হয়।’ বার্ধক্যে এসে সেই একই কথা কি বললেন না তিনি যে, যন্ত্রের গণনার পদ্ধতি ধনের পরিমাপ হয় মানুষের দেহ দিয়ে, যাতে men are men no longer but numbers – কেউ হয় ৪৭ ফ আর কেউ হয় ৬৯ ঙ? (Raktakarabi)
এই অনুষঙ্গে এই ভাবনা খুব অসংগত নয় যে, পুঁজির ইংরেজি হল capital! এই ক্যাপিটাল শব্দটি লাতিন caput থেকে যার অর্থ head বা মাথা। মধ্যযুগে, অর্থাৎ ফিউডাল ব্যবস্থায় মানুষের অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাপ হত গবাদি পশুর মাথা গুনে। তার থেকে পুঁজিবাদ যখন প্রবল আকার নিল, তখন সোনাদানা ছেড়ে মানুষের মাথাই হল পুঁজি বা capital: This wealth he measures in gold, or in souls or in facts, or in human bodies…। চার্লি চ্যাপলিনের Modern Times সিনেমার প্রথম দৃশ্যটি মনে পড়াটা একেবারেই অবধারিত, যেখানে একপাল ভেড়ার পরেই সাবওয়ে দিয়ে পিলপিল করে উঠে আসে মানুষ, যন্ত্রের জাঁতাকলে আবদ্ধ মানুষ। (Raktakarabi)
রক্তকরবী-র যক্ষপুরীতে দেখি মানুষকে সংখ্যা হয়ে যেতে দেখা যায় স্পষ্টভাবেই। চন্দ্রা যখন জানতে চায় যক্ষপুরীর কাজ কবে ফুরোবে, বিশু জবাব দেয়: (Raktakarabi)
“যক্ষপুরে অঙ্কের পর অঙ্ক সার বেঁধে চলেছে, কোনও অর্থে পৌঁছয় না। তাই ওদের কাছে আমরা মানুষ নই, কেবল সংখ্যা।”
পাঁজিতে তো দিনের শেষ লেখে না। একদিনের পর দুদিন, দুদিনের পর তিনদিন; সুড়ঙ্গ কেটেই চলেছি, এক হাতের পর দু হাত, দু হাতের পর তিন হাত। তাল তাল সোনা তুলে আনছি, এক তালের পর দু তাল, দু তালের পর তিন তাল। যক্ষপুরে অঙ্কের পর অঙ্ক সার বেঁধে চলেছে, কোনও অর্থে পৌঁছয় না। তাই ওদের কাছে আমরা মানুষ নই, কেবল সংখ্যা। (Raktakarabi)
কতকটা দুঃখ করেই বিশু বলে: “গাঁয়ে ছিলুম মানুষ, এখানে হয়েছি দশ পঁচিশের ছক। বুকের উপর দিয়ে জুয়োখেলা চলছে।” বিশু তো মানুষ, রক্তমাংসের ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ। যক্ষপুরী তাকে একটা সংখ্যা দিয়েছে বটে, কিন্তু সত্যি সংখ্যা সে হয়ে ওঠেনি। তাই সে বলে: (Raktakarabi)
একদিকে ক্ষুধা মারছে চাবুক, তৃষ্ণা মারছে চাবুক; তারা জ্বালা ধরিয়েছে, বলছে, কাজ করো। অন্য দিকে বনের সবুজ মেলেছে মায়া, রোদের সোনা মেলেছে মায়া, ওরা নেশা ধরিয়েছে, বলছে, ছুটি ছুটি। (Raktakarabi)
আরও পড়ুন: রক্তকরবী: বইয়ের শতবর্ষ, নাটকের নয়
অথচ যক্ষপুরীতে ছুটি বিষম বালাই। সুতরাং বিশু বলে মোক্ষম কথাটি: “মদের পেয়ালা নিয়ে ভুলে যাই ভাগ্যের গণ্ডির মধ্যে আমরা বাঁধা। মনে করি আমাদের অবাধ ছুটি।” (Raktakarabi)
ফাগুলালও বুঝেছিল সেটা। বলেছিল, “বনের মধ্যে পাখি ছুটি পেলে উড়তে পায়, খাঁচার মধ্যে তাকে ছুটি দিলে মাথা ঠুকে মরে।” অতএব ব্যবস্থা রয়েছে মদের, তাতে কাজ না হলে মদের ভাঁড়ারের পাশেই অস্ত্রশালা। তাতেও কাজ না হলে একেবারে গায়ে গায়েই রয়েছে মন্দির। ফাগুলাল বিশুর কথায় বুঝেছিল, যক্ষপুরীতে তারা মানুষ হিসেবে আর সম্পূর্ণ নেই, টুকরো হয়ে গেছে। চন্দ্রাকে বলে: (Raktakarabi)
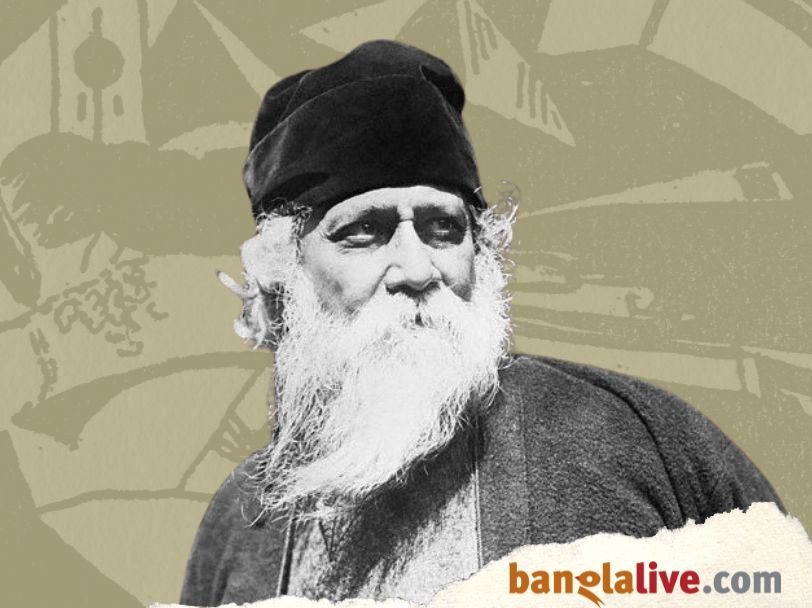
আমাদের বিশুপাগল বলে, আস্ত হয়ে থাকাটা কেবল পাঁঠার নিজের পক্ষেই দরকার; যারা তাকে খায়, তার হাড়গোড় খুরলেজ বাদ দিয়েই খায়। এমন-কি, হাড়কাঠের সামনে তারা যে ভ্যাঁ করে ডাকে, সেটাকেও বাহুল্য বলে আপত্তি করে। (Raktakarabi)
টুকরো করাটার একাধিক মাত্রা। অধ্যাপককে যখন বলতে শুনি, “জান নন্দিনী, আমিও আছি একটা জালের পিছনে? মানুষের অনেকখানি বাদ দিয়ে পণ্ডিতটুকু জেগে আছে। আমাদের রাজা যেমন ভয়ংকর, আমিও তেমনি ভয়ংকর পণ্ডিত। …সব জিনিসকে টুকরো করে আনাই এদের পদ্ধতি।” (Raktakarabi)
“নন্দিনী কি শুধুই নাম? নন্দিনী মানে তো মেয়ে, কন্যাও। যে কন্যা আনন্দ দেয়। সেই অনুষঙ্গে রঞ্জন বা কিশোরও হয়তো নিছক চরিত্র নাম নয়।”
শুধু অধ্যাপকটুকু জেগে আছে বলেই তো তার কোনও নাম নেই, সে শুধুই অধ্যাপক। যেমন সর্দার, মোড়ল এমনকী রাজা– সকলেই তাঁদের বৃত্তি নামে পরিচিত। যক্ষপুরীর যন্ত্রের অন্তর্গত সকলেরই একই চেহারা, নাম নেই তাদের। একমাত্র গোঁসাই-এর একটা নাম পাই নাটকে– কেনারাম গোঁসাই! সত্যিই কি এটা নাম? না তার বিশেষণ? (Raktakarabi)
টুকরো করার আরেকটা উপায়ও উদ্ভাবিত হয়েছে যক্ষপুরীতে। বিশু খবর দেয় যে “ওরা ঠিক করেছে এবার থেকে এখানে কারিগরের সঙ্গে তাদের স্ত্রীরা আসতে পারবে না” এর কারণটা সহজ: “সংখ্যারূপে ওদের হিসাবের খাতায় আমরা জায়গা পাই, কিন্তু সংখ্যার অঙ্কের সঙ্গে নারীর অঙ্ক গণিতশাস্ত্রের যোগে মেলে না।” Personality গ্রন্থের “Woman” প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: (Raktakarabi)
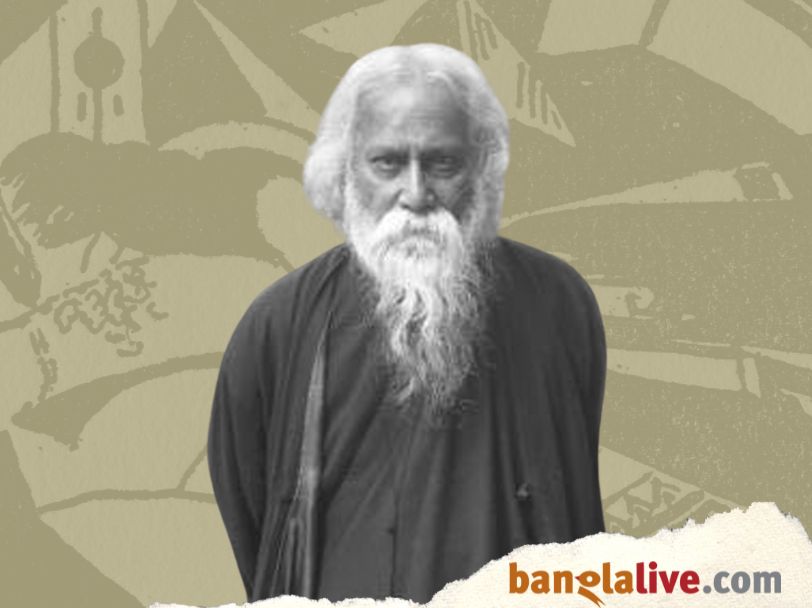
At the present stage of history civilization is almost exclusively masculine, a civilization of power, in which woman has been thrust aside in the shade. Therefore it has lost its balance and it is moving by hopping from war to war. … And at last the time has arrived when woman must step in and impart her life rhythm in this reckless movement of power. (Raktakarabi)
এই exclusively masculine ব্যবস্থায় নারীকে আসতেই হবে।
“রাজার সংলাপে বুঝতে পারি, রঞ্জন রাজার কাছেও যৌবনের প্রতীক। যৌবনকে কিশোরের থেকে টুকরো করে নিলে অখণ্ড মানুষটি থাকে কোথায়?”
রক্তকরবী-তে নন্দিনী আসে। নন্দিনীর নামটা রক্তকরবী-র বিভিন্ন পাঠে বিবর্তিত হয়েছে নানাভাবে। প্রথমে খঞ্জন বা খঞ্জনী ছিল রঞ্জনের সঙ্গে মিলিয়ে। কিন্তু দ্বিতীয় পাঠেই বদলে ফেললেন রবীন্দ্রনাথ। প্রথমে সুনন্দা নামটা ভেবেছিলেন। নন্দ্ ধাতুর মধ্যে আনন্দর অনুভবটা আছে। সুনন্দায় সেটাই মুখ্য। নন্দিনী নামটার মধ্যে সেই অনুষঙ্গটা রইল, কিন্তু সেই সঙ্গে নামটা অনেকটা ব্যাপ্ত হয়ে গেল। নন্দিনী কি শুধুই নাম? নন্দিনী মানে তো মেয়ে, কন্যাও। যে কন্যা আনন্দ দেয়। সেই অনুষঙ্গে রঞ্জন বা কিশোরও হয়তো নিছক চরিত্র নাম নয়। (Raktakarabi)
রক্তকরবী নাটকের শেষে নন্দিনী যখন আবিষ্কার করে রঞ্জনকে, রাজাকে তখন সে বলে, “আমাকে ঐ ঘুমেই ঘুম পাড়াও।” রাজা আক্ষেপ করে বলে “আমি যৌবনকে মেরেছি— এতদিন ধরে আমি সমস্ত শক্তি নিয়ে কেবল যৌবনকে মেরেছি। মরা-যৌবনের অভিশাপ আমাকে লেগেছে।” কিন্তু নন্দিনী রাজার সঙ্গে লড়াই-এর কথা ভাবেনি তখনও। কিন্তু যে মুহূর্তে সে শোনে ‘বালকের মতো …কচি মুখ’ কিশোর রাজার কারণে বুদ্বুদের মতো লুপ্ত হয়ে গেছে, তখন নন্দিনী বলে, “রাজা, এইবার সময় হল।…আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার লড়াই।” (Raktakarabi)
আরও পড়ুন: রক্তকরবী: নব্যপুরাণ রক্তকরবী ও কিছু মেয়েলি ভাবনা
রাজার মুখে যৌবনকে হত্যা করার কথার পরে নন্দিনীর প্রতিক্রিয়ার ভাবটিকে যদি বলি শম, তাহলে কিশোরের মৃত্যুর পরে নন্দিনীর ভাব পরিণত হয় উৎসাহে; শান্তরস থেকে সরে যায় বীররসের দিকে। তখন বুঝতে অসুবিধে হয় না আর, কিশোর নামমাত্র নয়, সে কৈশোরের ‘প্রাণঝরনার উচ্ছলধার’কেই ধারণ করে থাকে। সেই জন্যই দশম পাঠে কিশোর চরিত্রের অবতারণার আগে রবীন্দ্রনাথ বার-বার বদলেছেন রক্তকরবী-র খসড়া; আর একবার কিশোর সংযোজিত হয়ে যাওয়ার পরে নাটকটি নিয়ে দ্বিতীয়বার রবীন্দ্রনাথকে ভাবতে হয়নি! (Raktakarabi)
পূর্ণতায় পৌঁছনোর আকাঙ্ক্ষা রাজার সংলাপে ধরা পড়েছে কখনও কখনও। যৌবন বা পূর্ণতায় পৌঁছতে হলে কৈশোরের পথ ধরেই যেতে হয়। রাজার সংলাপে বুঝতে পারি, রঞ্জন রাজার কাছেও যৌবনের প্রতীক। যৌবনকে কিশোরের থেকে টুকরো করে নিলে অখণ্ড মানুষটি থাকে কোথায়? (Raktakarabi)
মুদ্রিত ও ডিজিটাল মাধ্যমে সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
অভ্র বসু। অধ্যাপক, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।