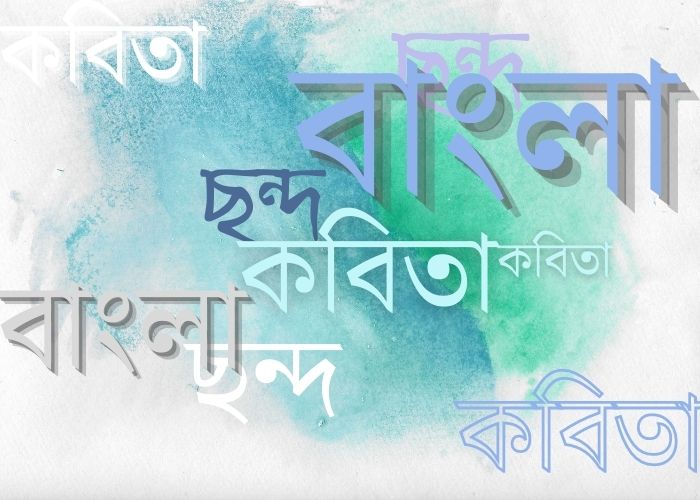মুখবন্ধ:
বহু বছর ধরে কবিতা-বিষয়ক পরিভাষা ও প্রাসঙ্গিক শব্দগুলির একটি নির্ভরযোগ্য সংকলন রচনার উদ্দেশ্য়ে বহু পরিশ্রমে কাজটি শুরু করেছিলাম। পূর্ণাঙ্গ শব্দকোশ রচনা তো এক অসম্ভব বিষয়, কিন্তু আমি চেয়েছিলাম, পরবর্তী কোন আগ্রহী গবেষক এ-নিয়ে প্রাণিত হন। কবিতা বিষয়ক একটি পত্রিকা উৎসাহের সঙ্গে ধারাবাহিক শব্দকোশটি প্রকাশ করতে শুরু করেছিল, কিন্তু নানা গোড়াতেই তা বন্ধ হয়ে যায়।
আমি কবি-লেখক তিলোত্তমা মজুমদারের আগ্রহে কাজটি নতুন করে শুরু করলাম। তাঁকে ভালবাসা। ওই পত্রিকায় লিখিত ভূমিকাটিও ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থাক। এই শব্দকোশ, আবার বলে রাখি, শুধু তরুণ প্রজন্মের উৎসাহীদের জন্য, পণ্ডিত বা গবেষকদের জন্য নয়। তাঁরাও খেয়াল রাখবেন আশা করি।
পরম শ্রদ্ধেয় ভাষাবিদ শ্রীযুক্ত সুভাষ ভট্টাচার্য আমাকে ব্যক্তিগতভাবে কাজটি শেষ করে তাঁর হাতে তুলে দিতে বলেছিলেন, সেটা আর পেরে উঠিনি। সুভাষদাকে অসীম কৃতজ্ঞতা।
[the_ad id=”270088″]
ভূমিকা:
ইংরেজিতে কবিতার পারিভাষিক শব্দগুলি নিয়ে একা্ধিক নির্ভরযোগ্য বই আছে। আর, শুধু কবিতার সমস্ত বিষয় নিয়ে তো এখনও অতুলনীয় ‘Princeton Encyclopaedia of Poetry and Poetics’। বাংলায় ‘সাহিত্যের শব্দার্থকোশ’ (সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়) বা ‘সাহিত্য সংজ্ঞার্থ অভিধান’ (বিমলেন্দু দাম)- এরকম দু-চারটি প্রামাণিক বই আছে বটে, কিন্তু শুধু কবিতার পারিভাষিক শব্দ নিয়ে কোনো বই খুঁজে পাওয়া মুশকিল।
এক-একটি প্রবিষ্টি (entry) নিয়ে দু-চার কথায় পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা অসম্ভব। তবুও, অভিধানের চিরাচরিত নিয়ম মেনে সেরকম প্রচেষ্টাই করা হল এই বিভাগে। এত করেও প্রতিটি শব্দ ধরে-ধরে কয়েক পঙ্ক্তি আলোচনাতেও দীর্ঘ সময় লেগে যাবে, কলেবরও হবে বিশাল। তাই নির্বাচিত শব্দসমুহই এ-বিভাগে স্থান পাবে।
বহু গ্রন্থের সাহায্য গৃহীত হয়েছে এ-কাজে। সবশেষে, সেসব গ্রন্থেরও একটি তালিকা (bibliography) সংযোজিত হবে, যাতে পাঠক তাঁর কৌতূহল নিরসনের সুযোগ পেতে পারেন। এখানে শুধু কৌতূহলটি জাগিয়ে তোলাই মুখ্য উদ্দেশ্য। বিশেষ করে, তরুণ প্রজন্মের কবি, কবিতা-অনুরাগী ও কাব্যের ছাত্রছাত্রীরাই এটির উদ্দিষ্ট পাঠক। এ-ব্যাপারে তাঁদের পরামর্শ ও মতামত খুবই দরকারি। তাঁরা সাড়া দেবেন, এটাই অনুরোধ। তাঁদের কারও যদি চোখে পড়ে এই বিভাগ, ত্রুটি উল্লেখ করে জানালে সংশোধন করে নেওয়া হবে।
কবিতার যেসব পঙক্তি উদাহরণ হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে, সেগুলি বিভিন্ন কবির নানা কবিতা থেকে গৃহীত। যেহেতু উদাহরণটিই মুখ্য তাই কবির নাম, কবিতার নাম ইত্যাদির উল্লেখ দরকারি বলে মনে হয়নি। কখনও-বা বানিয়ে-বানিয়ে উদাহরণ তৈরি করা হয়েছে। আবার, কবিতার পঙক্তি খোঁজার জন্যও সময় খরচ করা অনাবশ্যক মনে করে, বিভিন্ন বইয়ে যেসব উদাহরণের উল্লেখ আছে, সরাসরি তা গ্রহণ করেছি। বিশেষ করে পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের ‘ছন্দ-মীমাংসা ও অলংকার সমীক্ষা’ বইটি এক্ষেত্রে প্রভূত সাহায্য করেছে। সেখান থেকেই নেওয়া হয়েছে অধিকাংশ উদাহরণ।
আবার যেসব পরিভাষার উদাহরণ দেওয়া অপ্রয়োজনীয় মনে হয়েছে, দেওয়া হয়নি। কারণ, সে-পরিভাষাটির ব্যাখ্যাটুকুই হয়তো জেনে রাখা দরকার; ব্যবহারিক দিক দিয়ে তার কোনো গুরুত্ব নেই।
[the_ad id=”270086″]
অক্ষর:
কবিতার ছন্দরচনায় অক্ষরের গুরুত্ব অপরিসীম। সংস্কৃত এই শব্দ দিয়ে হরফ ও syllable দুই-ই বোঝায়। কিন্তু ইংরেজি syllable শব্দের পরিভাষা ‘অক্ষর’ করলে বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। প্রবোধচন্দ্র সেন গোড়ার দিকে ‘ধ্বনি’ বলতেন, কিন্তু রাজশেখর বসুর তাতে আপত্তি ছিল। ওঁর প্রশ্ন ছিল, “তবে sound বোঝাতে কী লিখব”? সতেন্দ্রনাথ দত্ত ‘শব্দপাপড়ি’ লিখতেন। অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ‘অক্ষর’ শব্দেরই পক্ষপাতী ছিলেন। প্রবোধচন্দ্র পরে ‘দল’ লিখেছেন, এটাই সাধারণভাবে গৃহীত। সংস্কৃত-ছন্দে লঘু ও গুরু অক্ষরবিন্যাসের একটি নির্দিষ্ট রীতি অনুযায়ী প্রকরণ আছে। বৈদিক-ছন্দে ওই রীতি কিছুটা শিথিল। প্রাকৃতে অক্ষরবিন্যাস দিয়ে ছন্দনির্ণয়ের রীতি নেই। অপভ্রংশ-ছন্দে তা বেশ শিথিল। বাংলা-ছন্দে অপভ্রংশের রীতিরই প্রভাব। বাংলায় লঘু-গুরু বা ‘গণ’ বিচার নেই।
অক্ষর ও syllable-এর তফাতটি কীরকম? ‘বদ্ধ’ এই শব্দটি ব+দ্ধ……এভাবে লিখলে অযুক্তাক্ষর বা যুক্তাক্ষর হয় কিন্তু syllable হিসাবে লিখলে লিখতে হবে……রুদ্ধদল ‘বদ’+মুক্তদল ‘ধ’; রুদ্ধদল ইংরেজিতে closed syllable, মুক্তদল open syllable। তাই প্রবোধচন্দ্রের বক্তব্য, “অক্ষর বা বর্ণকে ‘শব্দাংশ’ বা ‘বর্ণনির্মাণ’ বলা গেলেও সিলেব্ল্ বলা যায় না কিছুতেই”। রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল ‘অক্ষর’ মানে সিলেব্ল্ মানতেন না। ওঁরা ‘মাত্রা’ বলেছেন।
অক্ষরবৃত্ত: এ-ছন্দের আরও অনেকরকম নাম– তানপ্রধান, মিশ্রকলাবৃত্ত, মিশ্রবৃত্ত, অক্ষরমাত্রিক, বর্ণমাত্রিক। অক্ষরবৃত্ত নামটি প্রবোধচন্দ্রের দেওয়া, তানপ্রধান অমূল্যধনের। আরও অনেকে নানারকম নামে ডেকেছেন এই ছন্দটিকে। তবে, অক্ষরবৃত্তটাই চালু হয়ে গেছে বেশি। প্রবোধবাবু লিখেছেন : “অক্ষরবৃত্ত ছন্দের মূলে একটি ধ্বনিতত্ত্ব আছে। সেই তত্ত্বটি এই যে, অক্ষরবৃত্ত ছন্দের অন্তর্গত প্রত্যেকটি শব্দ শেষাংশে মাত্রাবৃত্তধর্মী ও অন্যাংশে স্বরবৃত্তধর্মী। সুতরাং অক্ষরবৃত্ত আসলে মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তের মিশ্রণজাত একটি যৌগিক ছন্দ”। তাঁর নিজের পছন্দ ছিল মিশ্রকলাবৃত্ত বা মিশ্রবৃত্ত নাম।
এ-ছন্দে এক-একটি অক্ষর এক-এক মাত্রার, এমনকী যুক্তাক্ষরও। এ-ছন্দের চাল দলবৃত্তের মতোই চার মাত্রার, কিন্তু দলবৃত্তে মাত্রার হিসেব আলাদা। অক্ষরবৃত্তের একটি পঙক্তি, যেমন “আলোকিত/পৃথিবীতে/অপরূপ/আমাদের/বেঁচে থাকা/টুকু”, এ-ছন্দে দু-মাত্রা উদ্বৃত্ত রাখতে হয়, তা-না-হলে পুরো কবিতা একনিশ্বাসে পড়ে যেতে হয়, সে খুব ঝামেলা। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী উদাহরণ দিয়েছিলেন :“বাজে লক্ষ ঢাকঢোল/চতুর্দিকে হট্টগোল/আর সহ্য হয় কত/প্রাণ হল ওষ্ঠাগত”। সত্যিই ‘হুলুস্থুলু’ ব্যাপার। তবে পরীক্ষামূলকভাবে, বা, পাকা কবি কৌশল করে এসব করতেও পারেন।
আমরা অনেকসময় বলি অমুক কবি ৮ মাত্রার করে তিনটি পর্বে কবিতাটি লিখেছেন! আসলে সেক্ষেত্রে দেখা যাবে, চার মাত্রার পর্বটি ভাঙলেও বেমানান লাগছে না: “মহাভার/তের কথা/অমৃত স/মান”, আর, অনেকসময় দেখতে যদি খারাপ লাগে দুটো পর্ব পরই ভাঙব, ৬+২=৮ মা্ত্রা করে নেব : “মহাভারতের কথা/অমৃত সমান”। কিন্তু একটা নিয়ম আছে, ৮-মাত্রার পর্ব করতে গেলে সত্যেন্দ্রনাথের সূত্রটি মাথায় রাখতে হবে : “বিজোড়ে বিজোড় গাঁথ, জোড়ে গাঁথ জোড়”। উপরের লাইনে যেমন জোড়ে-জোড়ে গেঁথে ৮ মাত্রা হয়েছে, তেমনি তিন-অক্ষরের পর তিন-অক্ষরের শব্দই রাখতে হবে: “অকূল কুন্তল পাশ-মেলে দিয়ে ক্লান্তির সাগরে”– ১+৩ বা ৩+৫ দিয়ে ৪ কিংবা ৮ মাত্রা করা যাবে না। ভাঙা তখন ব্যাকরণবিরুদ্ধ হয়ে যায়।
অক্ষরবৃত্তে একটা অক্ষর এক মাত্রা, যুক্তাক্ষরও একমাত্রা, কিন্তু ছন্দ বিশ্লেষণের সময় কীভাবে দেখাব? অসুবিধে আছে। তাই, বলা যাক, শব্দের মধ্যস্থিত রুদ্ধদল ১-মাত্রা, অন্তস্থিত রুদ্ধদল ২-মাত্রা; আর মুক্তদল তো সর্বত্রই ১-মাত্রা রইলই। তাহলে ছন্দ বিশ্লেষণে সমস্যা নেই। নীচের লাইনটিকে এভাবে scan করা যেতে পারে : “দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত”……
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
দূর দান্ তো পান্ ডিত্ তো পূর্ নো দুস্ সাধ্ ধো সিদ্ ধান্ তো
এবার ১৪ মাত্রার অক্ষরবৃত্তের উক্ত পঙ্ক্তিটির অক্ষর সংখ্যাও ১৪, গুনে দেখা যাচ্ছে। এখানে একটা কথা, কবিতার পঙ্ক্তিবিন্যাস অনুযায়ী কখনো-কখনো উচ্চারণ দিয়ে কোনো শব্দের মধ্যস্থিত রুদ্ধদলও ২-মাত্রা হতে পারে, যেমন: “তুমি বড়ো বদমাশ সারাদিন দুষ্টবুদ্ধি তোমার মাথায়”– এখানে ‘বদমাশ’ ৪-মাত্রা। কিন্তু যদি লিখি– “বদমাশ ছেলেটা আজ চুপচাপ শুয়ে আছে কেন”? — এখানে নিয়মানুযায়ী তিনমাত্রাই। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও স্পষ্ট বলেছেন, অক্ষরবৃত্তে মাত্রা টেনে বাড়ানো ঠিক নয়, “সাত মাত্রাকে গানের মতন টেনে আটমাত্রা পড়ার রীতি এখন নেই”। অর্থাৎ নীরেন্দ্রনাথের ভাষায় “কবিতা লিখতে গিয়ে লক্ষ রাখতে হবে, শব্দের উচ্চারণ আর ছন্দের চাল, এ-দুয়ের মধ্যে যেন ঠিকঠাক সমন্বয় ঘটে”।
অক্ষরবৃত্তের প্রচলিত ছন্দগুলি ছিল– একাবলী, পয়ার ও ত্রিপদী। যথাস্থানে এগুলি আলোচিত হবে। এখন শুধু উদাহরণ দিয়ে কাজ করা যাক :
একাবলী (৬+৫) : বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে
দেখা না হইত পরাণ গেলে।
পয়ার (৮+৬) : মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস ভনে শুনে পুণ্য়বাণ।।
ত্রিপদী (৬+৬+৮) : বিকচ কমলে যেন কুতূহলে
ভ্রমর পাঁতির দেখা।
এছাড়া মহাপয়ার, দীর্ঘত্রিপদীও রয়েছে।
[the_ad id=”270085″]
একটি প্রশ্ন, ৪-মাত্রা (বা ৮-মাত্রা) করে অক্ষরবৃত্তে কোনো কবিতার লাইনকে কতদূর টেনে নেওয়া যায়? ৮-মাত্রা ধরলে পয়ারে ১পর্ব, মহাপয়ারে ২পর্ব, অন্যান্যক্ষেত্রে আরও বাড়ানো যায়। কিন্তু কতটা? জীবনানন্দ ৫-পর্ব শেষে দু-মাত্রা উদ্বৃত্ত রেখে মোট ৪২-মাত্রার লাইন লিখেছেন: “অনেক দিনের গন্ধে ভরা ওই ইঁদুরেরা জানে তাহা– জানে তাহা নরম রাতের হাতে ঝরা এই শিশিরের জল”।
মাত্রাবৃত্তের মতোই অক্ষরবৃত্ত ছন্দেরও উৎস নিহিত ছিল অপভ্রংশের কিছু ছন্দে। পাদাকুলক ও মরহট্টা ছন্দই বিবর্তনের পথ ধরে অক্ষরবৃত্ত হয়েছে।
অক্ষরবৃত্ত ছন্দের অনেক সম্ভবনা। এ-ছন্দে (এবং অন্যান্য ছন্দেও) ভাল দখল থাকলে গদ্যছন্দে কবিতা লেখায় আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়। ছন্দ না-জেনে যাঁরা গদ্য কবিতা লেখেন, তাঁদের অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি থাকে, ভাবে-ভাষায়-প্রকরণে। অক্ষরবৃত্তে নিপুণ হলে কথ্য-চলিত বাক্যেও কবিতা লেখা যায়, ভাবগম্ভীর্যেও অটুট থাকা যায়। শৈলী হয়ে ওঠে স্মার্ট-ঝকমকে-গতিসম্পন্ন এবং হৃদয়সংবেদী উভয়তই।
জন্ম গড়শিমুলা গ্রামে (অধুনা জামতাড়া জেলা)। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের চাকরি থেকে স্বেচ্ছাবসর নিয়ে ২০০১ সাল থেকে লেখালেখির কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। কবি, প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক। ২০০৯ সালে অনুবাদের জন্য পেয়েছেন সাহিত্য একাডেমি পুরষ্কার। এ ছাড়াও পেয়েছেন অন্যান্য সম্মান ও পুরষ্কার। রয়েছে বারোটির বেশি প্রকাশিত গ্রন্থ।