১৭৫৭ সাল। মুর্শিদাবাদের পলাশী প্রান্তর। ইংলন্ড থেকে আগত, বলতে গেলে প্রায় বাপে তাড়ানো মায়ে খেদানো বখাটে আর প্রচন্ড ডাকাবুকো এক ইংরেজ ছোকরা রবার্ট ক্লাইভের সামান্য কিছু সৈন্যের হাতে বলতে গেলে প্রায় গো-হারান হারলো নবাব সিরাজদৌলার বিশাল সেনাবাহিনী। আর এই পরাজয়ের মধ্যে দিয়েই বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষই প্রায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বকলমে ব্রিটিশ শাসকদের হাতের মুঠোয় চলে এসছিল বলা চলে। অতঃপর ভাগ্যান্বেষণে এদেশে চলে আসা এক দুর্দমনীয়, দুঃসাহসী ইংরেজ যুবক কিভাবে রবার্ট থেকে লর্ডে পরিণত হলেন, হয়ে উঠলেন সারা দেশে সবচেয়ে ক্ষমতাবান ব্রিটিশ রাজপুরুষদের মধ্যে একজন, কোন জাদুতে একদা তাঁর নিজস্ব শূন্য ভান্ডার ভরে উঠেছিল অযুত কোটির ধনসম্পদে, কেন যুদ্ধের দিন নবাবের বিশাল সেনাবাহিনীর এক বৃহদাংশকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় রেখে পলাশী যুদ্ধপ্রান্তরের একপাশে চুপটি করে দাঁড়িয়েছিলেন নবাবের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড জনাব মিরজাফর মহাশয় – এসবের কোনটাই এই অধম প্রতিবেদকের আলোচনার বিষয়বস্তু নয়। এর জন্য অনেক জ্ঞানীগুণী আর ইতিহাসবেত্তা পন্ডিতেরা রয়েছেন। এক্ষেত্রে আলোচনার প্রেক্ষাপটটা একটু অন্যধরণের। সে প্রসঙ্গেই আসছি এবার।
এই কলকাতা শহরটা যে গোড়া থেকেই এদেশে ব্রিটিশ প্রভুদের সর্বাধিক পছন্দের জায়গা ছিল, এর আগে একাধিক লেখায় বলেছি সেকথা। বাঙলার পতনের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সমগ্র দেশে একচেটিয়া, নিরঙ্কুশ শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হবার পরেই শ্বেতাঙ্গ শাসকরা যে কটি বিষয়কে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তাঁর মধ্যে অন্যতম – মুঘল আমলের রাজধানী দিল্লী থেকে সমস্ত কেন্দ্রীয় ক্ষমতা স্থানান্তরিত করে তাদের প্রিয় ‘ক্যালকাটা’-য় নিয়ে আসা। আর এর ফলস্বরুপ ক্ষমতা দখলের মাত্র পনের বছরের মধ্যে, ১৭৭২ সালে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানীর তকমা পায় এই শহর। ফলে এই নগরীর চারদিকে অতি দ্রুত গজিয়ে উঠতে থাকে অসংখ্য হাটবাজার, বিপণী, সরকারি-বেসরকারি দফতর, লোকালয়, পতিতালয়, এদেশীয় এবং শ্বেতাঙ্গদের আলাদা আলাদা পাড়া। ধীরে ধীরে এর পাশাপাশি চালু হতে শুরু করে এক ভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান – সরাইখানা এবং হোটেল-রেস্তোরাঁ। প্রথমে তা বিদেশ থেকে এদেশে আসা মানুষজনের প্রয়োজন চরিতার্থ করার কারণে হলেও অতি দ্রুত শহরবাসী, বিশেষত কলকাতার ধনী বাবু সম্প্রদায়ের কাছে প্রচন্ড জনপ্রিয় হয়ে ওঠে প্রধানত দুটি কারণে। ব্যয়বহুল বিদেশি খাদ্য এবং মদ্য। সেইসব প্রসঙ্গেই আসব এবার।
১৮৩০। মধ্য কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হল এ শহরের প্রথম হোটেল কাম রেস্তোরাঁ স্পেন্সারস হোটেল। আর এর ঠিক দশ বছর পরে অর্থাৎ ১৮৪০ সালে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানীর বুকে আত্মপ্রকাশ করলো আরেক কিংবদন্তী সরাইখানা – গ্রেট ইস্টার্ন! এই দুই হোটেলের বিদেশী সুরা এবং ইয়োরোপীয়, মূলত ব্রিটিশ ঘরানার খাদ্যসম্ভারে আকৃষ্ট হয়ে শুধু বিদেশী তথা ব্রিটিশরাই নয়, এদেশীয় ধনী উচ্চবিত্ত বাবু সম্প্রদায়ও দলে দলে ভিড় জমাতে শুরু করলেন এই দুই হোটেলে। এদের স্টেক, রোস্ট আর ওয়াইন অথবা স্কচের স্বাদ গ্রহণ করাটা অভিজাত্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়ালো কলকাতার বাবুদের কাছে। তবে দুটি হোটেলই খুব দ্রুত জনপ্রিয়তা আর ব্যবসায়ীক সাফল্যের চুড়ায় পৌঁছলেও জন্মলগ্নের বছরকয়েকের মধ্যেই একটি ক্ষেত্রে স্পেন্সারসকে টেক্কা দিয়ে গেল গ্রেট ইস্টার্ন।
ডেভিড উইলসন ও গ্রেট ইস্টার্ন লোফ
বিখ্যাত ব্রিটিশ বেকার ডেভিড উইলসন। মধ্য কলকাতার কসাইটোলা অধুনা বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে একটা রুটির বেকারি ছিল ভদ্রলোকের। পরবর্তীতে উনি অকল্যান্ড হোটেল নামে একটি রেস্তোরাঁও খোলেন ওই অঞ্চলে। এহেন উইলসন সাহেবকে বিপুল অর্থের চুক্তির বিনিময়ে তাদের বেকারি বিভাগের প্রধান পরামর্শদাতা (চিফ অ্যাডভাইসারি শেফ) হিসাবে নিযুক্ত করে গ্রেট ইস্টার্ন। শুরু হয় এক নতুন ইতিহাস। যা এ শহরের বেকারি শিল্পের দুনিয়ায় এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল বলা চলে।

গ্রেট ইস্টার্নের মত ধনী মদতদাতার সাহায্যে তাঁর আজন্মলালিত স্বপ্নগুলোকে সাকার করতে উঠেপড়ে লাগেন উইলসন সায়েব। ইংলন্ড থেকে আমদানি করে একটি বিশাল টু স্টোরিড বেকিং ওভেন নিয়ে আসেন গ্রেট ইস্টার্নে। জন্ম হয় শহর বিখ্যাত গ্রেট ইস্টার্ন লোফ বা ব্রেডের। গোদা বাংলায় যার নাম পাঁউরুটি। পা দিয়ে দলেমেখে তৈরি হয় তাই ‘পাওরুটি’ বা ‘পাঁউরুটি’ এরকম একটা আজগুবি, কিম্ভূতকিমাকার ধারণা তৎকালীন বঙ্গসমাজে সল্পসময়ের জন্য থাকলেও খুব দ্রুত কেটে যায় সেটা এবং জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌছয় অনতিবিলম্বে। শুধু উচ্চবিত্ত নয়, এই পাঁউরুটির ডানায় ভর দিয়ে বাঙালি মধ্যবিত্তের দরজায় দরজায় পৌঁছে যায় গ্রেট ইস্টার্ন। শুরু হয় দোকানে দোকানে বিপণন। সেই ষাটের দশক, ভোরবেলা শ্রীমানি বাজারের সামনে হোটেলের নিজস্ব ভ্যানগাড়ি থেকে নামছে গ্রেট ইস্টার্ন ব্রাউন অথবা মিল্ক ব্রেড, এ দৃশ্য আজও জীবন্ত ষাট টপকানো এই অধম প্রতিবেদকের স্মৃতিতে। রুটি ছাড়াও শহরজোড়া খ্যতি ছিল গ্রেট ইস্টার্নের কেক, পেস্ট্রি আর প্যাটিসের। ক্রিসমাস বা নিউ ইয়ার্স ইভের সময় পেস্ট্রি কিনতে হোটেলের আউটলেটে আমবাঙালির দীর্ঘ লাইন, শহরের অনেক প্রবীণকে জিগ্যেস করলেই এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে।
এক সে বঢ় কর এক সাহেবী খানা, সুরা অথবা কেক -পাঁউরুটির জন্য তো বটেই, রেসিডেন্সিয়াল হোটেল হিসাবেও গ্রেট ইস্টার্নের খ্যাতি ছিল কলকাতা তথা দেশজোড়া। এমনকি দেশের সীমানা ছাড়িয়ে সে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল আন্তর্জাতিক স্তরেও। বিভিন্ন সময় এ হোটেলের আতিথ্য গ্রহণ করেছেন জগদ্বিখ্যাত সাহিত্যিক মার্ক টোয়েন, ইংলন্ডেশ্বরী দ্বিতীয় এলিজাবেথ, ক্রুশ্চভ, বুলগানিন, হো চি মিনের মত রাষ্ট্রনায়কেরা। কালগ্রাসে হোটেল স্পেন্সারস তার অতীত জৌলুশ হারালেও গ্রেট ইস্টার্নের রমরমা বজায় ছিল ষাটের দশকের একদম শেষভাগ পর্যন্ত। অতঃপর শুরু হয় ক্ষয় এবং পতনের পালা। কেন? সে প্রসঙ্গে পরে আসব।

এবার একটা গুরুমারা বিদ্যের গপ্পো শোনাই। ভাইসরয় আর্ল অফ মেয়োর ব্যক্তিগত রাঁধুনি থুড়ি শেফ হয়ে কলকাতায় এসেছিলেন ফ্রেদেরিকো পেলেত্তি নামে এক ইতালিয়ান। পরবর্তীতে অর্থাৎ ১৮৯০ সালে স্বাধীনভাবে রেস্তোরাঁর ব্যবসা শুরু করেন ভদ্রলোক। দুর্দান্ত রান্নাবান্নার জন্য অচিরেই বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে সেটি। এহেন পেলেত্তির সহকারী শেফ ছিলেন এঞ্জেলো ফিরপো নামে আরেক ইতালিয়ান। দীর্ঘকাল ফ্রেদেরিকোর শাকরেদ ছিলেন ফিরপো সায়েব। গুরুর কাছে শিখেছিলেন ইওরোপীয়-ইতালিয়ান ম্যাজিক কুইজিনের অনেক টপ সিক্রেট। খুব স্বাভাবিকভাবেই মনের কোনে নিজস্ব একটি রেস্তোরাঁর স্বপ্ন পুষে রাখা ছিল বহুদিন ধরে। সে সুযোগ এসেও গেল একদিন। ১৯১৭ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আবহের মধ্যেই চৌরঙ্গী রোডের ওপর নিজস্ব একটি রেস্তোরাঁ খুলে বসেন ফিরপোসায়েব। নাম দেন নিজের নামেই – ফিরপোজ। খ্যাতিতে কিছুদিনের মধ্যেই গুরু ফ্রেদেরিকোকে কয়েকশ কদম পিছনে ফেলে দেন শিষ্য এঞ্জেলো। অসামান্য পাঁউরুটি আর কেক পেস্ট্রির জন্য ফিরপোর খ্যাতি ছড়িয়ে পরে শহর জুড়ে। ফিরপোর ব্রেডলোফ আর কেকপেস্ট্রির সম্ভারপূর্ণ বিশাল শো রুম বিদেশের বহু নামীদামী বেকারি মালিকদের কাছেও রীতিমত ঈর্ষার কারণ ছিল সেসময়। তবে শুধুমাত্র কেক-পেস্ট্রি আর পাঁউরুটিতেই আটকে থাকার বান্দা ছিলেন না এঞ্জেল ফিরপো। অনতিবিলম্বে বেকারির পাশাপাশি খুলে বসেন ফিরপোজ বার কাম রেস্তোরাঁ। সেটিও যে অতি দ্রুত জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছয়, সে কথা বলাই বাহুল্য। বিশেষভাবে তাদের থ্রি কোর্স আর ফাইভ কোর্স লাঞ্চ অথবা ডিনার। যা বিখ্যাত ছিল ‘তেবল দি হোতে’ নামে। কি বিপুল সে খাদ্যসম্ভার! ১৯৪৩ সালে ফিরপোর এরকমই একটি মেনুচার্ট বা খাদ্যতালিকায় চোখ বোলানো যাক এবার। সেটি এইপ্রকার – স্টেক অ্যান্ড কিডনি পুডিং। স্প্যাগেটি। হ্যামবার্গার অ্যান্ড অনিয়ন। পমফ্রেট ফিলে উইথ টার্টার সস। রোস্টেড ল্যাম্ব উইথ গ্রিলড পট্যাটো। সসেজ উইথ ম্যাশড পট্যাটো। রোস্ট টার্কি/ ফাউল/ পোর্ক/ ডাক উইথ গ্রিন সালাদ অ্যান্ড স্টিমড পিস (মটরশুঁটি)। ফাইভ কোর্স লাঞ্চের সঙ্গে আবার এক পাত্তর স্কচ সৌজন্যমূলক, পাতি বাংলায় যাকে বলে গিয়ে – ‘অ্যাকদম ফিরি!’ পরবর্তী পেগগুলো যে গাঁটের কড়ি খসিয়েই নিতে হতো, সে কথা বলাই বাহুল্য।

ফিরপোর এই শহরবিখ্যাত তেবল দি হোতে অর্থাৎ তিন পদ বা পাঁচ পদের মেনু চার্টের মধ্যে কোনদিন কোন তিনটি অথবা পাঁচটি খাদ্যপদ গ্রাহকদের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে, সে সিদ্ধান্ত ছিল একান্তভাবেই রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষের। সেসময় একজন অথবা দুজনের থ্রি কোর্স / ফাইভ কোর্স লাঞ্চ / ডিনারের জন্য খরচ পড়ত ৬ থেকে ১৮ টাকা।
কিন্তু নিজেকে একটা নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে বেঁধে রাখা ধাতেই ছিল না ফিরপোসায়েবের। আর এরই ফলশ্রুতিতে জন্ম নেয় ফিরপো হোটেলের শহর কাঁপানো নাচঘর – লিডো রুম। ৬০-এর দশকে এখানেই নাচতেন সেসময় শহরের এলিট আর সেলিব্রেটি সম্প্রদায়ের বুকের বাঁপাশে উথালপাথাল তুফান তোলা এক বঙ্গতনয়া ! আরতি দাস ওরফে মিস শেফালি। সাধারন ছুটিছাটার দিনে পরপর তিনটে আর ক্রিসমাস ইভ বা থার্টি ফার্স্ট নাইটে টানা ছটা ক্যাবারে শো চলতো লিডো রুমে। বিভিন্ন সময় লিডো রুমের আতিথ্য গ্রহণ করেছেন নেপালের রাজারানী থেকে শুরু করে মহানায়ক উত্তমকুমার হয়ে একাধিক ক্ষেত্রের বহু রথী মহারথীরা।
কথায় বলে সবকিছুর উত্থান বা পতনের পিছনে নির্দিষ্ট কিছু কার্যকারণ থাকে। গ্রেট ইস্টার্ন বা ফিরপোর পতনটা শুরু হয়েছিল নকশাল আমলের হাত ধরে।
সব দিন কাহারও সমান নাহি যায়
সেটা ৭০ দশক। উত্তাল ঝোড়ো সময় ! গোটা শহরটা যেন ফুটন্ত আগ্নেয়গিরি একটা। দেয়ালে স্টেনসিলে আঁকা মাওয়ের মুখ। তলায় লেখা – ‘চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান !’ রাতের অন্ধকারে রাস্তায় পড়ে থাকা তরুণ যুবক অথবা পুলিশ কনস্টেবলের রক্তমাখা লাশ। সিনেমা হলে নাইট শো বন্ধ। সন্ধেবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাতবিরেতে আর বাড়িতে ফেরা যাবে কিনা এই মারাত্মক দমচাপা ভয়টা শিরদাঁড়ায় ঠান্ডা স্রোত নামিয়ে দিল সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে উচ্চবিত্ত অভিজাত নব্যবাবু সম্প্রদায়ের মধ্যে। রাতের পর রাত ফাঁকা পড়ে থাকতে থাকতে চরম লোকসানের সম্মুখীন হয়ে পড়ল হোটেল রেস্তোরাঁগুলো। শুধু গ্রেট ইস্টার্ন বা ফিরপো নয়, পার্ক স্ট্রিট-চৌরঙ্গীর সেই বিখ্যাত ‘নাইট লাইফ’-টাই বলতে গেলে প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছিল, নকশাল আমলের ওই গোটা তিনচার বছরে। এর সঙ্গে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মত যোগ হয়েছিল হোটেল ব্যবসার ওপর চাপিয়ে দেয়া গাদাখানেক নয়া নয়া সরকারি ট্যাক্স আর ক্যাবারে নাচের ওপর হাজারটা নিয়মকানুনের নিষেধাজ্ঞা। ফলে ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টাটুকুও করতে পারেনি গ্রেট ইস্টার্ন, ফিরপোর মত এ শহরের কিংবদন্তী হোটেলগুলো। ফিরপো হোটেলকে পরবর্তীতে ফিরপো মার্কেটে পরিণত করেন মালিকেরা। ঝুলবারান্দাওয়ালা সেই বিখ্যাত ওপেন এয়ার ব্যালকনি কাম ডাইনিং লাউঞ্জের জীর্ণ আর ক্ষয়িষ্ণু স্মৃতি নিয়ে চৌরঙ্গী রোডের বুকে আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে ফিরপো রেস্তোরাঁ। অন্যদিকে ধুঁকতে ধুঁকতে একদিন বন্ধই হয়ে যায় গ্রেট ইস্টার্ন। দীর্ঘদিন বন্ধ হয়ে পড়ে থাকার পর এক অবাঙ্গালী হোটেল ব্যবসায়ী তথা শিল্পপতি গোষ্ঠীর মালিকানায় চলে এসেছে বছরকয়েক হল। ভবিষ্যৎ কী তা ভবিষ্যৎই বলবে। তবে এপ্রসঙ্গে একটা কথা না বললে বোধহয় তথ্যনিষ্ঠার প্রতি অবিচার হবে। যে নকশালরা চৌরঙ্গী-পার্ক স্ট্রিট অঞ্চলে কোনওদিন একটা কালীপটকাও ছুঁড়ে মারতে যায়নি, সেই তাদের ঘাড়েই এসে পড়েছিল কলকাতার নৈশজীবন ধ্বংসের দায়, ঘটনার চরম দুর্ভাগ্যজনক দিক বোধহয় এটাই। আবার সেসময় শহরজোড়া আতঙ্ক আর ত্রাসের আবহটাকেও অস্বীকার করা যাবেনা কিছুতেই। অনেকের কাছে অস্বস্তিকর হলেও চরম সত্যি এটাও।

যাকগে, কি আর করা ! স্মৃতির সরণী ধরে এগোনো যাক ফের। ব্রিটিশ আমল শুধু ইংরেজ ঘরানাকেই ধারণ করে নিয়ে আসেনি তাদের এই প্রিয় শহরটায়। এক বিশাল আন্তর্জাতিক আবহের সিংহদরজাটাও খুলে দিয়েছিল কল্লোলিনী তিলোত্তমায়। পার্ক স্ট্রিটের মুখেই দাঁড়িয়ে থাকা পিপিং। মানে পিপিং রেস্তোরাঁ। এ শহরে চাইনিজ ডেলিকেসির আদিতম ঠিকানাগুলোর মধ্যে একটা। আজো মুখে লেগে রয়েছে সেই কোন ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে গিয়ে ওদের সেই ঝাল ঝাল লাল কাঁচালঙ্কা চেরা চিকেন মাঞ্চুরিয়ানের স্বাদ। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে ৬২ সালে কিংবদন্তী এই রেস্তোরাঁ এক পাঞ্জাবী শ্রেষ্ঠীর কাছে বেচে দিয়ে প্রবাসে (সম্ভবত হংকংয়ে) পাড়ি জমান পিপিং-এর চিনা মালিকরা। খুব সম্ভবত তৎকালীন ভারত চীন-যুদ্ধের আবহে শঙ্কিত হয়ে। আর এর পর থেকেই ক্রমাগত তার অতীত গৌরব হারাতে হারাতে ম্যাড়মেড়ে জৌলুশহীন হয়ে পড়ে পিপিং।
ট্রিংকাস, ম্যুলা রুজ আর ম্যাগনোলিয়া
অতঃপর আসি আরও তিনটে সরাইখানা তথা মধুশালার কথায়। ট্রিংকাস, ম্যুলা রুজ আর ম্যাগস। সাহেব জমানায় বার কাম রেস্তোরাঁর দুনিয়ায় তিন উজ্জ্বল নক্ষত্র ! এর মধ্যে ট্রিংকাস। ব্রিটিশ কলকাতায় তার যাত্রা শুরু করেছিল একটা কফি আর কেক পার্লারের মধ্যে দিয়ে। অচিরেই তা পরিণত হয়েছিল মধুশালা এবং সরাইখানা নামক এক মহীরুহে। অসাধারন সব খাবারদাবারের সঙ্গে দুনিয়ার যত নশিলা দারুশিল্পের সে এক স্বর্গীয় আয়োজন। এর পাশাপাশি দুর্দান্ত ব্যান্ড টিম ! এখানেই একদা গেয়ে গেছেন এ শহরের পপ সম্রাজ্ঞী পাম ক্রেইন, একদা আগুনে নকশালপন্থী গৌতম চট্টোপাধ্যায়, মহিনের ঘোড়ার মনিদা, কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর গিটার বাজিয়ে তাঁর জীবিকা অর্জন করেছেন এই ট্রিংকাসেই। এখানেই পারফর্ম করেছে কলকাতার ব্যান্ডপ্রেমীদের হার্টথ্রব ব্যান্ড – শিবা। কালক্রমে সেই ব্যান্ড টিম তার অতীত জৌলুশ হারালেও বার কাম রেস্তোরাঁ হিসাবে ট্রিংকাসের খ্যাতি আজও অম্লান !

ম্যুলাঁ রুজ। ব্রিটিশ জমানার পার্ক স্ট্রিটের আরেক মনমোহিনী আকর্ষণের নাম। নামকরণ হয়েছিল প্যারিসের জগদ্বিখ্যাত ক্যাবারে হাউসের নামে। দুর্দান্ত স্টেক আর ওয়াইন আর মুল্যাঁ রুজ – সমার্থক তিনটে নাম ছিল একদা এই শহরের সুরা এবং খাদ্যরসিক মহলে। বর্তমান হালচাল জানা নেই।
ম্যাগনোলিয়া। সংক্ষেপে ম্যাগস। পার্ক স্ট্রিটের ওপর, মুল্যাঁ রুজের ঠিক উল্টোদিকে। সেই কবে কলকাতাবাসীকে হ্যামবার্গারের স্বাদ চিনিয়েছিল এই বহুজাতিক রেঁস্তোরা। এছাড়াও ম্যাগনোলিয়ার সেই স্বর্গীয় স্বাদের আইসক্রিম ! খ্যাতি যার ভুবনজোড়া। শুধু পার্ক স্ট্রিটের রেস্তোরাঁয় নয়, পাড়ায় পাড়ায় কাঠের গাড়িতে করে বিক্রি হত এই দেবভোগ্য পদ। এ শহরে ৬০-৭০ পেরোনো অনেক প্রবীনের স্মৃতিতেই আজো উজ্জ্বল ম্যাগনোলিয়ার সেই পাকা আমরঙা সেই কাঠের গাড়ি। গাড়ির গায়ে কালো লেটারহেডে একটু টানা আর ত্যারচাভাবে লেখা কোম্পানির সেই সিগনেচার লোগো – ম্যাগনোলিয়া।
১৯২৭ সালে পার্ক স্ট্রিটের ঘাটে নোঙর ফেলেছিল ফ্লুরিজ। সেরা সব ফ্রুট কেক, রিচ পাম কেক, অ্যাসরটেড পেস্ট্রি, চিজ স্ট্র, ব্ল্যাক ফরেস্ট আর পাইনঅ্যাপল পুডিং-এর ডালি নিয়ে। বিশাল কাঁচের দেয়ালের পিছনে বসে কেক-প্যাটিস সহযোগে এক কাপ কফি- সে এক নেভার এন্ডিং ফেয়ারি টেল ! সেই রূপকথা আজো ধরে রেখেছে প্রায় শতাব্দী ছুঁতে চলা এই কেক-বিপণি।
এরা ছাড়াও গোটা পার্ক স্ট্রিট জুড়ে সাহেবি ঘরানার কত বার আর রেস্তোরাঁ। বিফস্টেকের জন্য বিখ্যাত অলিপাব আর মোকাম্বো, এক্লেয়ার স্যুপের রাজা স্কাই রুম, সুরা আর ব্যান্ডের খ্যাতিসম্পন্ন, নীল নিয়নের সেই শেয়াল আঁকা ব্লু ফক্স। এদের মধ্যে সবাই হয়তো ব্রিটিশ জমানার নয়। হয়তো বা কালের গ্রাসে বন্ধও হয়ে গেছে কেউ কেউ তবু এরা প্রত্যেকেই ছিল সাহেবি ঘরানার সফল উত্তরসুরী, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এসব মধুশালা আর সরাইখানায় বিভিন্ন সময় পারফর্ম করে গেছেন পপ জাদুকরী ঊষা আয়ার ( পরবর্তীতে উত্থুপ ), স্যাক্সো উইজার্ড ডোনাল্ড বিশ্বাস, কঙ্গো কিং সোনা ভাই, গিটার মায়েস্ত্রো ল্যু হিল্ট, পিয়ানো অ্যাকরডিয়ানের জাগলার আরিফ আহমেদ, সুরলোকের আরো আরো কত কত সব আশ্চর্য সন্তানেরা। সেই সব মধুর স্মৃতিকে আলবিদা বলে ফের এগোন যাক উত্তরমুখো, চৌরঙ্গীর দিকে।
কে যেন ডাকে বার-এ বার-এ
মেট্রো, লাইট হাউস, গ্লোব, নিউ এম্পায়ার। সায়েবি কলকাতার অতীত গৌরব। কিন্তু আজও স্মৃতিতে উজ্জ্বল তাদের বারগুলোর স্মৃতি। এরমধ্যে মেট্রো। টিকিট কাউন্টার আর ফটো ডিসপ্লের লম্বাচওড়া লনটা টপকে কাচের দরজা ঠেলে ঢুকলেই একটুকরো হলিউড। হিমশীতল এ সির ঠান্ডা। গোড়ালি ডুবে যাওয়া মখমলি কার্পেটে বাঁধানো সিঁড়ি বেয়ে উঠে হলে ঢোকার আগেই হাতের বাঁদিকে সেই বার। দেয়ালে ঝোলানো আভা গার্ডনার, অড্রে হেপবার্ন, সোফিয়া লরেন, স্টুয়ার্ট গ্র্যাঞ্জার, গ্রেগরি পেক, জন ওয়েন, ওমর শরিফ। বিশাল লম্বা বার কাউন্টারের উঁচু টেবিলে বসে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের সঙ্গে বিয়ার মাগে চুমুক। লুকোন সাউন্ডবক্সে পিয়ানোর টুংটাং, অথবা ডিন মার্টিন, ন্যাট কিংকোলের সেই ব্যারিটোন ভয়েস। সেই মেট্রো, আজ অতীতের ধংসস্তূপ। টেন কমান্ডমেন্টস, সাউন্ড অফ মিউজিক, গুড ব্যাড অ্যান্ড আগলিকে সঙ্গে নিয়ে উঠে গেছে লাইট হাউস, গ্লোব, একইসঙ্গে তাদের সেইসব বিখ্যাত বার লাউঞ্জগুলোও। একমাত্র সবেধন নীলমণির মত টিমটিম করে টিকে থাকা নিউ এম্পায়ার। একতলার পুরোটাই বিকিয়ে গেছে হালফিল শহরে আসা সব দেশি-বিদেশি খাবারের দোকানগুলোর কাছে। গোটা হলটাকে ঘিরে ফেলেছে তাদের ঝাঁ চকচকে বিজ্ঞাপনের গ্লো-সাইনবোর্ডগুলো। আসল সিনেমা হলটা কোথায়, কোন সিনেমা চলছে, দোতলার সেই ছোট্ট কিঊট বারটাও কি আর আছে ? সেই ঝুরঝুরে গাঠিয়া আর বাদামওয়ালা চানাচুর সহযোগে বিয়ারপানের আমেজ ? বোঝা যায় না কিছুই। বদলে শঙ্খবাবুর সেই – ‘মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে’ কবিতাটার কথা মনে পড়ে যায় বারবার।

গ্লোব, নিউ এম্পায়ার, লাইট হাউস চত্বরে ঘোরাফেরা করব আর পুরোন নিউ মার্কেটে একবার ঢুকব না, এ কখনও হতে পারে! মার্কেটের একদম পিছনে কেক গলি। পুরো গলিটা জুড়ে হাজাররকম কেক-পেস্ট্রির মেলানোমেশানো সেই স্বর্গীয় নিওলিথ সুবাস ! গলির প্রায় শেষপ্রান্তে নাহুম। বহিরাঙ্গে ও ভিতরে বহু পুরোন সব কাঠের কারুকাজ। এ শহরের কেক কিংবদন্তী। ১৯০২ সালে দোকানটি প্রতিষ্ঠা করেন নাহুম ইজরায়েল মোরদেকাই নামে এক ইহুদী ভদ্রলোক। অনতিবিলম্বেই গোটা শহরবাসীর কাছে প্রচন্ড জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এই কেক বিপণি। এদের ফ্রুট কেক, পাম কেক, প্লেইন কেক, চিজ কেক, চিজ পাফ, চিজ স্ট্র, লেমন টার্ট, রাম বল, ব্ল্যাক ফরেস্ট, পাইনঅ্যাপল পুডিং, প্যাটিস, ব্রেডলোফ আর অসংখ্য ধরনের ধরণের পেস্ট্রি – সবাই যাকে সেই হিন্দি সিনেমার ভাষায় বলে – ‘এক সে বাঢ় কর এক !’ একশ কুড়ি বছরের কাছাকাছি হতে চলল – কলকাতায় সাহেবি খানাপিনার সেই কেতা আজও ধরে রেখেছে নাহুম। তবে মাঝখানে একবার আশংকার কালো মেঘ জমেছিল এ দোকানের ভবিষ্যতের ওপর। দোকানের তৃতীয় প্রজন্মের মালিক ডেভিড নাহুম মারা যাবার পর এ শহরের নাহুম প্রেমিকরা ভেবেছিলেন এবার হয়তো….কারণ ডেভিড সাহেব ছিলেন নিঃসন্তান। কিন্তু তাদের সেইসব আশঙ্কাকে অমূলক প্রমাণ করে ইজরায়েল থেকে চলে আসেন ডেভিডের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং কর্মচারীদের অকুন্ঠ সহযোগিতায় সচল রাখেন শতাব্দী প্রাচীন এই প্রতিষ্ঠানটিকে। দীর্ঘজীবী হোক নাহুম!

তবে শহরের কিংবদন্তী খাদ্য প্রতিষ্ঠান মানচিত্রে নাহুম রয়ে গেলেও মিলিয়ে গেছে ওই নিউ মার্কেটেই জার্মান এবং পর্তুগীজ কেক অ্যান্ড লোফ ঘরানার দুই শহরবিখ্যাত দোকান। ওয়েস বেকারি আর মাক্স ডি গামা কনফেকশনার্স, যা অধিক পরিচিত ছিল ম্যাক্সো নামেও। দশ থেকে আশির দশক অবধি নাহুমের সঙ্গে খ্যাতি ও বিক্রির প্রশ্নে রীতিমত প্রতিযোগিতা চলতো এই দুই দোকানের। সম্ভবত ৮০র দশকের শেষভাগে প্রায় গায়ে লেগে লেগে বন্ধ হয়ে যায় এই দুই প্রবাদপ্রতিম কেক-বিপনি। এ দুঃখ যাবার নয় কিছুতেই।
সেটা ষাটের দশক। এই অধম তখন প্রাইমারি স্কুল। মনে আছে শীতকালে অ্যানুয়াল পরীক্ষার রেজাল্ট মোটামুটি একটু ভদ্রস্থগোছের হলে মেট্রোয় সাড়ে নটার মর্নিং শোয়ে সিনেমা দেখাতে নিয়ে যেত বাবা। মিকি অ্যান্ড ডোনাল্ড, টারজান দ্য এপম্যান, ড্রামস অফ ডেস্টিনি, মেরি পপিন্স… আরো কত সব জাদু সিনেমা। শো শেষে উপরি পাওনা হলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কোয়ালিটি, ম্যাগনোলিয়া বা জলি চ্যাপের আইসক্রিম আর নিউ মার্কেটে কেক গলির পেস্ট্রি। ঠিক এইরকম একটা দিনে আমাকে সোডা ফাউন্টেইন শপের গল্প শুনিয়েছিল বাবা। বিভিন্ন ধরনের ফলের স্বাদে ছাড়াও আরো অনেক কিসিমের সুগন্ধী সোডা পাওয়া যেত সেখানে। সারাবছর বিশেষ করে গরমকালে সোডাপ্রেমীদের ভিড় উপচে পড়ত ফাউন্টেইন শপে। চৌরঙ্গী রোড আর এস এন ব্যানার্জি রোডের মোড়ে বাড়িটার মাথায় যেখানে এক মানুষ সমান উঁচু চায়ের কাপে চা ঢালতো লিপটন কোম্পানির দু মানুষ সমান উঁচু চায়ের কেটলি, সেদিকেই কোথাও একটা আঙুল দেখিয়ে বাবা বলেছিল – ওখানেই ছিল দোকানটা। উঠে গিয়েছিল সম্ভবত এই অধম প্রতিবেদকের জন্মের আগেই।
সেই কবেকার কথা। পরে ভাবতাম – ধ্যুত ! ও আমারই স্মৃতিবিভ্রম। ওই ছেলেবেলায় কী শুনতে কী শুনেছিলাম। ভুল ভাঙ্গল বছর দুতিনেক আগে। ১লা বৈশাখ, বাংলা নববর্ষের দিন। কলেজ স্ট্রিটে দেখা লেখিকা ঋতা বসুর সাথে, সঙ্গী এক মধ্যবয়েসি বিদেশিনী। সম্ভবত ইংরেজ। কলকাতায় উনিও খুঁজে বেড়াচ্ছেন সেই সোডা ফাউন্টেন শপ। ওনার পিতৃদেব ছিলেন কলকাতায় ব্রিটিশ রাজ কর্মচারী। উনিও নাকি নিয়মিত যেতেন চৌরঙ্গীর সেই সোডা ফাউন্টেইন শপে। শোনামাত্র কেন জানিনা কাজীসাহেবের ওই গানটার কথা মনে পড়ে গেছিল – ‘তোমার মহাবিশ্বে কিছু হারায় না তো প্রভু।’ অতঃপর চটকাটা কাটিয়ে মেমসায়েবকে ততটুকুই বলতে পেরেছিলাম ঠিক যতটুকু লিখেছি এখানে। উনি কিঞ্চিৎ হতাশ হয়েছিলেন বটে। তবে একইসঙ্গে বিদেশিনীর চোখের কোনে চোরা খুশির ঝিলিকটা বলে দিয়েছিল – ‘যাক ! এ শহরে অন্তত একজন তো আছে যে আমার বাবার গল্পের ওই সোডা শপটা চেনে।’
পরবর্তীতে অনেক তত্বতালাশ করেও ওই দোকানের সম্বন্ধে আর কিচ্ছু জানতে পারিনি। যদি কেউ এব্যাপারে কিছু জানেন, জানাবেন অবশ্যই, এই অধমের তথ্যভান্ডার আরেকটু স্ফীত হবে।
চিনে পাড়াকে চিনে নিন
সেন্ট্রাল অ্যাভেন্যুয়ের ওপর প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিটের গলিতে বাঁক নেয়ার মুখে চাং ওয়া। এ শহরের আদিতম যত চৈনিক রেস্তোরাঁগুলির মধ্যে একটি। একই সঙ্গে অত্যন্ত সস্তায় বিদেশী মদ বিপণনের কারনে মধ্যবিত্ত ও অফিস কর্মচারীদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় প্রাচীন এই সরাইখানা। ১৯২৮ সালে যাত্রা শুরু। তবে এরও আগে, ১৯২২ সালে গনেশ অ্যাভেন্যুয়ে ‘ইয়াউ চিউ’ নামে একটি ছোট হোটেল খুলেছিলেন চাং ওয়ার মালিকরা। যদিও সেটি ছিল মুলত এদেশে আগমনকারী চিনা সম্প্রদায়ের জন্য। চাং ওয়ার হাত ধরেই এই রেস্তোরাঁ আক্ষরিক অর্থে সার্বজনীন হয় এবং অতি দ্রুত জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছোয়। অতঃপর এস ওয়াজেদ আলির ভাষায় – ‘সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে।’ আজও গ্রাহকদের রসনায় সমান জনপ্রিয় এদের চিমনি ডাক স্যুপ, মিট বল স্যুপ, চিকেন উইথ সয়া সস, চিকেন উইথ ওয়াইন সস, ফ্লেমিং ফিশ, ফিশ উইথ রেড চিলি অ্যান্ড ব্ল্যাক বিনসের মত জিভে জল আনা অসামান্য সব খাদ্যপদ।
সম্পূর্ণভাবে একটি চিনা ক্রিশ্চান পরিবারের পরিচালনাধীন এই রেস্তোরাঁ। পরিবারের মধ্যে মূলত তিনজন – মিসেস জোসেফাইন ও তাঁর দুই ছেলেমেয়ে জোয়েল ও জেনিফারই ব্যবসাটা সামলান। তাদের মায়ের নামে রেস্তোরাঁর একটি পদের নামকরণ করেছেন জোয়েল ও জেনিফার। জোসেফাইন নুডলস। চাং ওয়া প্রেমীদের কাছে সেটিও প্রচন্ড জনপ্রিয়। তাহলে আর কি ? চিল্ড বিয়ার আর ফ্লেমিং ফিশ সহযোগে একদিন হয়ে যাক চাং ওয়া।

লালবাজারের গায়ে পোদ্দার কোর্ট। পোদ্দার কোর্টের হাত ঘেঁষে মিটার পঁচিশেক এগোলেই টেরিটি বাজারের ওপর নান কিং। পুরোন চিনা স্থাপত্যের উপাসনালয়ের ধাঁচে তৈরি বিশাল লাল ইঁটের ইমারত। কলকাতা শহরে আদিতম চীনে খাবারের ঠিকানা সম্ভবত এটিই। জন্ম ১৯২৪ সালে। কেউ কেউ তর্ক তুলতেই পারেন – কেন ? গনেশ অ্যাভেন্যুয়ে ইয়াউ চিউয়ের জন্ম তো এর দুবছর আগেই। তাদের বলি – আরে বাবা সেটা তো আর সর্বসাধারনের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। শুধুমাত্র এদেশে আসা চিনা সম্প্রদায়ের মানুষজনেরই যাতায়াত ছিল সেখানে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে নান কিংয়ের হাত ধরেই চৈনিক আহার সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘটে শহরবাসীর। অসামান্য সব রন্ধন -শৈলীর জন্য এ রেস্তোরাঁর নাম ছড়িয়েছিল কলকাতার সীমা ছাড়িয়ে সেই সুদূর বম্বে (তখনও মুম্বাই হয়নি) অবধি। কলকাতায় এলে দিলীপকুমার, রাজ কাপুরের মত সুপারস্টাররা প্রায় নিয়মিত আসতেন এখানে। সাহিত্যিক সুনীল গাঙ্গুলীরও অত্যন্ত পছন্দের রেস্তোরাঁ ছিল এই নান কিং। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সদস্যরা বিশেষ করে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাকি খুব পছন্দ করতেন নান কিংয়ের খাবারদাবার – এ অঞ্চলের এক প্রবীণ সহ নাগরিক হং ম্যান একদা আমাকে বলেছিলেন একথা।
এ রেস্তোরাঁর দোতলায় ছিল একটি চৈনিক মনস্ট্রি বা উপাসনালয়। তথাগত বুদ্ধ আর চৈনিক এক যুদ্ধ দেবতার মূর্তি ছিল (এখনও আছে) এই প্রার্থনাস্থলে। রেস্তরাঁর মালিক আউ পরিবার ছিলেন এই উপাসনালয়ের ট্রাস্টি অর্থাৎ দেবোত্তর সম্পত্তির দেখভালকারী। টেরিটিবাজার শহরের পুরোন চিনা অধ্যুষিত এলাকা। কিন্তু এলাকার চিনা অধিবাসীদের প্রবেশাধিকার ছিলনা এই উপাসনালয়ে। এ নিয়ে তাদের মনে প্রচন্ড ক্ষোভ ছিল দীর্ঘদিন ধরে।
ষাটের দশকের শেষভাগ থেকেই সম্ভবত ওই নকশাল আন্দোলনের কারণেই নান কিংয়ে খাদ্যরসিকদের ভিড় কমতে থাকে দ্রুতহারে। লোকসানের মুখে পড়ে প্রাচীন এই রেস্তোরাঁ। এরকম চলতে চলতে ৭০ সালের মাঝামাঝি বন্ধই হয়ে যায় নান কিং। এর কিছুদিনের মধ্যেই আউ পরিবারের নামে নানারকম অভিযোগ আসতে থাকে এলাকার চিনা বাসিন্দাদের কাছে। রেস্তোরাঁ এবং মন্দিরের প্রাচীন এবং বহুমূল্য সব ভাস্কর্য নাকি খুব গোপনে বিক্রি করে দেয়া হচ্ছে অ্যান্টিক ডিলারদের। আরো কিছুদিনের মধ্যেই অভিযোগ আরো গুরুতর। পুরো সম্পত্তি ওই অঞ্চলের এক কুখ্যাত বাহুবলী তথা প্রোমটারের কাছে বেচে দিয়ে বিদেশে পাড়ি জমাতে চাইছে আউ পরিবার। এবার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের। আদালতের দারস্থ হন তারা। অবশেষে ২০১০-১১ সাল নাগাদ কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে উপাসনালয়ে প্রবেশের অধিকার পান সাধারণ মানুষ, বিশেষত এলাকার চিনা সম্প্রদায়।
নান কিং নিয়ে বেশ কয়েকটা অতিরিক্ত বাক্য লিখলাম কারণ স্রেফ একটা মন্দির থাকার কারণে কীভাবে বেঁচে গিয়েছিল প্রায় শতাব্দীপ্রাচীন একটি রেস্তোরাঁর ইমারত, সেটা জানা দরকার পাঠকদের। সারা ভারতে প্রচুর নামীদামী চিনা রেস্তোরাঁ দেখেছি , খেয়েছিও কোন কোনটাতে। সশরীরে না গিয়েও সারা দুনিয়ার অজস্র চিনা তথা মোঙ্গলিয় ঘরানার রেস্তোরাঁর ছবি দেখেছি অন্তর্জালে। নান কিংয়ের মত উপাসনালয় এবং রেস্তোরাঁর সংমিশ্রনে তৈরি এরকম সুবিশাল প্রাচীণ ভাস্কর্যসমৃদ্ধ একটা স্থাপত্য চোখে পড়েনি কোথাও। এই পর্যন্ত পড়ে যাদের মনে হচ্ছে অতিশয়োক্তি করছি, দয়া করে একদিন যান ওখানে। নাই বা হোল কলকাতার প্রথম চৈনিক রেস্তোরাঁয় খাওয়া, ওরকম একটা প্রাচীণ ইতিহাসের সামনে তো দাঁড়ানো যাবে।
পরিশেষে…
এ প্রতিবেদনের একদম গোড়ার দিকেই লিখেছিলাম শুধুমাত্র ইংরেজ ঘরানা নয়, একটা বিশাল আন্তর্জাতিক আবহের দরজা খুলে দিয়েছিল ব্রিটিশ আমল। বিশেষত এ শহরের খাদ্য সংস্কৃতিতে। ব্রিটিশ, জার্মান, সুইস, ইতালিয়ান, পর্তুগিজ, চিনা, ইহুদি, আরমানি, এরকম কত যে ধারা এসে মিশেছিল এ কলকাতা নামক মহাসমুদ্রে তার ইয়ত্তা নেই। এ যেন ঠিক সেই কবির ভাষায় – ‘শক হুন দল পাঠান মোগল / এক দেহে হল লীন।’ এই অধম প্রতিবেদকের পুরো লেখাটা একটু মন দিয়ে পড়লেই আশা করি সেটার যৌক্তিকতা প্রমাণিত হবে। এ পর্যন্ত পড়ে কেউ প্রশ্ন তুলতেই পারেন – কেন ? এব্যাপারে কলকাতা কি এখন আন্তর্জাতিক নয় ? থাই, মেক্সিকান, লেবানিজ, আফগানি, কতরকম খাবারের হোটেল রেস্তোরাঁ হয়েছে চারপাশে। হররোজ গজিয়েও উঠছে কতশত। বিদেশি খাবার খেতে এখন আর কষ্ট করে চৌরঙ্গী পার্ক স্ট্রিট দৌড়োতে হয় না। পাড়ার মোড়ের ফুড জয়েন্টেই পাওয়া যায়। প্রশ্নের উত্তরে সবিনয়ে বলি – সেটা ঠিকই তবে একটা ব্যাপার কি জানেন, এই পুরো ব্যাপারটার মধ্যেই কেমন যেন একটা ওপরদেখানো, মেকি, দোআঁশলা ফিউশন জাতীয় মার্কিন ইয়াঙ্কি ইয়াপ্পি সংস্কৃতির ছোঁয়া, পুরনো দিনের সেই ব্রিটিশ আভিজাত্যটা একেবারেই অনুপস্থিত যেখানে। তবে এটা প্রতিবেদকের একান্তই নিজস্ব ধারনা বা মতামত। কোনওরকম বিতর্ক উসকে দেওয়ার ন্যুনতম অভিপ্রায় নেই সেখানে।
দ্বিতীয় প্রশ্নটা মাথাচাড়া দিয়েছে নিজের মধ্যেই। নকশাল আন্দোলনই কি একমাত্র কারণ যার ফলে চৌরঙ্গী-পার্ক স্ট্রিট বলা ভাল কলকাতার নাইট লাইফটাই ওভাবে ধ্বংস হয়ে গেছিল? হাজার চেষ্টাতেও যা আর পুরোপুরি জোড়া লাগেনি কোনওদিন। উত্তরটাও খোঁজার চেষ্টাও করেছি সেই নিজের মধ্যেই। আরও একটা সম্ভাব্য কারণ উঠে আসছে সেখান থেকেই। হোটেল রেস্তোরাঁ ব্যবসার ওপর চাপিয়ে দেয়া অতিরিক্ত করের ভারবোঝা, ক্যাবারে নাচের ওপর নিষেধাজ্ঞা, এসব নিয়ে আলোচনার পরেও যা বলা হয়নি সেটা একটা ম্যাসিভ এক্সোডাস! এক ব্যাপক নিস্ক্রমণ। স্বাধীনতার পর দলে দলে চীনা, আরমানি , ইহুদি, পার্শি, পর্তুগীজ, পর্তুগীজ ভারতীয় (লুসো ইন্ডিয়ান), ইতালিয়ান, রেসিডেন্সিয়াল ব্রিটিশ, অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের দলে দলে এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়া, যার ফলে এই শহরের কসমোপলিটান ক্যারেক্টার অর্থাৎ মিশ্র বহুজাতিক চরিত্রটা হারিয়ে গেছিল বরাবরের জন্য। চলে যাওয়ার কারণ একাধিক। চিন-ভারত যুদ্ধ, ইজরায়েলের নির্মাণ, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, হংকং, একাধিক উন্নত দেশে নাগরিকত্ব আর সুখী জীবনের হাতছানি, এই সমস্ত কারণ একসঙ্গে মিলেমিশে বিষদাঁত বসিয়ে দিয়েছিল এ শহরে সাহেবি আমলের খানাপিনা সংস্কৃতি তথা নৈশজীবনের ওপর – দুর্ভাগ্যজনক হলেও মানতেই হবে এই ভীষণ অপ্রিয় সত্যটা।
জন্ম ও বেড়ে ওঠা উত্তর কলকাতার পুরোনো পাড়ায়। বহু অকাজের কাজী কিন্তু কলম ধরতে পারেন এটা নিজেরই জানা ছিল না বহুদিন। ফলে লেখালেখি শুরু করার আগেই ছাপ্পান্নটি বসন্ত পেরিয়ে গেছে। ১৪২১ সালে জীবনে প্রথম লেখা উপন্যাস 'দ্রোহজ' প্রকাশিত হয় শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় এবং পাঠকমহলে বিপুল সাড়া ফেলে। পরবর্তীতে আরও দুটি উপন্যাস 'জলভৈরব' (১৪২২) এবং 'বৃশ্চিককাল' (১৪২৩) প্রকাশিত হয়েছে যথাক্রমে পুজোসংখ্যা আনন্দবাজার এবং পত্রিকায়। এছাড়া বেশ কিছু প্রবন্ধ এবং দু চারটি ছোটগল্প লিখেছেন বিভিন্ন পত্রপত্রিকা আর লিটিল ম্যাগাজিনে। তার আংশিক একটি সংকলন বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে 'ব্যবসা যখন নারীপাচার' শিরোনামে। ২০১৭ সালে পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পুরস্কার।



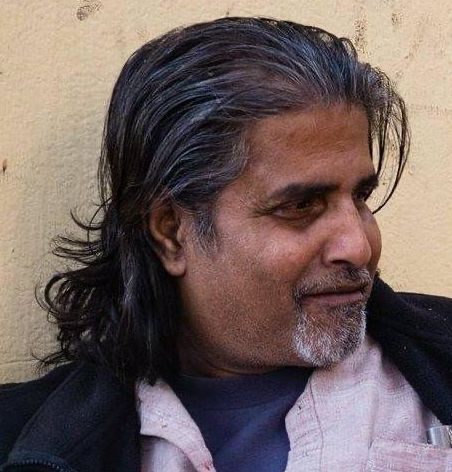
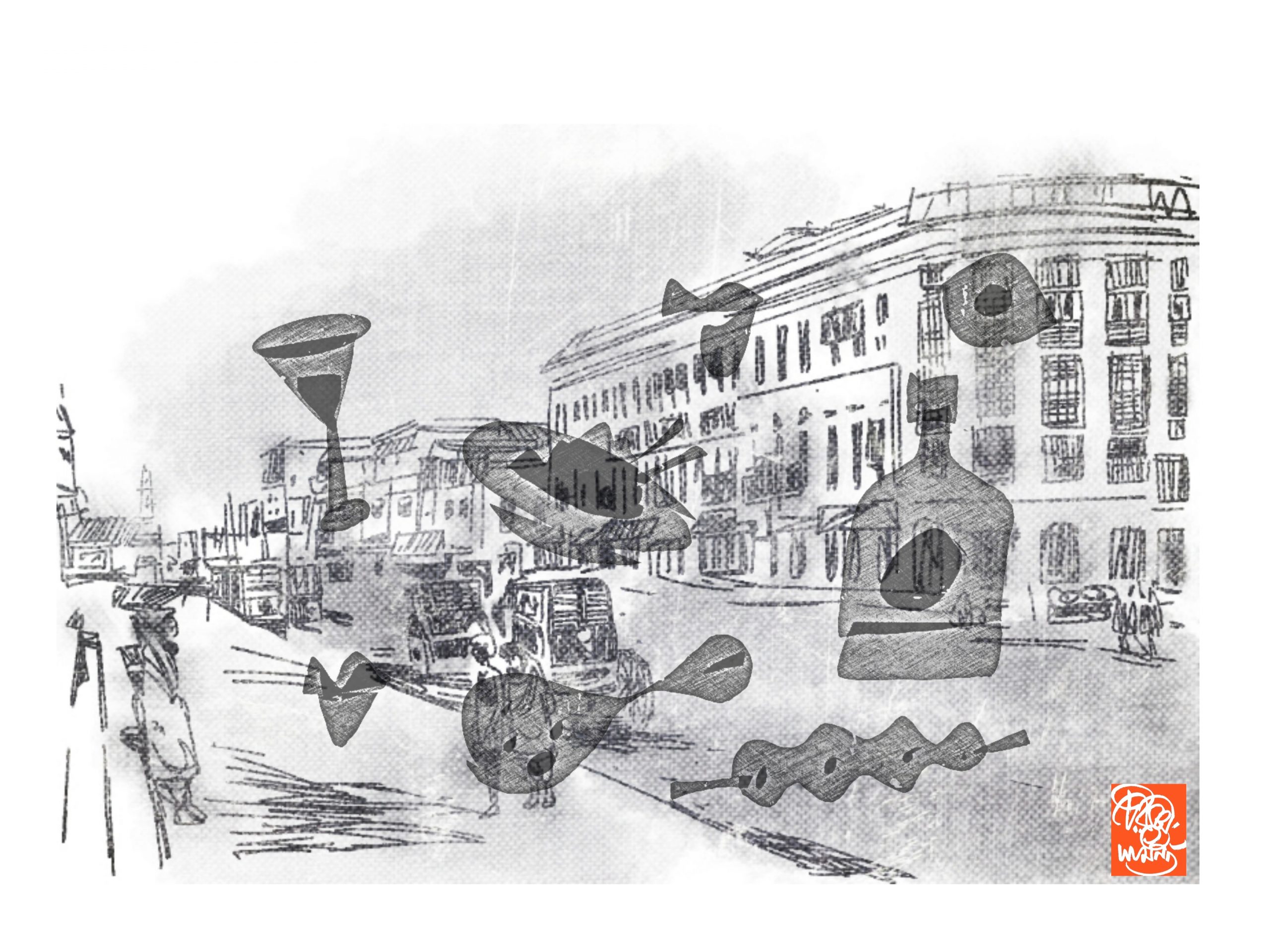
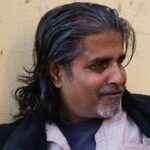
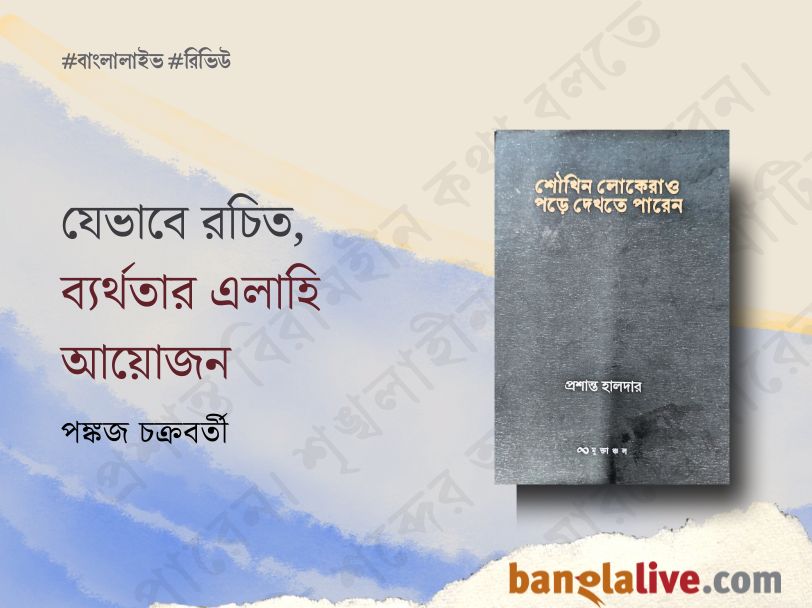
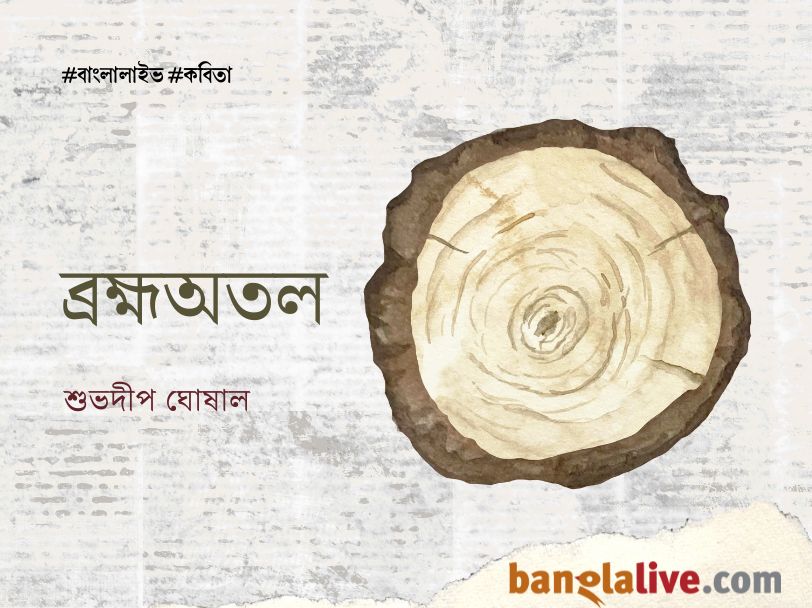
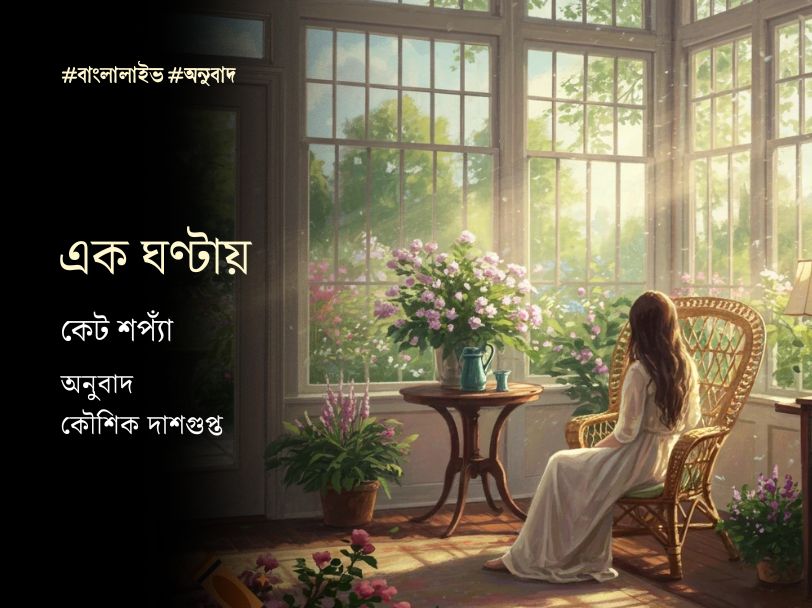

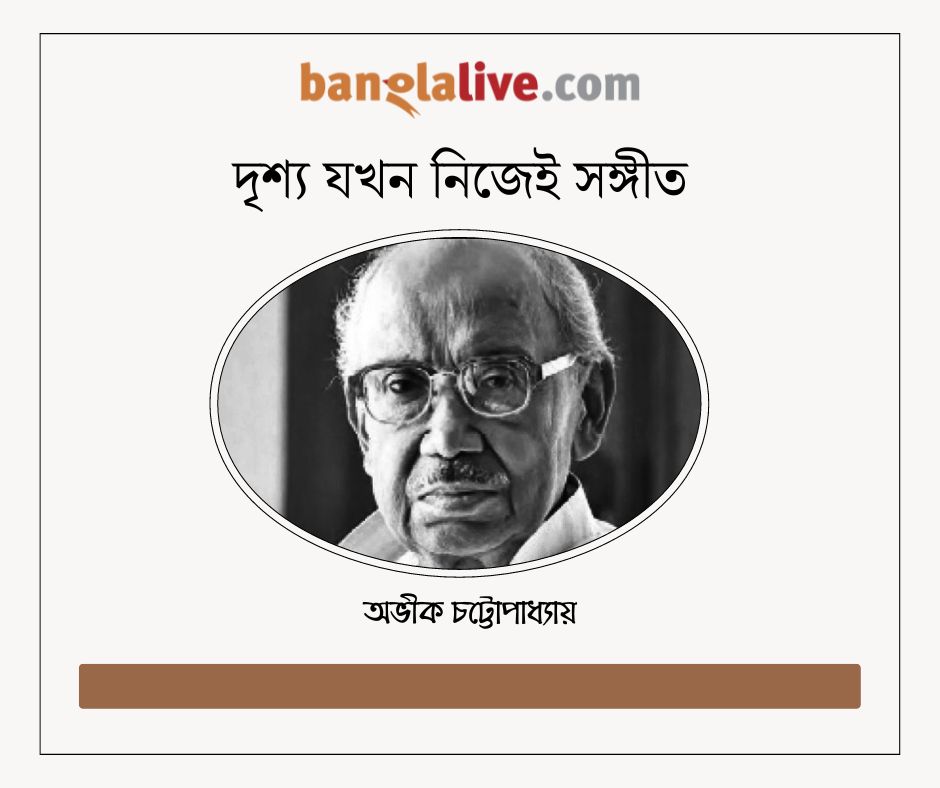

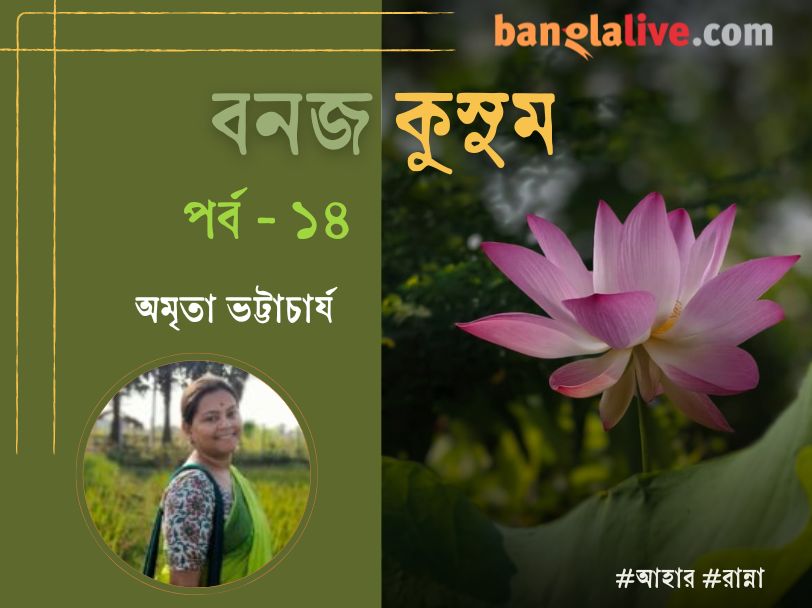

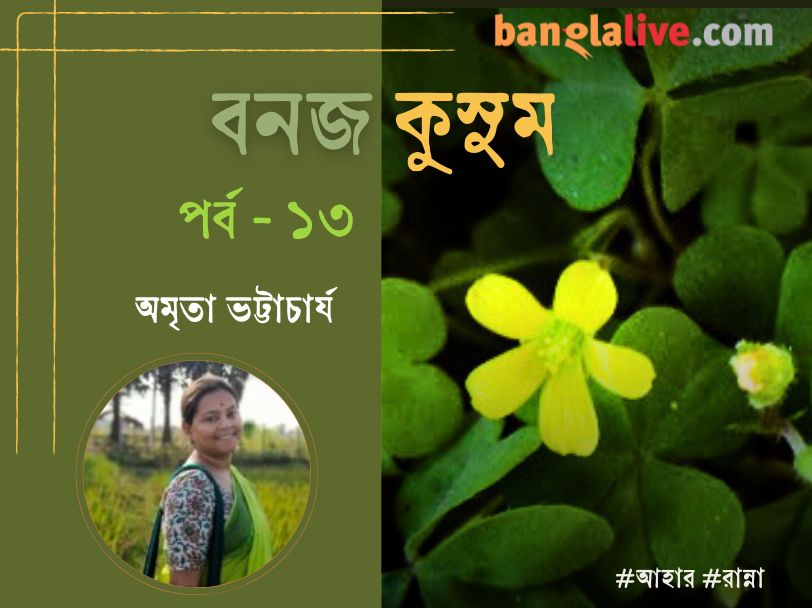

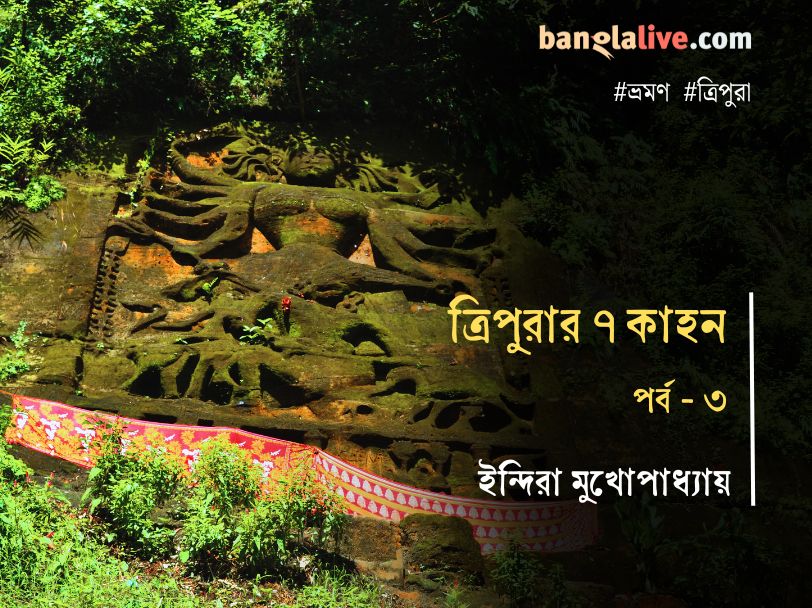
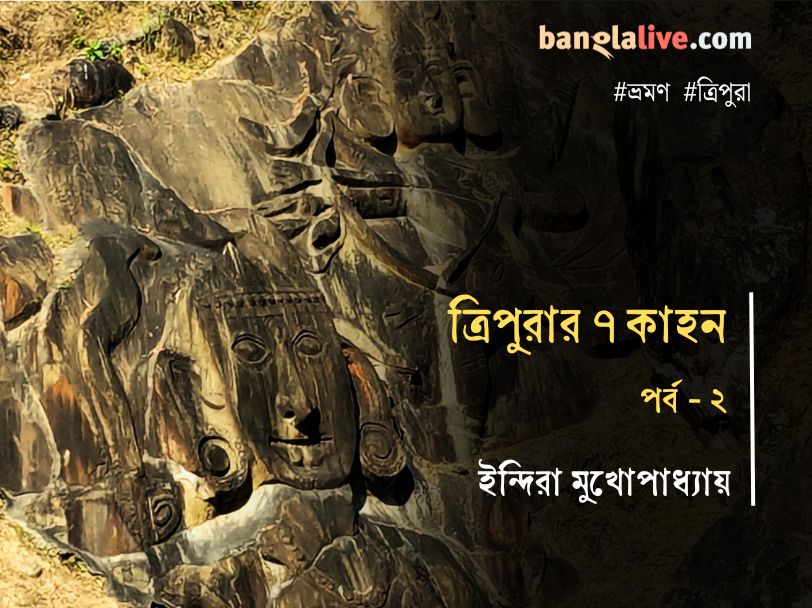
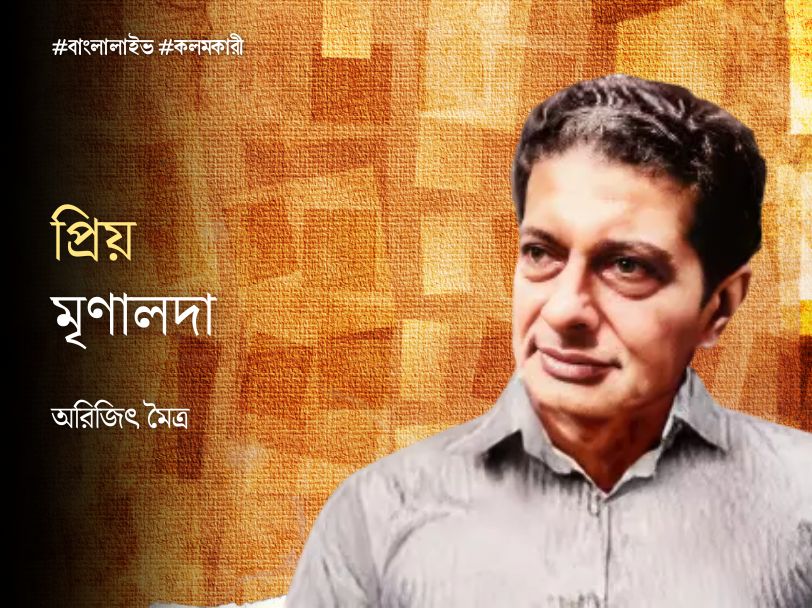

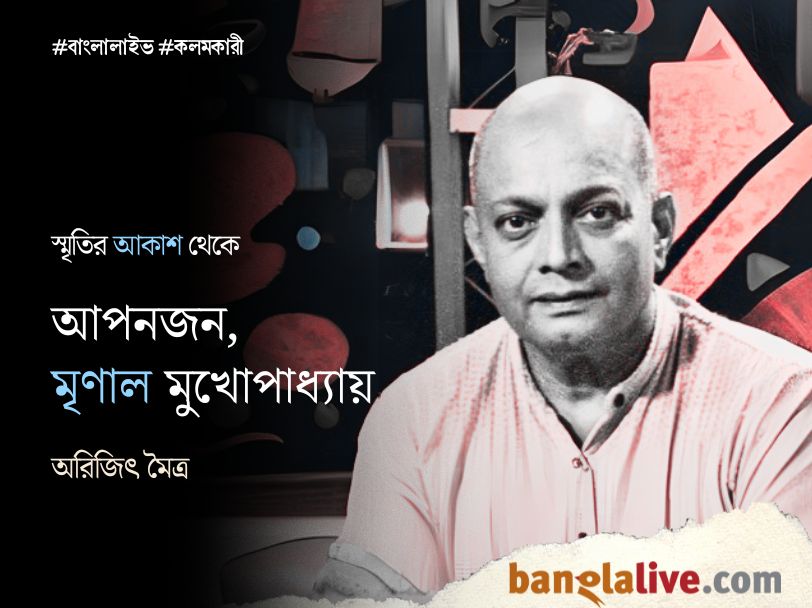



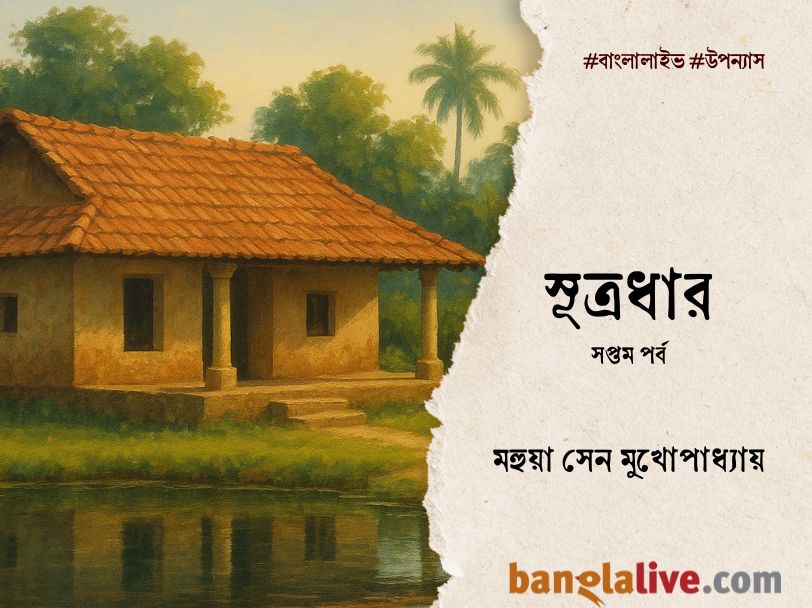
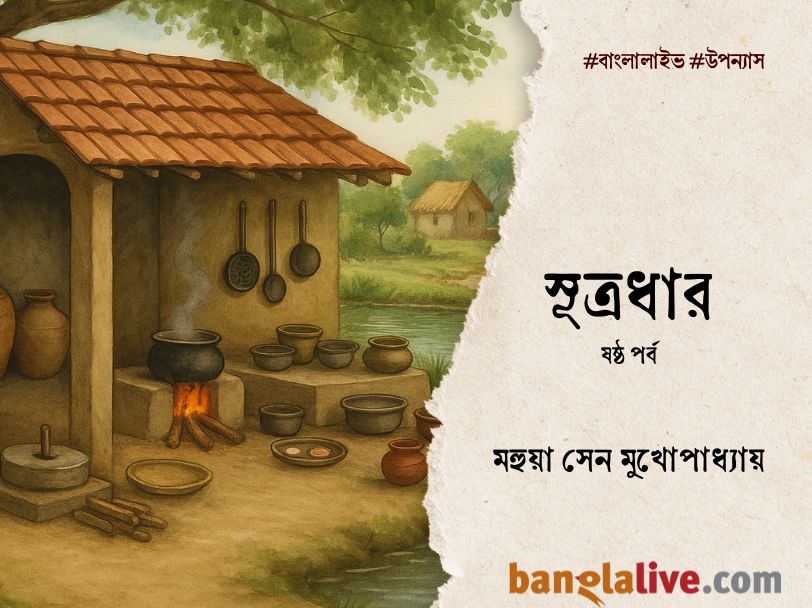
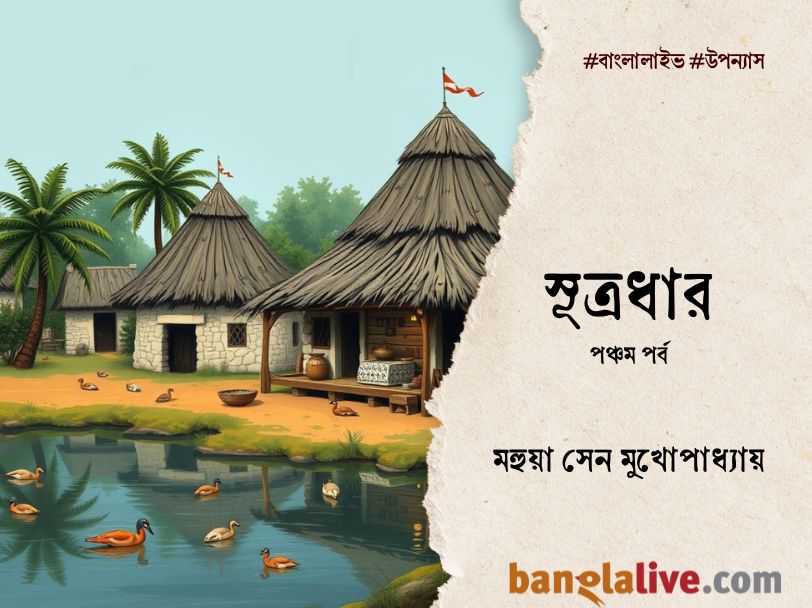
4 Responses
লেখাটা তো একটা এপিক হয়ে উঠলো, এই ইতিহাস হয়তো বেশ কয়েকজনের কাছে আজ আছে, কিন্তু এই বয়ান ? সাহেব কলকেতার খানা পিনা নিয়ে ধারাবাহিক হোক
বাহ বাহ দলিল একখানা
Darun sundor lekha…onek kichu jante parlam….aremnian khabar somporke kichu jante chai
opurbo lekha, kichuta jantam, onekta ojana